দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অবদান আলোচনা কর।
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) ছিলেন রবীন্দ্রযুগের ব্যতিক্রমী কবিব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথের অবিরল অতীন্দ্রিয়তার পরে যতীন্দ্রনাথের একটা বিদ্রোহ তাঁকে কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। রোমান্টিকতার বিলাসকুঞ্জ থেকে কবিতাকে যতীন্দ্রনাথ নিয়ে এলেন দুঃখদীর্ণ বাস্তবের প্রাত্যহিক আবর্তের মাঝখানে। রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে বর্ধিত হয়েও রবীন্দ্র পথ পরিহারী যতীন্দ্রনাথের জীবন জিজ্ঞাসার কেন্দ্রে যে বিশিষ্ট ভাবদৃষ্টি রয়েছে তাকে দুঃখবাদ নামেই অভিহিত করা যায়। অর্থা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দুঃখবাদী কবি—কথাটা অস্বীকারের উপায় নেই। কেননা কবির প্রকৃতি চেতনা, রোমান্টিক সৌন্দর্যের বিরোধিতা, ঈশ্বরবোধের বিশিষ্ট প্রকাশ এবং মানবপ্রেম এই দুঃখবাদী দর্শনের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। এর উৎসমূলে অবশ্য নানা কারণ বিদ্যমান। এঁদের সকলের সক্রিয়তা হয়তো সমস্তরের নয়, কিন্ত এঁদের যৌথ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই যে তাঁর মানসিকতা গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।
প্রথমেই যুগ পরিবেশের কথা ধরা যাক। তখন সমসাময়িক ইউরোপে এবং তার প্রভাবে বাংলাদেশেও জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ আস্তিক্যবোধ এবং বিশ্বাস ক্ষয়িষ্ণুতার মুখে। বিংশ শতক সর্বত্রই জিজ্ঞাসার এবং সংশয়ের যুগ। মঙ্গলবোধ, নিবিড় আধ্যাত্মিকতা, ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি, মানবতার জয়গান, সুন্দরের ধ্যান—ঊনবিংশ শতকের এই যে জীবনবোধ তার ভিত্তিতে সুস্পষ্ট ফাটল ধরেছিল। যতীন্দ্রনাথের কাব্যে এর প্রতিক্রিয়া সহজেই লক্ষ করা যায়।
তবুও বলা যায়, এই যুগ পরিবেশে যতীন্দ্রনাথ দুঃখবাদের কবি নাও হতে পারতেন। কারণ সমকালীন অন্যান্য কবিদের যুগচেতনা ঠিক তাঁদের কাব্যে এভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। আসলে, যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিচেতনার গভীরে জীবনকে দেখার এমন একটা ভঙ্গি দানা বেঁধেছিল যাকে দার্শনিক পরিভাষায় জড়বাদ নামে চিহিত করা যায়। মানুষের প্রত্যক্ষ জীবনসত্যকে সমস্ত বোধ এবং চিন্তার নিয়ামক বলে মনে করেছিলেন তিনি। তাই যুগ পরিবেশ এবং মানবজীবন ও আদর্শের বিপর্যয় তাঁর চিত্তকে এত গভীরভাবে নাড়া দিতে পেরেছিল। চেতনাবাদী হলেও যুগচিন্তা সংকটকে পরমহংসের মতো তিনি সহজেই অতিক্রম করতে পারতেন।
যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ যতটা দাশনিক জ্ঞানমার্গী, তার চেয়ে অনেক বেশি মানবিকতাভিত্তিক। মানুষের দুঃখ বেদনা, উৎপীড়িত লাঞ্ছিত জীবনকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই দুঃখবাদ। যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ তাই জড়বাদী দর্শন এবং মানবপ্রীতি থেকে উদ্ভূত। তবুও যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ একটা নঞর্থক ধারণা, রবীন্দ্রনাথের মতো দুঃখকে তিনি তত্ত্বলোকের অস্তিবাচক মাহাত্ম্যে উন্নীত করেননি। দুঃখের তপস্যায় যে মহান সত্যলাভ ঘটে, যতীন্দ্রনাথের কাছে তা ছিল ভাবালুতা মাত্র।
যতীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলি হল— ‘মরীচিকা’ (১৯২৩), ‘মরুশিখা’ (১৯২৭), ‘মরুমায়া’ (১৯৩০), ‘সায়ম’ (১৯৪০), ‘ত্রিযামা’ (১৯২৮), ‘অনুপূর্বা’ (১৯৪৬), ‘নিশান্তিকা’ (১৯৫৭)। এই সাতটি কাব্যের মধ্য দিয়েই আমরা যতীন্দ্রনাথের মানস ভাবনাটাকে আবিষ্কার করতে পারব।
কবি তাঁর ‘মরীচিকা’, ‘মরুশিখা’, ‘মরুমায়া’ কাব্যে কবিমন ভালোবাসাহীন জীবনের কঠিন দুঃখকেই ব্যক্ত করেছেন রঙ্গপরিহাসময় বক্রোক্তিতে। তাঁর শেষ তিনটি কাব্য ‘সায়ম’ ‘ত্রিযামা’ ও ‘নিশান্তিকা’ ভিন্ন সুরে হলেও, এই দুঃখের অভিব্যক্তিতেই বিশিষ্টতা লাভ করেছে। অর্থাৎ কবির সমগ্র জীবনদর্শনই গড়ে উঠেছে এই দুঃখবোধকে কেন্দ্র করে। প্রত্যক্ষ সৃষ্টিকে অতিক্রম করে স্রষ্টার সৌন্দর্যকে তিনি উপলব্ধি করতে চাননি; বাস্তবকে কল্পনার দ্বারা পূরণ করে নিতে চাননি। তিনি দেখেছেন, এই সৃষ্টি যদি একখানি কাব্যই হয়, তবে তা অতিশয় অসম্বন্ধ, অসম্পূর্ণ ও খেয়ালখুশিতে পরিপূর্ণ—
জগৎ একটা হেঁয়ালি—
যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খামখেয়ালি।
তই প্রকৃতির বুকেও খেয়ালের শেষ নেই, কোথাও শ্যামল সরস ভূখণ্ডে অজস্র বর্ষণ, আবার কোথাও ফসলহীন মরুভূমিতে বর্ষণহীন দাবদাহ এবং এর মধ্যে সমতাধিধান করার জন্য কেউই নেই। ‘ঘুমের ঘোরে’ কবিতায় সূর্যকে উদ্দেশ্য করে তার সেই বিখ্যাত উক্তি—
তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমায়—কী আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ?
চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি সাহারার বুকে?
তাই যে সর্বব্যাপী দুঃখ তাঁর কবিমনকে আক্রান্ত করেছে, তাকে তিনি আদর্শায়িত করেননি রবীন্দ্রনাথের মতো। অথবা দুঃখবাদী দার্শানিক শোপেনহাওয়ার কিংবা তাঁর অনুরাগী কবি মোহিতলালের দুঃখবোধের সমগোত্রও নয় তাঁর দুঃখ-চেতনা। স্রষ্টার প্রতি ক্রোধ নয়, দারুণ অভিমান তাঁর। ঈশ্বর-অবিশ্বাসী তিনি নন। বলেছেন— ‘স্রষ্টা আছে বা নাই’। ঈশ্বরের প্রতি দারুণ অভিমান নিয়ে তিনি স্পষ্ট বুঝেছেন যেখানে স্রষ্টারর দুঃখের শেষ নেই সেখানে তাঁরই সৃষ্ট বিশ্বপ্রকৃতি বাইরে যতই মোহিনী হোক আসলে তা দুঃখন্ত্রণার মায়াটোপ মাত্র। তাই অভিমানাহত কণ্ঠে কবি উচ্চারণ—
তুমি শালগ্রাম শিলা
শোওয়া বসা যার সকলি সমান তারে নিয়ে রাসলীলা।
সমস্ত দেখেশুনে কবির মনে হয়েছে এই বিশ্ববহ্মাণ্ডে কোন শৃঙ্খলা নেই, জগৎ প্রকৃতিতে কোন সুস্পষ্ট অর্থ নেই; সবটাই যেন ধোকাবাজি—
এ ব্রহ্মাণ্ডে নিজ ব্রহ্মেরই লাগেনি কি ভাই ধোঁকা?
‘মরীচিকা’ কাব্যের প্রথম কবিতা ‘বহ্নিস্তুতি’তে যেমন জানিয়েছেন— “সকল জ্বালার সব দীপ্তির পরিণাম শুধু ছাই” তেমনি প্রেমকেও তিনি দেখেছেন নিষ্ফল দাহন হিসেবে—
যৌবনে আমি করিনু ঘোষণা
প্রেম বলে কিছু নাই
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে
সব সমাধান পাই।
যতীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার প্রধানতম রঙ-ই হল ব্যঙ্গ। তথাকথিত দেশজননীর প্রতি ভক্তিসূচক বুলির অসারতা ব্যক্ত করেছেন কবি ব্যঙ্গরঙিন বেদনায়—
এ দেশকে ফের হাসতে হ’লে প্রচুর লক্ষ্মী-প্যাঁচা চাই।
বাঁচতে হলে হাসা চাই, আর হাসতে হলেও বাঁচা চাই।
ইঞ্জিনিয়ার কৰি যতীন্দ্রনাথের দুঃখ মূলত এই মানুষকে ভালোবাসারই দুঃখ। কণ্ঠে ব্যঙ্গবাণী, হৃদয়ে প্রচণ্ড ভালোবাসা— যতীন্দ্রনাথ সেই বেদনাবিদ্ধ মানবতারই কবি। এই মানবতাই তাঁর ভাষায় এনেছে রসোচ্ছল অমোঘতা। তাই ষড়মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যতীত আর কোন ছন্দোবৈচিত্র্যের সন্ধান করতে হয়নি তাঁকে, শব্দ ব্যবহারে শুচিবাইগ্রস্ততা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছেন তিনি।
যতীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য
- রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার সাহস তাঁর ছিল। তাঁর বিদ্রোহ যতটা না রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে, তার চেয়ে বেশি সমকালীন জগৎ ও জীবনের অসাম্যের বিরুদ্ধে। জীবনে ও সাহিত্যে মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ তাঁর অন্তরের উৎস থেকে উৎসারিত। আসলে কবির মধ্যে ছিল গভীর বেদনাময় আন্তরিকতা।
- তাঁর দুঃখবাদের মূল ভিত্তি ছিল মানুষের প্রতি মমত্ববোধ। দুঃখ যেহেতু ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাই ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বিদ্রোহ, অভিযোগ ও অভিমান। তাই তাঁর দুঃখবোধ একটি বিশেষ জীবনদর্শন।
- যতীন্দ্রনাথের স্টাইল নিজস্ব ও বিশিষ্ট। এই বিশিষ্টতা প্রকাশিত হয়েছে প্রকাশভঙ্গিতে, মানসিকতায়, কাব্যভাষায়।
- কবিতার নির্মিতিতে কবি বলিষ্ঠ সরসতা এনেছিলেন সচেতনভাবেই। শব্দচয়নে, বাক্যগঠনে বাংলা ভাষার প্রকৃত সমৃদ্ধি সাধনে তিনি ঐতিহ্যকে অনুসরণ করলেও ভাষার মধ্যে এনেছেন প্রাণ, তা নির্জীব নয়। ফলে যতীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাব ও ভাষার সম্বন্ধ পাঠককে আকৃষ্ট করে।


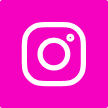


Leave a Reply