অন্ত্য-মধ্য বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা কর।
অন্ত্য-মধ্য বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
অন্ত্য-মধ্য বাংলার স্থিতিকাল ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই যুগের বাংলা ভাষা নানা ধারায় সমৃদ্ধ। যেমন— বৈষ্ণব পদাবলি, চৈতন্যজীবনী, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, আরাকানের মুসলমান কবিদের রচনা ইত্যাদি। এই সব ধারার বিভিন্ন রচনায় এই যুগের বাংলা ভাষার পর্যাপ্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। অন্ত্য-মধ্য যুগের বাংলা ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে সংক্ষেপে সূত্রবদ্ধ করা হল—
ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
(ক) পদের অন্তে একক ব্যঞ্জনের পরে অবস্থিত অকার লোপ পেল। যেমন—
আর শুন্যাছ আলো সই গোরাভাবে কথা
কোণের ভিতর কুলবধূ কান্দা আকু তথ্য।
(খ) পদের অন্তে যুক্তব্যঞ্জনের পরে অবস্থিত অকার লোপ পায়নি, উচ্চারিত হত। যেমন—
মিছা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাষবাস
অন্নবস্ত্র কতেক যোগাইব বারো মাস।
মুকুন্দ চক্রবর্তী
(গ) পদের অন্তে অবস্থিত একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী অ-কার-ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনিও রক্ষিত হয়েছে, লোপ পায়নি। যেমন—
বিশেষে বামন জাতি বড় দাগাদার।
আপনারা এক জপে আরে বলে আর।।
ভারতচন্দ্র
(ঘ) আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দমধ্যস্থ স্বর অনেক সময় লোপ পেয়েছে। যেমন— হরিদ্রা > হলদি।
(ঙ) অন্ত্য-মধ্য যুগে শব্দমধ্যস্থ ‘ই’ ও ‘উ’ অপিনিহিতি বা বিপর্যাসের প্রক্রিয়ায় কখনো কখনো তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে সরে এসেছে। ‘উ’ কখনো কখনো ‘ই’-তে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন— বেগুন > *বেউগণ > বাইগণ।
শাক বাইগণ মূলা আট্যা-থোড় কাঁচকলা
সকলে পুরিয়া লয় পাতি।।
মুকুন্দ চক্রবর্তী
(চ) মহাপ্রাণ নাসিক্য (অর্থাৎ বর্গের হ-যুক্ত পঞ্চম বর্ণ) অল্পপ্রাণ (অর্থাৎ বর্গের হ-বিহীন পঞ্চম বর্ণ) হতে আরম্ভ করেছিল আদি-মধ্য যুগের বাংলাতেই; অন্ত্য-মধ্য যুগে এই প্রবণতা ব্যাপকতর হল। যেমন— আহ্মি > আমি, তুহ্মি > তুমি, আহ্মার > আমার, তোহ্মার > তোমার ইত্যাদি।
রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
(ক) আদি-মধ্য বাংলায় সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুস্বচনে ‘রা’ বিভক্তির প্রয়োগ সূচিত হয়েছিল। অন্ত্যমধ্য বাংলায় এই রা বিভক্তি বিশেষ্যেরও কর্তৃকারকের বহুবচনে প্রযুক্ত হতে আরম্ভ করে। এছাড়া গুলা, গুলি বিভক্তির প্রয়োগ নির্দেশক বহুবচনে তো হতই, অনির্দেশক বহুবচনেও হত। যেমন—
কে বলে শারদ শশী ও মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে আছে তার কতগুলা।।
ভারতচন্দ্র রায়
(খ) ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল— র, এর ইত্যাদি। যেমন—
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে।।
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।
জ্ঞানদাস
(গ) –য়, – এ, – তে সপ্তমী বিভক্তি রূপে প্রযুক্ত হতে থাকে। যেমন—
উই চারা খাই বনে জাতিতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।।
মুকুন্দ চক্রবর্তী
(ঙ) সাধারণ ভবিষ্যৎকালের উত্তম পুরুষের বিভক্তি ছিল ‘ইব’। যেমন—
সখীর উপরে দেহ তণ্ডুলের ভার।
তোমার বদলে আমি করিব পসার ৷৷
মুকুন্দ চক্রবর্তী
(ছ) কিছু সংস্কৃত নামশব্দকে ক্রিয়ার ধাতুরূপে গ্রহণ করে তার সঙ্গে ক্রিয়ার বিভক্তি যোগ করা হত। নামধাতুর এই বহুল ব্যবহার অন্ত্য-মধ্য বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন— নমস্কার + ইলা = নমস্কারিলা, ইত্যাদি।


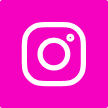





Leave a Reply