বাংলা গদ্যের বিকাশে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা কর।
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ শতকের গোড়ার দিকে অর্থাৎ প্রথম দু’একটি দশকে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রন অনুসরণ এবং অনুকরণ ঘটছিল বহুল পরিমাণে। সেই তুলনায় রবীন্দ্র গদ্যের অনুসৃতি নগন বরং সমালোচক বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন, এই সময়েই বাংলা গদ্যে নতুন স্টাইল তৈরি হচ্ছিল। প্রধানত যে দু’জন গদ্যকার সেই স্বতন্ত্র এবং নবতর গদ্যশৈলীর সন্ধান দিয়েছিল তাঁরা হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রমথ চৌধুরী।
১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট জন্মাষ্টমী তিথিতে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন অবনীন্দ্রনাথ। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতা গুণেন্দ্রনাথের পুত্র তিনি। প্রথাগতভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় তিনি বেশিদূর অগ্রসর হননি। অথচ সারাজীবন সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। তবে সাহিত্য স্রষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতি বিস্তারিত হয়েছিল চিত্রশিল্পীরূপেও। অবন ঠাকুর বালক বয়সে কিছুদিন নর্মাল স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন। পরে ভর্তি হন সংস্কৃত কলেজে। এই নর্মাল স্কুলের পড়াশোনা তার কাছে দুঃসহ ছিল। পড়াশোনায় মন না থাকলেও ছবি আঁকায় তার উৎসাহ ছিল প্রবল। আর ভালবাসতেন সঙ্গীতচর্চা করতে। বাংলা চিত্রশিল্পে তিনি একটি নিজস্ব ঘরানা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তার পূর্বে অঙ্কনবিদ্যা শিখেছেন তিনি কৃতবিদ্য অনেক শিল্পীর কাছে। তার প্রথম শিক্ষক ছিলেন গিলার্জি। এর কাছে তিনি প্যাস্টেল ও ওয়াটার কালার ড্রয়িং শেখেন, দ্বিতীয় শিক্ষক পামারের কাছে শেখেন লাইফ স্টাডি এবং অয়েল পেন্টিং। দেশি আদর্শে প্রথম যা আঁকেন তিনি তার নাম ছিল কৃষ্ণলীলার চিত্রাবলী। টাইকানের কাছে তিনি শিখেছিলেন জাপানি অঙ্কনরীতি। ওমর খৈয়াম চিত্রাবলি এঁকেছিলেন জাপানি আদর্শে। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে তার বিবাহ হয় সুহাসিনী দেবীর সঙ্গে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিতে এদেশে তিনি শিল্পগুরুরূপে স্বীকৃতি পান। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি দরবার উপলক্ষে যে আয়োজন হয় তার মঞ্চসজ্জা করার দায়িত্ব পান অবনীন্দ্রনাথ। এই সময়ে ইংরেজ সরকার তাঁকে সি আই ই উপাধি দেয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পান সাম্মানিক ডি. লিট.। ইতিপূর্বে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে হ্যাভেলের চেষ্টায় তিনি কিছু দিনের জন্য কলকাতা আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ হন। তার পূর্বে আর কোনো ভারতীয় শিল্পী এই মর্যাদা পায়নি। ১৯১৫ তে অবশ্য তিনি আর্ট স্কুলের চাকরি ত্যাগ করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিতভাবে তিনি ‘বিচিত্রা’ সভা স্থাপন করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি নতুন অধ্যাপক পদ তৈরি হয়। তার মধ্যে একটি রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি বাগেশ্বর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এরই মধ্যে লণ্ডনে, প্যারিসে (১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে) এবং টোকিওতে (১৯১৯-এ)। তাঁর ও তার অনুবর্তীৰ্গণের চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেছে। ১৯৩০ সাল থেকে কুটুম নাম দিয়ে একপ্রকার বিমূর্ত রূপ সৃষ্টি করতে থাকেন তিনি। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বভারতীর আচার্য পদের দায়িত্বভার ছিল তাঁর উপর। অবশেষে এই মহান এর জীবনাবসান ঘটে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর।
ক. কাহিনীমূলক রচনা: শকুন্তলা (১৮৯৫), ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৬), রাজকাহিনী (৯০৯), ভূতপত্রীর দেশ (১৯১৫), খাতাঞ্জীর খাতা (১৯১৬), নালক (১৯১৬), পথেবিপথে (১৯১৯), বুড়ো আংলা (১৯৩৪)।
খ. স্মৃতিকথামূলক রচনা: ঘরোয়া (১৯৪১), জোড়াসাঁকোর ধারে (১৯৪৪), আপনকথা (১৯৪৪),
গ. প্রবন্ধ গ্রন্থ: ভারতশিল্প (১৯০৯), বাংলার ব্রত (১৯১৯), বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী, ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ। এছাড়া মহাবীরের পুঁথি, উড়নচণ্ডীর পালা, গজকচ্ছপের পালা নামে কিছু রচনাও তার আছে।
শিশু সাহিত্যে অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাঁর কথনভঙ্গিমায় এমন একটি আন্তরিক আবেদনময় মন ভোলানোর বৈশিষ্ট্য আছে যা শিশুর হৃদয়ে দূর সঞ্চারী আবেগ তৈরি করে দিতে পারে। তার ভাষায় একটা সম্মোহনের আবেশ আছে। মহাভারতের শকুন্তলার কাহিনি নিয়ে কালিদাস, বিদ্যাসাগর বড়দের উপযোগী নাটক ও গল্প লিখেছেন। সেই একই কাহিনি অবন ঠাকুরের জাদু কলমের ছোঁয়ায় হয়ে উঠল শিশু মনের উপযোগী। বড়দের কাছেও সেই পাঠ এক ভিন্নতর আস্বাদ এনে দেয়। সংক্ষিপ্ত সরল বাক্যে কাব্যময় সেই ভাষা— ‘‘এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড়-বড় বট, সারি সারি তাল, তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল— ছোট নদী মালিনী।’’
মালিনীর জল বড় স্থির— আয়নার মত। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া— সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতকগুলি কুটিরের ছায়া। নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোট-ছোট পাখি, কত টিয়াপাখির ঝক গাছের ডালে-ডালে গান গাইত, কোটরে-কোটরে বাসা বাঁধত। দলে-দলে হরিণ, ছোট-ছোট হরিণ-শিশু কুশের বনে, ধানের খেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় ময়ুর নাচত। এই বনে তিন হাজার বছরের এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মহর্ষি কথদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী-কথ আর মা-গৌতমী ছিলেন, তাদের পাতার কুটির ছিল, পরনে ফল ছিল, গোয়াল-ভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল, আর ছিল বাকল-পরা কতকগুলি ঋষি-কুমার। তারা কন্বদেবের কাছে বেদ পড়ত, মালিনীর জলে তর্পন করত, গাছের ফলে। অতিথিসেবা করত, বনের ফুলে দেবতাদের অঞ্জলি দিত।
আর কি করত?
বনে-বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো-গাই ধলো-গাই মাঠে চরাতে যেত। মাঠ ছিল তাতে গাই-বাছুর চরে বেড়াত, বনে ছায়া ছিল তাতে রাখাল-ঋষিরা খেলে বেড়াত। তাদের ঘর গড়ার বালি ছিল, ময়ূর গড়বার মাটি ছিল, বেণু বাঁশের বাঁশি বটপাতার ভেলা ছিল; আর ছিল—খেলবার সাথী বনের হরিণ, গাছের ময়র, ছিল— মা-গৌতমীর মুখে দেবদানবের যুদ্ধ কথা, তাত-কন্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।
সকলি ছিল, ছিল না কেবল আঁধার ঘরের মাণিক ছোট মেয়ে-শকুন্তলা। একদিন নিশুতি রাতে অপ্সরী মেনকা তার রূপের ডালি—দুধের বাছা-শকুন্তলা মেয়েকে সেই তলে ফেলে রেখে গেল। বনের পাখিরা তাকে ডানায় ঢেকে বুকে নিয়ে সারা রাত বসে রইল। পাখিদেরও দয়ামায়া আছে, কিন্তু সেই মেনকা পাষাণীর কি কিছু দয়া হল!’
পুরনো কথাও নতুন সজীবতা নিয়ে উপস্থিত হয় এই রচনায়।
মা ঠাকুমার মুখে গল্প শোনার ভঙ্গিটি প্রায় অবিকৃতভাবে উঠে এসেছে ‘বুড়ো আংলা’য়। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ‘মৌচাক’ পত্রিকায়। বুড়ো আঙুলের আকারে একটি বালকের মানস ভ্রমণের কাহিনি এটি। রচনার পটভূমি বাংলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল। কারো কারো মতে প্রসিদ্ধ লেখিকা সালুমা লাগেরলফের রচনা থেকে অবনীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন। বিখ্যাত দিনেমার লেখক অ্যান্ডারসনেরও (১৮০৫-১৮৭৫) Thumbellina নামে এ জাতীয় একটি ছোটগল্প আছে।
‘ক্ষীরের পুতুল’-এ আছে রূপকথার সোনার কাঠির ছোঁয়া। দুয়োরাণী সুয়োরাণী আর বুদ্ধু ভুতুমের কাহিনি নিয়ে রচিত এ গল্প ছোটদের মনকে বিস্ময়াভিভূত করে। ক্ষীরের পুতুল এবং ‘খাতাঞ্জীর খাতা’য় লেখক যে নির্মল হাস্যরসের যোগান দিয়েছেন তা অনবদ্য। খাতাঞ্জির খাতার কাহিনি গড়ে উঠেছে বিখ্যাত ‘পিটার প্যান’ নামক বিদেশি গল্পের আদলে। খাতাঞ্জি অর্থাৎ কর্তা, গিন্নি, তাদের মেয়ে সোনা, আঙুটি ও পাঙুটি নামে তাদের দুই যমজ ছেলে, সোনাতন নামে ভৃত্য, তার বিড়াল-বৌ, কুকুর-বোহিন আর পুতু নামে এক পরী শিশুকে নিয়ে গড়ে উঠেছে কাহিনি। অবন ঠাকুরের বাল্যস্মৃতিও এ গল্পের উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। খাতাঞ্জি একজন সাংঘাতিক কৃপণ মানুষ, সবকিছুই তার হিসেব মাপা। আর পুতু স্বপ্ন জগতের দিশারি, তার আছে একটা সুবজ পাতাওয়ালা খাতা; রাঙা ফিতেয় বাঁধা তা। সে জানে সব ছেলের মনের সিন্দুকে একটি করে লুকোনো দেরাজ আছে, সেখানে আছে ওই সবুজ খাতা কেউ তার খবর পায়, কেউ বুড়ো হয়ে মরে গেলেও ওই সবুজপাতা লুকনো দেরাজের সন্ধানই পায় না।
‘ভূতপতরীর দেশ’ বাংলা শিশু সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। গ্রন্থটির আরও এক সম্পদ রচনার সঙ্গে যুক্ত লেখকের নিজের হাতে আঁকা ছবি। গ্রন্থটি সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছেন— ‘‘১৯১১ অব্দে অবনীন্দ্রনাথ একবার পুরী হইতে কোনারকে গিয়াছিলেন। বছর তিনচার পরে সেই নৈশ নিরুদ্দেশ যাত্রার স্মৃতি-সূত্র অবলম্বনে মেয়েলি আলাপ ছেলেমি প্রলাপ ছড়ার বাক্ছন্দ ও রূপকথার রঙ মিশাইয়া অদ্ভুত-কৌতুকরসের, স্বপ্ন-জাগরণের, সম্ভব অসম্ভবের, অতীত বর্তমানের বহু আয়তন ও বিচিত্রবর্ণ মায়াপট (ইংরাজীতে যাহাকে বলে fantasy) বুনিলেন—ভূতপত্রীর দেশ (১৯১৫)-এ। এই অসামান্য অসাধারণতার জন্যই বোধ করি বইটি উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে।’’
কাহিনির নায়ক স্বয়ং লেখক। মাসিপিসির বাড়ি যাবার পথে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হল সে তারই বর্ণময় রোমাঞ্চকর চিত্র এই গ্রন্থ। ভূতপতরীর লাঠি, তেপান্তরের ঘোড়া ভূত, বুড়ো মনসা, কিচ্ কিন্দে, কাসুন্দে, হারুন্দে; আবার অন্যদিকে বোগদাদের নবাব, ঔরংজেব, রণজিৎ সিংহ, আকবর, নূরজাহান—সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক জগতের সন্ধান পাওয়া যায় এ গল্পে। স্থলভাগের গল্প শেষ হওয়ার পর শুরু হয়েছে পিসির বাড়ির গল্প সখানে পৌছতে গেলে সমুদ্রের তলা দিয়ে ডুব সাঁতারে যেতে হয়। সেই জলদেশের বর্ণনা বিচিত্রতর।
অন্যদিকে বুদ্ধদেবের সমকালীন কাহিনি নিয়ে লেখা হয়েছে ‘নালক‘ নামক ছোটদের উপন্যাস।
ইতিহাসকে আশ্রয় করে রোম্যান্সধর্মী গল্প তিনি লিখেছেন ‘রাজকাহিনী’তে। কিন্তু ইতিহাস শোনানো এখানে তাঁর লক্ষ নয়; তিনি চেয়েছেন গল্প শোনাতে, যে গল্পে আছে রূপকথার আবেশ। শিলাদিত্য, গোহ, বাপ্পাদিত্য, পদ্মিনী, হাম্বির, চণ্ড, কুম্ভ, সংগ্রাম সিংহ এবং হাম্বিরের রাজ্যলাভ সংক্রান্ত নয়টি গল্প আছে এতে। প্রতিটি গল্পেই কথা দিয়ে নির্মাণ করেছেন ছবি।
অবনীন্দ্রনাথ নিজে ‘ছবি লেখা’ কথাটি ব্যবহার করেছিলেন ‘খাতাঞ্জির খাতা’ গ্রন্থে। আর তাঁর নিজের গ্রন্থগুলি প্রত্যেকটিই লেখার ছবি। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে সেগুলি ‘ছবিতা’— ছবি আর কবিতার এক বিরল সমন্বয়। তিনি যেন তুলি দিয়ে কথা এঁকেছেন আর ভাষা দিয়ে ছবি লিখেছেন— “বাইরে দুপুর রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে— এমন গরম যে কেউ আর বাইরে নেই। কালবোশেখি আগুন ঝরে, কালবোশেখি রোদে পোড়ে, গঙ্গা শুকুশুকু, আকাশে ছাই।…” তাঁর এ জাতীয় ‘কাব্য-গল্প’-এর আরও এক নিদর্শন ‘আলোর-ফুলকি’-র গল্পগুলি।
ছোটদের জন্য লেখা ছাড়াও কিছু কিছু ভিন্নস্বাদের গল্প তিনি পরিবেশন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লিপিকা-র মতো কিছুটা গল্পচিত্র এগুলি। নাম ‘পথে-বিপথে’। লেখক এখানে নিজেকে বক্তা ও অবিন এই দুটি সত্তায় উপস্থাপিত করেছেন। এখানে বাস্তবতা ও কল্পনা, কখনো কখনো অতিপ্রাকৃতিকতাও স্থান পেয়েছে। গল্পগুলি বেশিরভাগই প্রকাশিত হয়েছে ‘ভারতী’ পত্রিকায়।
শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের শিল্প আলোচনামূলক গ্রন্থের মধ্যে ‘ভারত শিল্প’ নামক গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। ‘হিতবাদী’ লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থে … নামক কয়েকটি প্রবন্ধ সঙ্কলিত আছে। তাঁর এ জাতীয় প্রবন্ধ লেখার গোড়ার কথাটি উল্লিখিত আছে ‘কি ও কেন’ নামক প্রবন্ধে।
অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তার আর এক নিদর্শন ‘বাংলার ব্রত’ গ্রন্থটি। গ্রন্থটিতে তিনি একশোরও বেশি আলপনার নকশা সংগ্রহ করেছেন। প্রায় দুই তিন বছরের চেষ্টায় এই কার্য সম্পন্ন করেছিলেন তিনি। গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে তিনি নিজের শিল্প সংক্রান্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শুধু শিল্পই নয়, অবনীন্দ্রনাথ এখানে ‘‘মেয়েলি লোকসাহিত্য—ব্রতকথা লইয়া বিস্তৃত ও মনোজ্ঞভাবে আলোচনা করিয়াছেন।’’ (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড)।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী, অধ্যাপক থাকাকালীন (১৯২১ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) শিল্পকলা বিষয়ক ২৯টি বক্তৃতা দেন তিনি। সেগুলি তখনকার প্রবাসী পত্রিকায় ছাপা হয়। পরে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে। বক্ততাগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর নন্দলাল বসু মন্তব্য করেছিলেন, ‘শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের বক্তৃতামালা রূপকলার আলোচনা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী গ্রন্থ এবং এ যুগে আমাদের মধ্যে রসবোধের উন্মেষ সাধনে অতুলনীয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বঙ্গসাহিত্যের এটি এক অমূল্য সম্পদ।
আলোচ্য গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রবন্ধগুলির শিরোনাম থেকে গ্রন্থের বিষয় সম্পর্কে ধারণা হয়। শিরোনামগুলি হল— শিল্পে অনধিকার, শিল্পের অধিকার, দৃষ্টি ও সৃষ্টি, শিল্প ও ভাষা, শিল্পের সচলতা ও অচলতা, সৌন্দর্যের সন্ধান, শিল্প ও দেহতত্ত্ব, অন্তর বাহির, মত ও মন্ত্র, শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড, শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড, শিল্পের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ভাল মন্দ, রস ও রচনার ধারা, শিল্পবৃত্তি, সুন্দর অসুন্দর, জাতি ও শিল্প, অরূপ না রূপ, রূপবিদ্যা, রূপদেখা, স্মৃতি ও শক্তি, আর্য ও অনার্য শিল্প, আর্য শিল্পের ক্রম, রূপ, রূপের মান ও পরিমাণ, ভাব, লাবণ্য সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গম।
প্রবন্ধগুলিতে লেখকের পাণ্ডিত্য, কৌতুকরসবোধ, অনুভবের প্রগাঢ়তা, আবেগের গভীরতা এবং প্রখর বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। জটিল তত্ত্বকথাও অনুভূতির গভীরতায় কতখানি সাবলীল এবং রসাবেদনময় হয়ে উঠতে পারে তার উদাহরণ এই প্রবন্ধাবলি। নিজ বক্তব্যকে পরিস্ফুটিত করতে গিয়ে তিনি কুরু-পাণ্ডব রাম-রাবণ প্রসঙ্গ থেকে কালিদাস, বৈষ্ণবপদ, রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে গ্রীক-রোমান শিল্পকলা, গ্যোটে, রা, মিলেট, বায়রণকার ব্যক্তিত্বের অংশে পরিণত করেছেন তিনি যে সেগুলি তাঁর বক্তব্যে বাহুল্য আকারে উপস্থিত হয়নি, প্রসঙ্গগুলি এসেছে সাবলীল অনিবার্যতায়। জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধও যে কতখানি রসপূর্ণ হতে পারে বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলী না পড়লে তা বোঝা দুঃসাধ্য।
শিল্পকে তিনি বলেছেন ‘নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা।’ প্রাচীন আলঙ্কারিকদের সঙ্গে সহমত হয়ে বলেছেন শিল্প হল ‘অনন্য পরতন্ত্রী’। শিল্প যে সাধনা বা শ্রমলব্ধ একটি বিষয় তা প্রকাশ করতে গিয়ে ‘শিল্পে অনধিকার’ প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন, প্রত্যেক শিল্পীকে স্বপ্নবরাম জাল নিজের মতো করে বুনে নিতে হয় প্রথমে, তারপর বসে থাকা—বিশ্বের চলাচলের পথে ধারে নিজের আসন বিছিয়ে চুপটি করে নয়—সজাগ হয়ে। এই সজাগ সাধনার গোড়ায় শ্রান্তিকে বরণ করতে হয়—‘‘Art is not a pleasure trip, it is a battle, a mill that grinds’ Millet”. অতঃপর কৌতুকরসে স্নিগ্ধ করে তিনি উল্লেখ করেছেন, “শিল্পের একটা মন্ত্রই হচ্ছে নালমতিবিস্তরেণ। অতি বিস্তরে যে অপর্যাপ্ত রস থাকে, তা নয়। অমৃত হয় ফোঁটা, তৃপ্তি দেয় অফুরন্ত। … আর ঐ অমৃতি জিলাবির বিস্তার মস্ত, কিন্তু খেলে পেট হয়ে ওঠে আর বুক চেপে ধরে বিষম রকম। এরপর শিল্পী আর কারিগরের প্রভেদ মন্তব্য করে শিল্পীর সৃষ্টিকেতিনি বলেছেন নির্মাণ অর্থাৎ ‘নিঃশেষভাবে পরিমাণের মত সেটি ধরা।’ একটা নির্মাণের মতো ঠিক আর একটা নির্মাণ সম্ভব কিন্তু শিল্পীর নির্মিতির অনুকরণ হয় না তা অনন্য পরতন্ত্রা।’
শিল্প হল সাধনার ধন। তাই শিল্পচর্চাতে অধিকার লাগে, অধিকারী হতে হয়। সেই ভাব আসে চর্চার মাধ্যমে। সেই অধিকার অর্জন করতে হয় বলে বিশ্বাস করেন অবনীন্দনাথ। সাময়িক প্রেরণায় তিনি একেবারেই বিশ্বাসী নন। কতকটা ব্যঙ্গের সুরে তিনি লছেন, অর্জন নেই, ইনস্পিরেশন এলো— এই অবস্থায় তাজ গড়তে গেলে গম্বুজ গড়া যায়। ইনস্পিরেশনের খেয়াল ছোট বয়সে শোভা পায় আর শোভা পায় পাগলে। আর্ট হল তাই যা গড়ে ওঠে শিল্পীর অপরিমিতি বা ইনফিনিটি এবং স্বতন্ত্রতা বা ইনডিভিডুয়ালিটি নিয়ে, ফলে শুধুমাত্র আঁকার স্কুলের নিয়মকানুনের মধ্যে যে আঁকতে শিখছে তার আর শিল্পী হয়ে ওঠা হয় না। খুব নির্মম সত্য উচ্চারণ করেছেন তিনি, আর্ট স্কুল থেকে যে একেবারেই আর্টিষ্ট বার হয় না তার কারণ আমি দেখেছি—সেখানে ছেলেগুলো খেটেই চলে বাঁধা নিয়মে। অর্থাৎ শাস্ত্র দিয়ে শিল্প হয় না। ফটোগ্রাফির সীমাবদ্ধতা আর শিল্পের নিজস্বতা নিয়ে তিনি মত জ্ঞাপন করেছেন ‘অন্তর বাহির’ নামক প্রবন্ধে। রঙ আর রূপের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা বিবৃত হয়েছে ‘বর্ণিকাভঙ্গম’ প্রবন্ধটিতে। শিল্পে আদর্শ বলে যে কোনো স্থায়ী মানদণ্ড নেই সেকথাও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন ‘সৌন্দর্যের সন্ধান’ নামক প্রবন্ধে।
আলোচ্য প্রবন্ধগুলিতে শুধু যে লেখকের বিশ্লেষণী দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় আছে তা-ই নয়, উপস্থাপনার কাব্যময় ভঙ্গির নিদর্শনও আছে প্রায় সর্বত্র। ‘সুন্দর-অসুন্দর’ নামক প্রবন্ধে বাস্তবচেতনা আর কাব্যময়তার অপূর্ব সমন্বয় সুন্দর অসুন্দর—জীবন নদীর এই দুই টান একে মেনে নিয়ে যে চললো সেই সুন্দর চললো। আর যে এটা মেনে নিতে পারলে না সে রইলো যে-কোনো একটা খোঁটায় বাঁধা। শিল্পের অধিকার প্রবন্ধে তার বক্তব্য— ‘আর্টের একটা লক্ষণ আড়ম্বরশূন্যতা—সিমপ্লিসিটি। অনাবশ্যক রঙ-তুলির কলকারাখানা দোয়াতকলম, বাজনা-বাদি সে মোটেই সয় না। এক তুলি এক কাগজ একটু জল একটি কাজললতা—এই আয়োজন করেই পূর্বের বড় বড় চিত্রকর অমর হয়ে গেলেন। কবির এর চেয়ে কমে চলে গেল। …এ যেন রূপকথার রাজপুত্রের যাত্রা—স্বপ্নপুরীর রাজকুমারীর দিকে।’ কী অসামান্য কথাচিত্র। আর্য সভ্যতায় অনার্য শিল্পের অবদান অন্বেষণ করে তিনি উপমা প্রয়োগে বললেন, ‘‘পাকা ফলের বুকের মাঝে যেমন শক্ত কষি, তেমনি আর্য শিল্পের অন্তরে অন্তরে অনার্য শিল্পের প্রাণ বীজের মতো লুকিয়ে রয়েছে—তাকে ফেলে হয়তো রস পেতে পারি, কিন্তু সে যদি বাদ যেতো আরম্ভেই একেবারে তবে নিষ্ফলা হত আর্য সভ্যতা এটা নিশ্চয়।’’
অবনীন্দ্রনাথের আত্মকথনমূলক রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘ঘরোয়া’ (১৯৪১), ‘আপনকথা’ (১৯৪৬), ‘জোড়াসাঁকোর ধারে’ (১৯৪৪)। শেষতম ‘আপনকথা’ বইটি লেখকের শৈশবস্মৃতিতে ভরা। এই গ্রন্থও হিসেবি বড়দের জন্য লেখা নয়। এখানে আছে মনের কথা, পদ্মদাসী, সাইক্লোন, উত্তরের ঘর, এ-আমল সে-আমল, এ-বাড়ি ও-বাড়ি, বারবাড়িতে অসমাপিকা, বসত-বাড়ি— এই নয়টি অধ্যায়। হাতে-খড়ি আর ব্যাপটাইজ হয়ে যাবার মজাদার ঘটনার পাশাপাশি শেষ অধ্যায়টিতে আছে বসতবাড়ি নিয়ে তীব্র আবেগের কথা। এখানেও লেখকের অস্ত্র তাঁর জাদ-ভাষা। গ্রন্থের প্রথম এবং শেষ অধ্যায়টি পুরোপরি উচ্চ লেখকের এ গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য আর ভাষার মুন্সীয়ানা প্রমাণের জন্য: প্রথম অধ্যায়— “যে খাতার সঙ্গে ভাব হল না, তার পাতায় ভালো লেখাও চলল না। এই খাতা কাছে-কাছে রয়েছে ভাব হয়ে গেল এটার সঙ্গে। ভাব হল যে-মানুষের সঙ্গে কেন বলা চলল নিজের কথা সুখ-দুঃখের। আমার ভাব ছোটোদের সঙ্গে— তাদেরই দিলেন খাতা। আর যারা কিনে নিতে চায় পয়সা দিয়ে আমার জীবন-ভরা সুখ-দুঃখের কাহিনি এবং সেটা ছাপিয়ে নিজেরাও কিছু সংস্থান করে নিতে চায় তাদের আমি দূর থেকে নমস্কার দিচ্ছি। যারা কেবল শুনতে চায় আপন কথা, থেকে থেকে যারা কাছে এসে বলে ‘গল্প বলো’, শিশু-জগতের সত্যিকার রাজা-রানী বাদশা-বেগম তাদেরই জন্যে আমার এই লেখা ক’খানা।
ছাপা হবে হয়ত বইখানা। একদিন কোনো বেরসিক অল্প দামে কিনে নেবে আমার সারাজীবন খুঁজে খুঁজে পাওয়া যা কিছু সংগ্রহ। এইটে মনে পড়ে যখন, তখন হাসি পায়। বলি, এ কি হয় কখনো? সব কথা কি কেউ জানতে পারে, না জানাতেই পারে কোনো কালে? অনেক কথা রয়ে যাবে, অনেক রইবে না, এই হবে, তার বেশি নয়।
একটা শোনা কথা বলি। তখন বাড়িতে প্ল্যানচেট চালিয়ে ভূত নামানো চলছে। দাদামশায়ের পার্ষদ দীননাথ ঘোষাল প্ল্যানচেটে এসে হাজির। বড়ো জ্যাঠামশায় তাকে জেরা শুরু করলেন— পরকালাটা এবং পরকালটার বৃত্তান্ত শুনে নিতে চেয়ে। প্ল্যানচিটে উত্তর বার হল— “যে-কথা আমি মরে জেনেছি, সে-কথা বেঁচে থেকে ফাঁকি দিয়ে জেনে নেবে এ হতেই পারে না।’’
আমিও ওই কথা বলি। অনেক ভুগে পাওয়া এ-সব কাহিনী, কিনতে গেলে ঠকতে হয়, বেচতে গেলে ঠকতে হয়। বলে যাওয়া চলে কেবল তাদেরই কাছে নির্ভয়ে, মনের কথা বেচাকেনার ধার ধারে না যারা, যাত্রা করে বেরিয়েছে যারা, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে, কেউ কাঠের ঘোড়ায় চড়ে, নানা ভাবে নানা দিকে আলিবাবার গুহার সন্ধানে। ছোটো ছোটো হাতে ঠেলা দিয়ে যারা কপাট আগলে বসে আছে, যে-দৈত্য সেটাকে জাগিয়ে বলে, ‘ওপুন চিসম্প চশমা খোলো, গল্প বলো। যারা থেকে থেকে ছুটে এসে বলে— ‘এই নুড়ি ছোঁয়াও, সে দাদামশায়, লোহার গায়ে ধরে যাবে সোনা। কুড়িয়ে পাওয়া পুরানো পিদুম ঘষে যারা ফেলে, অথচ ছাড়ে না কিছুতে সাত-রাজার-ধন মানিকের আশা।”
‘বসত বাড়ি’ শেষ অধ্যায়: ‘মানুষের সঙ্গ পেয়ে বেঁচে থাকে বসত-বাড়িটা। যতক্ষণ মানুষ আছে বাড়িতে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের ধারা বইয়ে ততক্ষণ চলেছে বাড়ি হাব-ভাব চেহারা ও ইতিহাস বদলে বদলে। কালে কালে স্মৃতিতে ভরে, বাড়ি-স্মৃতির মাঝে বেঁচে থাকে বাড়ির সমস্তটা। বাড়ি ঘর জিনিসপত্র সবই স্মৃতির গ্রন্থি দিয়ে বাঁধা থাকে একালের সঙ্গে। এইভাবে চলতে চলতে, একদিন যখন মানুষ ছেড়ে যায় একেবারে বাড়ি, স্মৃতির সূত্রজাল ঊর্ণার মতো উড়ে যায় বাতাসে; তখন মরে বাড়িটা যথার্থভাবে। প্রত্নতত্ত্বের কোঠায় পড়ে জানায় শুধু, মন দেশী ছাঁদের না বিদেশী ছাঁদের, মোগল ছাঁদের না বৌদ্ধ ছাঁদের। তার পর একদিন আসে ও আসে আর্টিস্ট। বাঁচিয়ে তোলে মরা ইট কাঠ পাথর এবং ইতিহাস-প্রত্নতত্ত্বের মুর্দাখানার নম্বর-ওয়ারি করে ধরা জিনিসপত্র গুলোকেও তারা নতুন প্রাণ দিয়ে দেয়। সঙ্গ পাচ্ছে মানুষের, তবে বেঁচে উঠেছে ঘর বাড়ি সবই।
আমি বেঁচে আছি পুরানোর সঙ্গে নতুন হতে হতে; তেমনি বেঁচে আছে এই তিনতলা অডিটাও, আজ যার মধ্যে বাসা নিয়ে বসে আছি আমি। আজ যদি কোনো মারোয়াড়ী দোকানদার পয়সার জোরে দখল করে এ-বাড়িটা, তবে এ-বাড়ির সেকাল-একাল দুই-ই লোপ পেয়ে যাবে নিশ্চয়। যে আসবে, তার সেকাল নয় শুধু একালটাই নিয়ে সে বসবে এখানে। দক্ষিণের বাগান ফুয়ে উড়িয়ে ওখানে বসাবে বাজার, জুতোর দোকান, ঘি-ময়দার আড়ৎ ও নানা— যাকে বলে প্রফিটেবল-কারখানা, তাই বসিয়ে দেবে এখানে। সেকাল তখন স্মৃতিতেও থাকবে না।
স্মৃতির সূত্র নদীধারার মতো চিরদিন চলে না, ফুরোয় এক সময়। এই বাড়িরই ছেলেমেয়ে— তাদের কাছে আমাদের সেকালের স্মৃতি নেই বললেই হয়। আমার মধ্যে দিয়ে সেই স্মৃতি—ছবিতে, লেখাতে, গল্পে—যদি কোনো গতিকে তারা পেল তো বর্তে রইল সেকাল বর্তমানেও। না হলে, পুরোনো ঝুলের মতো, হাওয়ায় উড়ে গেল একদিন হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে।”
এমনই উপাদেয় ‘ঘরোয়া’ আর ‘জোড়াসাঁকোর ধারে’ গ্রন্থটির ভাষাও। দুটি গ্রন্থই রানী চন্দের সঙ্গে যৌথভাবে লেখা। ‘ঘরোয়া’ গ্রন্থটি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্রনাথ ২৭শে জুন ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন, “অবন, তোমার বিবরণ শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে মরা গাঙে বান ডেকে উঠল। বোধ হয় আজকের দিনে আর দ্বিতীয় কোনো লোক নেই যার স্মৃতি চিত্রশালায় সেদিনকার যুগ এমন প্রতিভার আলোকে প্রাণে প্রদীপ্ত হয়ে দেখা দিতে পারে—এ তো ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য নয়, এ যে সৃষ্টি—সাহিত্যে-এ পরম দুর্লভ। প্রাণের মধ্যে প্রাণ রক্ষিত হয়েছে—এমন সুযোগ দৈবে ঘটে। একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে একটা সময়ের ছবি সুন্দর ফুটেছে এই গ্রন্থে। ব্যক্তি মানুষটিকেও পুরোপুরি পাওয়া যায় এখানে। রবীন্দ্রনাথের ‘ছেলেবেলা’ গ্রন্থটিরই শুধু তুলনা চলে এর সঙ্গে।
‘জোড়াসাঁকোর ধারে’-তে লেখকের মুখের কথা লেখার টানে ধরে রেখেছেন রানী চন্দ। গ্রন্থের ভূমিকায় সেকথা উল্লেখ করেছেন লেখক। গ্রন্থটি শুরু হয়েছে সংলাপের আদলে। লেখক বলেছেন— “তোমাদের এখানে আজ বর্ষামঙ্গল হবে? আমাদেরও ছেলেবেলা বর্ষামঙ্গল হত আমরা কি করতুম জানো? আমরা বর্ষকালে রথের সময়ে তালপাতার ভেঁপু কিনে বাজাতুম; আর টিনের রথে মাটির জগন্নাথ চাপিয়ে টানতুম, রথের চাকা শব্দ দিত ঝঝন; যেন সেতার নূপুর সব একসঙ্গে বাজছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ত দেখতে পেতুম, থেকে থেকে মেঘলা আলোকে রোদ পরাত চাঁপাই শাড়ি-কি বাহার খুলত! তবে শোনো বলি একটা বাদলার কথা।’’ —এভাবেই শুরু হয়েছে স্মৃতিচারণ। একেবারে গল্প বলার ধরনে। মুখে মুখে ছাঁদ অবিকৃত আছে ভাষার বনেটেও। মুখে মুখে গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতা অবনীন্দ্রনাথের। সেই শুনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, ‘তুমি লেখো না, যেমন কত মুখে মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো।’ সেই উৎসবের ফল ফলেছিল ‘শকুন্তলা’ গ্রন্থে। আসলে শিল্পীকে চিনে নিতে ভুল করেননি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ওই উৎসাহটুকুর পর অবনীন্দ্রনাথ আর থেমে থাকেননি। আলোচ্য গ্রন্থে এক এক করে কুড়িটি অধ্যায়ে ধরা আছে সেকাল, সেই বাড়ি আর শিল্পীর মনের ইতিহাস।
অবনীন্দ্রনাথের গদ্যশৈলির বৈশিষ্ট্য
১. কথা বলার ভাষা আর লেখার ভাষার মধ্যে যে ফারাক আছে তা মুছে যায় অবনীন্দ্রনাথের লেখায়।
২. প্রধানত ছোটদের জন্যই তিনি লিখেছেন।
৩. তাঁর লেখায় আছে রূপকথার গল্প বলার ছাঁদ।
৪. গুরু-গম্ভীর বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সেই লেখাতেও আছে স্নিগ্ধ কৌতুকরসের একটা আবরণ।
৫. উপমার প্রয়োগে কথাও ছবি হয়ে ওঠে তার রচনায়।
৬. পুরনো কথাকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করার কৌশল তার করায়ত্ত।
৭. গদ্যশৈলীতে নিজস্ব একটি ঘরানা বা স্টাইল নির্মাণ করতে পেরেছেন অবনীন্দ্রনাথ।


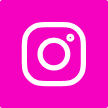


Leave a Reply