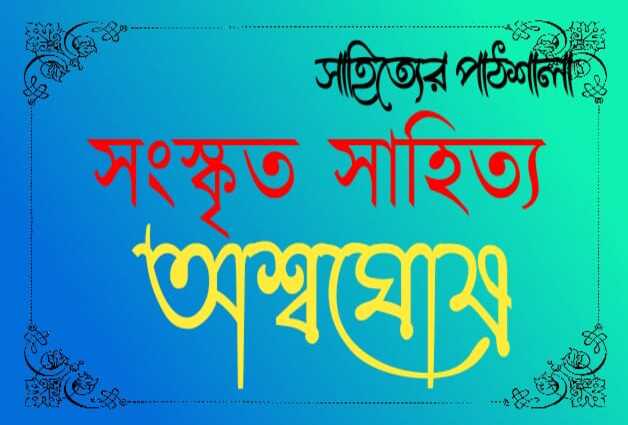
সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে অশ্বঘোষের অবদান আলোচনা কর।
অশ্বঘোষ
রামায়ণের ধ্রুপদী যুগের সূচনাপর্বে কবি, নাট্যকার ও বৌদ্ধ ধর্মাচার্য অশ্বঘোষ ধর্মীয় ঐতিহ্যে ও সাহিত্যিক অবদানে অবিস্মরণীয়। কবি, পণ্ডিত, ধর্মপ্রবক্তা ও দার্শনিক অশ্বঘোষ, নাগার্জুন ও বসুমিত্র এই তিন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধলেখক কনিষ্কের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। ম্যাকডোনেল এ প্রসঙ্গে বলেছেন— “Aswaghosha was, according to the Buddhist tradition, a contemporary of King Sudhaka.”
বিভিন্ন কিংবদন্তি থেকে অশ্বঘোষের জীবন ইতিহাসের কিছু তথ্য জানা যায়। চীনদেশে প্রচলিত মত এই যে—তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, তাঁর মাতার নাম ছিল সুবার্ণাক্ষী এবং তাঁর নিবাস ছিল সাকেত (অযোধ্যা)। কবি অশ্বঘোষ বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারত, জৈন ও বৌদ্ধদর্শনে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।
অশ্বঘোষের প্রচলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ‘বুদ্ধচরিত’ ও ‘সৌন্দরনন্দ’ নামক মহাকাব্য এবং ‘শারিপুত্রপ্রকরণ’ নামক নাটক এবং ‘গণ্ডীস্তোত্রগাথা’ গীতিকাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ‘বজ্রসূচী’, ‘সূত্রালংকার’ এবং ‘মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূত্র’ অশ্বঘোষের উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁর রচনার ধারায় সহজ সুন্দর বৈদর্ভী রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগেও তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। তাঁর রচনানৈপুণ্য ও বৈচিত্র্যের প্রশংসায় ফরাসি অধ্যাপক সিলবাঁ লেভি বলেছেন— ‘‘In his richness and variety, he recalls Milton, Kant and Voltaire.”
বুদ্ধচরিত
অশ্বঘোষের সাহিত্যসৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল ‘বুদ্ধচরিত’ নামক মহাকাব্য। গ্রন্থের নামকরণ থেকে একথা স্পষ্ট যে বুদ্ধের জীবনীই এই মহাকাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ সিং-এর মতে ‘বুদ্ধচরিত’ ২৮টি সর্গে নিবদ্ধ। চীনা অনুবাদে ২০টি সর্গ এবং তিব্বতী অনুবাদে ২৮টি সর্গের পরিচয় পেলেও আমাদের দেশে ১৭টি সর্গের বেশি পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে শেষ চারটি সর্গ অমৃতানন্দ নামক কোনো এক কবির রচনা।
সিদ্ধার্থের জন্ম থেকে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি পর্যন্ত বুদ্ধদেবের ঘটনাবহুল ও মহত্বমণ্ডিত জীবনবৃত্তান্ত এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কপিলাবস্তুর শাক্যবংশে বুদ্ধদেবের জন্ম, যশোধরার সঙ্গে তাঁর বিবাহ, বিষয়ভোগে সিদ্ধার্থের উদাসীনতা প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছেন। বিষয়ভোগে উদাসীন সিদ্দার্থ নগরভ্রমণে বেরিয়ে দেখেন লোলচর্ম এক বৃদ্ধকে। এই দৃশ্য থেকে তিনি সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন।পুরাঙ্গনাদের সতৃষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও বুদ্ধদেবের মনে বৈরাগ্যের জন্ম হল সংসারত্যাগী এক সন্ন্যাসীকে দেখে। সংসারের করুণ পরিণতি জেনেও মানুষ কেমন করে আনন্দে মত্ত হয়, তা জেনে সিদ্ধার্থ বিস্ময়বোধ করেন— ‘‘ইদং চ রোগব্যসনং প্রজানাং পশ্যংশ্চ বিশ্রম্ভমূপৈতি লোকঃ’’। পক্ষান্তরে নিশীথ শয়নে সুপ্ত রমণীগণের অবস্থা দর্শনের বিতৃষ্ণায় তিনি সংসার ত্যাগের সংকল্প করলেন। রাজা এবং প্রজারা হাহাকার শুরু করলেন। শুদ্ধোধন নিজেকে দশরথের অবস্থায় সঙ্গে তুলনা করে বললেন—
অজস্য রাজ্ঞস্তনয়ায় ধীমতে
নরাধিপায়েন্দুসখায় মে স্পৃহা।
গতে বনে যস্তনয়ে দিবং গতো
ন মেঘবাস্পঃ কৃপণং জিজীবহ।।
যশোধরার বিলাপে সীতার ছায়া পড়েছিল। সিদ্ধার্থ সত্য সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালেন। তাঁর সাধনায় বাধা দেয় দৈত্যরূপ ‘মার’ এবং সেই ‘মার’ ও তার অনুগামীদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হল। সেই যুদ্ধের বর্ণনায় বীররসের সার্থক পরিচয় লাভ করা যায়। গয়ার নিকটবর্তী স্থানে সিদ্ধিলাভ করে বুদ্ধ নামে পরিচিত হন এবং কালে নির্বাণ প্রাপ্ত হন।
‘বুদ্ধচরিতে’র ভাষা প্রাঞ্জল এবং প্রসাদগুণযুক্ত। চিত্রনৈপুণ্য এবং ভাষা ও ভাবের সম্মিলিত আবেদন হৃদয়গ্রাহী। অলংকারের ঔচিত্য, শব্দের ঝংকার ও ছন্দের সুষমা সত্যই প্রশংসনীয়। কয়েকটি সর্গে কাব্যের ধারার সহিত দর্শনের গূঢ়তা মিশ্রিত হওয়ায় কিছু ক্ষতি হয়েছে। সংসারের তৃষ্ণার্ততাপ নিবারণের জন্য উপযুক্ত পীযুষামৃত যদি কেউ পান করতে পারে, তাহলেই এই রচনার সার্থকতা। কবি তাঁর অপূর্বকৌশলে শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র প্রভৃতি অঙ্গরসের পোষকতায় শান্তরসের পরিপাক ও চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন।
সৌন্দরনন্দ
‘সৌন্দরনন্দ’ অশ্বঘোষের আরেকখানি মহাকাব্য। Keith মনে করেন এই গ্রন্থটিই কবির প্রথম মহাকাব্য। গ্রন্থটি ১৮টি সর্গে বিভক্ত। কপিলাবস্তু নগরের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে কাব্যটির সূত্রপাত। বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের বৌদ্ধধর্মগ্রহণ ও বুদ্ধের নির্দেশে সেই ধর্ম প্রচার এই মহাকাব্যের মূল উপজীব্য।
শাক্যরাজ শুদ্ধোধনের দুই পুত্র সবার্থসিদ্ধ ও নন্দ জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থ সংসার সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত হলেন এবং নন্দ সুন্দরী নাম্নী রূপসীর পাণিগ্রহণ করলেন। নন্দ তাঁর রূপসী স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। সংসারের দুঃখময়তা সম্বন্ধে বুদ্ধ নন্দকে অবহিত করেন—
মলপঙ্কধরা দিগম্বরা প্রকৃতিস্থের্নমদত্ত রোমভিঃ।
যদি সা তব সুন্দরী ভবেৎ নিয়তং তেহস্য ন সুন্দরী ভবেৎ।।
কিন্তু নন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। তরুণী স্ত্রীর বিলাপ এবং নন্দের অন্তর্দ্বন্দ্ব মর্মস্পর্শী হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কবি এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বলেছেন—
তং গৌরবং বুদ্ধগতং চকর্ষ ভার্যানুরাগঃ পুনরাচকর্ষ
সৌহনিশ্চয়ান্নাপি যযৌ ন তস্তৌ তবং তরঙ্গেজ্বিব রাজহংসঃ।।
কবিপ্রতিভা ও দার্শনিক প্রতিভার সার্থক সমন্বয় ঘটেছে ‘সৌন্দরনন্দ’ মহাকাব্যে। কাব্যের শেষে কবি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি কাব্যের ছলে তত্ত্বকথা প্রকাশ করেছেন— ‘‘কাব্য ব্যাজেন তত্ত্বং কথিতামিহ ময়া মোক্ষঃ পরিমিতি।’’ তাঁর কাব্যে কটু ঔষধ মিশ্রিত হয়েছে মধুর সঙ্গে— ‘‘পাতুং তিক্তমিবৌষধং মধুযুতং হার্দ্যং কথং স্যাদিতি।’’
কবির ‘সৌন্দরনন্দ’ কাব্যের ভাষা অলংকার ও ছন্দপ্রয়োগের সুষমা কুশলতারই পরিচয় পাওয়া যায়।। পুত্র জন্মের শুভলগ্নে ক্রিয়ার ব্যবহার কী প্রাঞ্জল— ‘‘চচার হর্ষঃ প্রাণনাশ পাম্মা জঞ্জাল ধর্মঃ কলুষঃ শশান।’’ অশ্বঘোষের কাব্যে রামায়ণের প্রভাব স্পষ্ট।
শারিপুত্রপ্রকরণ
বুদ্ধ জাতিতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু শারিপুত্র ব্রাহ্মণ। তাই ব্রাহ্মণ হয়ে ক্ষত্রিয়ের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করা উচিত কিনা এর উত্তরে মৌদ্গল্যায়ন বলেন অনুচিত। কিন্তু শারিপুত্রের অন্তরে জেগেছে বোধিলাভের তীব্র ব্যাকুলতা। শেষে তিনি উপযুক্ত যুক্তি দ্বারা মৌদ্গল্যায়নের যুক্তি খণ্ডন করেন। পরবর্তীকালে উভয়ে মিলিতভাবে বুদ্ধের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন।
এই নাটকে চোর, মাতাল প্রভৃতি নিম্নস্তরের চরিত্রচিত্রণে কবির নৈপুণ্য দেখা যায়। এছাড়া এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।
গণ্ডীস্তোত্রগাথা
‘গণ্ডীস্তোত্রগাথা’ ২৯টি শ্লোকে নিবদ্ধ গীতিকাব্য। শ্লোকগুলি স্রন্ধরা ছন্দে নিবদ্ধ। বৌদ্ধমঠের গণ্ডীনামক বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর ধ্বনির মর্মগত আবেদন এবং গণ্ডীর প্রশংসা করে শ্লোকগুলি রচিত। এই ধ্বনি বৌদ্ধদের কাছে খুব পবিত্র। Winternitz-এর মতে এটি কুমারলাটের সমসাময়িক রচনা।
বজ্রসূচী
অশ্বঘোষের নামে প্রচলিত হলেও অনেকে গ্রন্থটিকে আচার্য ধর্মকীর্তির রচনা বলে অনুমান করেন। বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই গ্রন্থে গ্রন্থাকারের তীব্র বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত সামাজিক বর্ণব্যবস্থার সমালোচনাই এই গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়।
মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূত্র
এই গ্রন্থটিতে অশ্বঘোষের জীবনোপলব্ধি বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি মহাযানী ভিক্ষু হন। মূলত মহাযান সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য এটি রচিত। Winternitz-এর মতে এটিও অশ্বঘোষের রচনা নয়।
কবির ক্রান্তিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টির সংযোগ ঘটেছে অশ্বঘোষের রচনায়। কালিদাসের ওপর অশ্বঘোষের প্রভাব দেখা যায়। যেমন ‘বুদ্ধচরিতে’র এই উক্তি—
অতোহপি নৈকান্তসুখোহস্তি কশ্চিৎ
নৈকান্তদুঃখং পুরুষং পৃথিব্যাম্।।
অনুরূপ উক্তি ‘মেঘদূতে’ও পাওয়া যায়—
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছতি উপরি চ দশা চক্রানেমিক্রমেণ।।
কোনো কোনো শ্লোকে তাঁর মধ্যে পাণ্ডিত্য ফুটে উঠেছে—
ঋতুর্ব্যতীত পরিবর্ততে পুনঃ ক্ষয়ং প্রয়াত পুনরেতি চন্দ্রমাঃ।
গতং গতং নৈবতু সন্নিবর্ততে জলং নদীনাং চ নৃণাঞ্চ যৌবনম্।।
পরিশেষে বলা যায় অশ্বঘোষের রচনা অতি চিত্তাকর্ষক।


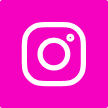


Leave a Reply