বামপন্থী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব আলোচনা কর।
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার অঙ্গনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর মৃত্যুর পর আজও তিনি অতীত নন, বরং বর্তমান। কারণ তাঁর কবিতা হাজার জনের দিকে মেলে দেওয়া ভালোবাসারই তীব্র সংরাগময় কাব্য। তিনি তাঁর হৃদয়কে মেলে ধরেছিলেন বৃহত্তর মানব সমাজের দিকে, যেখানে নিয়ত দুঃখ ও সংঘর্ষের বেদনায় জন্ম নিচ্ছে আগামীকালের ইতিহাস। তাঁর কবিতার সমস্ত মাধুর্য যেন নিহিত আছে তাঁর অভিজ্ঞতার আহরণ ও প্রকাশ বেদনার আন্তরিকতায়। বস্তুত এই আন্তরিকতার ঐশ্বর্যেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদকে অবলম্বন করেও কবিতাকে সার্থক ও রসোত্তীর্ণ মূর্তি দান করতে পেরেছেন।
১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি নদীয়ার কৃষ্ণনগরে মাতুলালয়ে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। পিতা ক্ষিতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মা যামিনী দেবী। পিতার আবগারী বিভাগে বদলির চাকরি হওয়ায় কবির শৈশব কাটে বিভিন্ন স্থানে। কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশান থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। কবি ছাত্রজীবন থেকেই ছিলেন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ১৯৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দে ‘বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিশোর ছাত্রদল’এ যুক্ত হন। ১৯৩৯-এ যুক্ত হন লেবার পার্টির সঙ্গে। ১৯৪২-এ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪৬-এ দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকার সাংবাদিক হয়ে আসেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে তিনি কারাবরণ করেন এবং ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কারামুক্তি ঘটে। জেল ফেরৎ কবির জীবনে আর্থিক দুরবস্থা দেখা দিলে মাত্র পঁচাত্তর টাকা বেতনে একটি নতুন প্রকাশনা সংস্থার সাব-এডিটর হন। ১৯৫১-তে ‘পরিচয়’ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। এই বছরই গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৬৭-তে যুক্তক্রন্ট ভেঙে দেওয়ার কারণে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে তিনি দ্বিতীয়বার কারাবরণ করেন এবং তেরো দিন কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৮১ খ্রিস্টাবে পার্টির সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি নেন এবং তারপর বামপন্থী রাজনীতি পরিত্যাগ করে দক্ষিণপন্থী পার্টি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি সমর্থন করলে তিনি হয়ে ওঠেন সবচেয়ে বিতর্কিত চরিত্র। মৃত্যুর দিনেও সেই বিতর্ক থেকে গিয়েছিল।
কবির কাব্যগ্রন্থগুলি হল— ‘পদাতিক’ (১৯৪০), ‘অগ্নিকোণ’ (১৯৪৮), ‘চিরকুট’ (১৯৫০), ‘ফুল ফুটুক’ (১৯৫৭), ‘যত দূরেই যাই’ (১৯৬২), ‘কাল মধুমাস’ (১৯৬৬), ‘ছেলে গেছে বনে’ (১৯৭২), ‘একটু পা চালিয়ে ভাই’ (১৯৭৯), ‘জল সইতে’ (১৯৮১), ‘চইচই চইচই’ (১৯৮৩), ‘বাঘ ডেকেছিল’ (১৯৮৫), ‘কাগজের নৌকা’ (১৯৮৯), ‘ধর্মের কল’ (১৯৯৯) ইত্যাদি।
সুভাষ মুখোপাধ্যায় এমন একজন মানুষ যিনি নিজের মতো করে জগতটাকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সে ভাবেই আমৃত্যু পথ চলেছেন পদাতিক কবি। এক বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে পথ চলতে সাহায্য করেছিল এবং এ কারণে তিনি অন্য অনেক সহযাত্রীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর মৃত্যু তাই আমাদের কাছে নতুন করে তাকে পাওয়া। তাঁর আদর্শ ও বলিষ্ঠ প্রত্যয়কে নিজেদের অন্তরে উপলব্ধি করে নিজেদেরকে দেউলিয়াপনা থেকে মুক্ত করার তাগিদ অনুভব করা। কারণ তিনি জানতেন—
ফুলকে দিয়ে
মানুষ বড় বেশী মিথ্যে বলায় বলেই
ফুলের ওপর কোনদিনই আমার টান নেই।
আগুনের ফুলকি—
যা দিয়ে কোনদিন কারো মুখোশ হয় না।
(পাথরের ফুল)
জীবনশিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায় কোনদিন মুখোশ পরেননি। সেই তার অহংকার। কাব্যক্ষেত্রে কখনও কখনও আমরা এমন কবির সম্মুখীন হই যাঁর কবিতা পড়া মাত্রই মনে হয়, কথার সুর বা অর্থের গৌরব নয়, আসলে কবির অনুভূতি এক বিশুদ্ধ আন্তরিকতার দীপ্তিতেই কাব্য হয়ে প্রকাশ পায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সে ধরনের কৰি। তাঁর কবিতার সমস্ত মাধুর্য যেন নিহিত আছে তাঁর অভিজ্ঞতার আহরণ ও প্রকাশ বেদনার আন্তরিকতায়। মন ও মুখের ভাষা যে নতুন-ঐক্যে গাঁথা পড়ে কবির কাব্যে, তাঁর কবিতা তার অতি সহজবোধ্য উদাহরণ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই বাংলা কাব্যজগতে প্রথম কবি যিনি পুরোপুরি রাজনৈতিক কবিতা নিয়ে আসরে উপস্থিত হয়েছেন।
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘পদাতিক’ সাড়া জাগিয়েছিল অখণ্ড বাংলায়। একালের পাঠক লক্ষ করলেন ‘পদাতিক’-এর প্রকাশক ‘কবিতা ভবন’ (১ম সং ১৯৪০) এবং বুদ্ধদেব বলেন— ‘দশ বছর আগে বাংলার তরুণতম কবি ছিলাম আমি। …সম্প্রতি এই ইর্ষিতব্য আসন সমর সেনেরও বেদখল হয়েছে, বাংলার তরুণতম কবি এই সুভাষ মুখোপাধ্যায়।’ অরুণ মিত্রের মতে এই প্রথম পর্যায়ের কবিতায় ছিল ছন্দনিয়ন্ত্রণ, শব্দ প্রয়োগের নতুনত্ব এবং জনমুখী দৃষ্টি। লক্ষ্য করার মতো তাঁর তির্যক কথনভঙ্গি। সূচিপত্রবিহীন ২৩-টি কবিতার সংকলন ‘পদাতিক’, যাতে আছে বুর্জোয়া ছাঁদের হাতছানি সত্ত্বেও নবযুগ আনার ইচ্ছা, মিলিত অগ্রগতির ইচ্ছা এবং শেষকার পথ অজানা থাকলেও অব্যাহত গতি। কবি জানান— ‘প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/ এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা’। তরুণ কবি উপলব্ধি করতে শিখেছেন—‘ইতিহাস অর্থনীতির হাতে বাঁধা’। কবি পরিস্থিতি থেকে শিখেছেন— ‘কৃষক, মজুর! তোমরা শরণ/ জানি, আজ নেই অন্য গতি।’ প্রচল রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে কবিমন–‘ছেঁড়া জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে/ বেঁধে নিই মন কাব্যের প্রতিপক্ষে’। অর্থাৎ ভাববাদী কবিতার বিরুদ্ধে কবি, কন্ঠে আছে শ্লেষ ও আত্মপরিবর্তনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা–ত্রিশঙ্কু মনে আছে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব। শ্লেষ মধ্যবিত্ত ভাববাদী মানসিকতার প্রতি—‘সম্মতি নেই মজুর ধর্মঘটেও/ ভাংচি ঘটায় শৃগাল বুদ্ধি ভাড়াটে’। এখানে বিষ্ণু দে এবং সমর সেনের শৈলী উঁকি দিয়ে যায়। ‘দলভুক্ত’ কবিতায় জানিয়ে দেন কবি–‘নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নেই সুখ’। ‘পদাতিক’ কবিতায় উপলব্ধি আছে–‘বুঝেছি ব্যর্থ পৃথিবীর পাড় বোনা/ স্বপ্নের ভাঁড় সামনেই ওল্টানো’। বলা বাহুল্য বুর্জোয়া ‘শ্রেষ্ঠী বিলাপ’ কবিতায় কবি শ্রেষ্ঠীদের পক্ষ থেকে সমর্পণের কথা বলেন—‘জনজাগরণে সদলবলেই মেনেছি হার–/ হে বলশেভিক, মারণমন্ত্র মুখে তোমার’। ‘অত:পর’ কবিতায় শ্লেষাক্ত কন্ঠস্বরে জমিদারশ্রেণীর পক্ষ নিয়ে কথা বলার ভান করেন। ‘চীন: ১৯৩৮’ কবিতার পরিসর ভারত ছাড়িয়ে যুদ্ধরত চীনে প্রসারিত। বামপন্থী কবিতায় পরিসরবৃদ্ধির চেহারাটি অন্য অনেক বামপন্থী কবির লেখাতেই মিলবে। ‘আর্ষ’ কবিতায় কবি তৎকালীন বাংলা প্রগতিশীল ট্রাডিশন মেনে উচ্চারণ করেন— ‘আমাকে সৈনিক করো তোমাদের কুরুক্ষেত্রে ভাই’। ‘পদাতিক’ কবি সুভাষ কার্যত: পথে নামেন, জনতার সখ্যে মাতেন, ক্রমশ তাঁর কন্ঠে উচ্চারিত হয়–রাস্তাই একমাত্র রাস্তা। সুভাষের কবিতায় রাস্তা বা পথের মেটাফর চলে আসে নানা ভাবে—
মাথায় লাঠির বাড়ি খেয়ে পড়ে-যাওয়া
গাঁয়ের হাড়-জিরজিরে বুড়োর মতো
রাস্তাটা
একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে।
(রাস্তার লোক/যতদূরেই যাই)
রবীন্দ্রনাথ, সমর সেন, সুকান্ত পথের মেটাফর ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সুভাষের সঙ্গে এঁদের কারুর এক্ষেত্রে মিল নেই। অমলেন্দু বসু একদা বলেছিলেন—সুভাষের কবিতায় তিনি পান তিনটিই সুর—ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ সুর, চড়া গলার সুর, স্বগতোক্তির সুর। তিনটিতেই লেগে আছে এক অটল অধ্যায়। চড়া গলার সুর একদা সময়ের দাবিতেই হয়ত সুভাষ, অরুণ মিত্র, বিষ্ণু দে এবং আরো অনেকের কবিতায় দেখা দিয়েছিল। সুভাষের কবিতায় পেয়েছিলাম—
বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ
রুখবো দস্যুদলকে আজ,
দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ
ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ!
(জনযুদ্ধের গান)
অশ্রুকুমার সিকদার বলেছেন নাজিম হিকমতের কবিতা অনুবাদের পর সুভাষের কবিতার শৈলীও বদলে যেতে থাকে। নাজিম হিকমতের কবিতা বেরিয়েছিল ১৯৫২-তে। তার পর ‘ফুল ফুটুক’ (১৯৫১-৫৭) নিশ্চয়ই তা মনে করাবে। কিন্তু ‘যত দূরেই যাই’ (১৯৬২) থেকে ‘ছেলে গেছে বনে’ (১৯৭২) বদলে গেছে অনেক। তারপরে বদল আসে আরো অনেক। আনুপূর্বিক কবিতা পড়তে গেলে তা পাঠকের টের না পাওয়ার কথা নয়। অশ্রুকুমার লক্ষ্য করেছেন সুভাষের কবিতা কখনও সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মতো হয়ে ওঠে, কখনো তা ‘কবিতার ছদ্মবেশে গদ্য’। কিন্তু মাঝে মাঝে যেমন কবিতাও হয়ে ওঠে গদ্য, তেমনি গদ্যেও কবিতার রঙ লাগে। রেখাচিত্র আঁকার এক দক্ষতা ক্রমশ: স্ফুটতর হয়ে ওঠে তাঁর কবিতায়—
মাথার ওপর একটানা দীর্ঘ তারে
ছড় টেনে
ঝড়ের সুর বাজাতে বাজাতে গেল
একটা মন্থর ট্রাম।
কখনও কখনও আগে অল্প কথায় গল্প বলার ঝোঁক–
অনেক অলিগলি ঘুরে
মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে
বাবা এল।
ছেলে এল না।
সুকান্তও একদা বলেছিলেন—কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি। গদ্যময় পৃথিবীতে দুজনেই একদা হতে চেয়েছিলেন–পার্টিজান কবি। কিন্তু সুভাষ দুটো দিক থেকে সরে গেলেন। প্রথমত: পার্টিপ্রচারের মুখপাত্র হয়ে থাকতে চাইলেন না। দ্বিতীয়ত: প্রসারিত বাংলায়, দুয়ার খুলে পৌঁছতে চাইলেন মানবতার রাজ্যে, দেশের সাধারণ, মারখাওয়া, বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষের মধ্যে। কবিতাকে জোর করে পিছনের সিটে বসিয়ে রেখে লড়াকু সাংবাদিক সুভাষ গ্রামে-গঞ্জে, শহর-নগরে কলকারখানায় খেতখামারে চষে বেড়িয়েছেন। লিখেছিলেন— ‘আমার চোখ আমার পা দুটিতে বাঁধা। পা নড়িয়ে নড়িয়ে আমি দেখি। …আমি দেখি বাংলাদেশের মুখ।’ রমাকৃষ্ণ মৈত্র ঠিকই বলেছেন— ‘বজবজের দু-বছর নর নারীর জীবনযাপন সুভাষের ব্যক্তিগত ও কাব্যগত জীবনে ব্যঞ্জনাক্ষুব্ধ সমুদ্রে একটি লাইট হাউস-এর কাজ করেছে।’ একটা স্তরে ছিল শপথ, অঙ্গীকার, পরিস্থিতির কথা। তারপরে এল দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গাপীড়িত ‘জীবনের গোলকধাঁধার’ কথা, ‘চিরকুট’ পর্বে। ক্ষুদ্ধ কবিকন্ঠ ছিল স্ট্রাইকের উচ্চারণে। ‘ফুল ফুটুক’ থেকেই সম্ভবত, মিছিলকে ছুঁয়েই অবশ্য, ব্যঞ্জন হেড়িয়া (বজবজের কাছে একটি জায়গা) জীবন কবিকে শিখিয়েছে মানুষের কথাকেই বড়ো করে তুলতে। ‘যত দূরেই যাই’ (১৯৬২) থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠল অতি সাধারণ লোকজনের কথা। তখন-ও অবশ্য দুলে দুলে দুলে ওঠা নিশান বন্দনা। সংকট উত্তরণের শক্তি তিনি কুড়িয়ে নিতে চান প্রকৃতি ও জীবনের দিকে চোখ রেখে। তরুণদের ওপর পুলিশ নির্যাতনে ব্যঙ্গবিদ্রূপ—
আর পাঁচ মিনিট। আর পাঁচ মিনিট
মশাইরা, দাঁড়িয়ে যান–
পড়ে যাবে আরও একটা লাশ
খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে খেলা।
সুভাস মুখোপাধ্যায় গণ জীবনের কবি, তাঁর কবিতা জীবনরসের কবিতা। তাঁর জীবনরসের ভিত শক্ত বলেই জেহাদের কবিতা আসে মাঝে মাঝে। পাবলো নেরুদার কথা মনে পড়ে, পার্থক্য সত্ত্বেও, এ প্রসঙ্গে। যতই দিন গিয়েছে সুভাষের কবিতা প্রবচন, বাগধারা, লোকগল্প, রূপকথা প্রভৃতির আশ্রয় নিয়ে বক্তব্যকে তুলে ধরেছে। কিছু উদাহরণ—
ক) লক্ষ্মীর চেলাচামুণ্ডার উৎপাতে
সরস্বতী দাঁড়ান এসে ফুটপাথে
খ) গৌরী সেনের বাপের টাকায়
বাছাধনেরা ফলার পাকায়
গ) কান-কাটাদের রাজ্যে
ঠোঁটকাটারা যাই বলুক না
আনে না কেউ গ্রাহ্যে।
ঘ) আদার ব্যাপারী তাই বুঝি না
জাহাজের হালচাল কিছুই
এই সব ব্যবহারে দুটো কাজ হয়। জনজীবনের নিবিড় সংযোগে মানুষের কাছের হয়ে ওঠে কবিতার স্বর। সমাজচেতনা, রাজনৈতিক চেতনা, জীবনচেতনা প্রকাশের স্বতন্ত্রতা ফুটে ওঠে। রাজনৈতিক কবির এই স্বতন্ত্রতা বাংলা কবিতায় অবশ্যই ব্যতিক্রম।
জনজীবনের মধ্যে সর্বদা অবস্থান কবিকে বাঁচায়, পার্টিজান কবিকেও বাঁচায়। যান্ত্রিক পার্টিজান কবিতা মুমূর্ষু হয়ে ওঠে। জনজীবন সন্নিহিত কবিতা কবিতাকে ছড়িয়ে দেয় মানুষের মধ্যে। তার মধ্যে মানুষ আবিষ্কার করতে পারে নিজেকে, ধারপাশের লোককে, মুঠো তোলা শ্লোগান তৎপর মানুষকেও। এই পথেই সুভাষের কবিতা হয়ে উঠেছে চিরভাস্বর। তাঁর শেষপর্যায়ের আচরণ ও কবি-উচ্চারণ নিয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু যথার্থ কবিতাপাঠক তাতে আবিষ্কার করতে পারেন অনেক কিছু—প্রত্যক্ষে না হোক, পরোক্ষে।
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য
- সুভাষ সুখোপাধ্যায় বোধ হয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা বা প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা লিখে কাব্যজীবন শুরু করেননি। ‘পদাতিক’ কাব্যের প্রথম কবিতা ‘সে দিনের কবিতা’-তে তিনি সমকালীন জীবনের রূপক মেলে ধরলেন।
- রাজনীতি ও কবিতাকে তিনি পৃথক করে দেখেননি। তাই ‘পদাতিক’ কাব্যগ্রন্থের ‘রোমান্টিক’ কবিতায় তিনি লিখলেন— “ছেঁড়া জুতোটার ফিতেটা বাধতে বাধতে/বেঁধে নিই মন কাব্যের প্রতিপক্ষে/ সেই কথাটাই বাধে না নিজেকে বলতে/শুনবে যে কথা হাজার জনকে বলতে।”
- আবেগের সঙ্গে বহির্বিশ্বের অপরূপ সমন্বয়ে সুভাষের ‘চিরকুট’ কাব্যটি উজ্জ্বল। এখানে কবি অভিজ্ঞতায় অনেক সুস্থির, বিশ্বাসের দীপ্তিতে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর কখনও বিদ্রুপে ব্যঙ্গে তীক্ষ, কখনও বা আবেগে ব্যথায় বিধুর। তাই এগিয়ে চলার গান বিপ্লবের সম্ভাবনায় সংহত হয়— “দিগন্তে দিগন্তে দেখি/বিস্ফারিত আসন্ন বিপ্লব।’’
- ‘মিছিলের মুখ’ কবিতায় প্রেমের নতুন স্বরূপ উদঘাটিত হল।
- বাংলা কাব্যে তাঁর অসাধারণ প্রসদ্ধির অন্যতম কারণ তাঁর কবিতার অসাধারণ আঙ্গিক সিদ্ধি, শব্দচয়নে অনায়াস সিদ্ধি ছিল লক্ষ্যণীয় যেমন— “যে ভাগে সে ভাঙ্গে/যে লড়ে সে গড়ে’’ ইত্যাদি।
- পুরাণ প্রসঙ্গের উপস্থাপনায়ও তাঁর কৃতিত্ব যথেষ্ট। যেমন— ‘শকুনি রণচণ্ডী’, ‘কুম্ভকর্ণ-দধিচীর হাড়’ প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণ প্রতিমায় তাঁর কাব্য সুসজ্জিত। ‘সাত ভাই চম্পা’র প্রসঙ্গ এনেছেন রূপকথার আর্কেটাইপে। কবিতার মধ্যে নাটকীয়তা ও গল্পময়তা এনেছেন তিনি। ছন্দের ক্ষেত্রে স্তবক বিন্যাসে নতুনত্ব এনেছেন কবি।


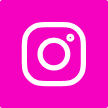



Leave a Reply