বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর।
বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ
সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের অনুবাদের মধ্যে দিয়ে বাংলা নাটক রচনার সূত্রপাত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এদেশে রঙ্গালয় ও নাটক পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলতে থাকে। কেননা নাট্যশালার সঙ্গে নাটক রচনার সূত্রটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে হেরাসিম (গেরাসিম) লেবেডেফ নামে রুশদেশীয় এক ভদ্রলোক কলকাতায় প্রথম নাট্যশালা নির্মাণ করেন, যা ‘বেঙ্গলী থিয়েটার’ নামে খ্যাত।
বেঙ্গলী থিয়েটারে লেবেডেফ ‘The Disguise’ নামে একটি ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ অভিনয় করেন ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর। এছাড়া মলিয়ের-এর ‘Love is the Best Doctor’-এর অনুবাদ করেন লেবেডেফ। এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার পর থেকে নাট্যমোদীরা জানতে পারল যাত্রা ছাড়াও অন্য কোন বিনোদন ব্যবস্থা রয়েছে। এর পরে লেবেডেফের অনুসরণে কেউ কেউ ধনী-জমিদাররা তাদের বাড়িতে সখের নাট্যালয় তৈরি করলেন এবং নাট্যরচনায় উৎসাহিত করলেন নাট্যকারদের। কেননা, সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়া নাট্যশালার ডাকেই নাট্যকার মধুসূদনের আবির্ভাব ও বাংলা নাটকের জয়যাত্রা সেখান থেকেই শুরু হয়।
লেবেডেফের ‘বেঙ্গলী থিয়েটার’ প্রতিষ্ঠার পর সখের নাট্যশালার সূত্রপাত ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে এবং তার বিস্তৃতি ১৮৭২ সালে ন্যাশানাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার প্রাক্-মুহূর্ত পর্যন্ত। কারণ ন্যাশানাল থিয়েটারই প্রথম সাধারণের রঙ্গালয়। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর তার নারকেলডাঙ্গার বাড়িতে হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে প্রথম রজনীতে অভিনীত হয় ভবভূতির ‘উত্তররামচরিতে’র ইংরেজি অনুবাদ।
এরপর ১৮৩৫ সালে নবীনচন্দ্র বসু তাঁর শ্যামবাজারের বাড়িতে নাট্যশালা নির্মাণ করেন। প্রথম অভিনয় হয় ভারতচন্দ্রের ‘বিদ্যাসুন্দরের’ নাট্যরূপ। তিনি স্টেজ, দৃশ্যপট ও আলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। মঞ্চে তিনি প্রথম অভিনেত্রী গ্রহণ করেন।
১৮৫৩ সালে নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ওরিয়েন্টাল থিয়েটার’। এখানে ‘ওথেলো’ নাটকের অভিনয় হয়। ১৮৫৪ সালে প্যারীমোহন বসু তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ‘জোড়াসাঁকো থিয়েটার’ প্রতিষ্ঠা করে শেক্সপিয়রের ‘জুলিয়াস সীজার’-এর অভিনয় করান।
কলকাতার প্রখ্যাত ধনী আশুতোষ দেব তাঁর বাড়িতে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। এখানে নন্দকুমার রায়ের লেখা ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলা’ নাটক (কালিদাসের নাটকের অনুবাদ) অভিনীত হয়। বহুদিন পরে বাঙালির রঙ্গালয়ে বাংলা নাটকের অভিনয়ে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এছাড়া বাণভট্টের ‘কাদম্বরী’ অবলম্বনে মণিমোহন সরকারের ‘মহাশ্বেতা’ নাটকও এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।
রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটকের অভিনয় হয় ১৮৫৭ সালে রামজয় বসাকের বাড়ির নাট্যশালায়। ১৮৫৮তে এই নাটকের অভিনয় হয় গদাধর শেঠের বাড়ির নাট্যশালায়। তাছাড়া এই একই বছর চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়ির নাট্যশালায় এই নাটক অভিনীত হয়।
পরবর্তীকালে ১৮৫৬-তে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, ১৮৫৮-তে পাইকপাড়ার বেলগাছিয়া নাট্যশালা, ১৮৫৯ সালে রামগোপাল মল্লিকের প্রাসাদে মেট্রোপলিটন থিয়েটার, ১৮৬৫-তে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গনাট্যালয়, ১৮৬৫-তে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি, ১৮৬৫-তে ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো থিয়েটার, ১৮৬৮-তে বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় এবং ১৮৬৮-তে বাগবাজার এমেচার থিয়েটার এবং শ্যামবাজার নাট্যসমাজ প্রভৃতি সখের রঙ্গালয় বাংলা নাটক রচনাকে উৎসাহিত করে।
প্রাক্-মধুসূদন নাট্যপর্বে উল্লেখযোগ্য নাট্যকাররা হলেন— নন্দকুমার রায়, তারাচরণ শিকদার, যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, উমেশচন্দ্র মিত্র এবং রামনারায়ণ তর্করত্ন।
নন্দকুমার রায়
১৮৫৫ সালে নন্দকুমার রায় কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’ নাটকের অনুবাদ করেন। ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলা’ নামে। নাটকটি আশুতোষ দেবের বাড়িতে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। বাংলা নাট্যসাহিত্যে কালিদাসকে প্রথম আনয়নের ক্ষেত্রে তার নাম বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
তারাচরণ শিকদার
বাংলা নাটকের উদ্ভবপর্বে মৌলিক নাটক রচনার সূত্রপাত ১৮৫২ সালে তারাচরণ। শিকদার ও যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের যথাক্রমে ‘ভদ্রার্জুন’ ও ‘কীর্তিবিলাস’ নাটকের মধ্যে দিয়ে।
তারাচরণ শিকদারের ‘ভদ্রার্জুন’ (১৮৫২) শুধু প্রথম নাটক নয়, তা প্রথম সার্থক নাটক। সকমার সেন যথার্থই বলেছেন—“ইহাই (ভদ্রার্জুন) ইংরেজি ও সংস্কৃতের যুক্ত আদর্শে রচিত প্রথম মৌলিক মধুরান্তিক বাঙ্গালা নাটক”। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ-৪৮)।
মহাভারতের অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রাহরণ নাটকটির বিষয়বস্তু। নাটকটি পঞ্চাঙ্ক নাটক। ইংরেজি নাটকের মতো এই নাটকের অঙ্ক বিভাগ করা হয়েছে। এই নাটকের মধ্যে সংস্কৃত প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে। নাটকের দৃশ্যের নাম করা হয়েছে সংযোগস্থল। নাটকের প্রস্তাবনার নাম করা হয়েছে ‘আভাস’। নাটকের প্রথম অঙ্কে রয়েছে যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদের আগমন এবং তারই চক্রান্তে বার বৎসরের জন্য অর্জুনের রাজ্যত্যাগ। দ্বিতীয় অঙ্কে সুভদ্রার বিবাহের উদ্যোগ। তৃতীয় অঙ্কে প্রভাসতীর্থে অর্জুনের আগমন, সুভদ্রা ও অর্জুনের পারস্পরিক পূর্বরাগ ও বিবাহ। চতুর্থ অঙ্কে নারদ কর্তৃক দুর্যোধনের বরবেশে দ্বারকায় যাত্রা। পঞ্চম অঙ্কে সুভদ্রাহরণ, কৌরবদের অপমান ও বলরামের ক্ষোভ। নাট্যকার মহাভারতের অনুসরণে নাটক রচনা করলেও বাঙালির স্বভাবধর্ম অনুযায়ী ঘটনাকে সাজিয়েছেন। কারণ এতে বাঙালি সমাজের বাস্তব চিত্র যেমন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দুশ্চিন্তা, অন্তঃপুরিকাদের কথোপকথন, বিবাহের প্রথা ও স্ত্রী আচার প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।
নাটকের সংলাপও গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত। পয়ার ও ত্রিপদীতে পদ্যগুলি রচিত। গদ্যাংশের ভাষা সরল ও গ্রাম্যতা মুক্ত। বলদেব ছাড়া কোন প্রধান চরিত্র তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে অপ্রধান চরিত্রগুলি যেমন—ভীম, রোহিণী, দুঃশাসন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নায়িকা সুভদ্রার ভূমিকা নাটকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। তাহলেও পাশ্চাত্য রীতির আঙ্গিক অনুসরণে বাংলা মৌলিক নাটকের সূত্রপাত হিসাবে তারাচরণের ‘ভদ্রার্জুন’ বাংলা নাট্যসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত
‘কীর্তিবিলাস’ (১৮৫২) নাটকের জন্য যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৭২) বাংলা নাটকে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। ‘কীর্তিবিলাস’ নাটকটি বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম বিয়োগান্ত নাটক। আসলে সংস্কৃত নাটক যেহেতু বিষাদান্ত হয় না, তাই সংস্কৃত নাটকের অনুকারী নাট্যকাররা এই রীতি ভাঙতে পারেননি। তাই যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত প্রচলিত এই রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে প্রথম বিষাদান্ত নাটক রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন।
‘কীর্তিবিলাস’ নাটকের মূল বিষয় হল বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা কি বিপদ ঘটায় তার পরিণাম। সপত্নী পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার-কাহিনি অবলম্বনে রূপকথার গল্পের আদলে নাট্যকার কাহিনি বিন্যাস করেছেন। পাশ্চাত্য নাটকের মতো ‘কীর্তিবিলাস’ পঞ্চাঙ্ক নাটক। সংস্কৃত নাটকের মতো গুরুতে প্রস্তাবনা রয়েছে। প্রত্যেক অঙ্ক বিভিন্ন দৃশ্যে বিভক্ত। দৃশ্যের নাম ‘অভিনয়’। নাটকটিতে শেক্সপিয়ারের হ্যামলেটের অনুসরণ প্রচেষ্টা আছে। নাটকটি গদ্যে ও পদ্যে রচিত। চটুল সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব লক্ষ করা যায়। স্বগতোক্তির বাহুল্যও রয়েছে। ‘কীর্তিবিলাস’ নাটকের পদ্য পয়ারের শৃঙ্খলে বাঁধা।
নাটকটি বিষাদান্ত নাটক হলেও সেই পরিণতি দর্শককে অভিভূত করতে পারে না। কারণ কার্য-কারণ পরম্পরায় নাটকের কাহিনি গড়ে ওঠেনি। রাজপুত্রের প্রতি রাজমহিষীর বিদ্বেষভাব, সপত্নী পুত্রের প্রতি হিংসা নাটকীয় ধারার সঙ্গে বর্ণিত হয়নি, বরং তা অনেকটা অসংলগ্ন। তবুও বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম বিষাদান্ত নাটক রচনার প্রয়াস হিসাবে তারাচরণ শিকদার স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।
হরচন্দ্র ঘোষ
বাংলা নাটকের উদ্ভবপর্বে হরচন্দ্র ঘোষ অনুবাদমূলক নাটক রচনার জন্য খ্যাতি করেছেন। শেক্সপীয়ারের প্রথম বাংলা নাট্যানুবাদ করে তিনি স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।
হরচন্দ্র ঘোষ ১৮৫৩ সালে শেকসপিয়রের মার্চেন্ট অব ভেনিস (Merchart of Venice) অবলম্বনে ‘ভানুমতী চিত্তবিলাস’ রচনা করেন। নাটকটি হুবহু অনুবাদ নয়। নাট্যকার নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন—“যদ্যপিও ইহাতে উল্লিখিত ইংরেজি কাব্যের আনুপূর্বিক অনুবাদ না হউক তথাপি বর্ণিত মহাকবি শেক্সপিয়রের সপ্তাবের বশে অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মর্ম গ্রহণ করা হয়েছে।’’
নাট্যকারের নাটক রচনার উদ্দেশ্য ছিল এদেশের বালকদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য উৎসাহ বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্য সফল হয়নি এবং নাটকটি জনপ্রিয়তাও লাভ করেনি। নাটকটি গদ্যে ও পদ্যে লেখা।
এরপর ১৮৫৮ সালে ‘কৌরব বিয়োগ’ রচনা করেন। এই নাটকটি গদ্যে রচিত। মহাভারতের দুর্যোধনের উরুভঙ্গ এবং অন্ধ রাজার যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়ার কাহিনি এই নাটকের বিষয়। নাটকটি স্কুলপাঠ্য করার জন্য রচিত হয়েছিল, নাট্যকারের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। নাটকটি বিবরণধর্মী এবং গল্প বলার ভঙ্গিতে রচিত।
১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষ শেক্সপিয়ারের ‘রোমিও জুলিয়েট’ অবলম্বনে ‘চারুমুখচিত্তহরা’ নাটক রচনা করেন। সংস্কৃত নাটকের মতো এই নাটকে নান্দী ও প্রস্তানা যুক্ত হয়েছে। মূলত অভিনয়ের জন্য নাটকটি রচিত। সংলাপের সারল্য বেশ আকর্ষণীয়।
তাঁর সর্বশেষ নাটক ‘রজত গিরিনন্দিনী’ ১৮৭৪ সালে রচিত। নাটকটি বর্মী আখ্যায়িকা অবলম্বনে লেখা ইংরেজি নাটকের অনুবাদ। ১৮৭২-এ সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ায় নাটক রচনা ও অভিনয় দেখার প্রবণতা বাড়ায় তিনি এই নাটক রচনা করেন। এটিও উচ্চাঙ্গের নাটক নয়।
শেক্সপীয়ারের নাটক অনুসরণে বাংলা নাটক রচনার প্রথম প্রয়াসের দিক থেকে হরচন্দ্র ঘোষ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।


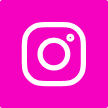


Leave a Reply