বাক্য কাকে বলে? বাক্যের বিভিন্ন প্রকারভেদ উদাহরণসহ আলোচনা কর।
বাক্য ও বাক্যতত্ত্ব
ইংরেজি syntax শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলায় আমরা ‘বাক্যতত্ত্ব’ কথাটি ব্যবহার করে থাকি। ইংরেজিতে এই Syntax শব্দটি এসেছে গ্রীক Syntaxis থেকে। গ্রীক ভাষায় এই শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন গ্রীক বৈয়াকরণ দিওনুসিওস থ্রাক্স (Dionusious Thrax)। গ্রীক ভাষায় শব্দটির অর্থ ‘একত্র বিন্যাস’। এই থেকে বাক্যমধ্যে শব্দসমূহের একত্র বিন্যাসের তত্ত্ব অর্থে ক্রমে Syntax কথাটি প্রচলিত হয়।
Syntax হল যেহেতু বাক্যের তত্ত্ব সেহেতু এই বাক্যতত্ত্বের আলোচনায় প্রবেশ করার আগে প্রথমেই জানা দরকার ভাষাবিজ্ঞানে বাক্য (Sentence) বলতে কী বোঝায়? প্রাথমিক পরিচয়ের জন্যে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া সংজ্ঞাটি স্মরণ করা যেতে পারে— “যে পদ বা শব্দ সমষ্টির দ্বারা কোনও বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বক্তার ভাব প্রকটিত হয়, সেই পদ বা শব্দ-সমষ্টিকে বাক্য (sentence) বলে।’’ এই সংজ্ঞাটিতে বাক্যের শুধু ভাব প্রকাশের দিকটির উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, বাক্যের গঠনগত বৈশিষ্ট্যটি উল্লিখিত হয়নি, তাই ভাষাচার্য পরবর্তীকালে বাক্যের অর্থগত ও গঠনগত দু’টি দিক মিলিয়ে একটি সংশোধিত সংজ্ঞা রচনা করেন। তাতে তিনি বলেন— “কোনও ভাষায় যে উক্তির সার্থকতা আছে, এবং গঠনের দিক হইতে যাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেইরূপ একক উক্তিকে ব্যাকরণে বাক্য (Sentence) বলা হয়।’’
অর্থাৎ বাক্য হচ্ছে এমন কতকগুলি নির্বাচিত উপাদানের পরম্পরাক্রমিক বিন্যাস যেগুলিকে ভাষাবিশেষের বিশেষ ছাঁদ, রূপপরিবর্তন ও সুরতরঙ্গের বিশেষ নিয়ম অনুসারে মিলিত করে একটি এককরূপে গড়ে তোলা হয়েছে। সহজ করে বলা যায়, বাক্য হচ্ছে ভাষার একক (unit); ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে প্রথম যে বৃহত্তম একক আমরা পাই তা হল বাক্য। এই বাক্য এমন কতকগুলি নির্বাচিত উপাদান নিয়ে গঠিত যেগুলিকে আমরা শব্দ বলি। একটি ভাষায় যত শব্দ প্রচলিত আছে তার সবগুলি একটি বাক্যে ব্যবহৃত হয় না, ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন অনুসারে আমরা এক-একটি বাক্যে নির্বাচিত কয়েকটি শব্দই ব্যবহার করে থাকি। বাক্যের এই উপাদানগুলি বা শব্দগুলিকে বাক্যের মধ্যে যে মিলিত করা হয় তাদের সেই মিলনের ব্যাপারে প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব নিয়ম আছে।
বাক্য আমাদের মনের ভাব বিনিময় মাধ্যম হল বাক্য। কতকগুলি অর্থপূর্ণ পদ পাশাপাশি বসে মনের ভাবকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তখন তা বাক্য হয়ে ওঠে। বাক্যের মূলপদ হল ক্রিয়াপদ। এই ক্রিয়াপদ অর্থের ভিত্তিতে মূলত দুই প্রকার—সমাপিকাক্রিয়া ও অসমাপিকাক্রিয়া। একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়াপদ একটি থাকতেই হয়। আসলে সমাপিকা ক্রিয়াই অর্থকে পূর্ণ করে বাক্যকে সম্পূর্ণ করে। যেমন—‘লকডাউনের জন্য ছাত্রছাত্রীরা কলেজ না গিয়ে বাড়িতে বসে ইন্টারনের ব্যবহার করে পড়াশোনা করছে।’ এই বাক্যে না গিয়ে, বসে, করে এই তিনটি অসমাপিকা ক্রিয়া রয়েছে কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া একটি তা হল ‘করছে’। অন্যদিকে একটি পূর্ণ বাক্যকে অর্থের বাস্তবতা সাধন করতে তিনটি গুণকে বজায় বাখতে হয়। সেগুলি হল— (১) যোগ্যতা (২) আকাঙ্ক্ষা (৩) আসত্তি বা নৈকট্য।
যোগ্যতা
আমরা একাধিক পদকে পাশাপাশি বসিয়ে দিলেই বাক্য গঠন করতে পারব না। অর্থের বাস্তবতাকে বজায় না রাখলে কিন্তু বাক্য হয় না । অর্থের এই বাস্তবতাকেই যোগ্যতা বলে। যেমন—‘সূর্য রাত্রিতে দেখা যায় । গঠনগত দিক থেকে অর্থাৎ পদগুলি ব্যবহারে কোন ভূল নেই কিন্তু পদগুলির নিজস্ব অর্থ থাকলেও বাক্যটির বাস্তবের অর্থ ঠিক নয়। সূর্য রাত্রিতে দেখা যায় না দিনের বেলা দেখা যায়। অতএব বাক্যটির যোগ্যতা নেই। সুতরাং বলা যায় বাক্যে ব্যবহৃত পদ সমষ্টির অর্থগত সামঞ্জস্যকেই বলে যোগ্যতা।
আসক্তি
পদগুলিকে এলোমেলোভাবে সাজালে বাক্য হয় না। পদগুলিকে সঠিকস্থানে বসাতে হয়। তবেই অর্থ বোধগম্য হয়। অর্থানুযায়ী পদগুলিকে সঠিকভাবে সাজানোকেই বলা হয় আসক্তি বা নৈকট্য। যেমন— করছে ছাত্রছাত্রীরা বসেই পড়াশোনা বাড়িতে। এই বাক্যটির অর্থ বোধগম্য নয় কারণ পদগুলিকে ঠিকঠাক সাজানো হয়নি। আসলে বাক্যটির আসক্তি বা নৈকট্যের অভাব বর্তমান। বাক্যটি ঠিকঠাক সাজালে হয়—ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতে বসেই পড়াশোনা করছে।
আকাঙ্ক্ষা
আমরা যখন কোন বাক্য গঠন করি বা পড়ি, কিছুটা পড়ার পর একটা জিজ্ঞাসা তৈরি হয়, তাকেই আকাঙ্ক্ষা বলে, যেমন—আমি বাড়িতে বসেই-, এতটুকু বলার পর একটা কৌতূহল তৈরী হয়, তারপর কী? বাক্যের এই কৌতূহল সৃষ্টির ক্ষমতাই হল ‘আকাক্ষা’। তারপর আকাঙ্ক্ষা নিরসনের ক্ষমতা বাক্যের থাকতে হবে অর্থাৎ বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করতে হবে— আমি বাড়িতে বসেই পড়াশোনা করব। বাক্যের অর্থগত চাহিদাপূরণের ক্ষমতাকেই আকাঙ্ক্ষা বলে।
এই নিয়মগুলিকে একত্রে পদবিধি বা বাক্যবিধি বলা যায়। এইসব নিয়মের দুটি দিক হল বাক্যের মধ্যে শব্দগুলি সাজাবার বা বিন্যাসের নিয়ম আর বাক্যের প্রয়োজন অনুসারে শব্দগুলির রূপ পরিবর্তনের নিয়ম। বাক্যের মধ্যে শব্দগুলির বিন্যাস (word order) অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে কোন শব্দ কোথায় বসবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী রকম হবে তা ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে বলে বাক্যতত্ত্ব (Syntax)।
ঐতিহ্যগত ব্যাকরণে বাক্যতত্ত্ব ও বাংলা বাক্য
বাক্যের বিভিন্ন দিকতার গঠন, উপাদান, শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত ঐতিহ্যগত ব্যাকরণেই হয়েছিল। আধুনিক বর্ণনামূলক ও গঠনগত (Descriptive and Structural) ভাষাবিজ্ঞান এবং বিশেষ করে রূপান্তমূলক-সৃজনমূলক ব্যাকরণে (Transformational Generative Grammar) বাক্যতত্ত্ব যে রকম সূক্ষ্ম সমুন্নতি লাভ করেছে তাতে আগেকার ঐতিহ্যাগত ব্যাকরণে আলোচিত বাক্যতত্ত্বের অনেক ত্রুটি ও ঘাটতি চোখে পড়তে পারে। কিন্তু যেহেতু ঐতিহ্যগত ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক ছিল না, মূলত এককালিক বর্ণনামূলকই ছিল, এবং যেহেতু তার কিছুকিছু মূল ধারণা আধুনিক বাক্য বিশ্লেষণেও প্রতিষ্ঠাভূমি রূপে কাজ করে, সেহেতু আধুনিক বর্ণনামূলক বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনার আগে ঐতিহ্যগত ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্বের মূলসূত্রটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।
বাংলা বাক্যের গঠন ও গঠনগত শ্রেণীবিভাগ
ঐতিহ্যগত ব্যাকরণে বাক্যকে প্রথমে দুটি অংশে ভাগ করা হয়— উদ্দেশ্য (Subject) ও বিধেয় (Predicate)। মোটামুটিভাবে যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে বিধেয় বলে। যেমন— অপু চলে গেল। এই বাক্যে ‘অপু’ হল উদ্দেশ্য এবং ‘চলে গেল’ হল বিধেয়। উদ্দেশ্য ও বিধেয় বাক্যের গঠনের এই দুটি মৌলিক উপাদান নির্ণয় করে ঐতিহ্যগত ব্যাকরণে গঠনগত দিক থেকে বাক্যকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(১) সরল বাক্য (Simple Sentence) মিশ্র বা জটিল বাক্য (Complex Sentence) (৩) যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য (Compound Sentence)।
সরলবাক্য
একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) নিয়ে গঠিত বাক্যকে সরল বাক্য বলা হয়। যেমন— ছাত্ররা লেখাপড়া করছে। এখানে একটি কর্তা— ছাত্ররা, এবং ক্রিয়া একটি— করছে।
যৌগিক বাক্য
একের বেশী প্রধান উপবাক্য সংযোগে গঠিত, কোনো সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য তৈরি করে, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন— তিনি পন্ডিত কিন্তু তিনি সাধাসিধে। এখানে দুটি সরলবাক্য বা উপবাক্য আছে— ‘তিনি পন্ডিত’ এবং ‘তিনি সাধাসিধে’। এই বাক্য দুটিকে একটি সংযোগক দ্বারা কিন্তু যুক্ত করা হয়েছে।
জটিল বাক্য
একটি প্রধান বাক্যাংশ এবং এক বা একাধিক অপ্রধান বাক্যাংশ নিয়ে গঠিত বাক্যকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলা হয়। যেমন—যদি বিনয় পাশ করে তাহলে সে পুরস্কার পাবে। এখানে ‘সে পুরস্কার পাবে’ মূল বক্তব্য বা প্রধান বাক্য, আর শর্তাধীন বাক্য বা অপ্রধান বাক্য হল—‘যদি বিনয় পাশ করে।’
জটিলবাক্যের অন্তর্গত প্রধান ও অপ্রধান দুটি বাক্যকেই খণ্ডবাক্য বা উপবাক্য (Clause) বলে। প্রধান ও অপ্রধান দুটি বাক্যই যেহেতু একটি বড় বাক্যের অংশ, সেহেতু বড়বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি হল উপবাক্য বা খন্ডবাক্য। উপবাক্যকে দু ধরনের— ১. প্রধান বা স্বাধীন উপবাক্য ২. আশ্রিত উপবাক্য।
উপবাক্য (clause) ও পদগুচ্ছ/বাক্যাংশ(Phrase)
উপবাক্য বাক্যের সমগ্র অংশ হলেও একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় থাকে। কিন্তু পদগুচ্ছে সর্বদা উদ্দেশ্য ও বিধেয় সর্বদা থাকে না। পদগুচ্ছ হল এক আপেক্ষিক একক যা গোষ্ঠিবদ্ধ পদসমষ্টি। এই বিষয়ে ড. রামেশ্বর শ’ সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন—“যে বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে ভালবাসতেন তিনি পথের পাঁচালি লিখতে পেরেছেন’। এই বাক্যে ‘যে বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে ভালবাসতেন’ হল আশ্রিত বা অধীন উপবাক্য আর ‘তিনি পথের পাঁচালি লিখতে পেরেছেন’ হল প্রধান উপবাক্য। আর ‘প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ পথের পাঁচালি লিখতে পেরেছেন’—এই বাক্যে ‘প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ’ হল একটা পদগুচ্ছ।
বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে বাক্যতত্ত্ব ও বাংলা বাক্য
বর্ণনা অনুসারে বাক্য পাঁচ প্রকার— ১. নির্দেশক বাক্য, ২. প্রশ্নসূচক বাক্য, ৩. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য, ৪. প্রার্থনাসূচক বাক্য, ৫. বিস্ময়সূচক বাক্য
নির্দেশক বাক্য
যে বাক্যে কোন বক্তব্য বা তথ্য বা বিবৃতি প্রকাশ করা হয় তাকে নির্দেশক বাক্য বলে। যেমন— আমরা গ্রামে বাস করি। নির্দেশক বাক্য আবার দুই প্রকারের— ক) ইতিবাচক/হ্যাঁ-বাচক/অস্তৰ্থক বাক্য খ) নেতিবাচক/না-বাচক/ নঞর্থক বাক্য।
ক) ইতিবাচক/হ্যাঁ-বাচক/অস্তৰ্থক বাক্য— যে বাক্যে অর্থকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় বা স্বীকার করা হয় তাকে ইতিবাচক বাক্য বলে। যেমন—আমি গান গাই।
খ) নেতিবাচক/না-বাচক/নঞর্থক বাক্য— যে বাক্যে অর্থ না অর্থে প্রকাশ করা হয় তাকে নেতিবাচক বাক্য বলে। যেমন—আমি গান গাই না।
প্রশ্নসূচক বাক্য
যে বাক্যে কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা প্রকাশিত হয়, তাকে প্রশ্নসূচক বাক্য বলে। যেমন—তুমি কোথায় আছো?
অনুজ্ঞাসূচক বাক্য
যে বাক্যে আদেশ, অনুরোধ, উপরোধ ইত্যাদি প্রকাশ করা হয় তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে। যেমন—বাড়িতে পড়তে বসো।
প্রার্থনাসূচক বাক্য
যে বাক্যে মনের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাকে প্রার্থনাসূচক বাক্য বলে। যেমন—হে স্রষ্টা আমাদের রোগমুক্তি দাও।
বিস্ময়সূচক বাক্য
যে বাক্যে আশ্চর্য হওয়ার অনুভূতি প্রকাশিত হয়, তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। যেমন— সে কী ভীষণ পরিস্থিতি!


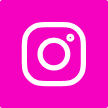


Leave a Reply