বিভক্তি কাকে বলে, উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোচনা কর।
বিভক্তি
‘বিভক্তি’ কথার আক্ষরিক অর্থ হল ‘বিভাজন’। বিভক্তিগুলি পদকে বাক্যের মধ্যে তাদের ভূমিকা ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভক্ত করে। বিভক্তি আছে বলেই প্রতিটি পদ বাক্যের মধ্যে নিজের অবস্থান, গুরুত্ব ও কার্যকারিতা স্পষ্ট করতে পারে। একক ভাবে শব্দ বা ধাতুকে বাক্যে ব্যবহার করা যায় না। কারণ বিভক্তিহীন শব্দ বা ধাতু বাক্যের মধ্যে নিজের অবস্থান ও কার্যকারিতা খুঁজে পায় না। পদগুলির ভিতর পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনেও বিভক্তি বড়ো ভূমিকা পালন করে। সুতরাং বাক্যের মধ্যে বিভক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অথচ বিভক্তির সুস্পষ্ট কোনও অর্থ নেই। বিভক্তি এমন এক সূক্ষ্ম সুতোর মতো কাজ করে, যা বাক্যস্থ পদগুলিকে নিজের নিজের জায়গায় বেঁধে রাখে।
যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ শব্দ বা ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে পদ গঠন করে এবং বাক্যের মধ্যে পদগুলির ভূমিকা, পারস্পরিক সম্পর্ক ও বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে, তাকে বিভক্তি বলে।
বিভক্তির শ্রেণিবিভাগ
বিভক্তিকে তার ভূমিকা অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা হয়— ১. শব্দবিভক্তি, ২. ধাতুবিভক্তি বা ক্রিয়াবিভক্তি।
শব্দবিভক্তি
যে বিভক্তি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দকে নামপদে পরিণত করে বাক্যে ব্যবহারযোগ্য করে তোলে, তাকে শব্দবিভক্তি বলে। শব্দবিভক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কারক নির্দেশ করা, অর্থাৎ নামপদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্পর্ক স্থাপন করা।
মৌলিক বিভক্তি
যে বিভক্তিগুলি অন্য কোনো বিভক্তি থেকে সৃষ্টি হয়নি, অর্থাৎ যারা অন্য কোনো বিভক্তির রূপান্তরিত চেহারা নয়, তাদের বলে মৌলিক বিভক্তি। বাংলা ভাষায় এর বিপরীত কোনো পরিভাষা নেই। যে বিভক্তিগুলি অন্য কোনো বিভক্তি থেকে উৎপন্ন হয়, তাদের আমরা সাধিত বিভক্তি বলতে পারি। বাংলা ভাষায় মৌলিক শব্দবিভক্তি আছে ৫ টি। এগুলি হল— কে, রে, র, এ, তে। অন্য সব বিভক্তি এই তিনটি বিভক্তি থেকেই পাওয়া যায়। যেমন: কে>একে, রে>এরে, র>এর/দের/কার, এ>য়, তে>এতে প্রভৃতি। এইগুলিকে সাধিত বিভক্তি বলা যায়।
তির্যক বিভক্তি
সংস্কৃত ভাষায় কোন কারকের কোন বচন ও কোন পুরুষে কী শব্দবিভক্তি প্রয়োগ করা হবে, তা সুনির্দিষ্ট করা আছে। বাংলায় শব্দবিভক্তিগুলি সংস্কৃতের মতো নির্দিষ্ট কারকের জন্য নির্দিষ্ট করা নেই। মোটামুটিভাবে বলা যায় বাংলার প্রায় সব শব্দবিভক্তিই একাধিক কারকে এবং কিছু কিছু বিভক্তি সব কারকেই ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলা কারকগুলিরও নিজস্ব বিভক্তি আছে। তবে কার্যক্ষেত্রে এমনটা ঘটে না। এক কারকের বিভক্তি অন্য কারকে প্রযুক্ত হয়ে যায়। এইভাবে যখন এক কারকের বিভক্তি অন্য কারকে প্রযুক্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় তির্যক বিভক্তি। বর্তমানে অধিকাংশ পাঠ্য বইয়ে বলা হয়েছে: যে বিভক্তি একাধিক কারকে ব্যবহৃত হয়, তাকে তির্যক বিভক্তি বলে। ধারণাটি ভুল নয়, তবে বিভ্রান্তিকর। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। আমার জানি ‘তে’ বিভক্তি সাধারণ ভাবে অধিকরণ কারকের বিভক্তি হলেও বিভিন্ন কারকে এর প্রয়োগ দেখা যায়, তাহলে কি ‘তে’ বিভক্তিকে আমরা সবসময়ই তির্যক বিভক্তি বলবো? আমরা যদি বলি: ‘আমি বাড়িতে আছি।’ তাহলে অধিকরণে ‘তে’ বিভক্তির প্রয়োগ ঘটেছে। এটি কি তির্যক বিভক্তি? না, এটি তির্যক বিভক্তি নয়। যদি বলা হয় ‘বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।’ তাহলে দেখা যাচ্ছে কর্তৃ কারকে ‘তে’ বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে। এইটি হল তির্যক বিভক্তি। সুতরাং কোনো বিভক্তি একাধিক কারকে প্রযুক্ত হলেই তাকে আমরা তির্যক বিভক্তি বলতে পারি না, ওই বিভক্তিটি সাধারণ ভাবে যে কারকে প্রযুক্ত হওয়ার কথা, যদি সেই কারকে প্রযুক্ত না হয়ে অন্য কারকে প্রযুক্ত হয়, তখনই তাকে তির্যক বিভক্তি বলা যাবে। এই প্রসঙ্গে নিচের তালিকায় আমরা দেখে নিই বাংলায় কোন কারকে কোন বিভক্তির প্রয়োগ স্বাভাবিক।
বাংলা কারক ও অকারক পদের স্বাভাবিক বিভক্তি ও অনুসর্গ
কর্তৃ কারক— শূন্য বিভক্তি
কর্ম কারক— কে, রে বিভক্তি
করণ কারক— দ্বারা, দিয়ে প্রভৃতি অনুসর্গ
নিমিত্ত কারক— জন্য, নিমিত্ত প্রভৃতি অনুসর্গ
অপাদান কারক— থেকে, চেয়ে প্রভৃতি অনুসর্গ
সম্বন্ধ পদ— র, এর, দের,কার প্রভৃতি বিভক্তি
অধিকরণ কারক— এ, তে, য় বিভক্তি
সম্বোধন পদ— শূন্য বিভক্তি
শূন্য বিভক্তি
যে বিভক্তি অপ্রকাশিত থাকে, যার কোনো চিহ্ন বা বাহ্যিক রূপ নেই, তাকে শূন্য বিভক্তি বলে। শূন্য বিভক্তির ব্যাপারেও একটি মারাত্মক ভুল ধারণা কোনো কোনো বইয়ে রয়েছে। সে সব বইয়ে বলা হয়েছে শূন্য বিভক্তির চিহ্ন ‘অ’। (তাঁদের এই ভ্রান্তির একটিই কারণ, তা হল— ‘অ’-এর কোনো কার নেই।) কিন্তু বাংলা ভাষায় ‘অ’ বিভক্তি বলে কোনো বিভক্তি নেই। এই বিষয়টি যুক্তি সহকারে প্রমাণ করাও যায়। এখানে তিনটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করছি।
১. শুভ আজ কলকাতা থেকে আসছে। –এই বাক্যে শুভ পদটিতে শূন্য বিভক্তি আছে। এখন আমরা জানি ‘শুভ’ (শুভ = শ্+উ+ভ্+অ) শব্দটিতে আগে থেকেই শেষ ধ্বনি রূপে অ আছে। এখন এর সাথে ‘অ’-বিভক্তি যুক্ত হলে সন্ধির নিয়মে শুভ+অ=শুভা হয়ে যেতো।
২. দৃশ্যটি দেখে আমার বাক্ হারিয়ে হারিয়ে গেলো।–এই বাক্যের বাক্ পদটিতেও শূন্য বিভক্তি আছে। শূন্য বিভক্তি = অ হলে ‘বাক্’ শব্দটি আর হসন্ত হতো না। হস্ চিহ্নটি লোপ পেতো।
৩. বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।–বিদ্যুৎ পদে শূন্য বিভক্তি আছে। শূন্য = ‘অ’ হলে বিদ্যুৎ+অ = বিদ্যুত হতো (ঠিক যেমন ভাবে বিদ্যুৎ+এ = বিদ্যুতে হয়), অর্থাৎ, ৎ-টি স্বরান্ত ত-এ পরিণত হতো।
উপরের তিনটি উদাহরণ থেকে খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, শূন্য বিভক্তি আসলেই শূন্য, এর কোনো ধ্বনি হয় না। তা ছাড়া অ একটি পরিপূর্ণ স্বরধ্বনি, তাকে শূন্যের সঙ্গে অভিন্ন করে দেওয়া কখনোই যুক্তিযুক্ত নয়। ‘অ’ যদি শূন্য হয়, তবে ‘এ’ কেন শূন্য নয়? দুটিই তো স্বর।
সমান্তরাল বিভক্তি
এই পরিভাষাটি নতুন শোনা যাচ্ছে। আমরা দেখেছি বাংলা ভাষায় একই অর্থবহ একাধিক বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। এদেরকেই সমান্তরাল বিভক্তি বলা হয়। যেমন: এ, তে, য়— তিনটি বিভক্তি সম্পূর্ণ সমার্থক।
ধাতুবিভক্তি বা ক্রিয়াবিভক্তি
যে বিভক্তিগুলি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধাতুকে সমাপিকা ক্রিয়াপদে পরিণত করে, তাদের ধাতুবিভক্তি বা ক্রিয়াবিভক্তি বলে। (জেনে রাখা ভালো, অসমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠনে বিভক্তি নয়, প্রত্যয় যোগ করা হয়)। ক্রিয়াবিভক্তির শ্রেণিবিভাগ করার আগে কয়েকটি ক্রিয়াপদকে ভেঙে বিভক্তিগুলি চিহ্নিত করে দেখাবো। এখানে আমরা ক্রিয়াপদের সাধু রূপ ব্যবহার করবো। (চলিত ভাষায় ক্রিয়াবিভক্তি চিহ্নিত করতে গেলে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হবে না, কারণ চলিতে অনেক সময় এদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়।)
নিচের উদাহরণগুলিতে ক্রিয়াবিভক্তিগুলি চিহ্নিত করে দেওয়া হল—
করিতেছিলাম = কর্+ইতে+আছ্+ইল্+আম
বলিয়াছিলাম = বল্+ইয়া+আছ্+ইল্+আম
বলিয়াছিলে = বল্+ইয়া+আছ্+ইল্+এ
দেখিতেছি = দেখ্+ইতে+আছ্+ই
দেখিতেছিস = দেখ্+ইতে+আছ্+ইস
করিতে থাকিব = কর্+ইতে+থাক্+ইব্+অ
দেখিতে থাকিবেন = দেখ্+ইতে+থাক্+ইব্+এন
উপরের উদাহরণগুলিতে চিহ্নিত অংশগুলি ক্রিয়াবিভক্তি। ইয়া/ইতে- প্রত্যয় এবং আছ্/থাক্ সহায়ক ধাতু।
ধাতুবিভক্তি বা ক্রিয়াবিভক্তির শ্রেণিবিভাগ
ক্রিয়াবিভক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়— কালবাচক ক্রিয়াবিভক্তি ও পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি। উপরে প্রদত্ত উদাহরণগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে ‘ইল্’ অতীত কাল নির্দেশ করছে ও ‘ইব্’ ভবিষ্যৎ কাল নির্দেশ করছে। তাই এরা কালবাচক ক্রিয়াবিভক্তি। অপরদিকে ‘আম’, ‘এ’ ‘ই’, ‘ইস’, ‘অ’, ‘এন’ এগুলি বিভিন্ন পুরুষ নির্দেশ করছে। যেমন: আম— উত্তম পুরুষ, ইস— তুচ্ছার্থে মধ্যম পুরুষ, এন— সম্মানার্থে মধ্যম/প্রথম পুরুষ। তাই এগুলি পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি। পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি সবসময় সমাপিকা ক্রিয়ার একেবারে শেষে থাকে। যেমন: করিতেছি = √কর্+ইতে+√আছ্+ই। এখানে ই হল বর্তমান কালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তি।
বাংলা পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তির তালিকা
বর্তমান কাল
উত্তম পুরুষ: ই— যেমন: আমি করি। আমি করিতেছি।
সম্মমানীয় মধ্যম পুরুষ: এন— আপনি করেন।
সাধারণ মধ্যম পুরুষ: অ/ও— তুমি কর/করো।
তুচ্ছ মধ্যম পুরুষ: ইস— তুই করিস।
সাধারণ প্রথম পুরুষ: এ— সে করে। রাম বলে।
সম্মানীয় প্রথম পুরুষ: এন— তিনি বলেন।
অতীত কাল
উত্তম পুরুষ: আম— যেমন: আমি করিলাম, করিয়াছিলাম।
সম্মানীয় মধ্যম পুরুষ: এন— আপনি গিয়াছিলেন।
তুচ্ছ মধ্যম পুরুষ: ই/ইস— তুই গিয়াছিলি/গিয়াছিলিস।
সাধারণ মধ্যম পুরুষ: এ— তুমি বলিয়াছিলে।
সাধারণ প্রথম পুরুষ: অ— সে বলিয়াছিল।
সম্মানীয় প্রথম পুরুষ: এন— তিনি বলিয়াছিলেন।
ভবিষ্যৎ কাল
উত্তম পুরুষ: অ— আমি বলিব।
সম্মানীয় মধ্যম পুরুষ: এন— আপনি বলিবেন।
তুচ্ছ মধ্যম পুরুষ: ই— তুই বলিবি।
সাধারণ মধ্যম পুরুষ: এ— তুমি বলিবে।
সাধারণ প্রথম পুরুষ: এ— রাম বলিবে।
সম্মানীয় প্রথম পুরুষ: এন— রামবাবু বলিবেন।
উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে: সম্মানীয় মধ্যম পুরুষ ও সম্মানীয় প্রথম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তি সব কালেই ‘এন’। এছাড়া ভবিষ্যৎ কালে সাধারণ মধ্যম ও সাধারণ প্রথম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তি আলাদা নয়।
বাংলা কালবাচক ক্রিয়াবিভক্তি দুটিই আছে। অতীতে ইল্ এবং ভবিষ্যতে ইব্। বর্তমানে কালবাচক ক্রিয়াবিভক্তি থাকে না বা শূন্য।


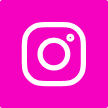





Leave a Reply