ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।
ব্যক্তিনিষ্ঠ বা আত্মগৌরবী প্রবন্ধ
বস্তুনিষ্ঠ তথা বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ যুক্তি-তর্ক, তত্ত্ব-তথ্য-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠককে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করতে প্রয়াসী। ব্যক্তিগত তথা আত্মগৌরবী প্রবন্ধে পাঠকের সঙ্গে প্রাবন্ধিকের গড়ে ওঠে এক নিকট বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তত্ত্ব, তথ্য, জ্ঞান ইত্যাদি এ-জাতীয় রচনায় লেখকের হৃদয়ানুভূতির রসে জারিত হয়ে পাঠকের আবেগ ও কল্পনাকে উদ্ৰিক্ত করে। যে-কোনো বিষয়-ই ব্যক্তিনিষ্ঠ বা মন্ময় প্রবন্ধের বিষয় হয়ে উঠতে পারে যদি প্রবন্ধকারের ব্যক্তিত্ব ও হৃদয়াবেগের সজীব স্পর্শ তাতে থাকে। কোনো মত বা বাণী প্রচারে সোচ্চার না হয়ে ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ পাঠককে কাছে টেনে নেয়।
ব্যক্তিনিষ্ঠ বা আত্মগৌরবী প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য
ভাবপ্রধান বা মন্ময় প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—
- যুক্তি ও মননশীলতার পরিবর্তে লেখকের হৃদয়াবেগেরই প্রাধান্য থাকবে;
- বিষয়বস্তু লেখকের কল্পনা তথা ভাবরসে জারিত হয়ে পাঠকহৃদয়কে স্পর্শ করবে;
- সরস, মর্মস্পর্শী, আত্মগত ভঙ্গিতে পাঠককে কাছে টেনে নেন প্রাবন্ধিক;
- বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধকারের মতো মন্ময় প্রাবন্ধিক সোচ্চার বা উদ্দেশ্যতাড়িত নন, বরং আত্মমগ্ন ও কিছুটা রহস্যময়।
- ভাবপ্রধান প্রবন্ধ মূলত ব্যক্তিগত, নৈর্ব্যক্তিক নয়;
- আবেগ ও কল্পনার প্রোজ্জ্বলতায় এ প্রবন্ধ লেখকের ব্যক্তিত্বের দর্পণ;
- ভাষার ব্যবহারে প্রবন্ধকার অনেক বেশি স্বাধীনতা পান এবং পাঠকের সঙ্গে আন্তরিক বিনিময় গড়ে তোলেন।
সমাজ, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের ভাণ্ডারটি বাংলায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ হলেও ব্যক্তিগত তথা মন্ময় প্রবন্ধ, যা মনের পরিধিকে প্রশস্ত করে ভাবকল্পনার মাধুর্যে তেমন রচনা বিশেষ সুলভ নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধে তাঁর কবিচেতনা, দার্শনিক উদারতা ও এক প্রসন্ন উজ্জ্বল পরিহাস লক্ষ করা যায় সন্দেহ নেই, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হৃদয়ের স্পর্শ অপেক্ষা বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ও ভাবসম্পদই সেখানে বড় হয় ওঠে যেন। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত ও বিচিত্র প্রবন্ধ ব্যক্তিগত প্রবন্ধের নিদর্শন রূপে গণ্য হয়ে থাকে। এক শীলিত ও কবিত্বমণ্ডিত সাধু গদ্যে জীবন সাহিত্য-প্রকৃতি-আত্মা-সৌন্দর্য বিষয়ক ভাবনা ডায়েরির শৈলিতে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের এক অনন্য চলনকে বৈশিষ্ট্যময় করে তুলেছিল ‘পঞ্চভূত’ গ্রন্থে। বক্তিগত প্রবন্ধের আত্মপ্রক্ষেপময় ভঙ্গি বিশেষ সার্থকতা লাভ করেছিল বিচিত্র প্রবন্ধ সংগ্রহে। তাঁর ‘জীবনস্মৃতি’ ও ‘ছিন্নপত্র’-ও এই মন্ময় ভাবকল্পনার দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল। অন্যান্যদের মধ্যে এই শ্রেণির প্রবন্ধকার হিসেবে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করা যায়। নাম করা যেতে পারে ব্যক্তিগত প্রবন্ধধর্মী রচনায় অনবদ্য পরিহাস ও রম্যতার স্বাক্ষর রেখে যাওয়া লেখক সৈয়দ মুজতবা আলি এবং ‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’ ও ‘উত্তর তিরিশ’-এর মতো ব্যক্তিগত রচনার সংকলনের জন্য স্মরণীয় প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর নাম।
একটি সার্থক ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ
বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ একটি সার্থক আত্মগৌরবী প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত। সংবেদনশীল ব্যঙ্গ-পরিহাসের কৌতুকোজ্জ্বল আবরণে রূপাকাশ্রয়ী উপাখ্যানের আদলে লেখক গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলিতে সমকালীন রাজনীতি-সমাজনীতি-ধর্মনীতি ও সাহিত্যের পর্যালোচনা করেছেন। নসীরামবাবুর আশ্রিত, অহিফেনাসক্ত কমলাকান্ত এক নিষ্কর্মা অধোর্ন্মাদ ব্রাহ্মণ, যার ব্যক্তিমানসের আত্মকথনমূলক লঘু পরিহাসের প্রীতিরসে জারিত রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
বঙ্কিমচন্দ্র আত্মজীবনী লেখেননি কিন্তু কমলাকান্তের জবানীতে লেখা এই রচনাগুলি আত্মজৈবনিক লক্ষণাক্রান্ত, বঙ্কিমের জীবনদর্শনের আধারস্বরূপ। প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ আর নসীরামবাবুর আফিম ছাড়া কমলাকান্তের আর কোনো বন্ধন নেই। অনন্য বিদ্যা-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও কমলাকান্ত যেন তার পারিপার্শ্বিকের সমস্ত কিছু থেকে নির্লিপ্ত এক আশ্চর্য মানুষ যে নিজেকে নিয়ে এবং সাধারণ জগৎ ও জীবনকে নিয়ে এক কৌতুককর দার্শনিক মানস-ক্রীড়ায় নিরত। এই কমলাকান্ত ব্যক্তি বঙ্কিমেরই প্রতিচ্ছবি, যার চিন্তা-ভাবনা ও বিবিধ বিক্ষিপ্ত মন্তব্যে বঙ্কিমেরই জীবনদর্শন প্রতিফলিত। অনেকে কমলাকান্তের এই আত্মকথনধর্মী প্রবন্ধগুলিকে উনিশ শতকের ইংরেজ প্রাবন্ধিক টমাস ডি কুয়েন্সির Confessions of an English Opium Eater-এর অনুসরণে রচিত বলে মনে করেন, যদিও ডি কুয়েন্সির বৃহদায়তন আত্মকথন কমলাকান্তের কথকতার মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সাহিত্যরস সমন্বিত নয়। সংবেদনশীল কবিমনের যে সরস জীবনদৃষ্টি কমলাকান্তের রচনাগুলিকে বিচিত্র ভাবের সমাহারে এক সর্বকালিক উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ করেছে, ডি কুয়েন্সির লেখায় তা পাওয়া যায় না। বঙ্কিমের ব্যক্তিগত জীবনবোধ, সমাজ জীবনের নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সমস্যা বিষয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ কমলাকান্তের চরিত্রে এক অনবদ্য স্বাতন্ত্র্য আরোপ করেছে। এদিক থেকে দেখলে ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আশাভঙ্গ ও জীবনসঙ্কটের দর্পণ।
আফিম সেবন করে কমলাকান্ত লাভ করে দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যকর্ণ এবং তখন বঙ্কিম তাকে অবলম্বন করে সমাজ, জীবন ও ব্যক্তি মানুষ সম্পর্কে এমন সব প্রশ্ন তোলেন যা সর্বকালের ন্যায়-নীতি-মানবাত্মার প্রশ্ন। আত্মগৌরবী, ভাবনিষ্ঠ প্রবন্ধের সীমানা তখন ব্যক্তিনিষ্ঠতার চৌহদ্দি পেরিয়ে সর্বকালিক হয়ে ওঠে।
গ্রন্থভুক্ত ‘বিড়াল’ শীর্ষক প্রবন্ধে কমলাকান্ত উচ্চ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, আর চতুষ্পদ, ক্ষুধার্ত ‘আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত’ মার্জারটি যেন সারা পৃথিবীর দরিদ্র ও ক্ষুৎপীড়িত মানবসম্প্রদায়ের মুখপাত্র। দিব্যনেত্র উন্মোচিত হলে কমলাকান্ত অনুভব করে যে সংসার যেন এক পেঁকিশাল, যেখানে জমিদার, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, বিচারক, বাবু, লেখক সকলেই পিষ্ট হচ্ছে। দিব্যকর্ণপ্রাপ্ত কমলাকান্তের আর এক স্মরণীয় উপলব্ধি এই যে, মানুষ মাত্রেই পতঙ্গবিশেষ, কোনো-না-কোনো বাসনাবহ্নিতে দগ্ধ হবার জন্যে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত। ‘বসন্তের কোকিল’ নামের রচনাটিতে কমলাকান্তের নেশাগ্রস্ত দৃষ্টির সামনে দেখা দেয় যে কোকিলটি সে শুধুই স্বার্থপর, নসীরামের জীবনে বর্ষাবিধুর দিনগুলিতে তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। ব্যঙ্গ-পরিহাসে সমুজ্জ্বল রূপকের আঙ্গিকে কমলাকান্তের দৃষ্টিতে মানুষ ও তার জীবনকে দেখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। ‘মনুষ্যফল’ প্রবন্ধে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে কমলাকান্তের মনে হয়েছে বিভিন্ন ফলবিশেষ। দেশহিতৈষী তার চোখে শিমুল আর ব্রাহ্মণ ধুতুরা ফলস্বরূপ। ‘মনুষ্য সকল ফল বিশেষ, মায়া বৃন্তে, সংসার বৃক্ষে ঝুলিতেছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে’—এই হল কমলাকান্ত তথা বঙ্কিমের জীবন দর্শনের দৃষ্টান্ত। ‘বড়বাজার’ শিরোনামের ব্যঙ্গাত্মক রচনায় বঙ্কিম চতুপার্শ্বে দেখেছেন সওদাগরি সমাজ ও সভ্যতার নীতিহীন লাভ-লোকসানের চিত্র। নারীর রূপসজ্জা, পণ্ডিতের বিদ্যাচর্চা, ইংরেজের রাজ্যশাসন, সাহিত্যিকের সাহিত্যানুশীলন ইত্যাদি সবকিছুতেই ক্রয়-বিক্রয়ের এক মনোহারী আবহাওয়া।
‘আমার মন’, ‘একা’, ‘আমার দুর্গোৎসব’ ও ‘একটি গীত’—কমলাকান্তের এই রচনাগুলি সবই শুদ্ধ আত্মসমীক্ষা। ব্যক্তিগত অনুভূতিমূলক ‘একা’-য় কমলাকান্তের দিব্যকর্ণে সমগ্র মানবজাতির প্রতি পরম প্রীতির সুরটিই বাজে—“প্রীতি সংসারে সৰ্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি’’। স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে মনুষ্যপ্রীতিই যথার্থ ধর্ম। ‘আমার মন’ শীর্ষক প্রবন্ধটিতেও কমলাকান্ত অনুরূপ মানবপ্রেমের বাণী উচ্চারণ করে—‘‘আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল্য নাই।’’ এই মানব-প্রীতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ স্বদেশপ্রীতি আর সে কারণে ‘আমার দুর্গোৎসব’-এ কমলাকান্তের দৃষ্টিতে মূর্ত হয়ে ওঠে দেশজননীর ‘মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্ত রত্নভূষিতা’ রূপটি। ‘কমলাকান্তের জোবানবন্দী’ শিরোনামের বহুপঠিত রচনাটিতে প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরু চুরি-বিষয়ক সওয়াল-জবাবের রঙ্গ-ব্যঙ্গের আড়ালে সামাজিক ন্যায়বিচার ও আইনপদ্ধতির যে তীব্র সমালোচনা বঙ্কিম আমাদের সামনে পেশ করেন তা এককথায় তুলনারহিত—“গরু আমার নয় ত কার! আমি ওর দুধ খেয়েছি, দই খেয়েছি, ছানা খেয়েছি, মাখন খেয়েছি, ননী খেয়েছি ও গরু আমার হল না, আর তুই বেটী পালিস্ বলে কি তোর বাবার গরু হলো!”
‘কমলাকান্তের দপ্তর’-এর রচনাগুলি ব্যক্তিগত ও ভাবপ্রধান প্রবন্ধের চমৎকার নিদর্শন। বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিসর্বস্ব বিশ্লেষণ অপেক্ষা লেখকের ব্যক্তিত্বের মাধুর্য, দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্বতা ও অভিনবত্বই এইসব রচনায় বড়ো হয়ে উঠেছে। ইংরেজ প্রাবন্ধিক চার্লস ল্যাম্বের মতোই বঙ্কিম ‘কমলাকান্ত’ (ল্যাম্বের Eila) নামক চরিত্রের আড়ালে থেকে দেশ, কাল, সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনা ও উপলব্ধিসমূহকে এক অসামান্য রসসিক্ত গদ্যে প্রকাশ করেছেন এইসব প্রবন্ধে।
তথ্যসূত্র:
| কাব্যজিজ্ঞাসা – অতুলচন্দ্র গুপ্ত | Download |
| কাব্যতত্ত্ব: আরিস্টটল – শিশিরকুমার দাস | Download |
| কাব্যমীমাংসা – প্রবাসজীবন চৌধুরী | Download |
| ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব – নরেন বিশ্বাস | Download |
| ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব – অবন্তীকুমার সান্যাল | Download |
| কাব্যজিজ্ঞাসার রূপরেখা – করুণাসিন্ধু দাস | Download |
| কাব্য-শ্রী – সুধীরকুমার দাশগুপ্ত | Download |
| সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য – কুন্তল চট্টোপাধ্যায় | Download |
| সাহিত্য ও সমালোচনার রূপরীতি – উজ্জ্বলকুমার মজুমদার | Download |
| কাব্যালোক – সুধীরকুমার দাশগুপ্ত | Download |
| কাব্যপ্রকাশ – সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত | Download |
| নন্দনতত্ত্ব – সুধীর কুমার নন্দী | Download |
| প্রাচীন নাট্যপ্রসঙ্গ – অবন্তীকুমা সান্যাল | Download |
| পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা – নবেন্দু সেন | Download |
| সাহিত্য প্রকরণ – হীরেণ চট্টোপাধ্যায় | Download |
| সাহিত্য জিজ্ঞাসা: বস্তুবাদী বিচার – অজয়কুমার ঘোষ | Download |


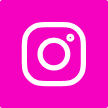


Leave a Reply