ভ্রমণ-সাহিত্য কাকে বলে? একটি সার্থক ভ্রমণ-সাহিত্য আলোচনা কর।
ভ্রমণ-সাহিত্য
অচেনাকে জানবার আগ্রহ মানুষের চিরদিনের। নিজে যেটুকু অঞ্চলকে প্রয়োজনের তাগিদে চিনি, তার বাইরে জনপদগুলির চেহারা কেমন, সেখানকার মানুষের জীবন-যাত্ৰা কীরকম, সেই দেশগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কিছু আছে কিনা— এসব মানুষ দীর্ঘকাল থেকে জানতে চেয়েছে এবং আজও চায়। এই কারণেই মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েনের মতো পরিব্রাজক পুরাকালে ভ্রমণের নেশায় পৃথিবী-পরিভ্রমণ করেছিলেন, এ যুগের রামনাথ বিশ্বাসের মতো মানুষও বিশ্বপর্যটনে বার হয়েছিলেন। মানুষের মনে এই নেশা আছে বলেই আজো স্বল্প বা দীর্ঘ ছুটিতে মানুষ বেরিয়ে পড়ে অচেনা অথবা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসমৃদ্ধ জায়গায় বেড়াবার জন্য। মানুষের মনের এই চিরন্তন পিপাসাই ব্যক্ত হয়েছে কবিগুরুর কণ্ঠে—
বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব কতনা অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।
ভ্রমণের নেশা মানুষের আছে বলেই অজানার সঙ্গে তার পরিচয় লিপিবদ্ধ করে রাখবার প্রচেষ্টাও মানুষ অনেক দিন থেকেই করে আসছে। অবশ্য বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক বিবরণ, বিভিন্ন মানুষের জীবনযাত্রার তথ্যসমৃদ্ধ পরিচিতিই যদি এইসব রচনার একমাত্র উপকরণ হতো। তাহলে ভূগোল এবং সমাজবিজ্ঞানের গ্রন্থের মতোই তাদের আকর্ষণ হতে কেবল তথ্যের কারণেই। কিন্তু এইসব ভ্রমণকাহিনী যে সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠেছে তার কারণ সেখানে কেবল অজানা তথ্যই নেই, আছে মানুষের ভালো-লাগা মন্দ লাগার অনুভূতি। সেই কারণেই বস্তুগত বিবরণকে অতিক্রম করে মানুষের অনুভূতির রঞ্জক তাদের বিচিত্রভাবে উপভোগ্য করে তুলেছে।
এই প্রসঙ্গে ভ্রমণবৃত্তান্ত কেমন করে সাহিত্য হয়ে ওঠে, শুধু অভিজ্ঞতা থাকলেই যে হয়, এ বিষয়ে দু-একজন সাহিত্যিকের অভিমত স্মরণ করতে পারি। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, ঘটনার নামই অভিজ্ঞতা নয়, ঘটনা হচ্ছে কাঁচা মাল যা থেকে অভিজ্ঞতার সৃষ্টি। এবং সেই সৃষ্টি মনের বিশেষ এক রকম রসায়ন-ক্রিয়া বিশেষ একটি ক্ষমতাসাপেক্ষ। অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, ‘বেরোবার আগে আমি বিস্তর পড়াশোনা করি, ফিরে আসার পরেও আরো পড়ি। তারপর লিখতে বসি ভ্রমণকাহিনী।
অবশ্য এইসঙ্গে যদি ভাষার ঐশ্বর্য যুক্ত হয় তবে ভ্রমণকাহিনী আরো আস্বাদ্য এবং রমণীয় হয়ে ওঠে। সেইজন্য বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের হাতে ভ্রমণকাহিনী প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যে পরিণত হয়। যেমন এ কালের বিশিষ্ট ভ্রমণসাহিত্য রচয়িতা যাযাবর যে দুটি ভ্রমণ কাহিনী লিখেছিলেন—‘দৃষ্টিপাত’ এবং ‘ঝিলম নদীর তীরে’, কেবল অনবদ্য ভাষার কারণেই সেগুলি বার বার পড়া যায়। এর একটু উদাহরণ— ‘‘বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ; তাতে আছে গতির আবেশ, নেই যতির আয়েস।’’
ভ্রমণকাহিনীর সূত্রপাত কবে থেকে, বলা খুবই শক্ত, তবে স্থানের বর্ণনা বা যাত্রাপথের বর্ণনা বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগেই পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতমূলক কাব্যে গৌরাঙ্গদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কথা আছে। গোবিন্দদাসের কড়চায় লেখা হয়েছে—
তারপরে দ্বার হইতে হইয়া বাহির।
গঙ্গা পার হয়ে তবে চলে ধর্মবীর।
পার হৈয়া প্রভু চলে কণ্টক নগরে।
পেছনে পেছনে যাই” সেবা করিবারে।
পদাবলীর বিখ্যাত কবি নরহরি চক্রবর্তী রচনা করেছিলেন ‘নবদ্বীপ পরিক্রমা’ ও ‘ব্রজ পরিক্রমা’। ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের তৃতীয় অংশের বর্ণনীয় বিষয় ছিল প্রতাপাদিত্যকে দমনের জন্য মানসিংহের যশোহর আগমন ও বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করে ভবানন্দসহ দিল্লীযাত্রা। এখানেও ভ্রমণ পথের কিছু বর্ণনা আমরা পাই।
তবে এগুলিকে আমরা ভ্রমণকাহিনীর পূর্বাভাসই বলবো ভ্রমণকাহিনী নয়। কারণ ভৌগোলিক জ্ঞান যে মধ্যযুগীয় কবিদের খুব ভালো ছিল না, থাকাটা প্রত্যাশিত নয়, তার প্রমাণ কবি মুকুন্দর ‘গুজরাট নগরপত্তন’। এই গুজরাট নগরের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসকে কেউ যদি ভৌগোলিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেন, তিনি যে কিছুটা আশাহত হবেন, নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভ্রমণকাহিনীর সূচনা আমরা ধরতে পারি জয়নারায়ণ ঘোষালের ‘কাশী-পরিক্রমা’ গ্রন্থটিকে। অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষ দিকে রচিত। কাশীর মন্দির, তৎকালীন জীবনযাত্রা, ব্যবসায়বাণিজ্য ইত্যাদি অনেক কিছুই সেখানে ভ্রমণ করতে গিয়ে জয়নারায়ণ ঘোষাল লক্ষ করেছিলেন এবং গ্রন্থে তার নিপুণ পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য এরকম— ‘‘তাৎকালিক কাশীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহা একশত বৎসরের যবনিকা তুলিয়া অবিকল কাশীর মূর্তিটি আমাদের কক্ষে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে।’’
একেবারে প্রথমদিকে রচিত তিনটি ভ্রমণকাহিনীর কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। এগুলি হল যদুনাথ সর্বাধিকারীর ‘তীর্থ-ভ্রমণ’, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ব্যক্তিক স্পর্শযুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং রমেশচন্দ্র দত্তের ইওরোপ ভ্রমণসংক্রান্ত ডায়েরির অনুবাদ। যদুনাথ সর্বাধিকারীর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে, কিন্তু এটি রচিত আরো প্রায় চল্লিশ বছর আগে। মাত্র চল্লিশ টাকা সম্বল করে কীভাবে তিনি তীর্থযাত্রা করেছিলেন চার বছর ধরে কোথায় কোথায় ভ্রমণ করেছেন, তার বিবরণ দিয়েছেন তার রোজনামচায়। গ্রন্থটিতে শুধু যে বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা আছে তাই নয়, সেখানকার মানুষ ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কীর্তিরও পরিচয় আছে। যেমন গয়ার ভিক্ষুকদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, ভিক্ষুক সকলেই। যাহার দশ হাজার টাকার অঙ্গভূষণ আছে, এক কড়া কড়ির জন্য সেও লালায়িত। তাহাদিগকে যদি কেহ কহে, তোমরা এমত ভিক্ষা জন্য কি জন্য ক্লেশ কর। তাহারা উত্তর করে যে, আমাদের যাহা ধনসম্পত্তি, এই মত ভিক্ষাভিন্ন অন্য উপায়ে তাহা হয় নাই।
ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে কিছুটা গল্প-কাহিনী সংযোগ করলে তা আরো উপভোগ্য হয়ে ওঠে বলে আধুনিক কালের ভ্রমণসাহিত্যে এই প্রবণতা খুব বেশি দেখা যায়। প্রবোধকুমার সান্যাল দুটি অসাধারণ ভ্রমণকাহিনী রচনা করেছেন— ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ এবং ‘দেবতাত্মা হিমালয়’। এর মধ্যে প্রথম গ্রন্থটিতে একটি উপভোগ্য কাহিনি আমরা লাভ করি।
ভ্রমণ-সাহিত্যে বাংলা ভাষা রীতিমত সমৃদ্ধ বলা চলে। কাহিনী প্রায় বর্জন করে রমণীয় ভাষায় ভ্রমণ বৃত্তান্ত ফুটিয়ে তুলেছেন অনেকে। উল্লেখ করা যায় জলধর সেনের ‘হিমালয়, অন্নদাশঙ্কর রায়ের ‘পথে-প্রবাসে’, দেবেশ দাসের ‘ইয়োরোপা’, রামনাথ বিশ্বাসের ‘লালচীন’, মনোজ বসুর ‘চীন দেখে এলাম’ প্রভৃতি গ্রন্থের। কেবল দর্শনীয় স্থান পরিভ্রমণ করেছেন এবং আন্তরিক ভাবে তা একের পর এক গ্রন্থে বর্ণনা করে গিয়েছেন এমন লেখকও আছেন, যেমন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আবার ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে গল্পের ভাগ একটু বেশি যোগ করেছেন এমন লেখকও আছেন, যেমন শঙ্কু মহারাজের বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা গ্রন্থটি পাঠ করে গল্পের স্বাদও কিছু পাওয়া যাবে। অবধূতের লেখা ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ গ্রন্থে অবশ্য ঘটনার নাটকীয়ত্ব অনেক বেশি। পর্বত-অভিযান নিয়ে যেসব গ্রন্থ বংলায় লেখা হয়েছে, উত্তেজনার খোরাক সেখানেও আমরা অনেক পাই, যথা গৌরকিশোর ঘোষের ‘নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি’ বা বীরেন্দ্রনাথ সরকারের রহস্যময় রূপকুণ্ড। ভ্রমণকাহিনী ঐতিহাসিক গবেষণার আরক-গ্রন্থ হয়ে রয়েছে, এমন উদাহরণও আছে, যেমন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ।
একটি ভ্রমণ-কাহিনীর পরিচয়
গল্প-উপন্যাস নয়, একটি ভ্রমণ-কাহিনী রচনা করেই পাঠকদের হৃদয় জয় করেছেন, এমন কয়েকটি গ্রন্থের নাম যদি করতে হয়, সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘দেশে-বিদেশে’ যে তাদের অন্যতম হবেই, নিঃসন্দেহে সে কথা বলা যায়। বিশ্বভারতী গ্রন্থটির সমালোচনা করতে গিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এই একই কথা বলেছিলেন— ‘‘বাঙলা ভাষায় দেশভ্রমণকে অবলম্বন করে … অন্যতম রসসৃষ্টি।’’
সাধারণভাবে দেখতে গেলে এটি লেখকের কাবুল যাত্রা ও অল্প দিন সেখানে বসবাসেরই স্মৃতি-রোমন্থন। কাবুল তো বিদেশ, সুতরাং গ্রন্থের নাম ‘দেশে-বিদেশে’ কেন, এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এ বিষয়ে লেখকের উত্তর, “দেশে বিদেশে” শব্দার্থে লিখেছি অর্থাৎ বইয়েতে কিছুটা ‘দেশের বর্ণনা পাবে যথা পেশাওয়ার ইত্যাদি, আর বাকিটা ‘বিদেশের অর্থাৎ এ স্থলে কাবুলের। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এ গ্রন্থ রচিত, কাজেই পেশওয়ার তখন অবিভক্ত ভারতবর্ষেরই অন্যতম অঙ্গ ছিল।
মূলত তিনটি পর্যায় আছে এই যাত্রার। সূচনায় দেখি, হাওড়া স্টেশন থেকে কাবুলের উদ্দেশে যাত্রা ও শেষ পর্যন্ত কাবুলে পৌঁছানো; দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখকের কাবুলের প্রবাসজীবনের বর্ণনা এবং তৃতীয় পর্বে আমীর আমানুল্লার সংস্কার-প্রচেষ্টার হাস্যকর বাড়াবাড়িতে কাবুলে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি এবং তারই ফলস্বরূপ লেখকের কাবুল ত্যাগ। কাবুলের রাজনৈতিক অবস্থা, ক্ষমতা হস্তান্তরের বিশদ বর্ণনা বা ব্রিটিশ আধিপত্য কায়েমের ইতিহাস বা একটি পুতুল শাসক বসিয়ে রুশ আগ্রাসন ঠেকিয়ে রাখবার প্রচেষ্টার বিবরণ এখানে নেইরাজনৈতিক অবস্থার কথা যেটুকু এসেছে তা শেষ পর্বে আমানুল্লার সংস্কার-প্রয়াস প্রসঙ্গেই। কিন্তু সম্ভবত সেই জন্যই গ্রন্থটি কাবুলের ক্ষমতা-উত্থানপতনের দলিল না হয়ে একটি অসাধারণ ভ্রমণ-আলেখ্য হয়ে উঠতে পেরেছে।
গ্রন্থের আরম্ভটিই অসাধারণ। কাবুল আমাদের অপরিচিত দেশ, সেখানকার রীতিনীতি, আদব কায়দাও আমরা কিছু জানি না বললেই হয়। অন্য দিকে এর লেখক শান্তিনিকেতনের ছাত্র, বহুভাষাবিদ এক পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতিমান। কাজেই একটি গুরুগম্ভীর ভূমিকা দিয়ে গ্রন্থ শুরু হবে, এটাই ছিল প্রত্যাশিত। অথচ শুরুটা হয়েছে এইভাবে—‘‘চাদনি থেকে ন-সিকে দিয়ে একটা শর্ট কিনে নিয়েছিলুম।’’ অতঃপর ট্রেনে সহযাত্রী এক ফিরিঙ্গি তার ফিয়াসে-প্রদত্ত নিজহাতে প্রস্তুত ডিনার যখন বার করে তখন দেখা যায় লেখকের জ্যাকেরিয়া স্ট্রিট থেকে কেনা ডিনার-প্যাকের সঙ্গে তার এতটুকু তফাত নেই।
এইরকম হালকা চালেই এগিয়েছে ভ্রমণকাহিনী। পেশোয়ার যাওয়ার পথে শিখ এবং পাঠানের বিলক্ষণ আধিক্য দেখে লেখকের মনে বিবিধ চিন্তা জাগে, এগুলিকে আর যাই বলা যাক, গুরুতর গবেষণার বিষয় বলা যাবে না, কারণ এর মধ্যে একটি ছিল ‘তুলনামূলক দাড়িতত্ত্ব’। পাঠানদের আড্ডা এবং মজলিসের যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তাতে এদের সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়ে যায়, ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক পরিচয়ের যাবতীয় তথ্য দিতে বসলেও বোধহয় এদের এত ভালো পরিচয় আমরা লাভ করতাম না। বাঙালিদের সঙ্গে গল্পবাজ পাঠানদের যে এত মিল, সেটা জানতে পেরে আমরা কৌতুক বোধ করি। পেশোয়ারে গিয়ে পাঠানদের দিলদরাজ আতিথ্যের যে পরিচয় পেয়েছেন সেটাও উল্লেখ করবার মত। এমনিতে অত্যন্ত শান্ত এবং সজ্জন। কিন্তু ‘‘বেইমান বললে পাঠানের রক্ত খাইবার পাসের টেম্পারেচার ছাড়িয়ে যায়, আর ভাইকে বাঁচাবার জন্য সে অত্যন্ত শান্তমনে যোগাসনে বসে আঙুল গোণে, নিদেনপক্ষে তাকে কটা খুন করতে হবে।’’
বাজার, সরাইখানা আর আড্ডা হচ্ছে কাবুলের সবচেয়ে দর্শনীয় বস্তু। কাবুলের সামাজিক জীবন মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(ক) খাস কাবুলী, (খ) ভারতীয় অর্থাৎ পঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান ও খেলাফৎ সমর্থক ভারতত্যাগী-মুজাহির এবং (গ) বিভিন্ন রাজদূতাবাসের কর্মচারী।
কাবুল প্রবাসের বহু চিত্তাকর্ষক ঘটনা গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ আছে, অনেক টুকরো শায়েরি এবং কবিতার প্রয়োগে কাহিনী সমৃদ্ধ হয়েছে, বহু বিচিত্র চরিত্র সেখানে স্থান পেয়েছে, কিন্তু কাবুলে লেখকের একনিষ্ঠ সেবক আবদুর রহমানের চরিত্র পাঠকদের মনে যে গভীর রেখায় দাগ কেটে যায় তা গ্রন্থপাঠের দীর্ঘদিন পরেও মুছে ফেলা যায় না। অথচ তার চেহারার বর্ণনা শুনলে তাকে ভয়ংকরই মনে হতে পারে—‘ছ ফুট চার ইঞ্চি।… লম্বাই মিলিয়ে চওড়াই। দুখানা হাত হাঁটু পর্যন্ত নেবে এসে আঙুলগুলো দু কাঁদি মর্তমান কলা হয়ে ঝুলছে। পা দুখানা ডিঙি নৌকার সাইজ। … এ কান ওকান জোড়া মুখ হাঁ করলে চওড়া-চওড়ি কলা গিলতে পারে। এবড়ো খেবড়ো নাক, কপাল নেই।”
তার আপ্যায়নের ঘটাও একটু শোনানো দরকার, ‘‘ছোটখাটো একটা গামলা ভর্তি মাংসের কোরমা বা পেঁয়াজ-ঘিয়ের ঘন কাথে সেরখানেক দুম্বার মাংস—তার মাঝে মাঝে কিছু কিছু বাদাম কিসমিস লুকোচুরি খেলছে, এক কোণে একটি আলু অপাংক্তেয় হওয়ার দুঃখে ডুবে মরার চেষ্টা করছে। আরেক প্লেটে গোটা আষ্টেক ফুল বোম্বাই সাইজের শামী কাবাব। বারকোশ পরিমাণ মাত্রায় এক ঝুড়ি কোফতা-পোলাও আর তার ওপর বসে আছে একটি আস্ত মুর্গী-রোস্ট।
শেষ বর্ণনাটি এইরকম—‘‘বহুদিন ধরে সাবান ছিল না বলে আবদুর রহমানের পাগড়ি ময়লা। কিন্তু আমার মনে হল চতুর্দিকের বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর রহমানের পাগড়ি আর শুভ্রতম আবদুর রহমানের হৃদয়।’’
চরিত্রটি কীরকম প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এবং শেষ বিদায় কতটা মর্মস্পর্শী হয়েছে তা খানিকটা বোঝা যাবে ১৯৪৯ সালের ২৬ জুন তারিখে রবিবারের হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড পত্রিকায় ‘দেশে বিদেশে’র সমালোচনা প্রসঙ্গে করা এই মন্তব্য থেকে— “Even if the rest of the book faded out of memory, the figure of Abdur Rahaman with his broad chest and even broader heart, his soiled turban and tearful eyes giving a send-off to his master would haunt the memory for ever.”
কোনো সন্দেহ নেই, ‘দেশে বিদেশে’ একটি স্মরণীয় ভ্রমণকাহিনী এবং বাংলা সাহিত্যের সম্পদবিশেষ।
তথ্যসূত্র:
| কাব্যজিজ্ঞাসা – অতুলচন্দ্র গুপ্ত | Download |
| কাব্যতত্ত্ব: আরিস্টটল – শিশিরকুমার দাস | Download |
| কাব্যমীমাংসা – প্রবাসজীবন চৌধুরী | Download |
| ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব – নরেন বিশ্বাস | Download |
| ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব – অবন্তীকুমার সান্যাল | Download |
| কাব্যজিজ্ঞাসার রূপরেখা – করুণাসিন্ধু দাস | Download |
| কাব্য-শ্রী – সুধীরকুমার দাশগুপ্ত | Download |
| সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য – কুন্তল চট্টোপাধ্যায় | Download |
| সাহিত্য ও সমালোচনার রূপরীতি – উজ্জ্বলকুমার মজুমদার | Download |
| কাব্যালোক – সুধীরকুমার দাশগুপ্ত | Download |
| কাব্যপ্রকাশ – সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত | Download |
| নন্দনতত্ত্ব – সুধীর কুমার নন্দী | Download |
| প্রাচীন নাট্যপ্রসঙ্গ – অবন্তীকুমা সান্যাল | Download |
| পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা – নবেন্দু সেন | Download |
| সাহিত্য প্রকরণ – হীরেণ চট্টোপাধ্যায় | Download |
| সাহিত্য জিজ্ঞাসা: বস্তুবাদী বিচার – অজয়কুমার ঘোষ | Download |


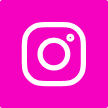


Great post. https://Bandur-Art.Blogspot.com/2024/08/the-ultimate-guide-to-no-mans-sky-mods.html