রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সংস্কৃত নাটকের অবদান আলোচনা কর।
রঙ্গমঞ্চ ও সংস্কৃত নাটক
আমাদের ভারতীয় নাটকের প্রাচীন ঐতিহ্য সংস্কৃত নাটক। প্রথম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তার বিস্তারের কাল। পণ্ডিতদের মতে ঋকবেদেই নাটকের মৌলিক উপাদান পাওয়া যায়। ‘সরমা ও পণি’, ‘যম ও যমী’, ‘পুরূরবা ও ঊর্বশী’ প্রভৃতি সংবাদ-সূক্ত বা গাঁথা পরবর্তীকালে নাট্যরচনাকে প্রভাবিত করেছিল। যজ্ঞের অনুষ্ঠানে উদাত্ত-অনুদাত্ত স্বরে বেদমন্ত্রের উচ্চারণ ও গীতনাট্যাভিনয়ের প্রাক্-প্রস্তুতি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।
সংস্কৃত নাটক ও নাট্যাভিনয় নিয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মতামত রয়েছে। Sylvan Levy বা Hartel উপরোক্ত মত মেনেছেন। আবার Sten Konow মৌলিক আনন্দানুষ্ঠানের পরিবর্তিত রূপকেই নাটক বলে ধরে নিয়েছেন। Pischel তো পুতুলনাচকেই নাটকের পূর্বসূরি মনে করেছেন। শ্যাডো-প্লে বা ছায়ানাট্য থেকে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব, মনে করেছেন অধ্যাপক ডাস। এদিকে অধ্যাপক কীথ (Keith) অনুমান করেছেন রামায়ণ-মহাভারত বীণা সহযোগে বিভিন্ন জনপদে ও রাজসভায় আবৃত্তি ও গান করার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় নাটকের সৃষ্টি হয়েছে। এইসব পরস্পরবিরোধী মত থেকে কোনো সিদ্ধান্তে আসা মুশকিল।
ভরতমুনি তাঁর ‘নাট্যশাস্ত্রে’ সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তির একটি উপাখ্যান বলেছেন। রূপকের আড়ালে এখানে নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটুকু বোঝা যায়। চতুর্বেদে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ছাড়া কারো অধিকার ছিল না বলে গরিষ্ঠ জনতার দাবীতে ব্রহ্মা ‘পঞ্চমবেদ’ সৃষ্টি করতে বলেন। ঋকবেদ থেকে পাঠ্য, যজুর্বেদ থেকে অভিনয়, সামবেদ থেকে সঙ্গীত এবং অথর্ববেদ থেকে রস আহরণ করেই পঞ্চবেদ সৃষ্টি হবে, যা কিনা নাট্যবেদ হিসেবেই পরিচিত হবে। এই ‘নাট্যবেদ’ প্রয়োগে বা অভিনয়ে দেবতারা ‘অশক্ত’ বলে ইন্দ্র জানালে ব্রহ্ম ভরতমুনির ওপরেই দায়িত্ব দেন। তিনি একশত শিষ্যের সাহায্যে ‘ইন্দ্ৰধ্বজ’ উৎসব উপলক্ষে দেব ও অসুরের কাহিনী নিয়ে নাট্যরচনা করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। মহাদেবের পরামর্শে এতে ‘কৈশিকী বৃত্তি’ অর্থাৎ সুকুমার বৃত্তি, মানে নাচ গান যুক্ত করা হয়। এবং এরই প্রয়োজনে চব্বিশজন অপ্সরা রমণীর সৃষ্টি করেন। নৃত্যগীতে পারদর্শিনী এদের সহযোগে ‘দেবাসুর যুদ্ধ’ বা ‘অসুর বিজয়’ নাটকের অভিনয় করা হয়। কিন্তু অভিনয়ের সময়ে অসুরবৃন্দ তাদের পরাজয়ের দৃশ্য দেখে হাঙ্গামা বাধালে ইন্দ্ৰ ধ্বজদণ্ড প্রহারে তাদের জর্জরিত করেন। তারপর থেকে ইন্দ্ৰধ্বজ সবসময়ে রঙ্গালয়ের মঙ্গল চিহ্ন রূপে ব্যবহৃত হয়। এবং তখন থেকেই ভাবনা চিন্তা শুরু হয়, এই ধরনের খোলা জায়গায় অভিনয় করা নিরাপদ কিনা! তাই থেকেই বোধ করি রঙ্গস্থলকে চারিদিকে ঘিরে রঙ্গালয় তৈরি করে আপাত নিরাপত্তায় অভিনয় করার ব্যবস্থা হতে থাকে। এরপরে ব্রহ্ম তাঁর দলবল নিয়ে হিমালয়ে ‘ত্রিপুরদাহ’ নাটকের অভিনয় করেন। মনে হয়, এসবই মুক্তমঞ্চেই অভিনীত হয়েছিল। কেননা, অসুরদের হাঙ্গামা থেকে রক্ষার জন্য ব্রহ্ম এরপরেই বিশ্বকর্মাকে ‘নাট্যগৃহ’ বা ‘নাট্যবেশ্ম’ তৈরি করতে বলেন। তারপর থেকেই সংস্কৃত নাটক রঙ্গালয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। সেই অনুযায়ী নাট্যরচনাও শুরু হয়।
ভরতের নাট্যশাস্ত্র রচনার সময় পর্যন্ত (দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক) তিনি নাট্যরচনার যে পরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায়, নাটক বা রূপক বা দৃশ্যকাব্য দশপ্রকার ছিল। নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্গ, বীথী ও প্রহসন। এর সবগুলিই নাটক, তবে গঠন ও রসগত কিছু ব্যতিক্রমের কারণে বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। এগুলির আবার আঠারো রকমের উপরূপকেও উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, নাটিকা, ত্রোটকম, গোষ্ঠি, নিউকম ইত্যাদি।
ব্রহ্মার ভাষণে সংস্কৃত নাটকের রচনা ও অভিনয়ের মূল সুর ও উদ্দেশ্য বুঝে নেওয়া যায়। মানবজীবনের বিভিন্ন ভাব ও সেই উপযোগী রসবস্তুকে কার্যের দ্বারা ফুটিয়ে তোলার শক্তিসম্পন্ন এই নাটক হবে জনশিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। এই নাটক মানুষকে ধর্মে কর্মে, সামাজিক কর্তব্যে, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা ও অনুশীলনে সঠিকভাবে উদ্দীপিত করবে। আবার দুঃখবেদনায় ভারাক্রান্ত ভাগ্যহীন মানুষ অবসন্ন হয়ে পড়লে এই নাটক জাগিয়ে তুলবে আশা-আনন্দ, হতভাগ্য মানুষকে দেবে সান্ত্বনা। তবে সব নাট্যবস্তুই গড়ে উঠবে ভাবাবেগ বা emotion-এর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে মনুষ্যজীবনকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই।
সংস্কৃতে লিখিত নাটকের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রাচীনতম হল কণিষ্কের সভাকবি অশ্বঘোষ রচিত ‘শারিপুত্র প্রকরণ’। নাটকটির অংশমাত্র পাওয়া গেছে। তবুও প্রথম শতাব্দীতে লিখিত এই প্রাপ্ত অংশ থেকেই বোঝা যায় নাট্যসাহিত্য তখনই পূর্ণ বিকাশলাভ করেছিল। তার অনেক আগেই নাটক রচনা ও অভিনয় যে শুরু হয়ে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ (বা পঞ্চম শতকে লেখা পাণিনির রচনায় শীলালিম ও কৃশাশ্ব নামে দুই নাট্যশাস্ত্রকারের উল্লেখ থেকেই অনুমান করা যায় যে, সেই সময়েই নাট্যরচনা প্রচলিত ছিল। ব্যাকরণে ব্যঞ্জনবর্ণের বিচারে তিনি অভিনেত্রী প্রসঙ্গ এনেছেন, তাতেও বোঝা যায় অভিনয়ধারা তখনই চালু ছিল। ভরতমুনির পূর্ববর্তী নন্দিকেশ্বরের নাট্যশাস্ত্রেও অভিনয়রীতির কথা রয়েছে। রামায়ণ মহাভারতেও অভিনয়ের প্রসঙ্গ রয়েছে এবং অভিনেতা অর্থে ‘শৈলুষ’ শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। যদি মনে হয়, নাটক রচনা ও অভিনয় খ্রিস্ট্র-পূর্বাব্দ থেকেই সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত ছিল, যদিও প্রাপ্ত লিখিত নাটক হিসেবে অশ্বঘোষের ‘শারিপুত্র’-কেই প্রথম বলে এখন অবধি মেনে নিতে হবে। তারপরে সভাকবি ভাসের (খ্রিস্ট্রীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দী) লেখা তেরখানি নাটক (স্বপ্নবাসবদত্তা, চারুদত্ত, প্রতিমা, পঞ্চরাত্র, ঊরুভঙ্গ, কর্ণভার, বালচরিত, দূত-ঘটোৎকচ প্রভৃতি); চতুর্থ শতাব্দীতে লেখা কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, বিক্রমোবর্শী ও মালবিকাগ্নিমিত্রম্; পঞ্চম শতাব্দীতে বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, দেবী চন্দ্রগুপ্ত; ষষ্ঠ শতাব্দীতে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক; সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীহর্ষের লেখা রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, নাগানন্দ; অষ্টম শতাব্দীতে ভবভূতির মহাবীরচরিত, মালতীমাধব, উত্তররামচরিত; অষ্টম-নবম শতাব্দীতে ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার, যশোবর্মার রামাভ্যুদয়, ময়ুরাজের উদাত্তরাঘব, দিঙনাগের কুন্দমালা, অনঙ্গের তাপসবৎসরাজ; নবম-দশম শতাব্দীতে মুরারীর অনর্ঘরাঘব, রাজশেখরের কপুরমঞ্জরী, বালরামায়ণ, বালমহাভারত; একাদশ শতকের পরবর্তীকালে লেখা নাটকের মধ্যে জয়দেবের (বাংলা কবি জয়দেব নয়) প্রসন্নরাঘব, বীরনাগের কুন্দমালা, ভাস্করের উন্মত্তরাঘব, ক্ষেমেন্দ্রের চিত্রভারত, কুলশেখরের সুভদ্রা-ধনঞ্জয়, রামকৃষ্ণের গোপালকেলিচন্দ্রিকা, রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, বিলহণের কর্ণসুন্দরী, বিশ্বনাথের মৃগাঙ্ক, বৎসরাজের কিরাতাৰ্জুনীয়ম্, সমুদ্রমন্থন, ত্রিপুরদাহ, উদ্দাগুণের মল্লিকামারুত, রামভদ্রের প্রবুদ্ধরৌহিনেয় উল্লেখযোগ্য।
সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার কালিদাসের যুগ এবং তারপরে দশম শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় উল্লেখযোগ্য উৎকৃষ্ট নাটকগুলি রচিত হয়েছে। তার মধ্যে অষ্টম শতাব্দীতে ভবভূতি পর্যন্ত সংস্কৃত নাট্যধারা জীবন্ত ছিল। ভাস, কালিদাস, বিশাখদত্ত, শূদ্রক, শ্রীহর্ষ, ভবভূতি তাদের নাট্যরচনার মধ্যে দিয়ে সে যুগে তো বটেই, পরবর্তী আধুনিককাল পর্যন্ত সমাদৃত হয়ে এসেছেন। গভীর জীবনবোধ, মানবজীবনের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি, রচনাশৈলীর পারিপাট্য, সংলাপ রচনার গভীর কৃতিত্ব এবং পরিমিত সৌন্দর্য সৃষ্টিতে এঁদের মধ্যে কালিদাস সর্বশ্রেষ্ঠ হলেও, এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই সেই কৃতিত্ব লক্ষ করা যায়। প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বিষয়ে নিজস্বতা এবং স্বাতন্ত্র্যও ছিল। তারপরে সংস্কৃত নাটকে অবক্ষয় শুরু হয় এবং অজস্র অক্ষম রচনাকারের আবির্ভাব ও রচনার পরিচয় পাওয়া গেলেও, কোনো দিক দিয়েই সেইসব নাটক উৎকৃষ্ট হতে পারেনি। বরং রচনার একঘেয়ে ধারা, বিষয়বস্তুর পৌনঃপুনিকতা এবং ক্ষমতার ন্যূনতা-সংস্কৃত নাটককে ক্লান্ত ও অবসন্ন করে তুলেছিল।
সংস্কৃত নাটকের ও নাট্যকারের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া গেলেও, এগুলির অভিনয়ের পরিচয় বা ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না। তবে উৎকৃষ্ট নাটকগুলির সবই যে অভিনীত হয়েছিল, তার পরোক্ষ প্রমাণ দেওয়া যায়। অনেক নাট্যকারের সঙ্গেই নট-নটীর পরিচয়, নাটকের শুরুতেই অভিনয়-সংবাদ ও উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধন ইত্যাদি থেকে বোঝা যায় নাটকগুলি সে যুগে অভিনয়ের জন্যই লেখা। কালিদাসের সঙ্গে বিভিন্ন নটীর সুসম্পর্কের কথা তো গল্পকথায় পরিণত হয়েছে। ভবভূতি তো নটদের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের কথা এবং ‘মালতীমাধব’ নাটকটি রচনাকালে বিশেষ পরিচিত নাট্যদলের আন্তরিক সৌহার্দের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই যুগে উদ্যোক্তা রাজাদের সঙ্গেও নটনটীদের আন্তরিকতার কথা ভর্তৃহরি, বাণভট্ট প্রভৃতি সংস্কৃত লেখকেরা তাদের লেখায় জানিয়েছেন। এইসব থেকে স্বভাবতই ধরে নেওয়া যায়, সংস্কৃত যুগে নাটকগুলি নিঃসন্দেহে অভিনীত হত এবং দর্শকমণ্ডলী সেগুলি উপভোগ করত। বিদগ্ধ রসিকদর্শক সব নাট্যকারই খোঁজেন। ভবভূতি যথার্থ সহৃদয় নাট্যরসিকের জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করতেও প্রস্তুত ছিলেন। অরসিককে রসনিবেদনের বিড়ম্বনা কালিদাস ভুলতে পারেননি।
কালিদাস প্রমুখ শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের আবির্ভাবের পূর্বে দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে, ভরতমুনি তাঁর বিখ্যাত ‘নাট্যশাস্ত্র’ গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংস্কৃত যুগের নাট্যশালা কীরকম ছিল তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছে। প্রেক্ষাগৃহ, মঞ্চরূপ, নেপথ্য-বিধান, প্রয়োগ-পদ্ধতি, সঙ্গীত, নৃত্য—প্রভৃতি প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনা করেছেন। ‘নাট্যবেশ্ম’ বা রঙ্গালয়ের প্রধান দুটি ভাগ। অর্ধাংশ প্রেক্ষা বা দর্শকদের বসার জায়গা। দর্শকাসন হবে সোপানাকৃতি, ইট বা কাঠ দিয়ে তৈরি। ভূমি থেকে এক হাত ওপরে এই আসনগুলি ঢালুভাবে তৈরি মেঝেতে বসানো থাকবে। প্রত্যেক শ্রেণির জন্য আলাদা নির্দিষ্ট আসন থাকত। সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণ, তাদের জন্য শ্বেতবর্ণের আসন। মধ্যাংশে রক্তবর্ণ চিহ্নিত আসন ক্ষত্রিয়দের, পেছনের পশ্চিমদিকে পীতবর্ণ বৈশ্যদের এবং পূর্বদিকে নীলবর্ণ শূদ্রদের আসনরূপে নির্দিষ্ট থাকতো। রঙীন স্তম্ভ দ্বারা আসনের নির্দিষ্ট স্থল চিহ্নিত হতো। মধ্যিখানে উদ্যোক্তা রাজা বা ধনীগোষ্ঠির সপারিষদ আসন সাজানো থাকতো। বাকি অর্ধাংশ রঙ্গপীঠ, এই রঙ্গপীঠ আবার রঙ্গ শীর্ষ ও নেপথ্য গৃহে ভাগ করা ছিল।
আকার অনুযায়ী রঙ্গমঞ্চ হতো তিন প্রকার—বিকৃষ্ট, চতুর ও ত্রস্র্য। এই তিন প্রকার প্রামাণ্য রঙ্গমণ্ডপকে পরিমাণ অনুযায়ী জ্যেষ্ঠ, মধ্য এবং অবর—এই তিনভাগে ভাগ করা হত। একশো আট হাত (বা কিউবিট = ১.৫ ফুট) মাপ ছিল জ্যেষ্ঠের, চৌষট্টি হাত ছিল মধ্যের এবং বত্রিশ হাত ছিল অবরের। জ্যেষ্ঠ রঙ্গালয় দেবতাদের, মধ্যমাকার রাজাদের এবং অবর স্থির করা ছিল জনসাধারণের জন্য। এগুলির মধ্যে অভিনয়ের পক্ষে আদর্শ স্থানীয় হল ‘চতুরস্র-মধ্য’ রঙ্গালয়। এর আয়তন লম্বায় ৬৪ হাত এবং প্রস্থে ৩২ হাত।
সুপ্রাচীনকালে পর্বতগুহায় সঙ্গীত নাটক অনুষ্ঠান হতো। ‘নাট্যশাস্ত্রে’-ও নাট্যমণ্ডপকে পর্বত গুহাকৃতি বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে অভিনবগুপ্ত তাঁর টীকায় একে ‘প্রেক্ষাগৃহে শব্দের স্থিরতা রক্ষার জন্য’ বলে মনে করেছেন। নাট্যমণ্ডপকে ‘দ্বিভূমি’ বলাতে অনেকে দোতলা বলে অনুমান করেছেন। কেউ ভেবেছেন দর্শকদের জন্য নিম্নতল এবং অভিনয়ের জন্য উচ্চতল।
দর্শকদের সামনে থাকবে রঙ্গপীঠ বা মঞ্চ, তার পেছনে রঙ্গশীর্ষ ও নেপথ্যগৃহ। রঙ্গালয়ের ৬৪ হাত দৈর্ঘ্য ও ৩২ হাত প্রস্থের মধ্যে দর্শদের জন্য ৩২ x ৩২ হাত, রঙ্গ পীঠ ৮ x ৩২ হাত এবং রঙ্গশীর্ষ ৮ x ৩২ হাত ও নেপথ্যগৃহ ১৬ x ৩২ হাত। ভরতের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, দর্শকের সম্মুখে ছিল মূল অভিনয়স্থল বা রঙ্গ পীঠ, তার পেছনে কিছুটা উঁচুতে রঙ্গশীর্ষ। এই অভিনয় ক্ষেত্রের পেছনে পুতপ এবং ষড়দারুক (ছয়টি কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি) বা পেছনের দেওয়াল। তার দু’পাশে সংযুক্ত প্রবেশ-প্রস্থানের দুটি দরজা, যা দিয়ে নেপথ্যগৃহ থেকে মঞ্চে আসা যায়। নেপথ্যগৃহ মঞ্চ থেকে উঁচুতে থাকত। এখানে নট-নটীবৃন্দ সাজসজ্জা করতো, অভিনয়ের অবসরে অবস্থান করতো। এখান থেকেই নাটকের প্রয়োজনে নেপথ্য শব্দ সৃষ্টি করা হতো। যেসব চরিত্র মঞ্চে আনা যেত না তাদের কণ্ঠস্বর এখান থেকেই শোনানো হতো। এই নেপথ্যগৃহ থেকেই নট-নটী মঞ্চে প্রবেশ করতেন। উঁচু নেপথ্যগৃহ থেকে নিচু মঞ্চে তারা আসতেন বলে ‘মঞ্চাবতরণ’ শব্দটি চালু হয়েছিল।
নেপথ্যগৃহ ও মঞ্চের মাঝখানের দুই দরজায় থাকত যবনিকা (জবনিকা বা যমনিকা)। যবনিকাকে পটী, অপটী, তিরস্করণী, প্রতিসরা প্রভৃতি নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। নাটকের প্রধান রস অনুযায়ী যবনিকার রঙ হওয়া বিধেয় ছিল, কোথাও শুধু লাল রঙের উল্লেখ রয়েছে।
‘যবনী’ ও ‘যবনিকা’ দুটি গ্রীক ভাষার শব্দ। তা’বলে যবনিকার ব্যবহার যে গ্রীক নাটক থেকে এসেছে, তা ঠিক নয়। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় (খ্রিঃ পূঃ ৩২৭) থেকে ভারতের নানা শিল্পকলাতেই গ্রীক প্রভাব পড়েছিল। সংস্কৃত নাটকও এই সময়েই সমৃদ্ধ হতে থাকে। অতএব কিছু গ্রীক প্রভাব সংস্কৃত নাটকে পড়তেই পারে। ভারতের রাজসভায় কিছু গ্রীক নাটক অভিনীতও হত এমন প্রমাণ রয়েছে। ‘সীতাবেঙ্গা’ গুহায় গ্রীক আদর্শে তৈরি ভারতীয় নাট্যমঞ্চ আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে ‘যবনিকা’ গ্রীক নাটক থেকে আসেনি, প্রাচীন গ্রীক নাটকে যবনিকার ব্যবহার ছিল না। গ্রীস দেশের ‘lonic’ অঞ্চলের তৈরি বস্ত্রখণ্ড গ্রীক বণিকদের কাছে কিনে তাই দিয়েই ভারতীয় মঞ্চের যবনিকা প্রস্তুত হতো, সেই সঙ্গে গ্রীক ভাষা থেকে শব্দটিও চালু হয়। গ্রীক নাটকের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।
যাই হোক, ভরত-বর্ণিত যে তিন প্রকার রঙ্গালয়ের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তার মধ্যে বিকৃষ্ট হতো আয়তাকার, চতুরস্র ছিল বর্গাকার এবং ত্র্যস্র ত্রিভুজাকার। প্রত্যেকটি রঙ্গালয়ই উপওক্তভাবে বিভক্ত থাকতো। রঙ্গালয়টি নির্মিত হতো কাঠ ও পাথরের সাহায্যে। রঙ্গপীঠ বা মঞ্চ হবে দর্পণের মতো মসৃণ। কুর্মপৃষ্ঠ বা মৎস্যপৃষ্ঠের মতো কখনোই হবে না, হবে সমতল। মঞ্চ ও দর্শকাসন এমনভাবে নির্মিত হবে যাতে দর্শকের শ্রুতি ও দর্শন স্বাভাবিক ও সহজ হয়।
হিন্দু-বৌদ্ধ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত নাট্যরচনা ও অভিনয় প্রাচীন যুগে ভারতে খুবই উন্নতি লাভ করেছিল। নাটক লেখা এবং স্থায়ী মঞ্চে তা অভিনয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কেরালা প্রদেশের ত্রিচূড়ে এই রকম একটি প্রাচীন রঙ্গমঞ্চের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে।
পরবর্তীকালে কালিদাস প্রমুখ শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের নাটকগুলি অভিনীত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সেগুলি কোথায় কীভাবে, কোন প্রয়োগরীতিতে অভিনীত হয়েছিল, তার কোনো সুনির্দিষ্ট খবর পাওয়া যায় না।
‘সঙ্গীত রত্নকর’ গ্রন্থ থেকে জানা যায়, রাজপ্রাসাদে জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যপূর্ণ অভিনয়ের জন্য ‘সঙ্গীতশালা’ নামে হলঘর থাকতো। এখানে নাচ-গান এবং অভিনয়ের আয়োজন করা হতো। নগরের অভিজাত ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতেও অনুরূপ স্থানে নাটক অভিনয় হতো। হলঘরের মাঝখানে রাজা অথবা গৃহস্বামী আসন গ্রহণ করতেন, বাঁদিকে পুরনারীবৃন্দ এবং ডানদিকে সম্মানিত সভাসদবর্গ, রাজন্যবর্গ এবং তারপরে বিভিন্ন জন যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করত।
বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দ্বারা সংস্কৃত নাটকের পরিচর্যা হয়েছিল এবং রাজা বা অভিজাত ধনী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট দর্শকের উপস্থিতিতেই এগুলির অভিনয় হতো। ফলে জীবন সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং অধ্যাত্মবাদ ও প্রণয়লীলা—এই নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলের ভাবনার প্রতিফলনেই গড়ে উঠেছিল। সমগ্র সতীয় জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে উঠতে পারেনি। সূক্ষ্মভাব, কবিত্বপূর্ণ ভাষা, সৌন্দর্য বর্ণনা, অলঙ্কারছন্দের সুষমা ও গাম্ভীর্য সংস্কৃত নাটককে কাব্যময় করে তুলে বিদগ্ধ দর্শক-শ্রোতার মানস উপযোগী হয়ে উঠেছিল। বৃহত্তর ও সাধারণ জনজীবনের পক্ষে কখনোই আস্বাদনীয় হয়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া একই নাটকে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার (উচ্চশ্রেণীর পুরুষ মাত্র সংস্কৃত ভাষা, শিক্ষিত নারী শৌরসেনী প্রাকৃত এবং ভৃত্য ও নিম্নশ্রেণির পুরুষ-নারী মাগধীপ্রাকৃত ব্যবহার করত) সকলের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হত না। তাছাড়া এগুলিও বাস্তব সমাজে ব্যবহৃত মুখের ভাষা ছিল না, ছিল কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা।
সাধারণ লোকের জন্য নির্দিষ্ট কোনো নাট্যশালা ছিল না, সংস্কৃত নাটকগুলি তাদের জন্য লেখাও হয়নি, অভিনয় দেখবার অধিকার তাদের ছিল না। ফলে সংস্কৃত নাটক কতিপয় বিদগ্ধ লোকের আস্বাদনীয় হয়ে ছিল। আপামর জনসমাজের আস্বাদনের সামগ্রী হতে পারেনি। তবে সংস্কৃত নাটকের ধারার পাশাপাশি একটি লোকনাট্যের ধারা বয়ে চলেছিল এবং সাধারণজন এই লোকনাট্যের মধ্যেই তাদের নাট্যক্ষুধা নিবৃত্ত করত। এদের উৎসাহেই সেই যুগে ছায়ানৃত্য, পুতুলবাজি, ছালিক্য নাট্যরীতি বেড়ে উঠেছিল। কালিদাসের ‘বিক্রমোবর্শীয়ম্’ নাটকের মধ্যে এই দুই শ্রেণির দর্শকের কথাই রয়েছে, ভরতবাক্যে তা স্বীকারও করা হয়েছে। আঙ্গিকেও লোকনাট্য ও অভিজাত নাট্যের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যদিও অভিজাত-বিদগ্ধ দর্শকের আনুকূল্যের কথাই কালিদাস সবসময়ে চিন্তা করেছেন।
নবম-দশম শতাব্দী থেকেই সংস্কৃত নাট্যরচনা ও অভিনয়ের অবক্ষয় শুরু হয়। ফলে কালিদাসোত্তর যুগে ভবভূতি পর্যন্ত যে নাট্যধারা ছিল, অবক্ষয়ের সূত্রপাতে সেখানে অসংখ্য অক্ষম নাট্যকারের ভিড় দেখা গেল। বিষয় বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে, কবিত্বহীন এই সব দৃশ্যকাব্য সংখ্যায় বাড়লেও, মানে অতি নিম্নশ্রেণির হয়ে গেল। কিছু রচনা উচ্চভাবের হলেও, তত্ত্বকথা, অলঙ্কারভার এবং নাট্যগুণহীনতার জন্য কখনোই অভিনীত বা আদৃত হয়নি। ফলে এই সময়ে সংস্কৃত নাটক ধ্বংস ও অবনতির পথেই এগিয়ে ছিল। সর্বসাধারণের সঙ্গে যোগ হারিয়ে, কতিপয় মানুষের গণ্ডীর সীমাবদ্ধতায় আটকে থেকে, নাট্যগুণহীন কবিত্ব ও বর্ণনার বাহুল্যভারে এবং নবসৃষ্ট আঞ্চলিক ভাষাগুলির সঙ্গে ব্যবধান বেড়ে যাওয়ায় সংস্কৃত নাটক ক্ষীণপ্রাণ হয়ে পড়ে। এই সময়েই মুসলমান শাসকদের আনুকুল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে সংস্কৃত নাটক আরো দিগভ্রান্ত হয়ে পড়ে।
সমগ্র মধ্য যুগে আর সংস্কৃত নাটকের কোনো প্রসার বা উন্নতি হয়নি। মধ্য যুগে চৈতন্যদেব কৃষ্ণলীলার যে অভিনয় করেন, তা সংস্কৃত নাট্য বা মঞ্চরীতিতে করেননি, করেছিলেন লোকনাট্যের প্রচলিত ধারাতেই।
আধুনিক যুগে ইংরেজ আগমনের পর বিলিতি রঙ্গালয়, নাট্যরীতি ও অভিনয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে নব্য বাঙালি তাদের নাটক ও অভিনয়ধারা গড়ে তোলেন। দীর্ঘদিন বাদে আবার নাট্যশালা তৈরি করে নাট্যাভিনয়ের সংবাদ পাওয়া গেল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংরেজরা এখানে নাট্যাভিনয় শুরু করে। বাঙালির নাট্যচর্চা মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে শুরু হয় উনিশ শতকের প্রথম দিকেই। বলা যায়, বাঙালির নতুন যুগের নাটক ও নাট্যচর্চার সূত্রপাত সংস্কৃত নাটক ও নাট্যাভিনয়ের কোনরূপ প্রভাব থেকে নয়, একেবারেই ইংরেজদের অনুকরণ ও অনুসরণে গড়ে উঠেছিল।
তবে ধনী বাঙালির প্রাসাদ-মঞ্চে সখের নাট্যশালার মাধ্যমে এই পাশ্চাত্য মঞ্চ ও নাট্যাভিনয়ের প্রথা চালু হলেও, কিছু কিছু দিকে ভারতীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা যায়নি—
- প্রথম দিকে সংস্কৃত নাটক অভিনয় করা হয়েছে। পরে সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ অভিনয় করা হয়েছে।
- মৌলিক নাটক রচনার কালেও সংস্কৃত নাটকের প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। পাশ্চাত্য ভাবনায় বিভোর মধুসূদনও তার প্রথম বাংলা নাট্যরচনা ‘শর্মিষ্ঠা’য় প্রবলভাবে সংস্কৃত রীতি ও ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অন্য নাট্যকারদের কথা বলাই বাহুল্য।
- মঞ্চ বিদেশী ধরনের হলেও, তার সাজ-সজ্জা, জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য প্রদর্শন অনেকটাই সংস্কৃত নাট্যশালার যুগের ভাবনাতেই গড়ে উঠেছিল।
- হিন্দু-ঐতিহ্যে বিভোর বেশ কিছু অভিজাত বাঙালি ও নব্যশিক্ষিত বাঙালি ঐতিহ্যের তাগিদে সংস্কৃত নাটককে স্বীকরণ করার চেষ্টা করেছিলেন।
দীর্ঘ মধ্য যুগের বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও আধুনিক যুগে নবীন রঙ্গালয় ও নাটকাভিনয়ের সূত্রপাতকালে সংস্কৃত নাটক ও মঞ্চের ঐতিহ্যানুসরণ সূক্ষ্মভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। যদিও আধুনিক বাঙালির থিয়েটার ও নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ ও মঞ্চাভিনয় রীতিতেই গড়ে উঠেছিল।


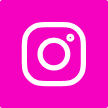


Leave a Reply