
সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে ভবভূতির অবদান আলোচনা কর।
নাট্যকার ভবভূতি
সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কবি কালিদাসের পরেই শ্রীকণ্ঠ-পদ-লাঞ্ছন” ভবভূতির স্থান। মূলত করুণ রসের নাট্যকার রূপে ভবভূতি খ্যাতিমান। তবে শূঙ্গার ও বীররসের নাট্যপ্রণয়নেও তিনি যথেষ্ট কুশলী ছিলেন। ভবভূতি লিখিত “মহাবীরচরিত’ নাটকে তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ভবভূতির জন্ম দক্ষিণাপথের পদ্মপুর নামে একটি নগরে। সেখানে তৈত্তরীয় শাখার কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগন বাস করতেন। সেই বংশের মহাকবি ভট্টগোপালের পঞ্চম সন্তান নীলকণ্ঠের পুত্র হলেন ভবভূতি। সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীতে ভবভূতি বর্তমান ছিলেন।
ভবভূতির রচিত তিনটি নাটকের সন্ধান মেলে— ‘মালতীমাধব’, ‘মহাবীরচরিত’, ও ‘উত্তররামচরিত’। তাঁর ‘উত্তররামচরিত’-এ করুণ রসের নির্বাধ অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়। ‘মালতীমাধব’ নাটকে নায়ক-নায়িকার সংবেদনাময় প্রেমসত্তার সরল চিত্রণ চোখে পড়ে। ‘মহাবীরচরিত’-এ আবার ভবভূতি আবার গুরুত্ব দিয়েছেন বীররস এবং শৃঙ্গাররসকে। এইভাবে নাট্যকার ভবভূতির জীবনদৃষ্টি ও সমবেদনা বহু বিচিত্র নাট্যসম্ভাবনার জন্ম দিয়েছে।
মালতীমাধব
ভবভূতির প্রথম নাটক ‘মালতীমাধব’। নাট্যরীতির নিরিখে ‘মালতীমাধব’ একটি প্রকরণ। সম্ভবত ‘বৃহতৎকথা’-র অন্তর্গত কোনো কাহিনির উপর নির্ভর করেই ভবভূতি নাটকটি রচনা করেছিলেন। দশটি অঙ্কে বিন্যস্ত নাটকটি অহেতুক দীর্ঘ। সমালোচকরা মনে করেছেন দশটির বদলে আটটি অঙ্ক হলেই যথেষ্ট পরিমিতিবোধ তৈরি হতে পারতো। কিন্তু নবীন বয়সের রচনা বলেই সম্ভবত নাটকটির মধ্যে শৈথিল্য, অসংযম এবং অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস ধরা পড়ে।
নাটকের কাহিনিবস্তু সহজ এবং সাদামাটা। উজ্জয়িনীর মন্ত্রিকন্যা মালতীর সঙ্গে অন্য রাজ্য থেকে আগত শিক্ষার্থী মাধবের প্রণয় নাটকের মূল আলোচ্য। মাধবের পিতা অমাত্য দেবারত এবং মালতীর পিতা ভূরিবসু সহাধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন, এবং তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন নিজের সন্তানদের বিবাহসুত্রে আবদ্ধ করবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মালতীর পিতা এই সম্পর্কে আগ্রহী হলেন না, বরং নিজের পছন্দসই পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ স্থির করে ফেলেন। এরপর বিবিধ বাধাবিপত্তির পেরিয়ে মাধবের বন্ধু মকরন্দ এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুণী কামন্দকীর কার্ষকুশলতায় মাধব ও মালতীর মিলন ঘটে। এই মূল কাহিনির পাশাপাশি একটি উপকাহিনিও নাটকে আছে, যেখানে মকরন্দের সঙ্গে মদয়ন্তিকার সম্পর্ক বিবৃত হয়েছে।
আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি মালতীমাধব দীর্ঘ নাটক। ফলে রচনার মধ্যে অসামঞ্জস্য তৈরি হয়েছে। কাহিনি নির্মেদ হলে নাটকটি আরো বেশি প্রশংসিত হতে পারতো। তা সত্ত্বেও ভবভূতি যথেষ্ট রচনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। নাটকে যে ভঙ্গীতে শৃঙ্গার, অদ্ভূত, বীভৎস ও রৌদ্র রসের অবতারণা করা হয়েছে, তা অভিনব। যেম মহাশ্নশানের বীভৎস বর্ণনা। এছাড়াও মালতীমাধব নাটক থেকে বামাচারী তন্ত্রসাধনার অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এই নাটকের আর একটি দিক হল বৌদ্ধ পরিব্রাজিকাদের চিত্র ও আদর্শ। তাদের মায়া-মমতা, বাৎসল্য, ব্রত প্রভৃতি ভবভূতি সুকৌশলে ব্যক্ত করেছেন।
মহাবীরচরিত
‘মহাবীরচরিত’ বা সংক্ষেপে ‘বীরচরিত’ রামচন্দ্রের জীবনের পূর্বাপর কাহিনি। এতে রামের সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশ থেকে রাবণ বধের পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে। ভবভূতি নাটকের সুচনায় বাল্লীকির কথা স্মরণ করেছেন। বাল্মীকির রামায়ণ বহির্ভূত ঘটনাও এতে আছে। তবে ঘটনার বিন্যাস ভবভূতির নিজস্ব, কল্পনার যোজনাও অল্প নয়। নাটকটি সাতটি অংকে বিভক্ত—কৌমার, পরশুরাম সংবাদ, সংসৃষ্ট, চরিত্র, আরণ্যক ইত্যাদি।
এই নাটকে ভবভূতির প্রধান কৃতিত্ব বহুবিচিত্র রসের সংমিশ্রণ। মালতীমাধবেই বোঝা গিয়েছিল ভবভূতি কোনো একটি নির্দিষ্ট রসের বশবর্তী নন, বরং নাটকের মধ্যে বিবিধ রসের সহাবস্থানেই তাঁর কবিত্বশক্তি তৃপ্ত হয়। এই নাটকেও ভবভূতি একাধারে বার, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক রসের মিশেল দিয়েছেন। পরশুরামের ক্রোধান্ধ মূর্তি সুন্দরভাবে চিত্রিত। হরধনু ভঙ্গের সংবাদে তিনি উত্তেজিত ও রামশাসনে তিনি শ্নেহমুধুর সম্পর্কে শৃঙ্গার রস লক্ষিত হয়। আবার কৈকেয়ীর অনুশোচনা করুণ রসের উদ্রেক করে।
মালতীমাধবের মতো এই নাটকের কাহিনিবিন্যাসে শিথিলতা না থাকলেও দীর্ঘবিস্তারি বর্ণনা এবং ভাষার আড়্ম্বর নাট্যগতিকে ব্যাহত হয়েছে। কিছু কিছু অংশ অপ্রয়োজনীয় এবং অহেতুক দীর্ঘ, যেমন—রাম ও পরশুরামের দুই অংকব্যাপী বাদ-বিসম্বাদ। তবে, এই নাটকে ভবভূতির মূল কৃতিত্ব কাহিনির মৌলিকতা। প্রচলিত রামায়ণের কাহিনিকে ভবভূতি নিজের দৃষ্টিভঙ্গী মতো পরিবর্তন করেছেন। যেমন—শূর্পণখা এই নাটকে মন্থরার ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছে, কৈকেয়ী আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য জাল চিঠি লিখেছেন, রাবণকে দেখা গেছে সীতাকে বিবাহে ইচ্ছুক ইত্যাদি। এই নব রামায়ণের পরিকল্পনা সমকালীন সমাজের নিরিখে অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজ, কিন্তু ভবভূতি তাতে পিছপা হননি।
উত্তররামচরিত
‘উত্তররামচরিত’ মহাবীরচরিতের পরিপূরক। এটি রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে রচিত। কিন্তু কী পরিবেশ সৃষ্টিতে, কী রস পরিণামে তা রামায়ণ থেকে স্বতন্ত্র। এই নাটকটিও সাতটি অংকে বিভক্ত— চিত্রদর্শন, পঞ্চবটী প্রবেশ, ছায়া, কৌশল্যা- জনকযোগ, কুমারবিক্রম, কুমার প্রত্যভিজ্ঞান, সম্মেলন। প্রথম অংকের আরম্ভ রাজা রামের কাছে খষি অষ্টাবক্রের আগমনকে নিয়ে। প্রথম অংকেই সীতা নির্বাসনের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। এই নাটকের আলেখ্য দর্শন অংশটি উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায় সীতা বারো বছর নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেছেন। দুই পুত্র লব-কুশ পালিত হচ্ছে বালীকির আশ্রমে। এরপরে রামের শম্কুক বধ, লবকুশের অশ্বমেধের ঘোড়াকে বাধাদান ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে কাহিনি এগোয়। ষষ্ঠ এবং সপ্তম অঙ্ক ভবভূতির মৌলিক কল্পনা। সেখানে নাটকের মধ্যেই আরো একটি নাটক অভিনীত হয়। বালীকি রাম-সীতার জীবনকে অবলম্বন করে একটি নাটক লিখেছিলেন, তা অযোধ্যায় অভিনীত হয়। সেই নাটক দেখে দর্শক এবং রামের হৃদয় পরিবর্তন হয়, এবং সীতা স্বমর্যাদায় রাজবাটীতে প্রত্যাবর্তন করেন।
ভবভূতি উত্তররামচরিতে করুণ রসের আকরে রামায়ণের মিলনান্ত পরিণতি দান করেছেন। এই নাটকের চরিত্রচিত্রণে ভবভূতির পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তরুণ কুশ-লবের চরিত্র মনোরম। রামের স্বার্থত্যাগ, নির্বাসিতা সীতার জন্য তাঁর মনোব্যাথা ও অনুতাপ ভবভূতির লেখণিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।
উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্ক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। বিশেষত তমসা ও মুরলার কথোপকথন, ছায়াসীতার পরিকল্পনা ভবভূতির কবিত্কে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে। বংকিমচন্দ্র যে কারণে এই অংকটি সম্পর্কে বলেছেন— “কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা অতি দুর্লভ’’।
শুধু তাই নয়, আধুনিক সমালোচকরা যাকে সাইকোলজিক্যাল প্লে বা মনঃসমীক্ষণধর্মী নাটকের কথা বলেন, তার প্রাথমিক ছাপ উত্তররামচরিতের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। রাম ও সীতার দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে জটিল মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ফ্রয়েডীয় মনোঃবিশ্লেষণের চরিত্রকে ধারণ করেছে।
ভবভূতির নাট্য-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য
- ভবভূতি নিঃসন্দেহে একজন শক্তিমান কবি। বিভিন্ন রস সৃষ্টিতে ভবভূতি অদ্বিতীয়। তবে করুণ রস বর্ণনায় ভবভূতি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মানহদয়ের যে বেদনা উত্তররামচরিতে চিত্রিত হয়েছে তা অনবদ্য। কালিদাসেও এতো রসের বৈচিত্র্য নেই। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছেন—‘মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়, উৎকটে ভবভূতি’। তবে মধুররস সৃষ্টিতেও ভবভূতির মৌলিকতা দুর্লভ নয়। এছাড়া বীরত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর ঘটনার বর্ণনায় ভবভূতি অনেকক্ষেত্রেই তাঁর পূর্বসূরী কালিদাসকে অতিক্রম করে গেছেন। যেমন মহাবীরচরিতে পরশুরামের রুদ্রপৌরুষ এবং রামচন্দ্রের বীরত্ব পাঠককে মুগ্ধ করে।
- প্রেম চিত্রাঙ্কনে কালিদাস ও ভবভূতি স্বগোত্র নন। কালিদাসের প্রেমবর্ণনা শিল্পসমুজ্বল। কালিদাসের লেখায় দীপ্তি আছে, ঐশ্বর্য আছে, বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু অনুভূতির গভীরতা খানিক কম। ভবভূতি সেখানে অনভূতির নিবিড়তায় সান্দ্র। ভবভূতির প্রেম স্পর্শকাতর। ভবভূতির প্রেমের বর্ণনায় সর্বত্রই সূক্ষ্মতা লক্ষ করা যায়। এই প্রেম সহজলভ্য নয়, অর্জন করতে হয়। শুধু তাই নয় ভবভূতি বিরহেও প্রেমের সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন। ‘উত্তররামচরিত’ এই ধারার দৃষ্টান্ত।
- ভবভূতির আর একটি গুণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপরূপ বর্ণনা। এক্ষেত্রে তাঁর সূক্ষ্ম বস্তজ্ঞানের পরিচয় লক্ষ করা যায়। দণ্ডক তথা পঞ্চবটীর অরণ্যশ্রী ভবভূতির রচনায় জীবন্ত ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, ভবভূতির লেখায় প্রকৃতির মানবায়ন ঘটেছে। প্রকৃতি যেন একটি স্বাবলম্বী চরিত্র হয়ে উঠেছে ভবভূতির রচনার মধ্যে। ‘উত্তররামচরিত’-এ প্রকৃতির এই মানবায়নের উদাহরণ মেলে তৃতীয় অঙ্কে।
- ভবভূতির ভাষার বৈদগ্ধ্যও উচ্চ প্রশংসিত। সে ভাষার যেমন দৃঢ়তা, তেমন অর্থগৌরব। ভবভূতি পণ্ডিত বংশের সন্তান, ফলে শৈশব থেকেই নিয়ত অধ্যয়নের ফলে সংস্কৃত ভাষার উপর তাঁর নিবিড় দখল তৈরি হয়েছিল। সেই দক্ষতার ছাপ ভবভূতির রচনার মধ্যে দেখা যায়। ভবভূতির ভাষা ললিত বা প্রাঞ্জল নয়, বরং দুরূহ, সমাসকন্টকিত। তুলনায় কালিদাসের ভাষা সাবলীল, বোধ্য, এবং সহজ প্রসাদগুণসম্পন্ন। বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সংলাপের দিকে এই আসক্তি ভবভূতিকে লেখার জটিলতাকে বৃদ্ধি করেছে। ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে ভবভূতির রচনার রসাস্বাদন করা কঠিন।
- ভবভূতির লেখার মধ্যে সরসতার অভাব রয়েছে। হাস্যরস ভবভূতির প্রায় কোনো নাটকে নেই। তাঁর গভীর জীবনবোধ কোথাও গিয়ে সাধারণ লঘু রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া থেকে তাঁকে বিরত করেছে। ফলে ভবভূতির লেখায় বিদূষক চরিত্র পাওয়া যায় না।
- ভবভূতির আর একটি বিশেষ গুণ মৌলিকতা। কাহিনির প্রয়োজনে প্রচলিত গল্পের কাঠামো থেকে ভবভূতি প্রায়শই সরে গিয়েছেন। ‘উত্তররামচরিত’, ‘মহাবীরচরিত’-এ এই প্রবণতা বেশ স্পষ্ট। ‘উত্তরচরিতে’ ছায়াসীতার পরিকল্পনা সংস্কৃত সাহিত্যের নিরিখেই অভূতপূর্ব।


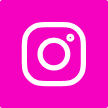


Leave a Reply