সখের নাট্যশালার ঐতিহাসিক মূল্য ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।
সখের নাট্যশালার ঐতিহাসিক মূল্য ও প্রভাব
উনিশ শতকে বাংলায় আধুনিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা এবং নাট্যাভিনয় ও বাংলায় নাট্যরচনার ধারাবাহিক সূত্রপাত করলো সখের নাট্যশালা। রঙ্গালয় ও নাটক—দুটোকেই ইংরেজদের বিদেশি থিয়েটার থেকে বাঙালির আঙিনায় নিয়ে এলো এই সখের নাট্যশালা। সেই রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনেই বাংলায় আধুনিক নাট্যরচনা শুরু হলো। বিদেশি থিয়েটারের যা কিছু বাঙালির নাট্যচর্চায় গ্রহণ করা হলো—সবই নিয়ে এলো সখের নাট্যশালা। প্রেক্ষাগৃহ, রঙ্গমঞ্চ, সাজসজ্জা, অভিনয়, সংলাপ উচ্চারণ, গীতবাদ্য, নাটকের গঠন ও আঙ্গিক—সখের নাট্যশালার মাধ্যমেই বাঙালির কাছে গৃহিত হলো—
- বিদেশী রঙ্গালয়ের মতোই এখানে রঙ্গমঞ্চ তৈরি করা হতো। বিদেশী থিয়েটারের অভিজ্ঞ লোক এনে তাদের সাহায্যেই মঞ্চনির্মাণ, দৃশ্যপট অঙ্কন, মঞ্চসজ্জা, ঐকতান বাদন মহার্ঘভাবে করা হতো।
- বিদেশী রঙ্গালয়ের অভিনয়রীতি এখানে অনুসৃত হয়েছিল। সে রীতি আঙ্গিক, বাচিক ক্রিয়া ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে গড়ে উঠতো। এই নাট্যশালার প্রধান অভিনেতারা প্রায় সকলেই বিদেশি থিয়েটারের অভিনয়রীতি দেখে, করে, অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। তারাই সখের নাট্যশালায় অভিনয়রীতিকে বিদেশি রীতিতে নিয়ন্ত্রণ করেছিল।
- বিদেশি রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ পদ্ধতিতে এখানকার মঞ্চ তৈরি হওয়াতে, সেই মঞ্চের প্রভাবে অভিনেয় নাটকের চরিত্রের আগমন-নির্গমন, ঘটনাস্থল, ঘটনার উপস্থাপনা রীতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। ফলে সংস্কৃতধর্মী নাট্যরচনার প্রভাব কাটিয়ে ক্রমে পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুযায়ী জটিল চরিত্র, বিস্তারিত ঘটনা, দ্বন্দ্ব, ঐক্যবদ্ধ গঠন, সংলাপ তৈরি হতে থাকে।
- এই নাট্যশালার প্রচেষ্টা থেকেই বাংলা নাটকে দেশীয় রীতি ও পাশ্চাত্য রীতির মিশ্রণের চেষ্টা হয়েছে। যেখান থেকে বাঙালির নিজস্ব নাট্যচর্চার সূত্রপাত দেখা যায়। এই সখের নাট্যশালার অভিনয়ের দাবিতেই বাংলায় মৌলিক নাট্যরচনা শুরু হয়েছে এবং বাংলায় নতুন নাট্যকারদের আবির্ভাব ঘটেছে। রামনারায়ণ, উমেশচন্দ্র মিত্র, মধুসূদন, মনোমোহন বসু, দীনবন্ধু (নাটক লিখলেও এখানে অভিনীত হয়নি) কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি নাট্যকারদের আবির্ভাব ও তাদের নাট্যরচনা এই রঙ্গালয়গুলি থেকেই হয়েছে। বেলগাছিয়া নাট্যশালা থেকে মধুসূদনের শুধু নাট্যরচনাই শুরু নয়, তাঁর বাংলা ভাষাতেই সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দীপনা দেখা দেয়। তাঁর নাট্যরচনা নিয়ন্ত্রণও করেছে এই নাট্যশালা। কালীপ্রসন্ন তাঁর বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের জন্য নাটক লিখেছেন, সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেছেন। রামনারায়ণের নাট্যরচনার সূত্রপাত, বিকাশ এবং ‘নাটুকে’ খ্যাতি তো এই রঙ্গালয়গুলি থেকেই। উমেশচন্দ্র মিত্র এই রঙ্গালয়ের তাগিদেই ‘বিধবাবিবাহ’ নাটক লেখেন, অন্য নাটকগুলিও এখানকার অভিনয়ের জন্যই লেখা হয়েছে। মনোমোহন বসু বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ের জন্যই তাঁর সব নাটকগুলি রচনা করেছেন। অন্যদের ক্ষেত্রেও কোনো না কোনো মঞ্চের দাবী কাজ করেছে।
- সখের নাট্যশালার প্রথম কুড়ি বছর (১৮৩১-৫১) মূলত ইংরেজি নাটক এবং ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের অভিনয় চলে। শেষ কুড়ি বছর (১৮৫২-৭২) মৌলিক নাটকের অভিনয় হয়। সাহেবদের অনুসরণে প্রথমে রঙ্গমঞ্চ তৈরি হলেও, বাংলায় অভিনয়যোগ্য নাটক ছিল না। তাই ইংরেজিতেই নাটক করতে হয়েছে নতুবা অনুবাদ করে নিতে হয়েছে। শেষে মৌলিক নাটকের দাবীতেই এসেছেন বাংলার নাট্যকাররা। বাংলায় নাটক লেখার চর্চা ও জোয়ার এনেছিল সখের নাট্যশালা।
- এখানে অভিনীত নাটকের মধ্যে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ও অনুসরণ,
পৌরাণিক কাহিনীর নাট্যরূপ, কিছু প্রহসন ও সামাজিক সমস্যামূলক নাটক, ইতিহাস অবলম্বনে নাটক এবং শেক্সপীয়ারের আদলে লেখা নাটক। কিছু নক্সাজাতীয় রচনা, পারস্পরিক ব্যক্তি ও পরিবারের উতোর-চাপানের জন্যই লেখা হয়েছিল।
- পরবর্তী সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগীদের কেউ কেউ সখের নাট্যশালাগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি হেমেন্দ্রনাথ মুখখাপাধ্যায়ের বাড়ির মঞ্চে ‘কিছু কিছু বুঝি’ প্রহসনে তিনটি চরিত্রে অভিনয় করেন। এটিই তার জীবনের প্রথম অভিনয়। ধর্মদাস সুর এই নাট্যপ্রযোজনাতেই প্রথম রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষরূপে কাজ করেন। স্টেজ ম্যানেজার হিসেবে তিনি এই মঞ্চনির্মাণ করে তার পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ও সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগে এঁরা দুজনেই তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিলেন।
- সখের নাট্যশালায় অভিনয়ের মাধ্যমে নব্যশিক্ষিত বাঙালির নাট্যবোধ, রুচি ও স্পৃহা গঠিত হয়েছিল। প্রচলিত যাত্রা থেকে সরে এসে নতুন থিয়েটারের প্রতি নতুন যুগের আকর্ষণ তৈরি করেছিল এই নাট্যশালাগুলি। এদের অভিনয়, সেই অভিনয়ে উপস্থিত নিমন্ত্রিত দর্শক এবং সংবাদপত্রের সমালোচকের মাধ্যমে এই খবর প্রাসাদ-মঞ্চের গণ্ডীর বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদপত্রগুলি সে সময়ে জনমত গঠনে ও আধুনিক রঙ্গালয়ের প্রসারে খুবই কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল।
- সখের নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষকদের হিন্দু জাতীয়তাবোধের ভাবনা, সংস্কৃতমুখীনতা, সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার কারণে আধুনিক নাট্যভাবনার ব্যাপকতম প্রকাশ এখানে হতে পারেনি। রামনারায়ণকে দিয়ে এই কাজগুলি হয়েছিল, তাই তিনি এই সময়ের সবচেয়ে আদৃত নাট্যকার। মধুসূদনের নাট্যসত্তার পূর্ণ স্ফূরণ সেই কারণেই এখানে হতে পারেনি। মধুসূদনের সেই মানসিক ক্ষোভ ও জ্বালা আমরা জানি। দীনবন্ধুর নীলদর্পণের মতো নাটক ১৮৬০-এ লেখা হয়ে গেলেও, এই নাট্যশালায় অভিনীত হয়নি। সাধারণ নাট্যশালার যুগ অবধি তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শাসনের উপজাত এই ধনী বাঙালি শ্রেণী ব্রিটিশের সহায়তা চেয়েছে, বিরোধিতা কখনোই নয়।
- ধনীদের প্রাসাদ-মঞ্চে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, রাজকর্মচারী ও অনুগৃহীত ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের সেখানে প্রবেশের সাধ্য ছিল। অথচ ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই যে নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রসার হয়ে চলেছে, তাদের নবজাগ্রত নাট্যস্পৃহা সখের নাট্যশালায় ধনীদের প্রাসাদ-মঞ্চের মাধ্যমে মেটেনি। প্রাসাদ-মঞ্চের আওতার বাইরে বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়কে প্রসারিত করবার প্রেরণা ও উদ্যম থেকেই মধ্যবিত্তের থিয়েটারের যাত্রারম্ভ। ১৮৭২-এ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বাংলা থিয়েটারের নতুন যুগের শুভ উদ্বোধন ঘটে।
- একথা ঠিক, যাত্রা, কবিগানের নিম্নরুচি থেকে সরে এসে শিক্ষিত মানস যে নতুন থিয়েটার ও নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, তাদের স্পৃহা এই সখের নাট্যশালাতেই কিছুটা সাজুয্য লাভ করেছিল। তাছাড়া সাহেবি থিয়েটারের শিক্ষা, তার ব্যবহার ও অভ্যাস এই নাট্যশালাগুলিতেই হয়েছে। বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সূচনাপর্বে সখের নাট্যশালাই ছিল বাঙালির নাট্যচর্চার শুধু প্রধান নয়, একমাত্র প্রবাহ।
- শৌখিন, ধারাবাহিকতাবিহীন, অস্থায়ী, আন্দোলন সৃষ্টিতে ব্যর্থ—ইত্যাদি যত ব্যর্থতার কথাই সখের নাট্যশালা প্রসঙ্গে বলা হোক না কেন, বাংলা থিয়েটার ও নাটকের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের ইতিহাসে সখের নাট্যশালার ঐতিহাসিক অবস্থান ও মূল্যকে কখনোই অস্বীকার করা যাবে না। সীমাবদ্ধতা ও সিদ্ধি নিয়েই তার ইতিহাস রচনা করতে হবে।


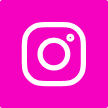


Leave a Reply