সামাজিক নাটক কাকে বলে? একটি সামাজিক নাটক আলোচনা কর।
সামাজিক নাটক
সাধারণভাবে নাটক বলতে আমরা সামাজিক নাটকই বুঝি। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বৃত্ত ছেড়ে নাটক যে মুহূর্তে সমাজের বিশেষ কোনো সমস্যাকে আশ্রয় করেছে, সেই মুহূর্তে আমরা বুঝতে পেরেছি বাংলা যাত্রাগান থেকে নাটকের পথ-পরিক্রমা কত স্বতন্ত্র হতে চলেছে। নাটক জীবননির্ভর, এবং জীবন বলতে প্রধানত মানুষের সামাজিক জীবনই বোঝায়, তাই আধুনিক নাট্যকলার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সামাজিক নাটকের উন্মেষের এক দৃঢ় সম্পর্ক আছে।
সামাজিক নাটক বলতে অবশ্য আমরা ঠিক সামাজিক মানুষের নাটক বুঝি না, বুঝি এমন এক ধরনের নাটক যার বিষয় কোনো সামাজিক সমস্যা। সেই হিসাবে যেসব নাটক সমস্যাপ্রধান নাটক হিসাবে চিহ্নিত, সেই সমস্যার প্রকৃতি সামাজিক হলে তাকে নিশ্চয়ই সামাজিক নাটক বলা যায়। আবার বাস্তবতাবাদী আন্দোলনে উদ্ভূত নাটককেও সেই একই কারণে সামাজিক নাটকই বলতে হবে। এই সূক্ষ্ম বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা বলতে পারি বিভিন্ন সময়ের যেগুলি প্রধান সামাজিক সমস্যা সেগুলিকে অবলম্বন করে লেখা নাটককেই আমরা আখ্যা দিই সামাজিক নাটক। যেমন ঊনবিংশ শতকের প্রধান সমস্যা ছিল কৌলীন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি। এই সঙ্গে ছিল অন্তঃসারশূন্য জমিদারদের আভিজাত্যবোধ এবং এইরকম দুই পরিবারের বংশানুক্রমিক লড়াই প্রভৃতি। পরবর্তীকালে সামাজিক সমস্যার পালাবদল ঘটেছে। যৌথ পরিবারের অবলুপ্তি এবং সংসার ক্রমশ ছোট থেকে আরো ছোট হওয়ার প্রবণতাই এখন সবচেয়ে বেশি প্রকট। এর ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলি এখনও ব্যক্তিগত সমস্যা হয়েই আছে, কিন্তু অচিরেই তা বৃহত্তর সামাজিক সমস্যায় রূপান্তরিত হবে, সে আশঙ্কা এখনই দেখা দিতে শুরু করেছে।
প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে সম্ভবত রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ (১৮৫৪)। সেকালে কুলীনদের বহুবিবাহ ছিল অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা এবং এই সমস্যাকেই তার জনপ্রিয় নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। রামনারায়ণ সামাজিক প্রহসনও কিছু লিখেছিলেন, যেমন বহু বিবাহের দোষ নিয়েই লিখেছেন ‘উভয় সঙ্কট’, স্বামীর লাম্পট্য দূর করায় স্ত্রীর কৌশল নিয়ে লিখেছেন ‘চক্ষুদান’, বড় প্রহসন হিসাবে লিখেছেন ‘যেমন কর্ম তেমনি ফল। ‘কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক’ যদিও তার জনপ্রিয় নাটক, নিটোল কাহিনির অভাবে একে খণ্ড খণ্ড ব্যঙ্গচিত্রের মতো মনে হতে পারে। নাটক হিসাবে বরং তার পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক ‘নবনাটক’ অনেক শিল্পশ্রুটিমুক্ত।
বাংলা নাটকের আদি যুগে রামনারায়ণের পরবর্তী অনেক নাট্যকারই সামাজিক নাটক লেখার চেষ্টা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের ‘বাল্যবিবাহ নাটক’, তারকচন্দ্র চূড়ামণির ‘সপত্নী নাটক’, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের ‘কাদম্বিনী নাটক’, উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবাবিবাহ নাটক’ প্রভৃতি। মধুসূদন দত্ত সামাজিক নাটক লেখেননি, কিন্তু তার ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’ এবং ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’—এই দুটি সামাজিক প্রহসন এই জাতীয় রচনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলা যেতে পারে। দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ অবশ্যই সামাজিক নাটক। যদিও আজ তা ইতিহাস হয়ে গিয়েছে, দীনবন্ধু যখন ও নাটক লেখেন তখন এই নৃশংস প্রথা ছিল নির্মমতম সামাজিক সমস্যা। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে জীবনযাত্রা গঠনের অপদার্থতা নিয়ে লেখা তার ‘সধবার একাদশী’, কিংবা ছোট প্রহসন ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ও পুরোপুরি সামাজিক প্রহসন এবং রচনাসৌকর্যে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর। তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং সর্বশ্রেণীর উপভোগ্য প্রহসন ‘জামাই-বারিক’।
একটি সার্থক বাংলা সামাজিক নাটক
বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় সামাজিক নাটকগুলির অন্যতম গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘প্রফুল্ল’, সুতরাং এই নাটকে সামাজিক নাটকের লক্ষণ কতোটা আছে এবং তার শিল্প-সার্থকতাই বা কতখানি, সংক্ষেপে তা আলোচনা করা যেতে পারে।
প্রফুল্ল’ নাটকের নাট্যকাহিনী মোটামুটিভাবে এইরকম যে, অল্প বয়সে পিতৃহারা যোগেশ নিজে প্রচুর কষ্ট করে বিধবা মা এবং দুটি নাবালক ভাই রমেশ ও সুরেশকে মানুষ করার চেষ্টা করেন। জীবনে যখন তিনি সৎপথে থেকে, ন্যায়নিষ্ঠভাবেই প্রতিষ্ঠিত, মেজভাই রমেশকে ওকালতী পাশ করিয়েছেন, ছোট ভাই সুরেশকে পড়াশুনায় কৃতী করতে না পারলেও অমানুষ হতে দেননি। সেই সময়েই সংসারে বিপর্যয় দেখা দেয়, তার ব্যাঙ্ক ফেল করে এবং তিনি সর্বস্বান্ত হন। তার এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে মেজভাই রমেশ তাকে দিয়ে বাড়ি ও সম্পত্তি লিখিয়ে নেয় নিজের নামে এবং এ পথের একমাত্র কাটা যোগেশের পুত্র যাদবকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে মিথ্যা চুরির অপবাদে সুরেশকে জেলে ঢোকায়। যোগেশ আঘাতের পর আঘাতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন এবং মদ্যপানে বিভোর হয়ে সমস্ত ভুলে থাকার চেষ্টা করেন। সংসারের প্রতি দৃষ্টি না থাকায় তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়, ছোট ছেলের শোকে মা উন্মাদিনী হন শেষে যাদবকে মারার অপকীর্তি রোধ করতে এসে রমেশের স্ত্রী প্রফুল্লও মারা পড়ে এবং প্রচলিত রমেশ বোধহয় এততদিনে প্রথম ধাক্কা খায়।
নাটকটি আমাদের দেশের একদা সামাজিক অবস্থাকেই প্রতিফলিত করে। এখানে যদিও আমরা কোন বিশেষ সামাজিক সমস্যাকে একক ভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারি না, কিন্তু আমরা সবাই বুঝি, একান্নবর্তী পরিবারের মূল সমস্যা এখানে উদঘাটিত হয়েছে। একার আয়ে যখন সংসার দাঁড়িয়ে থাকে, অথচ পোষ্য থাকে অনেকগুলি, তখন সেই একার বিপর্যয়ে গোটা সংসারটাই ভেসে যাবার উপক্রম হয়। এখানে অবশ্য যোগেশের আয়ে সংসার চললেও তিনি রমেশকে মানুষ করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও একটি প্রশ্ন আছে। ভায়েরা যাতে ঠিকমতো পড়াশুনা করতে পারে, কোনো আর্থিক অসুবিধা যাতে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে না পারে, এ ব্যাপারে তার যতো দৃষ্টি ছিল, ভাইগুলি ‘সত্যিই মানুষ’ হচ্ছে কিনা এদিকে দৃষ্টি তার একেবারেই ছিল না। ফলে, একচক্ষু হরিণের মতো তিনি তাদের পেছনে অকাতরে অর্থব্যয়ই করে গিয়েছেন, ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ হয়ে তাদের শাসনের দিকটা দেখতেই পাননি। এর আশঙ্কিত ফললাভও তিনি করেছেন। এই সঙ্গে অবশ্য আর একটি সামাজিক সমস্যার দিক উন্মোচিত করা দরকার, সেটি হল বেসরকারী ব্যাঙ্কের সমস্যা। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করার ফলে আমরা এখন যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করি তার মধ্যে প্রধান হল ধনসম্পত্তির নিরাপত্তা। মানুষ তার অর্থ সঞ্চয় করে তিল তিল করে, অথচ বেসরকারী ব্যাঙ্কিং প্রথায় যে-কোনদিন এক মুহূর্তে তা নস্যাৎ হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল—সেই আশঙ্কার বিধ্বংসী চেহারা আমরা প্রফুল্ল’ নাটকে দেখতে পাই। সুতরাং সমস্যার প্রকৃতি বিচার করলে নাটকটিকে সামাজিক নাটক বলে স্বীকার করতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়। অবশ্যই এর শিল্পসাফল্যের কথাটা এরপর আমাদের চিন্তা করতে হবে।
যে-কোনও ভাল নাটকেই চরিত্র ও ঘটনাকে আমাদের স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। প্রফুল্ল যেহেতু ট্র্যাজেডি হিসাবে সাধারণভাবে স্বীকৃত, এর পরিণতি এবং নায়ক চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এই নাটকের পরিণতি এবং ঘটনাধারার মধ্যে যে একটা কার্যকারণ-শৃঙ্খলের অভাব আছে এবং রোমহর্ষক ঘটনার প্রতি নাট্যকারের যে বেশি। আগ্রহ আছে তা আমরা বুঝতে পারি। দর্শকদের অভিনন্দন পাওয়ার জন্য জগমণি ও কাঙালীচরণকে তিনি প্রায় অবিশ্বাস্য চরিত্রে পরিণত করেছেন। প্রফুল্ল শেষ দৃশ্যে যে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার নায়িকা হয়ে যায়, সে প্রাধান্য তাকে প্রথমাবধি দেওয়া হয়নি। রমেশের মতো আদ্যন্ত শয়তান চরিত্র কোনো মানুষের হতে পারে কিনা এটাও ভাববার কথা। বিশেষ করে যোগেশ কেন মদ্যপানের মাত্রা বাড়িয়ে দেন, সারাজীবন যিনি নিজে দাঁড়াবার ও ভাইদের প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন তিনি একটি আঘাতেই—তা সে যতোই বড়ো হোক না কেন ভেঙে পড়েন, তা আমাদের বিস্মিত করে। এ কথা আরো ভাববার এই কারণেই যে, উদ্যম ও মনোভাব পঙ্গু হয়ে গেলে তাকে তো আমরা ট্র্যাজেডির আদর্শ নায়ক বলতেই পারি না, এবং যোগেশ ছাড়া নায়ক হিসাবে ভাববার মতো অন্য কোনো চরিত্রও ‘প্রফুল্ল’ নাটকে নেই। অবশ্য যোগেশ চরিত্রকে একটু অন্য ভাবেও চিন্তা করা যায়। তার চারিত্রিক ত্রুটি বা Frailty যদি আমরা ধরি অন্ধ ভ্রাতৃস্নেহ এবং ভাইয়ের আচরণে তিনি যদি বুঝে থাকেন এতোদিন তিনি পণ্ডশ্রম করেছেন—সঞ্চিত ধনের চেয়েও বড় সম্পদ তিনি হারিয়েছেন, এই অনুভূতি যদি তার জেগে থাকে, একমাত্র তবেই তার আচরণের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। ফলত, বিষয়ের বিচারে তো বটেই, রূপায়ণের ক্ষেত্রেও আমরা ‘প্রফুল্ল’কে মোটামুটিভাবে শিল্পসফল সামাজিক নাটক হিসাবে মেনে নিতে পারি।
তথ্যসূত্র:
| কাব্যজিজ্ঞাসা – অতুলচন্দ্র গুপ্ত | Download |
| কাব্যতত্ত্ব: আরিস্টটল – শিশিরকুমার দাস | Download |
| কাব্যমীমাংসা – প্রবাসজীবন চৌধুরী | Download |
| ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব – নরেন বিশ্বাস | Download |
| ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব – অবন্তীকুমার সান্যাল | Download |
| কাব্যজিজ্ঞাসার রূপরেখা – করুণাসিন্ধু দাস | Download |
| কাব্য-শ্রী – সুধীরকুমার দাশগুপ্ত | Download |
| সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য – কুন্তল চট্টোপাধ্যায় | Download |
| সাহিত্য ও সমালোচনার রূপরীতি – উজ্জ্বলকুমার মজুমদার | Download |
| কাব্যালোক – সুধীরকুমার দাশগুপ্ত | Download |
| কাব্যপ্রকাশ – সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত | Download |
| নন্দনতত্ত্ব – সুধীর কুমার নন্দী | Download |
| প্রাচীন নাট্যপ্রসঙ্গ – অবন্তীকুমা সান্যাল | Download |
| পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা – নবেন্দু সেন | Download |
| সাহিত্য প্রকরণ – হীরেণ চট্টোপাধ্যায় | Download |
| সাহিত্য জিজ্ঞাসা: বস্তুবাদী বিচার – অজয়কুমার ঘোষ | Download |


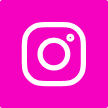


Leave a Reply