‘সাহিত্যের বিচারক’ প্রবন্ধের মূল ভাববস্তু ব্যাখ্যা কর।
- সাহিত্যের স্বাধীন রচনার এক এক জনের প্রতিভা সর্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে, সর্বকালের আসন গ্রহণ করে, তেমনি বিচারের প্রতিভাও আছে। ‘সাহিত্যর বিচারক’ প্রবন্ধ অবলম্বনে মন্তব্যটি বিচার কর।
সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক একজন স্রষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় যার প্রতিভা যুগাতিশায়ী। তিনি শুধু নিজে সৃষ্টি করেন না, তাঁর যুগে তিনি সৃষ্টির ধারাকেও নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন। সাহিত্যের আদর্শের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ থাকে এবং সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রীতিও অনেক বেশি। তাঁর প্রতিভার গুণে সকলে সাহিত্যের আদর্শকে অনুসরণ করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভা ছিল এমনই যুগাতিশায়ী। তাই তিনি সব্যসাচীর ন্যায় একদিকে সৃষ্টি, অন্যদিকে সাহিত্যের আদর্শ থেকে বিচ্যুত যশঃপ্রার্থী অপটু অধ্যবসায়কুণ্ঠ লেখকদের কঠোর সমালোচনা করে নিবৃত্ত করেছেন। তাঁর প্রতিভার গুণে তিনি শুধু তাঁর যুগের নয় সকল যুগের যেন প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তার পরে এস. টি. কোলরিক সর্বকালের বিচারকের আসন গ্রহণ করেছেন। সমালোচক বলেছেন— “The Criticism of to day may be said to be in direct descent from Coleridge.’’ স্বাধীন সৃষ্টির ক্ষেত্রেও যেমন আমরা অসাধারণ স্রষ্টার পরিচয় পেয়ে থাকি, তেমনি সমালোচনার ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়।
মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে এক একজন মানব হৃদয়ে চিরকালীন সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। উদাহরণ হিসেবে মহাকবি কালিদাস এবং ইংরেজ কবি ও নাট্যকার শেক্সপীয়র। তাঁদের প্রতিভা নিঃসন্দেহে সর্বকালের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি রাখে। সমালোচনার ক্ষেত্রেও তেমনি অ্যারিস্টটল, তাদের পরীক্ষা ও বিচারের ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত প্রখর। প্রত্যেক সমালোচকের মধ্যেই একজন সমালোচক বাস করেন। এই সমালোচক সৃষ্টিপ্রবাহের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। সৃষ্টি যাতে ভাববিগ্রহ রচনা করতে পারে, কোন ভাবালুতা, অপক্ষপাত প্রাচুর্য কিংবা শৈথিল্য এসে তাকে বিক্ষিপ্ত ও ব্যাহত করতে না পারে, সেদিকে সমালোচক সচেতন থাকেন। সৃষ্টি ও সমালোচনা যেন হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যায়। এখানে একাগ্রচিত্তে জীবনের উপাদানগুলি মন্থন ও নির্বাচন করে রচনার কাজে মননানিবেশ করতে হয়। সৃষ্টির মধ্যে জীবন সুসম্পন্নরূপে, প্রতীক মূল্য হয়ে অসাধারণ মহিমায় দেখা দেবে। সহিত্যস্রষ্টা ‘‘adresses himself with a single mind to the task of constructing life into an image which will convince us and delight.’’
স্রষ্টার মধ্যে যে সমালোচক বিরাজ করেন, তিনি স্রষ্টার সত্তার থেকে অভিন্ন বলে মৌলিক রচনার দিকে সমগ্র দৃষ্টি রাখেন। উপরন্তু স্রষ্টা-সমালোচক তাঁর নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে যতখানি সচেতন, অপরের সৃষ্টি সম্পর্কে নাও থাকতে পারেন। তিনি হয়ত প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শ ও রীতি ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু অপর একজন কবি কোন নতুন ধারা গ্রহণ করলেন, তাঁর সৃষ্টির উৎকর্ষ নিরূপণ করতে হলে, পূর্বের ব্যাখ্যা ও আদর্শ যথাযথভাবে সাহা নাও করতে পারে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সমালোচকের প্রয়োজন সাহিত্যরুচি ও বিচারবোধ। এমন সমালোচকই পাঠক-মনের প্রতিনিধি। তাঁর ব্যাখ্যা ও বিচার সাহিত্য-স্রষ্টার রচনাকে পাঠকমনে সহজে পৌঁছে দেয়। সাহিত্যের লেখক জীবনকে নতুন করে ব্যাখ্যা করেন, পুনর্বিন্যস্ত ও ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনিই জীবনশিল্পী। তিনি যেন জীবনের বন্ধুর পথে নিঃসঙ্গ পথচারীর মত যাত্রা করে করে পথ প্রস্তুত করেন। সমালোচকও সেই পথে হেঁটে দেখেন যে, তা চলার পক্ষে যোগ্য হয়েছে কি না এবং ওই পথ কোথায় ও কীভাবে লোকালয়ের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে। সমালোচকের পক্ষে জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। যেহেতু কাব্য ও সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় মানবজীবন অগ্রাধিকার লাভ করে, সেইজন্য মানব মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অপরিহার্য। বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতির ধারা বর্তমান কালের মানুষের হৃদয়কে পরিশীলিত করে তুলছে। ইতিহাস হল অতীত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। এই জ্ঞান না থাকলে সৃষ্টিকে সার্থক করে তোলা যায় না। টি.এস.এলিয়ট একে ট্র্যাডিশনরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। একে ইতিহাস সচেতনতা বলা যায়— ‘‘Tthe historical sense involves a perception not only of the pastness of the past, but of its presence’’। এ শুধু বর্তমানের জ্ঞান নয়, সমগ্র সংস্কৃতি ধারার সঙ্গে সম্যক পরিচয়জনিত অভিজ্ঞতা।
যাঁদের বিচারবুদ্ধি অভ্রান্ত, সাহিত্যের নিত্য লক্ষণগুলি যারা অন্তঃকরণের সংগে মিলিয়ে নিয়েছেন, স্বভাবে ও শিক্ষায় তাঁরা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করতে পারেন। তবে এক শ্রেণীর ব্যবসাদার সমালোচক আছেন তাঁদের বিদ্যা সম্পূর্ণ পুঁথিগত। তাঁরা সারস্বত দরবারের বাইরে বসে হাঁকডাক, তর্জন-গর্জন করে থাকেন, অন্তঃপুরের সংগে তাঁদের পরিচয় খুবই কম। রসাস্বাদন করার মত মানসিক শিক্ষা তাঁদের নেই। ভার্জিনিয়া উলফ এ প্রসঙ্গে বলেছেন—‘‘Reviewers we have but not a competent critic.’’ তাঁরা প্রকৃত বিচারক নন। তাই তাঁদের মতামত বা বিচারের উপর নির্ভর করা যায় না। ‘রামায়ণ’-এর পরিচয় দান প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তা মুখ্যতঃ সেই মহাকাব্য সম্পর্কে হলেও তা সাহিত্য সমালোচনার আদর্শ সুস্পষ্ট করেছে। তিনি বলেছেন—“কবি কথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন। এইরূপ পূজার আবেগ-মিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা; এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর-এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অথবা যেখানে পাঠকের হৃদয়েও তাঁর ভক্তি আছে সেখানে পূজাকারকের ভক্তির হিল্লোল তরঙ্গ জাগাইয়া তোলে। তাঁর মনে অন্য কোন প্রশ্ন থাকে না, সংশয়ও থাকে না। কবির মতে, সমালোচকের ধর্ম ও হল গ্রহকে ব্যাখ্যা করা, তার অন্তর্নিহিত সত্য ও সৌন্দর্যকে পরিস্ফুট করে দেওয়া।
সাহিত্য যদি স্রষ্টার নৈর্ব্যক্তিক মনের সৃষ্টি হত, তবে বিশ্লেষণমূলক বিচার পদ্ধতির সার্থকতা থাকত। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু সাহিত্যের বাণী স্বয়ংবরা। এলিয়ট বলেছেন যে, কবির কাব্য তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয়—কথাটি আংশিক সত্য। কবি তার কাব্যে যে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তা হয়ত তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করেননি, কিন্তু এই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা তিনি আত্মসাৎ করেছেন, স্বীকরণ করেছেন। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে তাদের প্রকাশ তার ব্যক্তিত্বের দ্বারা রঞ্জিত। একে তখন আর নৈর্ব্যক্তিক বলা চলে না। কাব্যে তদাত দৃষ্টিভঙ্গির অবকাশ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা বিজ্ঞানের মত ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত হতে পারে না। যেখানে আমরা নিজেকে প্রকাশে উৎসুক, সেখানে আমরা নিজেদের মধ্যে অপরিমিত ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করে থাকি। সেখানে সম্পদের প্রকাশে আপন ব্যক্তিপুরুষেরই প্রকাশ।
সাহিত্য সমালোচনার বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি শ্রদ্ধেয় কিনা তা বিচারযোগ্য। বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপাদান অংশগুলির মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে, ‘সাহিত্য সমগ্রকে সমগ্র দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে।’ মানুষের জীবনে নানান প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু প্রবৃত্তিসমূহকে ছিন্ন করে দেখলে মানুষের পরিচয় পাওয়া যাবে না। সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় অভাবনীয় যোগসাধনের দ্বারাই চরিত্রের বিকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের অভিমত সাহিত্যের বিচার সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়।
এলিয়ট তাঁর ‘The Frontiers of Criticism’ প্রবন্ধে সমালোচকের কর্তব্য সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি পাঠকবর্গকে উপলব্ধি ও আনন্দ সম্ভোগে সহায়তা করবেন। কবি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর সমাজ পরিবেশ, যুগের ভাবধারা, ভাষার অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করলে আমাদের ঐতিহাসিক তথ্যজিজ্ঞাসা সার্থক হয় বটে—কিন্তু কাব্য রসাস্বাদনে এই জ্ঞান সহায়তা করে না। স্যাফো যে দূর অতীতে ওড রচনা করেছিলেন, তাঁর কবিতা পাঠে সেই অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে পারলে আমাদের সার্থকতা ঘটে। সমালোচক সেই অভিজ্ঞতা গ্রহণের জন্য পথ প্রস্তুত করবেন। কিন্তু রসাস্বাদন পাঠকের চিত্ত বৃত্তির উপর নির্ভর করে। সমালোচক উপলব্ধি ও আনন্দ সম্ভোগে সহায়তা করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বিপদ এই যে, উপলব্ধি অতিকৃত ব্যাখ্যায় নতুন ভাষ্য রচনা করতে পারে এবং আনন্দ নিতান্ত উপভোগে পরিণত হতে পারে।
ব্যাখ্যামূলক সমালোচনার প্রধান ত্রুটি হল যে, সেখানে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা বেশী থাকে। মানসিক সংস্কারের কারণে সমালোচক কোন কাব্য অথবা উপন্যাসকে ব্যাখ্যা করতে পারেন। স্বদেশপ্রীতি তাঁর দেশের কোন সৃষ্টি বা রচনাকে হয়ত যথার্থভাবে বিচার না করে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে উৎসাহিত করবে। যেমন তরুণ রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাসের ‘শকুন্তলা’ নাটককে শেকসপীয়রের কালজয়ী সৃষ্টির উপরে স্থান দিয়েছিলেন। তাই বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বলা যাবে। এই প্রসঙ্গে স্কট জেমসের মূল্যবান অভিমতের উল্লেখ করে আমাদের আলোচনা শেষ হবে—‘‘The scientific judgement must step in; where upon the artist in the critic is displaced by the scientist, equipped with a bristling array of arguements to show why this poem, play or novel deserves admiration or the reverse.’’


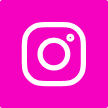



Leave a Reply