‘সাহিত্যের বিচারক’ প্রবন্ধের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।
- সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে।
- যেমনটি ঠিক তেমনটি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে।
- জগতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কারখানা সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি। ‘সাহিত্যের বিচারক’ প্রবন্ধ অবলম্বনে মন্তব্য তিনটি আলোচনা কর।
সাহিত্য প্রকতির আরশি কিনা দার্শনিক প্লেটো কর্তৃক সর্বপ্রথম উত্থাপিত এই প্রশ্নটি অত্যন্ত প্রাচীন। তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য মনীষী অ্যারিস্টটল এই প্রশ্নের উত্তর দেন। তার পরেও প্রশ্নটি নানাভাবে বিভিন্ন যুগে উত্থাপিত হয়েছে। প্লেটো মূলতঃ দার্শনিক হলেও তাঁর সংবেদনশীল কবি মন ছিল এবং তিনি তাঁর নিজের বক্তব্য ও রচনাকে বিভিন্ন কবির রচনার সাহায্যে সমৃদ্ধ করতেন। কবিরা যে কাব্য রচনা করেন তার মূলে আছে দৈবী প্রেরণা। যতক্ষণ এই প্রেরণা তাঁদের মধ্যে না আসে, ততক্ষণ অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের পক্ষে কোন কিছু রচনা সম্ভব নয়। কবি নাগরিক জীবনের উৎকর্ষের দিকে বেশী আগ্রহী ছিলেন বলে, কল্পনা-সমৃদ্ধ কাব্যকে সত্যোপলব্ধির জন্য প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। সাহিত্য ও অন্য ললিতকলাসমূহের মূল্য নাগরিক জীবন পরিবর্ধনের দিক থেকে তিনি নিরূপণ করেছেন। প্লেটোর মত কবি বা শিল্পী বাস্তবের বহিরঙ্গ রূপে অনুকরণ করেন। যা পরিদৃশ্যমান তা নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তনের পশ্চাতে আছে অপরিবর্তনীয় সত্য ও সৌন্দর্য। প্লেটো মনে করেন, এই পৃথিবী ভগবানের মনের ছায়া এবং কবিগণ এই ছায়াকে কাব্যে অনুকরণ করে থাকেন— ‘‘His work therefore is no more than an imitation of an imitaton.’’ কবি যুগের কাছে আবেদন না করে অন্তরের আবেগকে উদ্দীপিত করেন। এর ফলে মানুষের অসংযত প্রবৃত্তি সমূহ উদ্দাম হয়ে ওঠে। বাস্তব থেকে কবি যা গ্রহণ করেন, তার মধ্যে তিনি তাঁর ভাব ও ভাবনাকে সংযুক্ত করেন। বাস্তব সত্যের মৌল বিষয় তিনি প্রকাশ করেন। সুতরাং বাস্তবে যা অসংলগ্ন বিপর্যস্ত ও পারম্পর্য বিচ্যুত তাকে কবিও শিল্পী কল্পনার গৌরবে সমৃদ্ধ করে ঐক্য ও সংহতি দান করেন। অবশ্য কাব্য ও ললিতকলা থেকে যা উদ্দেশ্যমূলক রচনা তা স্বতই বাদ পড়বে। কারণ তা শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে, কোন কিছু প্রচারের জন্য রচিত নয়। কিন্তু যা খাটি কাব্য ও ললিতকলা তা অহৈতুকী আনন্দের সৃষ্টি। প্লেটোর সময়ে গ্রীকগণ হোমসরের যুগের কবিগণকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকরূপে মনে করতেন বলে তাঁর এই সমালোচনা।
রবীন্দ্রনাথও আলোচ্য প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। আমরা আমাদের আনন্দ বা শোক যখন প্রকাশ করি তখন সঙ্গতির সীমা অতিক্রম করি। যা একান্তরূপে আমাদের নিজস্ব সেখানে আমাদের প্রকাশ স্বাভাবিক সংযম রক্ষা করে। কিন্তু আমাদের যে অংশ অপরের কাছে ঘোষণা, তা আনন্দই হোক আর শোকই হোক, তা কিছুটা অতিকৃত হয়। কিন্তু অতিকৃত হলেও তাকে অস্বাভাবিক বলা যাবে না। জননীর পুত্রশোকের দুটি অংশ আছে। একটি তাঁর আপন হৃদয়ের গভীর বেদনা, অপরটি হল অন্যের কাছে পুত্রশোকের গৌরব প্রকাশ। অপরের কাছে শোক প্রকাশ করতে হলে তা প্রমাণের প্রয়োজন হয়। জননী তাঁর শোকের প্রবলতার দ্বারা পুত্রবিচ্ছেদ হেতু ক্ষতির প্রাচুর্য সকলকে জানান। তা পুত্রের মৃত্যুকে গৌরবান্বিত করার এক স্বাভাবিক প্রয়াস। যে প্রচণ্ড বিচ্ছেদে জননীহৃদয় ক্ষতবিক্ষত, সেই দুঃখ পৃথিবী গ্রহণ করবে না, স্বাভাবিক নিয়মে প্রাত্যহিকের বৃত্তে সে আবর্তিত হবে, শোকাতুরা জননী এই অবজ্ঞাকে গ্রহণ করতে পারেন না। সুতরাং তাঁর বিলাপ হৃদয়ের মমান্তিক দুঃখকে ঘোষণা করে। একের হৃদয়বেদনা যত বেশি অন্যের হৃদয় আলোড়িত করবে, ততই তার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন লোকের জীবনে হৃদয়ের অনুভূতি সঞ্চারিত না হলে, সত্য না হয়ে উঠলে, তার কোন সার্থকতা নেই। একের অনুভূতি অপরের মনে যখন গৃহীত হয়, তখন তাতে বিশেষ সান্ত্বনা ও সুখ থাকে।
বাস্তব জীবনে পুত্রহারা জননীর বিলাপ শোক পরিবেশে প্রত্যক্ষ গোচর। কিন্তু সেই সত্যকে সাহিত্যে পরিস্ফুট করতে হলে পরিবেশ রচনা করে, বর্ণনার সাহায্যে, ভাষার ব্যঞ্জনায়, অর্থবহ নানা ইংগিতে শোকের ব্যাপারকে সত্য করে তুলতে হয়। বাইরের দিক থেকে দেখলে একে কৃত্রিম বলে মনে হয়। কিন্তু অন্তর এই সত্যতাকে পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে থাকে। তাই অ্যারিস্টটল সাহিত্যের সত্যকে সেরা সত্য বলেছেন। ইতিহাসের সত্য সাধারণ সত্য, খণ্ডিত ও অকৃতার্থ, কিন্তু সাহিত্যের সত্য সার্থক সত্য।
পৃথিবীতে সমস্ত মানুষ আমাদের কাছে স্বল্প-পরিচিত। আমাদের পরমাত্মীয়ও তাঁর সমগ্রটি নিয়ে আমাদের কাছে পরিচিত নন। তাঁর জীবনের সামান্য অংশ আমরা দেখতে পাই। ফাঁকটুকু আমরা কল্পনায় ভরে তুলে সার্থক ছবি গড়ে তুলি। বাস্তবে যাঁর পরিচয় নানা তুচ্ছতা ও অসঙ্গতিতে ভরা, সাহিত্যে তাঁর জীবনের সার্থক প্রকাশ দেখে আমরা আনন্দিত হই। সাহিত্য যা জানায় তা সম্পূর্ণ করে জানায়। অবান্তরকে বাদ দিয়ে, শূন্যকে পূরণ করে, স্থায়ীকে রক্ষা করে, যা বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত তাহা সংহত করে সাহিত্য ভাবগত ঐক্য রচনা করে।
সাহিত্য মানব-জীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে, এবং তা গ্রহণ করে সাহিত্য স্রষ্টার মন। কিন্তু এই মনের অপর একটি অংশ বা সত্তা হল, বিশ্বমানব মন তা থেকে গ্রহণ-বর্জন করে কল্পনায় ও অনুভূতিতে তা পরিপূর্ণ করে প্রকাশ করে। মন সাধারণত প্রকৃতির মধ্য হইতে সংগ্রহ করে, সাহিত্য মনের মধ্য হইতে সঞ্চয় করে। এই মনের জিনিষকে সৃজনী প্রতিভায় নতুন রূপে গড়ে তোলা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাস্তব জগৎ ও সাহিত্য সৃষ্টি, এর মধ্যে মন ও বিশ্বমানব মনরূপ দুটি স্তর আছে। আমাদের অন্তরে দুটি অংশের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। একটি হল আমার নিজস্ব ও অপরটি মানবত্ব। উভয়ের মধ্যে মিল আছে ও ভাব বিনিময় ঘটে থাকে। এই দুয়ের দুর্ভেদ্য ব্যবধান রচনা করা হলে তবে তা আত্মার পক্ষে মহতী বিনষ্টি স্বরূপ। লেখক তার কল্পনার মাধ্যমে এই দুয়ের মধ্যে যোগসাধন করে থাকেন। সাহিত্য স্রষ্টার যে মানবত্ব তাই সৃষ্টি করে থাকে। সে লেখকের নিজত্বকে আপন করে, যা ক্ষণিক তাকে চিরন্তন মহিমা দেয় ও খণ্ডকে সম্পূর্ণতা দান করে থাকে। জগতের উপরে মনের কারখানা বসেছে। এই জগৎ হল সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান ও উৎস। মন এখান থেকেই উপকরণ সংগ্রহ করে থাকে। আবার বিশ্বমন তার কাছে থেকে নির্বাচন করে। সুতরাং সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।
কোন শিল্পসৃষ্টি বাস্তবের অনুকরণে হয় না। সর্বক্ষেত্রে বাস্তবের উপরে শিল্পীমনের ভাব ও ভাবনা প্রতিফলিত হয়ে তার রূপান্তর সাধন করে থাকে। শিল্পী বাস্তব জীবনের ন্যায় অথচ তা থেকে মহত্তর সার্থক ও সুসম্পূর্ণ জীবন সৃষ্টি করে তোলেন। বাস্তবের একান্ত অনুরূপ তাঁর সৃষ্টি হলে তাতে তাঁর শিল্পীসত্তা তৃপ্ত হবে না, পাঠকবর্গও তা গ্রহণ করবে না। কারণ প্লেটোর মতে তিনি গড়ে তোলেন—‘‘a weak imitation of phantoms, appearances, unsubstantial images. He creates only a copy of copy.’’ কাজেই জীবনের প্রতিলিপি গড়ে তোলা শিল্পীর আদর্শ হতে পারে না। বর্তমান কালে যাকে বাস্তব সাহিত্য বলে আখ্যা দেওয়া হয় তাও বাস্তবের প্রতিভাস মাত্র। প্রলেতারিয়ান সাহিত্য বাস্তব সাহিত্য। এই বাস্তবের অর্থ হল, জীবনে যে ঘটনাগুলি ঘটছে তাদের সম্ভাব্য পরিণতির রূপ অঙ্কিত করা। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও অনুকরণের কোন প্রশ্ন আসে না। সাহিত্য-স্রষ্টা ক্ল্যাসিক অথবা রোমান্টিক যে কোন রীতি অনুসরণ করুন না কেন, কোন ক্ষেত্রে তা অনুকরণ প্রিয়তার ব্যর্থতাকে প্রকাশ করে না। ক্ল্যাসিক রীতি বস্তুরূপকে প্রকাশ করে এবং রোমান্টিক রীতি বস্তুর স্বরূপকে পরিস্ফুট করে থাকে। উভয় রীতি জীবনাভিমুখীন।
চিত্র, ভাস্কর্য, অভিনয়, সংগীত ও নৃত্যকলা সবই কলাবিদ্যা। কিন্তু কোন কলাবিদ্যাই প্রকৃতির অনুকরণ নয়। জীবনকে মহত্তর করে নল সৃষ্টির প্রয়াস সর্বযুগেই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কাব্যই হোক বা চিত্র হোক উভয়ক্ষেত্রে শিল্পী আপন মনের ভাবকে বাইরে পরিস্ফুট করতে চান। অতএব কাব্য ও চিত্র হল মাধ্যম মাত্র। এই যে প্রকাশ তা শিল্পীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থেকে অপরের মনে সঞ্চারিত হয়। যারা মূর্তি রচনা করেছেন, তাঁরা জীবনকে সুসম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। অভিনয়ের মধ্যে অভিনেতা কখনো ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে, জীবন যাপনে যা সচরাচর পরিলক্ষিত হয় তা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়াস না করে, ভাবকে যথাযথরূপে অভিব্যক্ত করার চেষ্টা করেন। নৃত্যের ক্ষেত্রেও বাস্তবানুকরণের প্রয়াস থাকে না, তার অন্তর্নিহিত ভাবকে প্রকাশ করে দর্শকের রসলোক উদ্বুদ্ধ করে তোলা হয়। অথাৎ রূপ সৃষ্টি করা। ভাব যখন রূপের মধ্যে মূর্ত হয় তখন রসের উদ্বোধন ঘটে থাকে। অতএব রসসৃষ্টি কলাবিদ্যার আসল লক্ষ্য। সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা জীবনের রসপরিচয়কে আস্বাদন করি। বাস্তব জীবনের ভাব, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যস্রষ্টা চিরকালের ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। এই বাস্তবের উপর তাঁর মানস-লোকের আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে তার রূপান্তর সাধন করে। এই রূপান্তরকে কখনও অনুকরণ বলা যাবে না। এ বিধাতার সৃষ্টির মত অহৈতুকী লীলা।


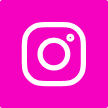



Leave a Reply