‘সাহিত্যের বিচারক’ প্রবন্ধের মূল ভাব নিজের ভাষায় লেখ।
- সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্তা। ‘সাহিত্যের বিচাক’ প্রবন্ধ অবলম্বনে মন্তব্যটি আলোচনা কর।
সাহিত্যের বিচারক প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— ‘‘সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্তা।’’ কবি মনে করেন যে, প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্রাকৃত জগতকে কবি-সাহিত্যিক তার মনের মধ্যে গ্রহণ করে তাকে আপন মনের জারক রসে জারিত করে একটা নতুন জগৎসৃষ্টি করেন এবং কাব্যে-সাহিত্যে বা যে-কোন কলাকৃতিতে তারই রূপায়ণ ঘটে। কবির দৃষ্ট প্রত্যক্ষ জগৎ যখন সাহিত্যে রূপায়িত হয়, তখন পাঠকের কাছে তা অপ্রত্যক্ষ জগতের চিত্র, অতএব দূরবর্তী বলে মনে হয়। এছাড়াও বাস্তব জগতে যে সমস্ত অপূর্ণতা, খণ্ডতা কিংবা শূন্যতা থাকে, তা পাঠকের কাছে পীড়াদায়ক হতে পারে মনে করে কবি প্রাকৃত জগতের চিত্রকে আরও অতিশায়িত করে, অবান্তর বর্জন করে এবং তার পূর্ণতা সাধন করে পাঠকের সামনে অর্থাৎ সাহিত্যে উপস্থাপিত করেন। অতএব প্রকৃতির সংগে সাহিত্যের একটা নিকট সম্বন্ধ থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে কবি-সাহিত্যিকের মন তাতে একটা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রকৃতিকে গ্রহণ করে মন এবং সেই মনই সৃষ্টি করে সাহিত্য, কিন্তু মনও প্রকৃতির আর্শি নয়, আবার সাহিত্যও নয় প্রকৃতির আর্শি। এদের পারস্পরিক সম্পর্কটিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— ‘‘মন প্রাকৃতিক জিনিসকে মানসিক করিয়া লয়, সাহিত্য সেই মানসিক জিনিসকে সাহিত্যিক করিয়া তোলে।’’
সাহিত্য প্রকৃতির আর্শি কিনা—এই প্রশ্নটি প্রথম উত্থাপন করেছিলেন বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো। পরবর্তীকালে তারই সুযোগ্য শিষ্য অ্যারিস্টটল প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছিলেন। প্লেটো মূলতঃ দার্শনিক হলেও তাঁর সংবেদনশীল কবি মন ছিল এবং তিনি তার নিজের বক্তব্য ও রচনাকে বিভিন্ন কবির রচনার সাহায্যে সমৃদ্ধ করতেন। কবিরা যে কাব্য রচনা করেন তার মূলে আছে দৈবী প্রেরণা। যতক্ষণ এই প্রেরণা তাঁদের মধ্যে না আসে, ততক্ষণ অনেক চেষ্টা করেও তাদের পক্ষে কোন কিছু রচনা সম্ভব নয়। কবি নাগরিক জীবনের উৎকর্যের দিকে বেশি আগ্রহী ছিলেন বলে, কল্পনা-সমৃদ্ধ কাব্যকে সত্যোপলব্ধির জন্য প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। সাহিত্য ও অন্য ললিতকলাসমূহের মূল্য নাগরিক জীবন পরিবর্ধনের দিক থেকে তিনি নিরূপণ করেছেন। প্লেটোর মত কবি বা শিল্পী বাস্তবের বহিরঙ্গরূপে অনুকরণ করেন। যা পরিদৃশ্যমান তা নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তনের পশ্চাতে আছে অপরিবর্তনীয় সত্য ও সৌন্দর্য। প্লেটো মনে করেন, এই পৃথিবী ভগবানের মনের ছায়া এবং কবিগণ এই ছায়াকে কাব্যে অনুকরণ করে থাকেন— ‘‘His work therefore is no more than an imitation of an imitation.’’ TO ACSTS কাছে আবেদন না করে অন্তরের আবেগকে উদ্দীপিত করেন। এর ফলে মানুষের অসংযত প্রবৃত্তি সমূহ উদ্দাম হয়ে ওঠে। বাস্তব থেকে কবি যা গ্রহণ করেন, তার মধ্যে তিনি তার ভাব ও ভাবনাকে সংযুক্ত করেন। বাস্তব সত্যের মৌল বিষয় তিনি প্রকাশ করেন। সুতরাং বাস্তবে যা অসংলগ্ন বিপর্যস্ত ও পারম্পর্য বিচ্যুত তাকে কবিও শিল্পী কল্পনার গৌরবে সমৃদ্ধ করে ঐক্য ও সংহতি দান করেন। অবশ্য কাব্য ও ললিত কলা থেকে যা উদ্দেশ্যমূলক রচনা তা স্বতই বাদ পড়বে। কারণ তা শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে, কোন কিছু প্রচারের জন্য রচিত নয়। কিন্তু খাটি কাব্য ও ললিতকলা তা অহৈতুকী আনন্দের সৃষ্টি। প্লেটোর সময়ে গ্রীকগণ হোমারের যুগের কবিগণকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকরূপে মনে করতেন বলে তাঁর এই সমালোচনা।
‘সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্তা’—রবীন্দ্রনাথের কারণটি যথাযথভাবে বিশ্লেষিত হওয়া জরুরী। কবি আলোচ্য প্রবন্ধেই মন প্রকৃতিকে গ্রহণ করে এবং সাহিত্যসৃষ্টি করে বলে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন–তার সংগেই উদ্ধৃত অভিমতটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। এই যে মন, প্রকৃতি ও সাহিত্যসৃষ্টি—এই সবের মধ্যে ঐক্য থাকলেও পার্থক্য আছে। তা হল—মন প্রকৃতিকে গ্রহণ করে নিজের প্রয়োজনে আর সাহিত্য যা গড়ে তোলে তা সকলকে আনন্দদানের জন্য। নিজের জন্য যা করা হয়, তা সাধারণ হলেও চলে, কিন্তু অন্য সকলের জন্য যা করা দরকার তাকে সম্পূর্ণ হতে হবে—এমনভাবে যা সকলের দৃষ্টিতে আসে। প্রকৃতি থেকে মন সংগ্রহ করে, সাহিত্য মন থেকে সঞ্চয় করে। এখন মনের জিনিসকে যদি বাইরে প্রকাশ করতে হয়, তখন তাকে এমন রূপ দিতে হয়, যাতে তা অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। যথার্থভাবে সাহিত্য কবিমানসের নবসৃষ্টি এবং এর জন্য প্রয়োজন উৎকৃষ্ট সৃষ্টি প্রতিভার। কবি বা শিল্পী কীভাবে সৃষ্টি করবেন এ বিষয়ে সমালোচক বলেছেন— ‘‘Artist makes his state of mind clear to others, when it carries the thought-content expressed over the thresh-hold of somebody else’s consciousness. Expression for the artist is communication.’’ এই যে প্রকাশ করার ক্ষমতা তার উদ্দেশ্য হল শিল্পীমানসের ভাব ও অভিজ্ঞতা অপরের মনে সঞ্চারিত করে দেওয়া। শিল্পী তার অনুভূতিকে বাইরে রূপসৃষ্টির মাধ্যমে রসাস্বাদনের উপযোগী করে তোলেন। কবি তার কবিতায় বিশেষ রূপকল্পের মধ্য দিয়ে তা সার্থক করেন, আর যিনি চিত্রকর তিনি চিত্রে প্রকাশ করে থাকেন। কাব্যের সংগে চিত্তের এখানে সাদৃশ্য যে, উভয়ে বাস্তবের অনুকরণ না করে শিল্পীর মানস জগতের অনুভূতি ও চিন্তাকে বাস্তব জগতের উপরে প্রতিফলিত করে। চিত্রে যখন একটি মুহূর্তের পরিচয় আমরা পাই, তখন তা ফটোগ্রাফের মত একটি বিশেষ ক্ষণকে আবদ্ধ করে না, গতিকে আভাসিত করে। কাব্যে ও চিত্রে মানুষের যে পরিচয় থাকে, তার সমগ্র রূপের ব্যঞ্জনা প্রকাশের দিকে শিল্পীর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। তথাপি প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলা যায় যে, সংগীত অথবা চিত্রকলার সৌন্দর্য বিদেশীগণও উপভোগ করতে পারেন। কিন্তু কবিতার সৌন্দর্য যেন বিশেষ ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ। কবি টি.এস. এলিয়ট বলেছেন— “no art is more stubbornly national than poetry.”
সাহিত্যিক তার কল্পনাকে, তাঁর সুখ-দুঃখকে প্রকাশ করেন সাহিত্যে, সেই কল্পনা বা সুখ-দুঃখ কোন এক বিশেষ মুহূর্তকে অবলম্বন করে গড়ে উঠলেও সাহিত্যে যখন তা রূপায়িত হয় তখন সাহিত্যিক তাকে শাশ্বত কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন আর তা বর্তমানকালে সীমাবদ্ধ থাকে না। কোন এক বিশেষ মুহূর্ত বা খণ্ডকাল থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে তাকে শাশ্বত কালের জন্য গড়ে তুলতে হলে সুবিশাল নিরবধি কালসীমার সংগে সামঞ্জস্য বিধান করে নিতে হয়। ক্ষণকালের কিংবা বর্তমানের মাপকাঠিতে তাই কাজ চলে না। কাজেই উৎকৃষ্ট সাহিত্য কখনো দেশকালে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, বর্তমান কাল কিংবা সংকীর্ণ সংসারের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করলে— সেটাই উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সঙ্গে তার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে কেবল উৎকৃষ্ট সাহিত্য। সাহিত্যে কাজকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— ‘‘অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।’’
‘‘সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশ মাত্র, কিন্তু তার পরিণাম হচ্ছে ইন্দ্রিয়মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ।’’ যা কবির নিতান্ত একলার বস্তু, যে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা তিনি উপলব্ধি করেছেন, তা আপন হৃদয়ে অবরুদ্ধ না রেখে সকলের জন্য তিনি প্রকাশ করে থাকেন। যা ক্ষণকালের জিনিস তাকে কবি বা সাহিত্যিক চিরকালের সামগ্রী করে তোলেন। সাহিত্যস্রষ্টা যা রচনা করেন তা নিছক বর্তমান কালের জন্য নয়। চিরকালের মানবসমাজকে লক্ষ করেই তিনি সৃষ্টি করেন। বিষয়টি কবি এলিয়ট অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন— “What matters is that there should always be at least a small audience for him in every generation.’’ কাল নিরবধি পৃথিবীও বিপুলা, ভবিষ্যতে তাঁর সৃষ্টি ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে শিক্ষিত জনমানবের চিত্তে আবেদন সৃষ্টি করবে। যে নাগরিক আবহাওয়ায় ভারতচন্দ্রের কবিতা শব্দ, সংগীত ও ছন্দের গুণে লোকমনে জনপ্রিয় হয়েছিল, কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই জনপ্রিয়তা হারিয়ে যায়। অতএব ‘সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্তা’।


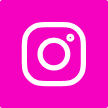



Leave a Reply