বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্যের বিকাশ ও বিবর্তনের পরিচয় দাও।
বাংলাদেশের অনুবাদ
অনুবাদ দুরূহ কর্ম। বিভাগ-পূর্ব সময়ে বড় কবি-সাহিত্যিকদের (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা বিষ্ণু দের মতো) বিচিত্র বিষয়ে অনুবাদে হতে দেখা যায়। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এই প্রবণতা অনেক পরে তৈরি হয়। কারণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রুচিজ্ঞানের অভাব। বিভাগ-পরবর্তী সময়ের সাহিত্যে যাদের নেতৃত্ব আমরা লক্ষ করি তাদের লেখক হয়ে ওঠা, সাহিত্যরুচি তৈরি হওয়া বলা চলে একেবারেই তাৎক্ষণিক এবং আনকোরা পর্যায়ের। এ পর্যন্ত তার বয়স পঞ্চাশ কিংবা কিছু অধিক। তবুও আধুনিক বিশ্বে পুজির নানামুখি সঞ্চালন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপ্লব, অবাধ তথ্য প্রবাহ সবকিছু মিলিয়ে কেউই আর নিশ্চল নয়। সেটা বাধ্য-অবাধ্য যেমন করেই হোক। সাহিত্য-সংস্কৃতিও এসবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন সেভাবেই এগুচ্ছে, বিবেচিতও হচ্ছে। বাংলাদেশে পূর্বের অভিজ্ঞতা এখন অতীত। অনেকেই অনুবাদে অনুরক্ত। সাফল্য তো পেয়েছেনই। আমাদের অর্ধ-শতাব্দীর বেশি সময়ের সাহিত্যে এখন আন্তর্জাতিক যোগাযোগও বিপুল। এটা অনেকের কাছেই এখন সহজ ও অনিবার্যও। যদি ধরি, ষাটের দশকে অনুবাদ কতোটা দুরূহ আর এখন কতোটা সহজসাধ্য! প্রচারমুখি বিশ্বে এ তাণ্ডব কতোটা জটিল, বহুমাত্রিক? জিল্লুর রহমান সিদ্দিক স্বাধীনতার অনতি পরে শেক্সপীয়রের সনেট অনুবাদ করতে গিয়ে লেখেন—‘‘অসুবিধে আছে শেকসপীয়র সনেটের তর্জমায়। ইংরেজীতে সবকথা তিনি সহজে বলেছেন, প্রায় কথ্যভাষার বাগধারায়, বাংলায় প্রায়ই তার কোন প্রতিরূপ নেই…বাংলা রূপান্তরের মধ্যে কৃত্রিমতা চলে আসে।’’ এটা সবকালের অনুবাদেরই চিরকালীন সমস্যা। তবুও অনুবাদ আছে। ভাষার বিকাশ ও বৈচিত্র্যের জন্যে, আবিষ্কারের ‘বহুভাষী মানবজাতির অন্তর্গত ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্যে অনুবাদ বিরাজমান। বাংলাদেশে এটি অনেক পরিমাণে সমৃদ্ধ। ব্যবসায়িক স্বার্থে, প্রচারের বাজারের কারণে অনুবাদের মান যে নিম্নগামি নয় তা-ও নয়। কিন্তু সরদার ফজলুল করিমের প্লেটোর রিপাবলিক কিংবা কবীর চৌধুরীর ‘বেকেট-বীক্ষা’র গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। অনেক উচ্চ এবং সমৃদ্ধ। শুধু এ সময়েই কেন পরাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ-পূর্বকালে মুনীর চৌধুরীর শেক্সপীয়ার-শ’ অনুবাদকর্ম কিংবা আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ‘ইলিয়াড’-এর অনুবাদ অমোচনীয়, ধ্রুপদী বললে ভুল হয় না। তবে অনুবাদের সমস্যা অনেক। ভাবগত, ভাষাগত তো বটেই। আর কবিতার অনুবাদ কি কখনও সম্ভব? কবি ব্যক্তিত্ব থাকলে সেটি আরও দুরূহ, ক্রমশ দুরূহতরও বটে। যা হোক, তবুও বাংলাদেশের সাহিত্যে অনুবাদ একটি নতুন ধারা এবং তা সচল ও বহমান ধারা। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের নাটকে অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে অনেক এবং তার সফল মঞ্চায়নও সম্ভব হয়েছে। নবতর প্রজন্মও এ পথে হয়েছেন অনুগামী। এখানে বিভাগ-পরবর্তী সময় থেকে অদ্যাবধি অনুবাদকদের একটি তালিকা প্রদান করার চেষ্টা হয়েছে। যথাসাধ্য তাদের কৃতকর্মের দৃষ্টিচেতনাও এখানে বিশ্লেষিত। তবে সীমাবদ্ধতা যে নেই তা বলা যাবে। আমাদের এখানে মৌলিক অনুবাদ ও অনূদিত ব্যক্তিরাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। অনুদিত নাটকের কৃতীদের নাটক অধ্যায়েই রাখা হয়েছে।
আকবরউদ্দীন
বিভাগোত্তর বাংলাদেশে দস্তয়ভস্কির ‘অপরাধ ও শাস্তি’, টলস্টয়ের ‘হাজী মুরাদ’, হেনরী এডামসের আত্মজীবনী, হেনরী জেমস এডামসে ‘শিক্ষাবিষয়ক আত্মচরিত’ (১ম ও ২য় খণ্ড) আকবরউদ্দীনের (১৮৯৫-১৯৭৮) গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ। রুশ সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখকদের এ অনুবাদ যেমন তীক্ষ্নধী তেমনি সাবলীল। তাঁর অনুবাদ অনেকটা মূলানুগ, আকর্ষণীয়। উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টি, কাহিনি ও ঘটনার পুনর্বিন্যাস, পরিবেশের সেটিংস যথাযথ। টলস্টয় কিংবা দস্তয়ভস্কির জীবনদৃষ্টি শিল্পমান অনুবাদে রক্ষা করা দুরূহ হলেও অনেকটা সফল হয়েছেন আকবরউদ্দীন। অনুবাদ সুপাঠ্য এবং আস্বাদনযোগ্য।
আনিসুজ্জামান
অসকার ওয়াইল্ড-এর ‘আদর্শ স্বামী’ (১৯৮২)-র অনুবাদ করেছেন আনিসুজ্জামান (জন্ম. ১৯৩৭)। অনুবাদে তাঁর চর্চা কম হলেও এক্ষেত্রে যথেষ্ট মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। অত্যন্ত সংযমও পরিলক্ষিত। সবচেয়ে বড় পরিবেশগুণ তিনি যথাযথ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন।
আবদার রশীদ
আবদার রশীদ (জন্ম. ১৯১৮) বাংলাদেশের সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি রঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক রসবোধ সম্পন্ন লেখক। জাঁ পল সাঁত্রের ‘ছায়াহীন কায়া’ (১৯৭৭), ‘ইলেকট্রা’ (১৯৭৯), ‘অ্যান্টিগনি’ (১৯৭৭) ইত্যাদি অনুবাদে তিনি গুরুত্বপূর্ণ। সাঁত্র নিয়ে যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি অর্জন করেছেন। অনুবাদে তিনি সৎ এবং পরিশ্রমী। চেতনাগত পরিশুদ্ধির চাপ আছে তাঁর কর্মকাণ্ডে। আবদার রশীদের সাঁত্র পঠন বেশ আকর্ষণীয়। বাংলাদেশের সাহিত্যে এমন অনুবাদ পাঠকের দৃষ্টিচেতনা ও রুচিকে আধুনিক মনস্ক করে তোলে।
আবদুল গনি হাজারী
‘স্বর্ণগর্ধভ’ (১৯৬৫), ‘ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষা’ (১ম ও ২য় খণ্ড)-এর নির্ভরযোগ্য অনুবাদ করেছেন। এটিই একমাত্র গ্রন্থ যেটি আমাদের নিকট ফ্রয়েডকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ করে দিয়েছে। তিনি ফ্রয়েড কর্তৃক অনুমোদিত জোয়ান রিভিয়ারের ইংরেজি অনুবাদ থেকে এটি গ্রহণ করেছেন। স্পষ্ট ও স্বচ্ছ দৃষ্টিচেতনায় আবদুল গনি হাজারী (১৯২৫-১৯৭৬) প্রচণ্ড দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। এতে তাঁর ভাষা কবিত্বপূর্ণ নয়, বুদ্ধিদীপ্ত ও মনন চেতনায় ঋদ্ধ। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত আবদুল গনি হাজারী রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডে এটি গ্রথিত রয়েছে। লুসিয়াস এপুলিয়াসের গোল্ডেন এ্যাস-এর অনুবাদ ‘স্বর্ণগর্দভ’। আসলে এটি লুসিয়াসের রূপান্তর (metamorphosis)-এর জনপ্রিয় নাম স্বর্ণগর্দভ। ইন্দ্রজাল সম্পর্কে অদম্য কৌতূহলের ফলে করিন্থের এক অভিজাত বংশের জনৈক লুসিয়াস কীভাবে একটি গাধায় রূপান্তরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি পেরিয়ে দেবী আইসিসের কৃপায় আবার নবরূপ ফিরে পেল’—তারই আখ্যান ‘স্বর্ণগর্দভ’। সমকালীন রোম সমাজের আলেখ্য এটি মৌলিক রচনার মতোই অনুবাদ করেছেন আবদুল গনি হাজারী। উল্লিখিত দুটো রচনার ক্ষেত্রেই তিনি মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের (জন্ম. ১৯৪০) অনুবাদ ‘শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস’ (১৯৯২), ‘দ্যাগ হ্যামারশোল্ড’ (১৯৬৯)। প্রমিথিউসের ভাবচেতনার স্বরূপ সাবলীল গদ্যে রচিত হয়েছে। তবে অনুবাদে তাঁর বেশি সাফল্য আসেনি। তবে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের অনুবাদ সুপাঠ্য; নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও ভঙ্গির কারণেই। এক ধরনের চেতনাগত বক্তব্যই তিনি এর ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সেটি তার স্বাতন্ত্র্য, অবশ্য অনুবাদের মতো ফর্মে এক ধরনের প্রাবন্ধিক উচ্চারণই তিনি করেন। প্রমিথিউস কীরূপে সাফল্য ও একালেও ফলদায়ক তার মূল্যায়ন একটি বক্তব্যরূপে প্রতিষ্ঠা পায়— এর ব্যত্যয় ঘটে না তার লেখায়।
আবদুস সেলিম
বোর্টল্ড ব্রেশট এর ‘গ্যালিলিও’ (১৯৭৮)-র অনুবাদ করেছেন আবদুস সেলিম। এটি এক অর্থে গ্যালিলিওর চেতনাগত দিক, অন্যদিকে ব্রেন্ট-এর নাট্যফর্মকে বজায় রেখে পাঠককে পরিতৃপ্তি দেওয়া। এসব দুরূহ কর্মপ্রয়াস। ব্রেষ্ট আধুনিক নাট্যকার হিসেবে এখন পৃথিবী শ্রেষ্ঠ। তাঁর নাট্যফর্ম গুরুত্বপূর্ণ; এমন বিষয় অনুবাদে বহাল রাখা নিশ্চয়ই যোগ্যতার ব্যাপার। আবদুস সেলিমের গ্যালিলিও সুপাঠ্যও বটে। যাবতীয় অন্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানচেতনার জয় পাঠক মহলের জন্য একটি অনিবার্য উপযোগ।
আবুল কালাম শামসুদ্দীন
অনুবাদের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান। তুর্গেনিভের The Virgin Soil-এর অনুবাদ অনাবাদী জমি (১৯৩৮), তুর্গেনিভের তিনটি গল্পের অনুবাদ ত্রিস্রোতা (১৯৩৯), তুর্গেনিভের Torrents of Spring-এর ছায়া অবলম্বনে রচিত খরতরঙ্গ (১৯৫৩) এবং হোমারের ইলিয়ড (১৯৬৭)র অনুবাদ করেছেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮)। চমৎকার অনুবাদে তিনি এসব গ্রন্থের চরিত্রকে পৌঁছে দিয়েছেন কাল-ভূগোল সীমা অতিক্রম করে সর্বদৈশিক ও কালিক আবর্তে। গদ্যভঙ্গি আড়ষ্ট নয়, কথাকারের ভূমিকায় তিনি হয়ে উঠেছেন নিজস্ব। শিল্পের ভাব ও সৌন্দর্য ভাষান্তরিত করা দুরূহ কাজ। কিন্তু অনুবাদক এ কঠিন কাজকে সহজ করেছেন, বজায় রেখেছেন এসব লেখকদের ধ্রুপদী ভাবমূর্তি। মার্কিন ঐতিহাসিক হ্যরল্ড ল্যাম্বর দিগ্বিজয়ী তাইমুর (১৯৬৫) গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন লেখক।
আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন
অনুবাদক ও প্রবন্ধকার। ‘আরবী ছোটগল্প’ (১৩৭১), ‘তুহাফুতুল ফলাসিফা’ (১৩৭১) প্রভৃতি গ্রন্থের সফল অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন। অনুবাদের ভেতর দিয়ে অনেক বিদেশি সাহিত্যের বিষয়কে তিনি পরিচয় করিয়েছেন।
আবু জাফর শামসুদ্দীন
কথাশিল্পী আবু জাফর শামসুদ্দীনের (১৯১১-১৯৮৯) ‘শিল্পীর সাধনা’ (১৯৬৭) অসম্ভব সুন্দর রচনা। শিল্পীর দৃষ্টিচেতনা, ভাষা, দার্শনিক চেতনা একটা সূক্ষ্মতার সমগ্রতা রচনা করে যেখানে নান্দনিক শুদ্ধতা অনুমান করা যায়। লেখক বাস্তবানুগ শিল্পবুদ্ধিতে বিশ্বাসী। চেতনা আছে দ্বান্দ্বিক সত্তার আবর্ত—যেটি এই গ্রন্থটিকে উচ্চতা দান করেছে। এছাড়া তাঁর অন্য অনুবাদ ‘খাপছাড়া’ (১৯৬৮), ‘পার্লার্কের সেরা গল্প’ (১৯৬৮)। বিভাগোত্তর কালচেতনার সমৃদ্ধির স্বরূপ পাওয়া যায় তাঁর অনুবাদকর্মে।
আবু শাহরিয়ার
‘শেক্সপীয়রের হ্যামলেট: ডেনমার্কের রাজকুমার’ (১৯৭৯) ‘অ্যান্টনী ও ক্লিওপেট্রা’ (১৯৭৮), ইউজীন ইয়েনেস্কোর ‘তপ্ত বাতাসে দুজন’ (১৯৭৭) অনুবাদ করেছেন আবু শাহরিয়ার। বাংলাদেশে শেক্সপীয়ারের অনুবাদ নতুন নয়। আবু শাহরিয়ার ট্র্যাজেডি নাটক হ্যামলেটকে একটু ভিন্ন ভঙ্গিতে নিয়ে এসেছেন। এর জন্য পঠনের আলাদা স্বাদ মেলে এবং এটা নিশ্চিত এতে করে মঞ্চেও শেক্সপীয়ার অভিনয়ের একটা বৈচিত্র্য তৈরি হয়েছে। অনুবাদের পরিপ্রেক্ষিতটি যথাযথ বজায় রেখেছেন। নাট্যকার। ইউজীন ইয়নেস্কোর নাটক অনুবাদেও তিনি স্বাতন্ত্রের পরিচয় দিয়েছেন।
আলম খোরশেদ
অনুবাদের কাজে এ সময়ে প্রসিদ্ধি পেয়েছেন। অনুবাদের দক্ষতাও আছে। ‘যাদুবাস্তবতা গাথা: ল্যাতিন আমেরিকার গল্প’ ছাড়াও বেশ কিছু উপন্যাস ও গল্পের অনুবাদ করেছেন। তবে যত্নের ঘাটতি আছে। অনেক ক্ষেত্রেই দ্রুততা পরিলক্ষিত, এতে মূল লেখক অনুপস্থিত রয়ে যান। যেটা কাম্য নয়।
আলী আনোয়ার
হ্যারল্ড পিন্টারের নাটকের অনুবাদ ‘অনিকেত বেদনা’ (১৯৮৫)। আলী আনোয়ার (১৯৩৫-২০১৪) মনস্বী লেখক। নাটক বিষয়ে তার আছে। প্রচুর পাঠ-অভিজ্ঞতা। অনুবাদে তিনি প্রচণ্ডরূপে মূলানুগ এবং সৃজনশীল। হ্যারল্ড পিন্টার ছাড়াও ইবসেনের নাটক নিয়েও তিনি কাজ করেছেন। নাটকের আবহ এবং তাঁর আধুনিক দৃষ্টিচেতনার প্রযওগ সম্পর্কে তিনি নির্ভুল, নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী। ভাষা ও দৃষ্টিকোণ পরিচ্ছন্ন ও সাবলীল।
আলী আহমদ
কামিলো হোসে সেলা’র অনুবাদ ‘পাস্কুয়াল দুয়ার্তের পরিবার’, ডেরেক ওয়ালকোটের কাব্যনাট্য অবলম্বনে ‘স্বপ্নগিরি’, নগীব মাহফুজের অবলম্বনে ‘চোর ও সারমেয় সমাচার’, ইভান তুর্গেনিভের অনুবাদ ‘প্রথম প্রেম’, মার্কেস অবলম্বনে ‘বারো অভিযাত্রীর কাহিনী’ এবং ‘মেঘ ও অন্যান্য দানব’, ওয়ে কেনজাবুরোর অনুবাদ ‘শিকার ও অন্যান্য গল্প’ এবং নগীব মাহফুজের অনুবাদ ‘খোঁজ’। আলী আহমদ (জ. ১৯৪৮) দক্ষ অনুবাদক। এ কাজেই তিনি পরিপূর্ণ মনোযোগী। মূলত কথাসাহিত্যের অনুবাদে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের অনুবাদে তিনি সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। উপন্যাসের পরিকাঠামো নির্মাণ, কাহিনি কথনে তাঁর যথেষ্ট মেধার স্বাক্ষর আছে। আলঙ্কারিক উচ্চতা ও শিল্পগুণ বজায়ে তিনি অনেকটাই মূলানুগ ও পরিচ্ছন্ন। কখনোই আলী আহমেদ স্বীয় কল্পনাকে বা বুদ্ধিকে আরোপ করেন না অনুবাদের মধ্যে। বাংলাদেশের সাহিত্যে অনুবাদের ক্ষেত্রে নিজস্ব একটি ঘরানার জন্ম দিয়েছেন তিনি।
আসকার ইবনে শাইখ
থর্নটন ওয়াইল্ডার অবলম্বনে ‘যন্ত্রণার চাপ’ (১৯৭৮) অনুবাদ করেছেন আসকার ইবনে শাইখ (জন্ম. ১৯২৫)। ষাটের গুরুত্বপূর্ণ এ নাট্যকার মৌলিক নাটক লিখলেও অনুবাদেও আধুনিক চিন্তার সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। বিশ্বনাটকের গুরুত্বপূর্ণ এ ব্যক্তিকে তিনি যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। ব্যক্তিসমাজের অন্তশ্চাপ, তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, কী এবং কেন কিংবা ইত্যাকার এমনসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের সমাজজিজ্ঞাসার একরকম বাইরের বিষয়ই ছিল। আসকার ইবনে শাইখ অনুপ্রেরণাবশত এ কাজটি সম্পন্ন করেছেন এবং সফল হয়েছেন। মজার অনুবাদ ‘যন্ত্রণার চাপ’।
আহমদ ছফা
আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১) অনুবাদ করেছেন ‘তানিয়া’ (১৯৬৭), ‘ফাউস্ট’ (১৯৮৬), বার্ট্রান্ড রাসেলের ‘সংশয়ী রচনাবলী’। ফাউস্টের অনুবাদ খুব জটিল কর্ম। কাজী আবদুল ওদুদের পর তিনি এ কাজটি করেছেন। তাঁর এ অনুবাদ সুখপাঠ্য হলেও কাব্যমেজাজ একটু আড়ষ্ট। উচ্চমার্গের এ কবির জীবনচেতনা, দার্শনিক বুদ্ধি পরিবর্তিত ভাষায় বজায় রেখে করা কঠিন। তবুও ছফার অনুবাদই বেশি জনপ্রিয় এবং পাঠক গ্রহণযোগ্যতা বেশি। অন্যান্য অনুবাদেও বেশ মননশীলতার পরিচয় লক্ষণীয়।
কবীর চৌধুরী
কবীর চৌধুরী (১৯২৩-২০১১) অনুবাদের জগতে এক বিস্ময়। বাংলাদেশের সাহিত্যে তিনি এখন অনুবাদের প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত। সাহিত্যের সব শাখায় সমান তালে তিনি অনুবাদ করে চলেছেন। তাঁর কর্মপরিধি বিশাল। বাংলাদেশের অনুবাদে তাঁর তুল্য ব্যক্তিত্ব বিরল বললে কম বলা হয় না। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যকর্মের বাংলা অনুবাদ ‘চেখভের গল্প’ (১৯৬৯), ‘সমুদ্রের স্বাদ’ (১৯৭০), ‘গ্রেট গ্যাটসবি’ (১৯৭১), ‘দি গ্রেপস অব র্যাথ’ (১৯৮৯), ‘রূপান্তর’ (১৯৯০), ‘বেউলফ’ (১৯৮৫), ‘অল দি কিংস মেন’ (১৯৯২), ‘ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সী’ (১৯৯৪), ‘চুম্বন’ (২০০০), ‘কাফকার নির্বাচিত গল্প’ (২০০১), ‘ব্লবিয়ার্ড’ (২০০১), ‘প্রেম ও কলেরা’ (২০০২), ‘অরণ্যের গল্পমালা’ (২০০২), ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’ (২০০১), ‘ক্রনিকল অব এ ডেথ ফোরটোল্ড’ (২০০২), ‘ক্যথরিনা ব্লুমের হারানো সম্ভ্রম’ (২০০৩), ‘ডিনারপার্টি’ (২০০৩), ‘নেটিভসান’ (২০০৫), ‘হোর্হে বোরহেসের নির্বাচিত গল্প’ (২০০৬), ‘দুই নোবেল বিজয়ীর নির্বাচিত ছোটগল্প’ (২০০৬), ‘ব্ল্যাক বয়’ (২০০৬), ‘দি লেইট বুর্জোয়া ওয়াল্ড’ (২০০৬), ‘ন্যুড চিত্রকর্ম’ (২০০৬), ‘মানুষের চিত্রকর্ম’ (২০০৬), ‘চোখের আলোয় দেখেছিলেম’ (২০০৬)। নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তর—‘আহ্বান’ (১৯৬৫), ‘শত্রু’ (১৯৬২), ‘পাঁচটি একাঙ্কিকা’ (১৯৬৩), ‘অচেনা’ (১৯৬৯), ‘শহীদের প্রতীক্ষায়’ (১৯৫৯), ‘হেক্টর’ (১৯৬৯), ‘ছায়াবাসনা’ (১৯৬৬), ‘সেই নিরালা প্রান্তর’ (১৯৬৬), ‘সম্রাট জোনস’ (১৯৬৪), ‘অমা রজনীর পথে’ (১৯৬৬), ‘প্রাণের চেয়ে প্রিয়’ (১৯৭০), ‘লিসিন্ট্রাটা’ (১৯৮৪), ‘ভেক’ (১৯৮৬), ‘বিহঙ্গ’ (১৯৮৬), ‘জননী সাহসিকা ও তার সন্তানরা’ (১৯৮৪), ‘গডোর প্রতীক্ষায়’ (১৯৮১), ‘উষা দিশেহারা ও অন্যান্য নাটিকা’ (১৯৯২), ‘ওথেলো’ (১৯৮১), ‘শাইলোর উন্মাদিনী’ (১৯৯০), ‘মানব বিদ্বেষী’ (১৯৯০), ‘বেকেটের দুটি নাটক’ (যুগ্মভাবে) (১৯৯৯), ‘বেকেটের তিনটি নাটক’ (২০০০), ‘শান্তি’ (১৯৯৮), ‘ফেইড্রা’ (১৯৯৬), ‘হ্যামলেট’ (২০০০), ‘সেরা তিন একাঙ্কিকা’ (২০০২), ‘সমরেশ কোথায়’ (২০০২), ‘ওয়াচ অন দি রাইন’ (২০০৩), ‘ক্যাথলিন’ (১৯৭৪), ‘অমা রজনীর পথে’ (১৯৮৭), ‘বেকেটের পনেরো নাটক’ (যুগ্মভাবে, ২০০৬), কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ—ভাৎসারোভের কবিতা (১৯৮০), আধুনিক বুলগেরীয় কবিতা (১৯৮০), রিস্তো বোতেভের কবিতা (১৯৮৮), রিস্তো স্মিনেনস্কির কবিতা (১৯৮৯), কাহলির জিবরানের কবিতা (১৯৯২), সচিত্র প্রেমের কবিতা (২০০০), গবেষণা গ্রন্থের অনুবাদ—‘আমেরিকার সমাজ ও সাহিত্য’ (১৯৬৮), ‘সপ্তরথী’ (১৯৭০), ‘মার্কিন উপন্যাস ও তার ঐতিহ্য’ (১৯৭০), ‘অবিস্মরণীয় বই’ (১৯৬০), ‘মানুষের শিল্পকর্ম’ প্রভৃতি। খুব স্বল্পকথায় অনেক দূরে পৌঁছান কবীর চৌধুরী। সব বিষয়ে সৃজনী চেতনা ও মননধর্ম তাকে বজায়। পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়কে বাঙালি পাঠকের সামনে তিনি উন্মুক্ত করেছেন। কবীর চৌধুরী সাবলীল বক্তব্য বয়ানে, মূলানুগ সত্যতা সুনিশ্চিত তার লেখায়।
কাওসার হুসাইন
‘ইতালো কালভিনের গল্প’ (১৯৯৬), ইউলিয়াম ব্লেইকের সঙ্গস অব ইনোসেন্স এন্ড এক্সপেরিয়েন্স অবলম্বনে ‘শুদ্ধতা ও অভিজ্ঞতার গান’ (১৯৯১), বেকনের প্রবন্ধ অনুবাদ করেছেন। মেধাবী এ লেখক অনুবাদে সাবলীল ও সচকিত। গদ্য নির্ভার, পরিশুদ্ধ। কাওসার হুসাইন (জন্ম. ১৯৬৩) যথোচিতরূপে মূলকে অনুসরণ করেছেন। কায়েম করেছেন নিজের স্বাতন্ত্র। সুপাঠ্য তাঁর রচনা।
কাজী মোহাম্মদ ইদরিস
বাংলাদেশের সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ লেখক কাজী মোহাম্মদ ইদরিস (১৯০৬-১৯৭৫)। সাংবাদিকতার সঙ্গে প্রধানত যুক্ত থাকলেও অনুবাদ বিষয়ে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। চীনের গল্প অবলম্বনে শিশু সাহিত্যে আলাদা একটি পাঠ তৈরি করেছেন তিনি। নাটকেও তাঁর বিপুল উৎসাহ ছিল। ‘স্ট্রীন্ডবার্গের সাতটি নাটক’ (১৯৭৮) অনুবাদই তার প্রমাণ। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় স্ট্রীন্ডবার্গে মতো খ্যাতিমান নাট্যকারকে তিনি অনুবাদের জন্য বেছে নিয়েছেন। খুব মননশীল পরিচর্যা পরিলক্ষিত এ অনুবাদে। সাতটি নাটকে পরিপূর্ণ স্ট্রীন্ডবার্গ পাঠকের সামনে উপস্থিত এবং পরিচিতি মেলে জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনেক বিষয়ের। এ নাটকটি অনুবাদের ফলে বাংলাদেশের নাট্যজগত হয়েছে সমৃদ্ধ। বিস্মৃতপ্রায় কাজী ইদরিস এ নাটক অনুবাদের ভেতর দিয়েই অমলিন।
খালিকুজ্জামান ইলিয়াস
বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয় ‘গালিভারস ট্রাভেলস’-র অনুবাদ ১৯৮৪ সালে, পরে প্রকাশিত হয় ‘মিখাইল শোলোকভের গল্প’ (১৯৮৫)। জোসেফ ক্যাম্পবেলের ‘মিথের শক্তি’ (১৯৯৪), রিচার্ডস রাইটার্স-র ‘ব্লাক বয়’ (১৯৯৫) ও ‘আমেরিকান হাঙ্গার’ (২০০৬), মার্কেজের ‘ ফ্রাগারেন্স অব গোয়াভা’ (২০০৪), ফ্রেডেরিক ডগলাসের ‘ন্যারেটিভ অব দ্য লাইফ অব অ্যান আমেরিকান সেভ’ (২০০৮), চিনুয়া অ্যাচিবির ‘অ্যারো অব গড’ (২০১৩), জর্জ ফ্রেজারের ‘গোল্ডেন বাউ’ (২০১৬) অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনুবাদ প্রশংসনীয় এবং প্রতিষ্ঠিত। গ্রন্থগুলোর নির্ভরযোগ্য ভূমিকা এবং লেখক সম্পর্কে বিস্তর ধারণা অনুবাদকের পরিশ্রমের ফসল। বিশ্বসাহিত্যের অনেক গ্রন্থই অনুবাদের কাজে নিরত তিনি। বাংলা ভাষার সাহিত্যকে ইংরেজিতে অনুবাদের কাজও তিনি করছেন।
খায়রুল আলম সবুজ
‘গাঙচিল’, ‘আন্তিগোনে’ (১৯৯০), ‘নোরা’ (১৯৯৬), ‘বুড়োবট ও শকুন’ (১৯৯৬) খায়রুল আলম (জন্ম. ১৯৫২) সবুজের অনুবাদ। নাটক অনুবাদে তিনি অনেকাংশে সফল। তবে তাঁর অনুবাদ মঞ্চকেন্দ্রিক, সাহিত্য রস সৃজনে পরিপূর্ণ মনে হয় না। নাট্যগুণ বজায়ে তিনি যথেষ্ট পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। খায়রুল আলম সবুজ এ কর্মে নিজেকে অনুবর্তী করেছেন তিনি, অর্জন করেছেন এদেশীয় কাঠামো ও পরিবেশ। অনুবাদে তাঁর নাট্যক্রিয়া প্রশংসনীয়, পরিশীলিত।
খোন্দকার আশরাফ হোসেন
খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৫০-২০১৩) কবি হলেও অনুবাদে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সম্প্রতি টেরি ঈগলটন সাহিত্যতত্ত্ব (২০০৪)-র অনুবাদে হয়েছেন খ্যাতিমান। কাঠামো, উত্তর-কাঠামো বিষয়ক বিশ্বের সাম্প্রতিক ধারণা এই গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। এগুলো ঈগলটনের চেতনারই অংশ কিন্তু অনুবাদক পুনঃসৃষ্টি সম্পন্ন করেছেন তাঁর লেখায়। ‘খোন্দকার আশরাফ হোসেনে’র গদ্য সৃজনশীল, সুপাঠ্য। সাহিত্যক্তের আলোচনায় এ গ্রন্থটি একটি অনিবার্য সংযোজন। এছাড়া পুরাণকোষগ্রন্থও আছে তাঁর। সফোক্লিসের ‘রাজা ঈদিপাস’ (১৯৮৬), ইউরিপিডিসের ‘আলসেস্টিস’ (১৯৮৭), ‘পাউল সেলানের কবিতা’ (১৯৯৭), ‘সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বের উপাদান’ (১৯৮৯) এসব গ্রন্থ অনুবাদের ভেতর দিয়ে এ ধারাটিকে তিনি করে তুলেছেন সমৃদ্ধ। কবির আবেগ শুধু নয়, পঠন-পাঠনে যথেষ্ট প্রদীপ্ত এ সমালোচক, সৃজনশীল-দক্ষ ও বিশ্বস্ত অনুবাদক।
গোলাম মোস্তফা
কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) উর্দু ও আরবি ভাষা, একই সঙ্গে ইসলামী ভাবচেতনার বিষয়ে ছিল যথেষ্ট আগ্রহ। কখনোই এ চেতনা থেকে তিনি বিসর্জিত হননি। শুধু আবেগ নয় এক ধরনের বিশ্বাসও ছিল তার এ বিষয়ে। এমন প্রণোদনা থেকে গোলাম মোস্তফার অনুবাদ—‘মুসাদ্দাসে-হালী’ (১৯৪৯), ‘কালামে ইকবাল’ (১৯৫৭), ‘আল কুরআন’, ‘শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া’ (১৯৬০)। ইসলামের প্রশস্তি কীর্তন বিধৃত হয়েছে এসব রচনায়। এক ধরনের আত্মপরিতৃপ্তির অনুষঙ্গ যুক্ত থাকায় এসব রচনা তেমন আকর্ষণীয় মনে হয় না। অবশ্য এ ধরনের রচনায় আবেগ ও ওতি স্বভাবতই অচেতন থাকে না। তবে কবি গোলাম মোস্তফার অনুবাদ এসব সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়।
চৌধুরী শামসুর রহমান
‘নিষিদ্ধ ফল’ (১৯৬০), ‘তাসকিরাতুল ওয়াকিয়াত’ (১৯৬৮), ‘টমাস জেফারসন’ (১৯৫৮), ‘প্রজাপতির বিচিত্র কথা’ (১৯৬২), ‘মেক্সিকো’ (১৯৬৭), ‘আফ্রিকার অভ্যন্তরে’ (১৯৬৯) এসব বিচিত্র রকমের অনুবাদে চৌধুরী শামসুর রহমান (১৯০২-১৯৭৭) বেশ সৃজনশীল। তিনি সৃজনশীল সাহিত্যিকও বটে। ষাটের সাহিত্য পরিমণ্ডলে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ নানাবিধ কারণে। তার মধ্যে অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ। শামসুর রহমানের আগ্রহও যেমন নানামুখি, তেমনি রসবোধ জ্ঞানেও তিনি প্রখর। বোধকরি আগ্রহ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে তাঁর রসবোধ। উল্লিখিত অনুবাদে তিনি একটা পর্যায় অতিক্রম করেছেন, সন্দেহ নেই। সাহিত্যের সন্ধিৎসায় এগুলো গুরুত্ববহও বটে কিন্তু পর্যাপ্ত নন তিনি। একমুখি বিষয়ে মনযোগী হলেই তার সাফল্য আরও বাড়ত মনে হয়। যেমন মেক্সিকো বা টমাস জেফারসন বিষয়ের কাজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিষিদ্ধ ফল। সেটি যে মানেরই হোক তাতে পাঠকের পাঠ থাকে। তবুও পূর্ব-পাকিস্তানে অনুবাদের পথরেখায় তিনি অমোচনীয় নন।
জাফর তালুকদার
জাফর তালুকদার (জন্ম. ১৯৫২) গল্পের অনুবাদ করেছেন। এসব গল্পে তিনি অনেকটা সাবলীল। তাঁর গল্পকাঠামোর নন্দনে এক রকমের ঐতিহ্যিক সামঞ্জস্য তৈরি হয়। বাইরের কাহিনি হলেও এক ধরনের ঐক্য পাওয়া যায় এদেশীয় ভাবচেতনার সঙ্গে। তাঁর অনূদিত গ্রন্থ ‘ইন্দোনেশিয়ার গল্প’ (১৯৮৯), ‘ঢেউয়ের গান’ (১৯৯১), ‘ভিনদেশী মজার গল্প’ (১৯৯৬), ‘ফ্রান্সের রূপকথা’ (১৯৯৭), ‘নানান দেশের রূপকথা’ (১৯৯৭), ‘বিদেশী মজার গল্প’ (১৯৯২) প্রভৃতি। অনুবাদের পরিচর্যায় তাঁর যাত্রা পাঠককে আশান্বিত করে।
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর (১৯২৮-২০১৪) গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ ‘শেক্সপীয়রের সনেট’ (১৯৭৭)। একটি দুরূহ কর্ম তিনি এক্ষেত্রে সম্পন্ন করেছেন। শেক্সপীয়ার অনেক বড় কবি, তাঁর সনেটের ছন্দবৈচিত্র্য, আলঙ্কারিক বিভা, উপস্থাপন প্রয়াস একদিকে যেমন মধুর অন্যদিকে তেমনি দুরূহ। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী অসাধারণ করে তুলেছেন তাঁর সনেটকে। এ বিষয়ক তার দীর্ঘায়ত ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। যা হোক, অনুবাদের ফলে বাংলাভাষাভাষীদের কাছে শেক্সপীয়ার অনেক সহজ হয়েছে, কবিবান্ধবকে চিনে নিতে পেরেছে। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী নিজেও কবি, সুতরাং কবির মর্ম তার আয়ত্তে, সনেট অনুবাদে সে বিবেচনাটি তিনি বজায় রেখেছেন। ‘অ্যারিওপাজিটিকা’ (১৯৭১), ‘স্যামসন অ্যাগানিসটিজ’ (১৯৭৩), ‘টেমপেস্ট’ (১৯৮৫) প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ। মিল্টন বিষয়ে তার পাঠ-অভিজ্ঞতা আছে, দৃষ্টিকোণ কিংবা দার্শনিক বুদ্ধির জায়গাটি অনুবাদকের করায়ত্ত । বাংলাদেশে মিল্টনচর্চায় তিনিই পথিকৃৎ। এ প্রয়াসটি আমরা তাঁর অনুবাদে লক্ষ করি। নাটকীয় অবয়ব ও আবহ, সংলাপগুণ, আবহগত পরিচর্যা বিদ্যমান অ্যারিওপাজিটিকা কিংবা স্যামসন অনুবাদে। সবচেয়ে বড় অনুবাদের ব্যাপারে দীর্ঘ পাঠ তিনি গ্রহণ করেছেন, পরিচর্যাতেও তিনি যত্নশীল এবং পরিশ্রমী। অনুবাদ বিষয়ে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী একটি গ্রন্থও লিখেছেন।
জি এইচ হাবীব
‘সোফির জগৎ’ (২০০২), ‘তুন্দ্রা ইঁদুরের পাহাড়’, ‘ফাউন্ডেশন’ (১৯৯২), ‘তাড়িখোর’, ‘অদৃশ্যনগর’, ‘পরদেশী গল্প’ (২০১২), ‘একজন লেখকের মৃত্যু’ (২০১৬), ‘নিঃসঙ্গতার একশ বছর’ (২০০০) অনুবাদ করেছেন জিএইচ হাবীব (জন্ম. ১৯৬৭)। তাঁর অনুবাদ আকর্ষণীয় ও সুখপাঠ্য। হেরমান হেসের ‘সেই নগর’, বোর্হেসের ‘আলিফ’, ‘মৃত্যু ও ক্যাম্পাস’, সারামাগোর ‘সেন্টার’ প্রমুখ বিশ্বশ্রেষ্ঠ গল্পকারদের গল্প টীকা-তথ্য-ভ্যাষ্য ও পরিচিতিসমেত সততার সঙ্গে বাংলাভাষী পাঠকের সামনে তিনি তুলে ধরেছেন। জিএইচ হাবীবের লেখক নির্বাচন রুচি-সিগ্ধকর। রোলা বার্থ লেখকের পরিশ্রমী অনুবাদ। বাংলা ভাষার পাঠকদের জন্য তিনি তাত্ত্বিক বার্থকে সহজলভ্য করে তুলেছেন। অনুবাদে আছে তাঁর মুন্সিয়ানার ছাপ, উইট-হিউমারকে এক ধরনের রসবোধের মাত্রায় উন্নীত করেন অনুবাদক।
জিয়া হায়দার
জিয়া হায়দার (১৯৩৬-২০০৮) নাটকের তত্ত্ব এবং অনুবাদ বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিজেও সৃজনশীল নাট্যকার। ‘এ্যান্টিগোনে’ (১৯৯২) তাঁর অনূদিত নাটক। এ নাটকে তিনি মূলানুগ, স্বচ্ছন্দ। গ্রীক থেকে ইংরেজি হওয়ার পর বাংলায় কিংবা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ সম্পন্ন হয়। জিয়া হায়দারও তেমনটি করেছেন। তাঁর গদ্য কাঙ্ক্ষিত, নাট্যভাষা ঋজু। তবে এটি তেমন পাঠকপ্রিয়তা পায়নি। কারণ, ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা। তবুও বাংলাদেশে এটি গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ, সন্দেহ নেই।
নাজিব ওয়াদুদ
‘অরহান পামুক’ (২০০৮), ‘বালজাকের আনাড়ী রসিকজন’ (২০১১), ‘চিনুয়া অ্যাচিবির জননায়ক’ (২০১২), ‘আধুনিক ফিলিস্তিনী গল্প’ (২০১৩), রাসকিনের কিশোর উপন্যাস ‘স্বর্ণদীর রাজা’ (২০১৩), ‘বিশ্বসেরা ছোটগল্প’ (২০১৪), ‘নোবেলবিজয়ীদের সাক্ষাৎকার’ (২০১৮) নাজিব ওয়াদুদের (জন্ম. ১৯৬১) অনুবাদ রচনা। মূলানুগ অনুবাদে নাজিব ওয়াদুদ যত্নশীল।
ফতেহ লোহানী
ইউজিন ও’নীলের ‘নাটক চতুষ্টয়’ (১৯৬৭), আর্থার মিলারের ‘একটি সামান্য মৃত্যু’ (১৯৭৯) ফতেহ লোহানী (১৯২০-১৯৭৫) অনূদিত নাটক। বিভাগ-পরবর্তী বাংলাদেশে তিনি নাটকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছেন। ও’নীলের নাটকের অনুবাদ বাংলা ভাষাভাষীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকান এ নাট্যকার বিশ্বসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ নাট্যব্যক্তিত্ব। পৃথিবীর অনেক ভাষায় তার নাটক যেমন অনূদিত তেমনি এ বিষয়ক ধারণা বা জ্ঞানও হয়েছে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। আর্থার মিলারের অনেকেই অনুবাদ করলেও ফতেহ লোহানীর অনুবাদ গ্রহণযোগ্য এবং বেশি নাট্যমনস্ক। ফতেহ লোহানী একাধারে নাট্যকার এবং নাট্য অনুবাদক। সে কারণে অনুবাদে তিনি ও’নীল কিংবা মিলারের প্রবণতা ও নাট্যক্ষেত্রটি বুঝে উঠতে সক্ষম। সেটির প্রমাণ তাঁর অনুবাদে মিলেছে।
বদিউর রহমান
বদিউর রহমান (জন্ম. ১৯৪৭) সমাজমনস্ক লেখক। ‘এরস্টিটলের পোয়েটিকস’ (১৯৯৫), ‘হোরেসের আর্সপোয়েটিকা’ (১৯৯৬), ‘লঙ্গিনাসের কাব্যতত্ত্ব’ (১৯৭৭) এসব অনুবাদে সাহিত্যতত্ত্বের নতুন জগতকে তিনি উন্মোচন করেছেন। সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় কিংবা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এ বিষয়ক কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন। বদিউর রহমান হোরেস কিংবা লঙ্গিনুসের পাঠে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে তাঁর ভাবনা একটু আড়ষ্ট, দ্বিধান্বিত। ‘পোয়েটিকস’ও এ কারণেই পাঠকপ্রিয়তা কম পেয়েছে। তবুও বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্যে এটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।
মতিনউদ্দীন আহমদ
‘অর্থনীতির গোড়ার কথা’ (১৯৬৪), ‘ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট’ (১৯৬৪), ‘শত জীবনের কথা’ (১৯৬২), ‘অশান্ত পৃথিবী’ (১৯৬০), ‘জনসংখ্যা বাড়ছে’ (১৯৫৯), ‘বিজন বনের রূপকথা’ (১৯৫৯), ‘হাতের কাছের কলকব্জা কিভাবে চলে’ (১৯৬৪), ‘চালাক হওয়ার পয়লা কিতাব’ (১৯৫৮), ‘জগৎ জুড়ে মজার খেলা’ (১৯৬৪) এমন অনেক কাজে তিনি সফল। মতিনউদ্দীন (১৯০০-১৯৮০) পরিশ্রমী এবং মেধাবী লেখক। মেধার পরিচর্যা করেছেন নানা বিষয়ে। বিচিত্রমুখি বিষয়ের চর্চা তিনি করেছেন। প্রধানত গল্পভঙ্গিটিতে তিনি বেশি ক্রিয়াশীল। উল্লিখিত এসব গ্রন্থেও তার প্রমাণ রয়েছে। তবে তার সম্ভাবনা আরও সিরিয়াস কর্মে সমন্বিত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল।
মফিজ চৌধুরী
শেক্সপীয়ারের ‘কিং লিয়র’ (১৯৭৮), ‘অ্যান্টনী ও ক্লিওপেট্রা’ (১৯৯২)-র অনুবাদ করেছেন মফিজ চৌধুরী। অনেকেই এ নাট্যকারের নাটকের অনুবাদ করেছেন এ পর্যায়ে মফিজ চৌধুরী ব্যতিক্রমী। চরিত্র পরিস্ফুটন, আবহ নির্মাণ, গল্প-বর্ণনায় তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সুপাঠ্য হয়ে উঠেছে তার অনুবাদ। তবুও সেটিংস কিংবা মূলানুবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।
মান্নান হীরা
মান্নান হীরার (জন্ম. ১৯৫৭) ‘কোরিওলেনাস’ (১৯৭৮) অনুবাদের ফলে নিজের নাটক হিসেবেই পরিগণিত বলা চলে।। বাংলাদেশের নাটকে এটি অনবদ্য সংযোজন। দেশীয় আবহটি চমৎকার বজায় রেখেছেন নাট্যকার।
মাফীজ দীন সেখ
মহাকবি গ্যাটের ‘ক্লাভিগো’ (১৯৯৪) নাটকের অনুবাদ করেছেন তিনি। এটি খুব দুরূহ অনুবাদ। বাংলাভাষীদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গ্যেটের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিচেতনার সতর্ক বিবেচনা এখানে পরিলক্ষিত।
মুনীর চৌধুরী
মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) মনস্বী নাট্যকার, তাঁর আধুনিকমনস্কতার তুলনা হয় না। অনুবাদের ক্ষেত্রটিতেও তিনি যথেষ্ট আধুনিক। বলা চলে বাংলাদেশের নাটকের অনুবাদে তিনি পথিকৃৎ। স্বল্প সময়ে অনেক মেধাবী কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন। বহুমনস্ক, বিরলপ্রজ গুণী এ নাট্যকারের পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরিত নাটক জর্জ বার্নাড শ’র ‘You never can tell’-এর রূপান্তর ‘কেউ কিছু বলতে পারে না’ (১৯৬৭), জন গলসওয়ার্দীর ‘The silver box’-এর রূপান্তর ‘রূপার কৌটা’ (১৯৬৯), জোহান অগাস্ট স্ট্রিণ্ডবার্গের ‘The father’-এর রূপান্তর ‘জনক’ (১৯৭০)। রপান্তরিত একাঙ্ক নাটক—‘স্বামী সাহেবের অনশনব্রত’ (১৯৪৬), ‘জমা খরচ ও ইজা’ (১৯৬৮), ‘মহারাজ’ (১৯৬৮), ‘গুর্গন খার হীরা’ (১৯৬৮), ‘ললাট লিখন’ (১৯৬৯)। অনূদিত পূর্ণাঙ্গ নাটক—উইলিয়াম শেকসপীয়ারের ‘টেমিং অব দি শ্র’র অবলম্বনে ‘মুখরা রমণী বশীকরণ’ (১৯৭০)। এ নাটকে অনুবাদকের দক্ষতার পরিচয় মেলে। যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়ে মুনীর চৌধুরী প্রকৃত নাটকীয় আবহ সৃষ্টি, দক্ষ সংলাপ তৈরি এবং রসবোধের তীক্ষ পরিমার্জনা এনে ইন্দ্রিয়গ্রামে যথেষ্ট প্রাণ সৃষ্টি করেন। নাটকটির অনুবাদক হিসেবে মুনীর চৌধুরী একটি দৃষ্টান্ত। অনূদিত রূপান্তরিত অসমাপ্ত নাটক—শেকসপীয়রের ‘ওথেলো’, টেনেসী উইলিয়ামস-এর এ স্ট্রীটকার নেড় ডিজায়ার অবলম্বনে ‘গাড়ীর নাম বাসনাপুর’, ‘রোমিওজুলিয়েট’, শেক্সপীয়রের মাচ এ্যাড়ু এ্যাবাউট নার্থিং-এর অনুবাদ ‘অকারণ ডামাডোল’, জর্জ বার্নার্ড শ’র ‘ম্যান এ্যন্ড সুপারম্যান’, ইউজীন ও’নীল মর্নিং বিকাস ইলেকট্রার অনুবাদ ‘ইলেট্রার জন্য শোক’, শেরিডানের ‘দি স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল’।
মুস্তাফিজুর রহমান
জাঁ পল সাঁত্রের ‘নিঃশব্দ নরকে’ (১৯৭৬)-র অনুবাদক মুস্তাফিজুর রহমান। এটি চমৎকার একটি রচনা। মাঝারী কলেবরের এ গ্রন্থটি বেশ পাঠকপ্রিয়। অস্তিত্ববাদী দর্শনিক সাঁত্র এবং তার চরিত্রের প্রতিচ্ছবি মেলে এই রচনায়। মুস্তাফিজুর রহমান সৃজনী প্রেক্ষণে কথক প্রয়াসে অনবদ্য থেকে অনুবাদটি সম্পন্ন করেছেন। রসবোধের প্রাচুর্যও বেশ আকর্ষণীয়। আলবার্তো কামুর ‘ক্যালিগুলা’ (১৯৭৬) তাঁর অন্য অনুবাদ। অ্যাবসার্ড দৃষ্টিভঙ্গি নয়, টেলিং-এর কারণেই তা বেশ গুরুত্ববহ।
মুহম্মদ নূরুল হুদা
‘পরিবর্তনের পথে’ (১৯৭২), ‘আগামেনন’ (১৯৮৭), ‘ইউনুস এমরের কবিতা’ (১৯৯২), ‘বাস্তুহারা’ (১৯৯৫), ‘ফ্লবারী ও কনরের গল্প’ (১৯৯৭), ‘নীল সমুদ্রের ঝড়’ (১৯৮৪), ‘রোমিও জুলিয়েট’ (১৯৯৮) প্রভৃতি কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার (জন্ম. ১৯৪৯) অনুবাদগ্রন্থ। নূরুল হুদার কবিতা অনুবাদ বেশ আকর্ষণীয়। খুব দ্রুত তা মর্মে পৌঁছয়। গদ্য ঝরঝরে, মুক্ত, দ্বিধাহীন ও সাবলীল। কবির ভিত্তিতে অন্য কবিদের খোঁজেন তিনি। বিশেষ করে শেক্সপীয়ার তাঁর আগ্রহের বিষয়। শেক্সপীয়ার নাটক লিখলেও কবিমনন ছিল খুবই উচ্চমানের। অনেকের মতে কবিভিত্তিটিই তার প্রধান, এমন সত্যটি অনুধাবন করেন। কবি নূরুল হুদা সে পরিপ্রেক্ষিতে শেক্সপীয়ারকে খুঁজে পেয়েছেন বলেই মনে হয়। এছাড়া তার অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থগুলোও মূল্যবান। সর্বোপরি বিষয়ের স্পষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টিকোণের গুণে কবিতা এবং গল্প দু-ধরনের অনুবাদেই তিনি পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন।
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) প্রচুর অনুবাদের কাজ করেছেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থ ‘রুবাইয়াত-ই-ওমর খয়্যাম’ (১৯৪২), ‘অমিয় শতক’ (১৯৪০), ‘দীওয়ানে হাফিজ’ (১৯৩৮), ‘শিক্ওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ’ (১৯৪২), ‘মহানবী’ (১৯৪৬), ‘বাইঅতনামা’ (১৯৪৮), ‘বিদ্যাপতি শতক’ (১৯৫৪), ‘কুরআন প্রসঙ্গ’ (১৯৬২), ‘মহররম শরীফ’ (১৯৬২), ‘অমর কাব্য’ (১৯৬৩), ‘ইসলাম প্রসঙ্গ’ (১৯৬৩), ‘Hundred Saving of the Holy Prophet’ (1945), ‘ Mystic Songs’ (1960)। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বহুভাষাবিদ পণ্ডিত, এবং সে কারণেই অনুবাদকর্মে তিনি স্বচ্ছন্দ্য, এগুলো প্রত্যেকটিই তাঁর ধ্রুপদীমানের কাজ। তবে কবিমনস্কতা দুর্বল হওয়ায় ওমর খৈয়াম কিংবা হাফিজ অনুবাদ বেশি পাঠকপ্রিয়তা পায়নি। প্রধানত গবেষণাধর্মী কাজেই তিনি বেশি সফল। বাংলাদেশের অনুবাদের ভিত্তিটি তার হাতেই প্রতিষ্ঠা পায়।
মোতাহের হোসেন চৌধুরী
‘ক্লাইভ বেলের সিভিলাইজেশনের সভ্যতা সভ্যতা’ (১৩৭২ ব.), বাট্রান্ড রাসেলের ‘কংকোয়েস্ট অব হ্যাপিনেস—সুখ’ (১৩৭৫ ব.) এগুলো মোতাহের হোসেন চৌধুরীর (১৯০৩-১৯৫৬) ধ্রুপদী অনুবাদ। বিশ্বশ্রেষ্ঠ বেল কিংবা রাসেল পাঠকের নিকট সুখপাঠ্য হয়ে ওঠেন অনুবাদের কারণেই। ‘সুখ’ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর অনবদ্য পাঠ। এটি আসলে অনুবাদকের নিজস্বতার গুণেই সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ এ লেখক সাহিত্য-সংস্কৃতি, জীবন ও জগত নিয়ে যে মনন-রুচির পরিবেশটি বাঙালিদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন, তার অংশ রাসেলের ‘সুখ’ নামক গ্রন্থটি। এটি আসলে রাসেলের সুখ নয় পরিণত হয়েছে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ‘সুখ’ বিষয়ক অভিজ্ঞান। অনন্যসাধারণ এ গ্রন্থটি অনেক পাঠকপ্রিয় এবং অবশ্যপাঠ্যরূপে পরিগণিত।
মোবারক হোসেন খান
বিচিত্র বিষয়ের অনুবাদ করেছেন। রূপকথা, রোম্যান্সধর্মী বিষয় নিয়েই তার অনুবাদ। অনুবাদের চর্চা তার দীর্ঘদিনের। শিশু-কিশোর উপযোগী এসব অনুবাদে তিনি অনেকটা সফল। তবে সব অনুবাদই গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনেক ক্ষেত্রে শিল্পমান বজায়ও থাকেনি। ‘তারাস বুলবা’ (১৯৯১), ‘ক্যাপ্টেন দুহিতা’ (১৯৮১), ‘নিঃসঙ্গ’ (১৯৭৯), ‘তিন তরঙ্গ’ (১৯৮৩), ‘শিকারীর গুহা’ (১৯৮১), ‘অ্যারাবিয়ান নাইটস’ (১৯৯৬), ‘টেইলস ফ্রম শেক্সপীয়ার’ (১৯৯৬), ‘সাগরের হাতছানি’ (১৯৯৬), ‘এমিলের গোয়েন্দাবাহিনী’ (১৯৯৫), ‘রূপকথার বিশ্ব’ (১৯৯৬), ‘কিশোর চিরায়ত কাহিনী’ (১৯৯৪), ‘এশিয়ার লোককাহিনী’ (১৯৮৫), ‘বিশ্বের অন্যান্য গল্প’ (১৯৯৫), আইভানভ’ (১৯৭৮), ‘পৃথিবীর প্রথম দিনগুলো’ (১৯৮৬), ‘নোবেল বিজয়ীদের নির্বাচিত গল্প’ (১ম খণ্ড, ১৯৮৫, ২য় খণ্ড ১৯৯১), ‘পৃথিবীর সেরা গল্প’ (১৯৮৭), ‘সাতনরী গপ্পো’ (১৯৮২), ‘আফ্রিকার নির্বাচিত গল্প’ (১৯৮৫), ‘বিস্ময় গ্রহের উপাখ্যান’ (১৯৯১), ‘ঈশপের গল্প’ (১৯৯২), ‘ঈশপের আরো গল্প’ (১৯৯২), ‘শ্রেষ্ঠ থ্রিলার কাহিনী’ (১৯৯৫), ‘বিশ্বনন্দিত গল্প’ (১৯৯১), ‘আমেরিকার ফার্স্টলেডীর বিচিত্র জীবন’ (১৯৯৭) প্রভৃতি তাঁর গ্রন্থ।
মোহাম্মদ হারুন-উর রশিদ
মোহাম্মদ হারুন-উর রশিদ (জন্ম. ১৯৩৯) অনুবাদের কাজ মননধর্মী। নিজস্ব শৈলী তিনি অর্জন করেছেন এক্ষেত্রে। ‘ভাষা চিন্তায় ও কর্মে’ (১৯৬৯), ‘মাছি’, ‘তিনটি ফরাসী প্রবন্ধ’ (১৯৮৪), ‘হাসান বয়াতীর সুখ-দুঃখ’ (১৯৯৪) তাঁর অনুদিত গ্রন্থ। মোহাম্মদ হারুন-উর রশিদ পরিশ্রমী এবং রুচিশীল অনুবাদক। হাসান বয়াতীর সুখ দুঃখ কিংবা ফরাসী প্রবন্ধের অনুবাদে সৃজনশীলতার ছাপ আছে। সুপাঠ্য তার অনুবাদ।
রশীদ হায়দার
ফ্রানৎসা কাফকার ‘কাঠগড়া’ (১৯৮৪)-র অনুবাদ করেছেন রশীদ হায়দার (জন্ম. ১৯৪১)। এই অনুবাদে লেখক অনেকটা সাবলীল। উপস্থাপিত ভাষ্য বেশ আকর্ষণীয়। কাফকা-অভিজ্ঞতা আমাদের ভিন্ন রুচির নিশানা দেয়। বিশেষ করে সাহিত্যের আধুনিক চিন্তাচেতনার বিনির্মাণে কাফকা পঠন এ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ। রশীদ হায়দার অনুবাদের ভেতর দিয়ে সে কাজটি সম্পন্ন করেছেন। মূলাশ্রয়ী স্বাধীন এই রচনাটি নিজস্ব স্টাইলে ভাস্বর।
শফি আহমেদ
জন স্টাইনবেক ‘মুক্তো’ (১৯৮৭), টি. এস. এলিয়ট ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’ (১৯৯৩), ওলে সোয়েংকা ‘দ্য লায়ন এ্যন্ড দ্য জুয়েল’ (১৯৯৪), টি. এস. এলিয়ট ‘পারিবারিক পুনর্মিলনী’ (১৯৯৫), মোমাডের ‘নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ’ (১৯৯৫), ‘নারী-কাহিনী’ (১৯৯৫) শফি আহমদের অনুবাদ। প্রত্যেকটি কাজেই শফি আহমেদ (জন্ম. ১৯৪৮) সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অনুবাদের সবচেয়ে বড় দিক, এতে তিনি নিজস্বতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। মূল লেখকের কণ্ঠস্বর বজায় রেখে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত হয়ে উঠেছেন তিনি এসব রচনায়। সজীব ও সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে স্টাইনবেক, এলিয়ট, সোয়েঙ্কার রচনায়। তাছাড়া তাঁর অনুবাদের গুণমত মানটুকু সম্পূর্ণ বজায় আছে।
শহীদ আখন্দ
উইলা ক্যাথারের ‘মানসী’ (১৯৫৯), জাঁ পল সাত্রের ‘যখন সুমতি’ (১৯৭৮), জাঁ পল সাত্রের ‘আরো কিছু জীবন’ (১৯৮০), জেড এ ভুট্টোর ‘আমাকে হত্যা করা হলে’ (১৯৮১) শহীদ আখন্দের অনুবাদ। শহীদ আখন্দ (জন্ম. ১৯৩৫) মূল্যবান কথাকার। তাঁর অনুবাদ প্রবলরূপে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত। সৃষ্টিতে সফলও বলা চলে। সাত্র-এর বর্ণনাকে নিজের মতো করে পরিবেশন করেছেন। যখন সুমতি পাঠকনন্দিত অনুবাদ। ভাষার ভেতরে রসবোধ ও প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে। ঐতিহ্যের আরাধ্য দিকটিও এখানে কায়েম হয়েছে।
শামসুর রাহমান
শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) ‘হ্যামলেট: ডেনমার্কের যুবরাজ’ (১৯৯৫) রচনা করেছেন। এটি শেক্সপীয়ারের মূলানুগ রচনা। নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। শামসুর রাহমান এক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। কিন্তু কবিচিন্তনে তা হয়ে উঠেছে শামসুর রাহমানের রচনা। শেক্সপীয়রের পুনঃসৃষ্টি বলা যেতে পারে এটিকে। স্বতন্ত্র স্বরে নতুন ইঙ্গিতে শামসুর রাহমানের ‘হ্যামলেট’ আমাদের সমস্ত সম্ভাবনাকে যেন উস্কে দিয়েছে।
শামসুদ্দিন চৌধুরী
‘অদৃষ্টবাদী জাক ও তার মণিব’ (১৩৯৯), ‘মাইকেল চেখভের অভিনয় পদ্ধতি’ (১৪০৯), ‘ইলিয়াদ’ (১৪১২), ‘চিলিতে অজ্ঞাতবাসে’ (১৪১৩), ‘নব উপন্যাসের পক্ষে’ (১৪১৭), ‘ক্লোদ লেভিস্রাউস: নির্বাচিত রচনা’ (১৪১৭), ‘ভার্জিলের ঈনিড’, ‘নন্দনতত্ত্ব’ (১৪১৭) প্রভৃতি তাৎপর্যপূর্ণ অনুবাদ করেছেন। সাধারণ, তাঁর নির্বাচন সাহিত্যতাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের প্রতি। তবে প্রতিটি গ্রন্থই তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনা।
শাহেদ আলী
বাংলা ‘ইতিবৃত্ত’ (১৯৯৪), মূল রচনা হেরোডোটাস। যার ইংরেজি আউব্রে দ্য সেলিনকোর্ট। হেরোডেটাস এর ‘ইতিবৃত্ত’র অনুবাদক শাহেদ আলী (১৯২৫-২০০১)। ইতিহাসের জনকের এ গ্রন্থটি মূল্যবান। হেরোডেটাসের ব্যাপক ইতিহাস ধারণার সূত্র, উৎস এ গ্রন্থে নির্ধারিত। লেখকের অনুবাদ প্রশংসিত।
সরদার ফজলুল করিম
প্লেটোর ‘রিপাবলিক’ (১৯৭৪) ‘জোয়েট’, কর্ণফোর্ড এবং এইচ. ডি. পি. লী’র ইংরেজি অনুবাদের ভিত্তিতে সম্পন্ন করেছেন সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-২০১৪)। তিনি বলেছেন—‘‘রিপাবলিককে সাহিত্যানুরাগী এবং আগ্রহী ছাত্র-সাধারণের নিকট সহজবোধ্য এবং অনুধাবনযোগ্য করার জন্য অধ্যায়ক্রম, টীকা, ব্যাখ্যা এবং আলোচনার চেষ্টা করেছেন। বিশ্বসাহিত্যে এ মৌলিক গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে তিনি পাঠকের রুচি ও চিন্তার পরিধিকে দিয়েছেন বাড়িয়ে। অনুবাদক বলেছেন ‘প্লেটোর ভাষাশৈলী ছিল বিস্ময়কর। তাঁর বিপুল সংলাপরাজি ব্যঞ্জনার দিক থেকে গদ্যকাব্যের ঝঙ্কারময় সৃষ্টি। এ দিকটি তিনি অনুবাদের সময় যথাযথ বিবেচনায় এনেছেন।’’ এ গ্রন্থের অনুবাদে লেখকের আয়োজন প্রশংসনীয়। ভূমিকা অংশটিও চমৎকার। এটির ভেতর দিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি প্রয়াস যেন সম্পন্ন হয়েছে। সংলাপ, কথোপকথনও বেশ উপভোগ্য। সরদার ফজলুল করিমের ভাষা সহজবোধ্য, সরল কিন্তু গভীর। গোটা গ্রন্থটি পঁচিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শিরোনামও নির্ধারিত। প্লেটোর ‘সংলাপ’, এ্যরিস্টটলের ‘পলিটিকস’, এঙ্গেলস রচিত ‘এ্যান্টিডুরিং’, রুশোর ‘সোশ্যাল কন্টাক্ট’ সরদার ফজলুল করিমের মূল্যবান অনুবাদ গ্রন্থ। সর্বশেষ বেরিয়েছে ‘আমি রুশো বলছি’ দি কনফেশনস্ (২০০৬)। রুশোর ‘দি কনফেশাস্-এ তিনি বলেছেন—‘‘রুশোর আত্মকথা বা কনফেশন্স্ রুশোর দর্শনের অংশ নয়। তাঁর দর্শন তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে লাভ করা যায়। রুশোর আত্মকথা হচ্ছে রুশোর অস্তিত্ব—তাঁর দৈহিক এবং মানসিক অস্তিত্বের প্রকাশ এবং তার দর্শনের ভিত্তিভূমি। এই অস্তিত্বেই তার দর্শন। তার দর্শন তার অস্তিত্ব থেকে অবিচ্ছন্ন।’ এর অনুবাদ নিয়ে তিনি বলেন—‘‘রুশোর কোনও আক্ষরিক বা অনাক্ষরিক অনুবাদ নয় বলতে পারি মর্মানুবাদ। মর্মকে নিয়ে আসাই বড় কর্ম।’’ বোধ করি এটাই তার অনুবাদের মূল কথা।
সাঈদ-উর রহমান
‘মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা’ (১৯৮৫) গ্রন্থটির সংকলক ও অনুবাদক সাঈদ-উর রহমান (জন্ম. ১৯৪৮)। গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। কিছু রচনা মার্কস কিংবা এরূপ চিন্তার যেমন প্লেখানভ, লেনিন, ট্রটস্কি, কডওয়েল, লুকাচ, থমসন প্রভৃতির রচনাকে একসঙ্গে করেছেন। মার্কসবাদী নন্দন দৃষ্টির লেখকরাও এ গ্রন্থে যত্নের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। এটিতে মার্কস-নন্দন সম্পর্কেও বিশেষ ধারণা আছে।
সিকান্দার আবু জাফর
সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫) প্রধানত কবি। বাংলাদেশের সাহিত্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে ‘রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম’ (১৯৬৬), সেন্ট লুইয়ের ‘সেতু’ (১৯৬১), বারনাড মালামুডের ‘যাদুর কলস’ (১৯৫৯), ‘সিংয়ের নাটক’ (১৯৭১) প্রভৃতির অনুবাদ করেছেন। এসব অনুবাদে তিনি সমৃদ্ধ। তবে একটু আড়ষ্ট মনে হয়। সিংয়ের নাটকে এক ধরনের সম্পূর্ণতা আছে। ব্যাপকতাও পরিলক্ষিত। নাট্যগুণ স্বচ্ছরূপে এখানে বজায় রয়েছে। এটির উন্নত রচনাগুণে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে অনেককেই আকৃষ্ট করেছে। ‘যাদুর কলস’ কিংবা ‘সেতুর’ ভেতর দিয়ে অনুবাদক হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধি পেয়ে যান।
সিরাজুর রহমান
সরস গদ্যকার সিরাজুর রহমান (জন্ম. ১৯৩৪)। ‘আন্তন চেখভের নাটক’, চার্লস ডিকেন্সের ‘গ্রেট এক্সপেকটেশন্স’, শার্লোট ব্রন্টির ‘জন এয়ার’, জেন অস্টিনের ‘প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস’—এসব অনুবাদে তিনি যথেষ্ট সফল। জনপ্রিয়ও বটে। মূল-অনুবর্তী অনুবাদ, কিন্তু যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকে চেখভকে চেনা যায় নিজের পরিবেশে। সিরাজুর রহমান অনুবাদে পাঠকের কাছাকাছি পৌঁছানোর ও যথোচিত সুবোধ্য করার চেষ্টা আছে।
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
প্রাচীনতম আকর রচনা ‘এ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব’ (১৯৭৫)। এটির অনুবাদ করে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (জন্ম. ১৯৩৬) অসাধ্য সাধন করেছেন। বিস্তারিত এবং সুস্পষ্ট তাঁর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা। টীকা ভাষ্যও আছে গ্রন্থটিতে। যথারীতি ইংরেজি থেকেই তিনি এ অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন। হেনরিক ইবসেনের ‘বুনো হাঁস’ (১৯৬৫) তাঁর অন্য অনুবাদ। এক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। অনুবাদকের ভাষার ব্যাপ্তিতে গভীর জীবনদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়। ইবসেনের এ অনুবাদের ভেতর দিয়ে তিনি তাকে বাঙালিদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন।
সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯২৭-১৯৮৪) লেখক ও গবেষক। পরিশ্রমী অনুবাদকও বটে। সাহিত্যতত্ত্বের অনেক জটিল বিষয়কে সহজভাবে তিনি পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছেন। লঙ্গিনুস কিংবা হোরেসের অনুবাদ তাঁকে গুরুত্ববহ করে তুলেছে। বাংলা ভাষায় এমন সাহিত্যতাত্ত্বিকদের পরিচিত করানো শুধু নয়, যোগ্যতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। সাহিত্য ধারণাই শুধু নয় নিজের বোধ ও উপলব্ধির একটা মাত্রাও তাঁর রচনায় লক্ষ করা যায়। ‘আরিস্টটলের সাহিত্যতত্ত্ব’ (১৯৭৬), ‘হোরেসের সাহিত্যতত্ত্ব’ (১৯৭৯), ‘লঙ্গিনুসের সাহিত্যতত্ত্ব’ (১৯৯৭) এগুলো যথাক্রমে অ্যারিস্টটলের Poetics, লঙ্গিনুসের On the Sublime, হোরেসের Ars Poetica-র অনুবাদ। এসব গ্রন্থের অনুবাদ নানা সময়ে হয়েছে কিন্তু সুনীল কুমারের অনুবাদ স্বাতন্ত্র্য এবং পৃথক পরিবেশ দাবি করে। বাংলা ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্র নির্বাচন, স্বচ্ছতা, যত্ন সবদিক বিবেচনা করলে সুনীল কুমার সিদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ভাষা সরল, তত্ত্ববহুল নয়। নিছক জটিল করে তোলেননি কিছু। উপযুক্ত তিনটি গ্রন্থেরই ভূমিকা প্রদান করেছেন তিনি। এটি পাঠকের বাড়তি লাভ।
সুব্রত বড়ুয়া
সুব্রত বড়ুয়ার (জন্ম. ১৯৪৬) অনুবাদ ‘দি রাইট স্টাফ’, ‘কণা’, ‘কোয়ান্টাম ও তরঙ্গ’ (১৯৮৪), ‘আমেরিকার ভৌগোলিক রূপরেখা’ (১৯৮৬), ‘শঙ্খচিল’ (১৯৯৪), ‘এমিল ও গোয়েন্দা কাহিনী’ (১৯৭২) প্রভৃতি। এগুলো তাঁর গুরুত্ববহ অনুবাদ।
সৈয়দ আলী আহসান
সব্যসাচী অনুবাদক সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)। তবে কবিতার অনুবাদেই তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। মেরিডিথের অনুবাদ আকর্ষণীয়। ইমেজ সৃষ্টি, পরিবেশ বর্ণনায় যথেষ্ট শিল্পীমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। একইভাবে হুইটম্যানের কবিতার গুরুত্ববহ অনুবাদ তিনি করেছেন। অনুবাদের মতো অনালোকিত দিকে শুধু আলো প্রক্ষেপণই নয় তিনি বিদেশী অনেক লেখককে আমাদের সমাজে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে ইডিপাসের অনুবাদের কথা বলে; এটি হয়ে উঠেছে সৈয়দ আলী আহসানের নাটক। অত্যন্ত জনপ্রিয় এই গ্রীক নাটককে বাংলাদেশে জনপ্রিয় ও বহুল পঠিত করেছেন সৈয়দ আলী আহসান। ‘ইকবালের কবিতা’ (১৯৫২), ‘প্রেমের কবিতা’ (যুগ্মভাবে ১৯৫৮), ‘হুইটম্যানের কবিতা’ (১৯৬৫), ‘ইডিপাস’ (১৯৬৮), ‘সাম্প্রতিক জার্মান গল্প’ (১৯৭০), ‘জার্মান সাহিত্য একটি নিদর্শনী’ (১৯৭৪), উইলিয়াম মেরিডিথের ‘নির্বাচিত কবিতা’ (১৯৮২), ‘সন্দেশ রাসক’ (১৯৮৭), ‘নাহজুল বালাঘা’ (১৯৮৮) প্রভৃতি তাঁর অনুবাদ।
সৈয়দ শামসুল হক
সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) অনুবাদে দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি সৃজনশীল অনুবাদ করেছেন। নাটক ও উপন্যাসের অনুবাদ করে তিনি বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। সৈয়দ হকের ম্যাকবেথের অনুবাদ অনেকটা আড়ষ্ট মনে হলেও ‘শ্রাবণ রাজা’র চমৎকার অনুবাদ পাঠক মহলে গৃহীত হয়েছে। ‘ম্যাকবেথ’, ‘টেমপেস্ট’ (১৯৮৮), ‘শ্রাবণ রাজা’ (১৯৬৯), ‘গোলাপের বনে দীর্ঘশ্বাস’ (২০০০) প্রভৃতি তাঁর অনুবাদকর্ম।
হাবীবুর রাহমান
শিশুসাহিত্যিক, শিশুদের জন্য অনুবাদ করেছেন। ‘চীনা প্রেমের গল্প’ (১৯৬৩), ‘জন কেনেডী’ (১৯৬২), ‘জীবনের জয়গান’ (১৯৬২), ‘পাল তুলে দাও’ (১৯৬১) এসব অনুবাদে তিনি সাবলীল। শিশু মনস্তত্ত্বের বিষয়টি লেখক বিবেচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর ভাষা সরল এবং রসসমৃদ্ধ। গল্পগুলো বাইরের হলেও এদেশীয় আবহে তা করে তুলেছেন তাৎপর্যময়। শিশুসাহিত্যে এ গ্রন্থগুলো প্রয়োজনীয় সংযোজন।


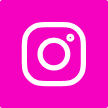






Leave a Reply