ভাগবতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক মালাধর বসুর কৃতিত্ব আলোচনা কর।
শ্রীকৃষ্ণবিজয়: মালাধর বসু
তুর্কি আক্রমণের পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সমাজ-পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আরো নির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, বাংলাদেশের ওপর এক বিরাট আঘাত নেমে এল; অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হল। বাংলার ভাগ্যাকাশে এক গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি নেমে এল। প্রায় মানবশূন্য হয়ে পড়ল বাংলা। অবশিষ্টাংশ মানুষজন বাঁচার তাগিদে পাশ্ববর্তী নিরাপদ জায়গায় চলে গেলেন। যারা রইলেন তাদেরকে অনেক নির্যাতন সহ্য করে থাকতে হল। এমন বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে বাঙালিকে নতুন আশার আলো দেখানোর মতো কেউ রইলেন না। বাস্তবে কোন যুগনায়ককে তখনো পর্যন্ত দেখা না গেলেও চিন্তাশীল লেখকের কলম সেই মুক্তিকামী নেতার সন্ধান দিতে চাইলো।
বোধহয় সেই তাগিদ থেকে শুরু রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ। রামচন্দ্র, কৃষ্ণ—নায়ক হয়ে উঠে আসলো। শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে বলেছেন— ‘‘বাঙলাদেশে তখন বিদেশী বিধর্মী এক ভিন্ন জাতির শাসনকর্তা বর্তমান, জাতির জাগরণের জন্য তাই এমন এক মহান আদর্শ পুরুষের চিত্র উপস্থাপনা দরকার, যিনি সর্বতোভাবে জাতির জীবনে প্রেরণা জোগাতে পারবেন। এ বিষয়ে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাতে সন্দেহ কি?” (সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়: আদি ও মধ্য) কাজেই কবি মালাধর বসু যে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ভাগবতের অনুবাদ করেছেন অনুমেয়। আর কৃষ্ণকথার জন্য ভাগবত পুরাণই শ্রেষ্ঠ। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রন্থটিকেই মালাধর অনুবাদের জন্য বেছে নেন। কৃষ্ণের মত জাতীয় নায়ক, তাঁর কথা, আদর্শকে বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাইলেন তিনি। এ উদ্দেশ্য আরো স্পষ্ট হয় যখন দেখা গেল তিনি সমগ্র ভাগবত অনুবাদ করলেন না, বারোটি স্কন্ধে অসম্পূর্ণ ভাগবতের মাত্র দুটি স্কন্ধ— দশম, একাদশ অনুবাদ করলেন। এই দুটি স্কন্ধেই মূলত কৃষ্ণকাহিনী বর্ণিত হয়েছে কৃষ্ণলীলার আকারে। ফলে কৃষ্ণকাহিনী বেছে নেওয়ার কারণ আরো নিদিষ্ট হল এই স্কন্ধ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে।
মালাধর বসুর কাব্য রচনাকাল
শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থটি সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। রাধিকানাথ দত্ত ও কেদারনাথ দত্ত এই সংস্করণ প্রকাশ করেন। এতে কাব্যটির রচনাকাল বিষয়ক একটি শ্লোক আছে, তা হল—
তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥
অর্থাৎ ১৩৯৫ শকাব্দে (১৪৭৩ খ্রিঃ) গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং ১৪০২ শকাব্দে (১৪৮০ খ্রিঃ) গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। আবার এক জায়গায় কবি লেখেন—
গুণ নাই অধম মুই নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।
এখানে একটা সংশয় দেখা দেয় তা হল গৌড়েশ্বরের পরিচয় নিয়ে। কেননা কবি যখন কাব্যরচনা শুরু করেন তখন গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন রুকনুদ্দিন বরবক শাহ (১৪৬০ খ্রিঃ – ১৪৭৪ খ্রিঃ) আর যখন কাব্যটি সমাপ্ত হয় তখন ছিলেন শামস্ উদ্দিন ইউসুফ্ শাহ্ (১৪৭৪ খ্রিঃ – ১৪৮১ খ্রিঃ)। এই দুই গৌড়েশ্বরের মধ্যে কবি কার কাছ থেকে উপাধি পেয়েছিলেন তা নিয়ে দ্বিধা আছে। কেননা কবি ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’-এর শুরু থেকে ‘গুণরাজ খান’ উপাধি ব্যবহার করেছেন। তাতে অনেক সমালোচকের মনে হয়েছে কাব্যারম্ভের পূর্বেই কবি এই উপাধি লাভ করেন। সেক্ষেত্রে রুকনুদ্দিন বরবক শাহেরই সম্ভাবনা দেখা দেয় কবিকে উপাধি প্রদানের।
মালাধর বসুর কবি পরিচিতি
মালাধর বসু বর্ধমান জেলার জামালপুর অন্তর্গত বর্তমান মেমারি রেলস্টেশনের কাছে কুলীন গ্রামে কুলীন কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহন করেন। কাব্যের শুরুতে কবি আত্মপরিচয় দিয়ে লেখেন—
বাপ ভগিরথ মোর মা ইন্দুমতি।
জার পুর্ন্যে হেল মোর নারা অনে মতি।
তার পিতা ভগীরথ, মাতা ইন্দুমতি। তারা মূলত বৈষ্ণব ছিলেন। পিতা-মাতার পুণ্যফলে কবির মনে কৃষ্ণভক্তি সঞ্চারিত হয়। ফলে তিনি এই কাব্য রচনা করেন। এছাড়া তিনি ব্যাসদেবের স্বপ্নাদেশও পান। মালাধর বসু ছিলেন সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর পরিবার তৎকালে বেশ প্রতিপত্তিশীল ছিল। কর্মসূত্রে কবি তৎকালীন রাজধানী (বাংলার) শৌড়ে থাকতেন। অনেকের মতে তিনি ‘ছত্রী’ নামক কোনো সামরিক পদে নিযুক্ত ছিলেন। জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’-এ এই সম্বন্ধে জানা যায়—
গুণরাজ ছত্রী তনয় মহাশয়
নানা মহোৎসব করি।
আর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মালাধর বসুর গ্রামের কথা। কুলীন গ্রামের কুলীন কায়স্থ বংশে তার জন্ম। স্বয়ং চৈতন্যদেব কবির গ্রাম সম্পর্কে তাঁর (কবির) আত্মীয় সত্যরাজ খান ও রামানন্দকে বর্ণনা করেছেন এই বলে—
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর।
কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়।
কুলীন গ্রাম সম্পর্কে চৈতনদেবের ভালোবাসারই প্রকাশ পেয়েছে এখানে।
শ্রীকৃষ্ণবিজয়: নামকরণ
মালাধর বসু রচিত ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যটি একাধিক নামে পরিচিত। ‘গোবিন্দবিজয়’, ‘গোবিন্দমঙ্গল’, এমনকি ‘শ্রীকৃষ্ণবিক্রম’ নামও পাওয়া যায়। তবে কাব্যটির ভূমিকাংশে (বিশ্বভারতী সংগ্রহের পুঁথিতে) ‘কৃষ্ণের বিজয়’ ও ‘গোবিন্দ বিজয়’-ই লেখা আছে। কৃষ্ণের নাম গোবিন্দ বলেই বোধ হয় এমন নামকরণ। ‘গোবিন্দবিজয়’ নামকরণ থাকলেও পরবর্তীতে ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ বলেই কাব্যটি জনপ্রিয় হয়। আবার মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কাব্যটিকে ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ বলেই উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃতম্-এ উল্লেখ আছে, মহাপ্রভু কাব্যটির প্রশংসা করে বলেছেন—
গুণরাজ খান কৈল ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেময়।।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত।।
এবার দেখে নেওয়া যাক ‘বিজয়’ শব্দটি ব্যবহারের পিছনে কী কারণ ছিল। ‘বিজয়’ শব্দটি বৈদিক গোত্রের। ঋকবেদে ‘বিজয়’ শব্দটি ‘জয়’ হিসেবেই ব্যবহৃত। আবার মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যে ‘বিজয়’ শব্দটি ‘অভিযান’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া ‘বিজয়’ শব্দটির অন্যান্য অর্থগুলি হল—‘বিক্রমচরিত্র’ আগমন, গমন ও যাত্রা। আবার কৃষ্ণের জন্ম মুহূর্তটিকে ‘বিজয়’ বলা হয়। ভগবান কৃষ্ণ অভিজিৎ নক্ষত্রে জয়ন্তী রাত্রিতে বিজয় মুহূর্তে জন্মেছিলেন। তবে ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ নামকরণের কারণ হিসেবে বলা হয়—দানবদের অত্যাচারে জর্জরিত এক চরম দুর্দিনে দৈত্যদের পরাভূত করার জন্যই কৃষ্ণের আর্বিভাব। তাই সেই দিক থেকে কৃষ্ণ চরিত্রের উৎকর্ষ, ঐশ্বর্য সমারোহ, বীরত্ব, বীর্যবত্তা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল কবির মূল লক্ষ্য। তাই ‘গোবিন্দ বিজয়’ বা ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ নামকরণ করা। এই নামকরণ সেই দিক থেকে সার্থক।
শ্রীকৃষ্ণবিজয়: শ্রেণিবিচার
শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রচারক ভাগবত পুরাণ আঠারোটি পুরাণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় গ্রন্থ। তাছাড়া বৈষ্ণবরা এই গ্রন্থটিকে তাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকার করেন। এই গ্রন্থ অবলম্বনেই মালাধর বসু বা গুণরাজ খান ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অনুবাদ করে রচনা করেন ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’। তবে কাব্যটি ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়। তিনি নিজেই জানিয়েছেন পণ্ডিতদের মুখে শুনে বা কথকঠাকুরের মুখে শুনে তার অর্থ তিনি পয়ারে বেঁধে রচনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি ভাগবতের ভাবানুবাদ করেছেন। এটি অনুবাদ কাব্য শাখার অন্তর্গত।
কাব্যটির মধ্যে আবার আখ্যান কাব্যের রূপ লক্ষ করা যায়। কারণ কাব্যটিতে বিভিন্ন কাব্য থেকে যেমন শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি থেকে উপাখ্যান সংগ্রহ করে সংযুক্ত করা হয়েছে। কাব্যটিকে গীতিকার শ্রেণিভুক্তকরা যায় কিনা তা দেখে নেওয়া যেতে পারে৷ গীতিকা মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত কিন্তু ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ লিখিত সাহিত্য। গীতিকা মূলত গাওয়ার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। তা অল্পকালের মধ্যেই প্রচারিত হয়েছিল। কেননা তা আঞ্চলিক ভাষায় প্রচারিত। তার জনপ্রিয়তাও কম ছিল। কিন্তু ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’-এ আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়নি। এর জনপ্রিয়তাও বেশি ছিল। কাজেই একে গীতিকা গোত্রীয় কাব্য বলে চলে না।
কাব্যটি লোকসাহিত্যের অন্তর্গতও নয়। তবে এতে লোককথার কিছু উপাদান আছে। কিন্তু লোক সাহিত্যের মূল ধারার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। লোকসাহিত্য মূলত মৌখিক, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর কোনো নির্দিষ্ট লেখক পাওয়া যায় না। ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ তেমন নয়। লোককথার মধ্যে অলৌকিকতা বিরাজমান। এই কাব্যে কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত, তাঁর বিভিন্ন অসুরকে বধ করার মাধ্যমে অলৌকিকতা আছে। কিম্বা পুনর্জীবন প্রাপ্তি ইত্যাদি কাব্যের মধ্যে আছে। আসলে লোককথা কোথাও কোথাও কবিকে প্রভাবিত করেছে। সামগ্রিকভাবে লোকসাহিত্যের বিষয় নিয়ে ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ বিজয় প্রকাশিত হয়নি। কাজেই তা লোকসাহিত্যের অন্তর্গত নয়। তাছাড়া মহাকাব্যগুলিতে এমন বর্ণনার পরিচয় পাওয়া যায়। মালাধর বসু তা কোথাও কোথাও অনুসরণ করেছেন মাত্র।
এবার দেখে নেওয়া যাক মঙ্গলকাব্যের কী কী বৈশিষ্ট্য ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে’র মধ্যে লক্ষ করা যায়। ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ শুরু হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা দিয়ে। এরপর নারায়ণের বাইশ অবতারের বন্দনা করা হয়েছে। গনেশ বন্দনা আছে। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বন্দনা আছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে আলাদা দেবদেবীর বন্দনা আছে। তবে মালাধর বসুর কাব্যে লৌকিক দেবদেবীর কথা নেই। তাই দেব-দেবী বন্দনার ক্ষেত্রে দুটি কাব্যের মধ্যে তফাৎ আছে। এছাড়া মঙ্গলকাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল— আত্মপরিচয় ও গ্রন্থোৎপত্তির কারণ। এখানে কবির আত্মপরিচয় থাকে বিস্তৃতভাবে। এমনকি নানা সমস্যা, সেখান থেকে উত্তরণ, আশ্রয়দাতা, পৃষ্ঠপোষকের বিশদ্ বিবরণ আত্মপরিচয় অংশে থাকে। কিন্তু মালাধর বসু এখানে কেবলমাত্র বাসস্থান ও নিজ পিতামাতার নামোল্লেখ করেছেন—
বাপ ভগিরথ মোর মা ইন্দুমতি।
জার পুণ্যে হেল মোর নারাঅনে মতি।।
কাজেই এক্ষেত্রেও বিশেষ মিল নেই। এছাড়া ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে’ মঙ্গলকাব্যের মতো বারমাস্যার বর্ণনা নেই, নেই চৌতিশা, বিবাহ আচারের নিখুঁত চিত্রণ নেই। তাই ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’কে ‘গোবিন্দমঙ্গল’, বলা হলে ও কাব্যের সঙ্গে তার মিল খুব কমই। মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্যও বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’-এ।
আবার আর একটি মতামত উঠে আসে ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ সম্বন্ধে। কাব্যটিকে ‘গোবিন্দবিজয়’ও বলা হয়। নামের শেষে এই যে ‘বিজয়’ শব্দটি আছে বলে অনেকে এটিকে ‘বিজয়কাব্য’ বলতে চান। তবে মঙ্গলকাব্য ধারার মতো বিজয়কাব্যনামে কোন স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হয়নি মধ্য যুগে। মধ্য যুগের প্রায় প্রতিটি কাব্যেই এই ‘বিজয়’ শব্দটি ব্যবহার করার চল ছিল। যেমন মনসামঙ্গল ধারায় মনসাবিজয় সৃষ্টি হয়নি, তাই একে ‘বিজয়কাব্য’ বলা যায় না।
তাহলে ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কি মহাকাব্যগোত্রীয়? কারণ মহাকাব্যের অনেক বৈশিষ্ট্য ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’-এ লক্ষ করা যায়। মহাকাব্যগুলি মূলত বীরগাধা। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি স্থান পেয়েছে। ঘটনার প্রয়োজনে কংস, জরাসন্ধ, বাণরাজা প্রমুখদের বীরত্বের কাহিনী যুক্ত হয়েছে। ফলে প্রাচীন মহাকাব্য বা জাতমহাকাব্যের মত ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ বীররসাত্মক কাব্য হয়ে উঠেছে।
মহাকাব্যের পটভূমি হয় স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল বিস্তারী। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ও ত্রিভুবনবিস্তৃত। মহাকাব্যের নায়ককে হতে হবে ধীরোদাত্ত। এই কাব্যের নায়ক কৃষ্ণও তাই। মহাকাব্যের নায়কোচিত সকল গুণই তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান। এসব দিক দিয়ে ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ Epic of Art বা Literary Epic-এর কাছাকাছি আসতে পেরেছে। এবার আমরা গুণরাজ খানের নিজের লেখা শ্লোক দিয়ে বিশ্লেষন করতে চেষ্টা করব। কাব্যের একবারে শুরুতে গ্রন্থের বিষয় নির্দেশ” শীর্ষক অংশে তিনি লিখছেন—
ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া।।
আর কাব্যের একদম শেষে ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাঠের ফলশ্রুতি’ শীর্ষক অংশে তিনি লিখেছেন—
অনেক আছএ সাস্ত্র ভারথ পুরানে।
বিস্তর করিল তাহে কৃষ্ণের বাখানে।।
সাধারণ লোক তাহা না পারে বুঝিতে।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলুঁ কৃষ্ণের চরিতএ।।
আমরা এই দুটি অংশে উল্লেখিত একটি বিশেষ শব্দের ওপর জোর দিতে চাই, তা হল— ‘পাঁচালি’ তা হলে কী? ‘পাঁচালি’ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত শব্দ ‘পঞ্চালী’ থেকে। এর আভিধানিক অর্থ পাঞ্চালি রীতির গীতবিশেষ। আবার ব্রতকথার পদ্যরূপকেও ‘পাঁচালী’ বলা হয়। এর অর্থ হল কোনও বিশেষ ছন্দোরীতিতে রচিত দেবমাহাত্ম্যমূলক ব্রতকথা।
কৃত্তিবাসী রামায়ণের নাম ‘শ্রীরাম পাঁচালী’ যা কিনা পয়ার ছন্দে রচিত। কাশীদাসী মহাভারত পয়ারে রচিত। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী পয়ার ও ত্রিপদীতে রচিত গীতকে ‘পাঁচালী’ বা ‘পাঞ্চালিকা’ বলেছেন। উল্লেখ্য পুরাণ পাঞ্চালী কাব্যের দুটি ভাগ নাটগীতি ও আখ্যায়িকা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—
বড়ুচণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ নাটগীতি আর মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ আখ্যায়িকা। ‘পাঁচালী’ শব্দটি মধ্য যুগের কাব্যে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। যেকোনো কাব্যকে মূলত মধ্যযুগে পাঁচালি হিসেবে গণ্য করা হতো। পাঁচালি প্রধানত ছন্দোরীতির নাম। পরবর্তীতে এই পাঁচালী কাব্যের রূপান্তর ঘটে। তার পরিচয় পাওয়া যায় ‘লক্ষ্মীর পাঁচালী’, ‘শনির পাঁচালী’ ইত্যাদি লেখাতে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দাশরথি রায়ের ‘পাঁচালী’ও পাঁচালির পরিবর্তিত রূপ।
যাইহোক কবি ‘পাঁচালী’ শব্দটি বোধহয় বিশেষ ভাবধারাকে বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া মালাধর বসু যখন কাব্যরচনা করেন তাঁর সামনে কোন আদর্শ রচনারীতি ছিল না। তিনিই একটি নতুন আদর্শ তৈরী করলেন; তাঁর হাতেই বাংলা পাঁচালি কাব্যের সূত্রপাত ঘটল।
মালাধর বসুর কবি-কৃতিত্ব
মালাধর বসু প্রথমে ভক্ত, পরে কবি। তাই কৃষ্ণের বীরগাথামূলককাব্য ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যে বিশুদ্ধ ভক্তিভাবের প্রাবল্য লক্ষ করা যায়। তবে সে ভক্তি ভাগবতে বর্ণিত বৈধী ভক্তি নয়; শাস্ত্রীয় ভক্তি। ফলে কাব্যটি হয়েছে ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবানের ঐশ্বর্য বর্ণনাত্মক কাব্য। মালাধর বসুর কবিকৃতিত্ব বিষয়ে আলোকপাত করতে গেলে সবার আগে চৈতন্যদেবের কথা বলতে হয়। চৈতন্য মহাপ্রভু কবির কাব্যপাঠে বিশেষ অনুরক্ত হয়ে, কাব্যটি সম্পর্কে উচ্ছ্বাসময় প্রশংসা করেছিলেন। কৃষ্ণ সম্পর্কে কবির লেখা ‘নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ’ এই ছত্রটি চৈতন্যদেবকে আপ্লুত করেছিল। শুধু তাই নয় মালাধর বসুর কাব্যের রসাস্বাদন করে গুণমুদ্ধ মহাপ্রভু কবির বংশকেও সাদরে অঙ্গীকার করেছিলেন। এ সম্পর্কিত শ্লোক কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্’-এ আছে—
গুণরাজ খান কৈল ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত।
“তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর৷৷
শ্রীচৈতন্যদেব যাঁর লেখা কাব্য পাঠে বিগলিত হন, তাঁর কবিত্ব নিশ্চয়ই উচ্চপর্যায়ের একথা ধরেই নেওয়া যায়। নইলে মহাপ্রভু কেন এত প্রশংসা করবেন। এর উত্তর কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেই দিয়েছেন। ‘ঐ নন্দের নন্দন’ …ইত্যাদি বাক্যটি মহাপ্রভুর হৃদয়কে হরণ করেছিল। সে কারণেই তিনি এত উচ্ছ্বাস দেখিয়েছেন। চৈতন্যদেব যে আগ্রহ নিয়ে জয়দেব, বিদ্যাপতি পড়তেন, মালাধর বসুর কাব্যে তাঁর তেমন কোন আসক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।
কবি যদি ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করতেন, তাহলে তাঁর কবিত্ব নিয়ে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ নামে অনুবাদ হলেও তা আসলে কবির মৌলিক রচনা। তাই কাব্যের উৎকর্ষক-অপকর্ষের দায়িত্বও কবিরই। আমরা আগেই বলেছি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই কবি কাব্যটি রচনা করেছিলেন। তাই যে অংশ কবির উদ্দেশ্যে পূরণের সহায়ক হতে পারে সেই অংশটুকুই তিনি গ্রহণ করেছেন। বোধকরি সে কারণেই তিনি মূল ভাগবতের অলংকার বাহুল্যকে বর্জন করেছেন। তবে তার অর্থ এই নয় যে, মালাধর বসুর কবিত্ব উৎকর্ষতায় উন্নীত হয়নি। কাব্যের নানা জায়গায় তাঁর কবিত্ব চরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়েছে। তাঁর কবিত্বের সবচেয়ে বড়দিক হল তাঁর উচ্ছ্বাসহীন সংযম। আবার অনেক জায়গাতেই তাঁর ভক্তি ভাবুকতার প্রকাশও ঘটেছে। যুগের প্রয়োজনে কৃষ্ণের বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে ভগ্নহৃদয় বাঙালির জীবনে আদর্শ স্থাপন করাই ছিল কবির উদ্দেশ্য। এ কাজ যে খুবই দুরূহ তা তিনি অত্যন্ত কবিত্বময় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—
আকাসের তারা জদি একে একে গনি।
সমুদ্রের জল জদি ঘটে পরমানি।।
পৃথুরির রেণু জদি করিএ গণন।
তবুও বলিতে নারি কৃষ্ণের করণ।।
অর্থাৎ আকাশের তারা যদিও বা গোনা যায়, সমুদ্রের জল ঘটে করে যদিও বা পরিমাণ করা যায়, পৃথিবীর ধুলিকণাও বুঝি গোনা সম্ভব কিন্তু কৃষ্ণের কীর্তি বর্ণনা করা সহজ নয়।
মালাধর বসুর সময়কালে কাব্যে রসের ও রুচির বিকার ঘটলেও সমাজে তা নিন্দার হত না। কেননা সে সময় তেমনি সাহিত্যই রচিত হত, বিশেষ করে ধামালী সাহিত্যে তো হতোই।সেই সময়ে একটি বৃহৎ কাব্য রচনা করে তিনি রস ও রুচির ক্ষেত্রে যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো কবির ধর্মসহিষ্ণু মনোভাব। ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ বৈষ্ণবদের ধর্মীয় গ্রন্থ। পরবর্তীকালে রচিত ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত’-এ যে পরিমাণ পরধর্ম বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে তা ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’-এ একবারেই নেই।
বাঙালি জাতি আরো একটি কারণে মালাধর বসুর কাছে ঋণী। তা হল তাঁর কাব্যের বাঙালিয়ানা। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতো এই কাব্যেও কবি বাঙালি জীবনের চিত্রই তুলে ধরেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাঙালি কবি মালাধরের হাতে বাঙালি রূপেই চিত্রিত হয়েছেন।


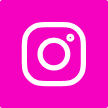









Leave a Reply