রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে যাত্রাপালার ভূমিকা আলোচনা কর।
যাত্রা
চারিদিকে দর্শক বসেছে। মাঝখানে একটুখানি খোলা জায়গায়, দর্শক সহজে দেখতে পায়, এমনভাবে কিছুটা উচু করে চৌকোণা প্লাটফর্ম তৈরি হয়েছে। সেখানেই চলেছে অভিনয়। একদিক দিয়ে নেমে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দর্শকের মাঝখানে একচিলতে সরু পথ দিয়ে গ্রীণরুমে ফিরে যাচ্ছে। গ্রীণরুম মানে যাহোক করে ঘেরা খানিকটা জায়গা। সেখানেই চলে মেকআপ, সাজসজ্জা এবং বিশ্রাম। মঞ্চের পাশেই বাজনদারের দল বাজনা বাজায়। স্মারক (প্রম্পটার) আরেকদিকে বসে পাত্রপাত্রীর ভূমিকা ও সংলাপ স্মরণ করিয়ে দেয়। খোলামঞ্চে, উন্মুক্ত আসরে অভিনয় চলে। কোনো দৃশ্যপট বা সেট-সেটিংস নেই। প্রয়োজনে একটি চেয়ার বা কয়েকটি বসবার জায়গা। ঐ চেয়ার ময়ুর সিংহাসন থেকে কনিষ্ঠ কেরানীর চেয়ার সবই হতে পারে।
গ্রীণরুম থেকে বেরিয়ে পাত্রপাত্রীরা দর্শকের মাঝখান দিয়েই এসে মঞ্চে উঠে অভিনয় করে। মঞ্চ আলোকিত করা হয়, যে যুগের যেমন আলোর ব্যবস্থা সেইভাবে।
যাত্রার এই মঞ্চব্যবস্থা এখনো চলে। খোলামঞ্চে খোলা আসরে যাত্রার অভিনয় চলে। শুধু যুগের ও বিজ্ঞানের উন্নতি ও পরিবর্তনের ফলে টেকনোলজির ব্যবহার বেড়ে গেছে। নাহলে, অভিনয় ও প্রয়োগপদ্ধতি দীর্ঘদিন একই রয়ে গেছে।
এই যাত্রাভিনয়ের ইতিহাস বিস্তৃত হয়েছে যুগে যুগে। নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান ধারা ইতিহাসেরই পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে। সেই ইতিহাস আলোচনা করা যেতে পারে।
ধর্মীয় উৎসবের নানা শোভাযাত্রায় নৃত্যগীত যোগে দেবমাহাত্ম্য প্রকাশ করা হত। দেব উৎসবে নৃত্যগীত ও শোভাযাত্রা থেকেই যাত্রার উদ্ভব হয়েছে। সংস্কৃত অভিধানে উৎসব অর্থেই ‘যাত্রা’ শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে যা-ধাতু থেকে উৎপন্ন বলে এর মধ্যে যাওয়ার ব্যাপারটি রয়েছে। এই ‘গমন’ উপলক্ষেই উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হত বলে কালক্রমে উৎসব অর্থেই ‘যাত্রা’ শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে দেবমাহাত্ম্য শুধুমাত্র শোভাযাত্রায় নয়, একই স্থানে বসেই সবাই উপভোগ করত। ক্রমে দেবপরিক্রমা বন্ধ হল, কিন্তু এই ধরনের ধর্মানুষ্ঠান ‘যাত্রা’ নামেই প্রচলিত হল। কালক্রমে, এইরকম ধর্মোৎসবে নৃত্যগীতের সঙ্গে অভিনয়ের উপাদানগুলি যুক্ত হতে থাকে। এইভাবে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেবদেবীর কাহিনীকে নৃত্যগীত-সংলাপ এবং অভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শন করাকেই ‘যাত্রা’ বলা হয়ে থাকে।
এই ‘গমন’ বিষয়ে নানামত দেখা যায়। সূর্যের গমনাগমনের ওপর কৃষিজীবন যেমন নির্ভর করতো, তেমনি তাকে কেন্দ্র করেই নানা উৎসব হতো। সূর্যের প্রধান দুই গমন—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ। দক্ষিণায়ণকে কেন্দ্র করে পূর্বভারতে রথযাত্রা উৎসব এবং সূর্যের বিষুবরেখায় অবস্থানকে কেন্দ্র করে চড়ক-উৎসব। মধ্য যুগে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার এবং ষোড়শ শতক থেকে চৈতন্য প্রভাবে তার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। ফলে কৃষ্ণকে উপলক্ষ করে ‘কৃষ্ণযাত্রা’ গড়ে ওঠে। সূর্যের স্থান সেখানে কৃষ্ণ নিয়েছে, দ্বাদশ রাশি রূপান্তরিত হয়েছে দ্বাদশ গোপিনীতে। এইভাবে দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা। রথযাত্রায় সূর্যের জায়গায় কৃষ্ণ, পরে জগন্নাথ। সূর্য কখনো কখনো শিবঠাকুরও হয়েছেন।
দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়ভাষীদের ‘মারী-আম্মা’র বাৎসরিক পূজানুষ্ঠানকে ‘মারী যাত্রা’ বলে। মৎস্যজীবীদের নৈমিত্তিক পূজানুষ্ঠানকে ‘যাত্রে’ বলে। উড়িষ্যায় গাজনের মতো অনুষ্ঠানকে বলে ‘সাহীযাত্রা’। উড়িয়া ভাষায় মেলা অর্থে ‘যাত’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সাঁওতালদের মধ্যে ‘যাত্রাপরব’, দ্রাবিড়ভাষী ওঁরাওদের মধ্যে ‘ওঁরাওযাত্রা’ প্রচলিত রয়েছে।
পাঁচালী থেকে যাত্রার উদ্ভব হয়েছে বলেও কেউ কেউ মনে করেছেন। প্রাচীন পাঁচালীর রূপ জানা নেই। মধ্য যুগে আখ্যানমূলক রচনাকেই বলত পাঁচালী। রাম পাঁচালী, শনির পাঁচালী। উনিশ শতকের সমসাময়িক হাফ-আখড়াই, দাঁড়া-কবি এবং নতুন যাত্রার প্রভাবে নতুন পাঁচালী তৈরি হয়েছে। মঙ্গল গান কিংবা শাক্তবিষয়ক গানও প্রচলিত ছিল কৃষ্ণ-বিষয়ের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে। বেহুলা লখিন্দরকে নিয়ে গান হতো। উনিশ শতকে ‘ভাসানযাত্রা’ এখান থেকে এসেছে। পাঁচালী থেকেই যাত্রার উৎপত্তি এই মতকে পরবর্তীকালে কেউ গ্রহণ করেননি। তবে পাঁচালীর পাঁচটি অঙ্গ (পা-চালি, নাচাড়ি, বৈঠকি, ভাব কালি ও দাঁড়া-কবি) একজন গায়কের পক্ষে সবসময়ে করা সম্ভব হয়নি বলে, গান ও ছড়া অংশে অন্য সহায়ক নেওয়া হতো। পরে এই সহায়ক সংখ্যা বেড়ে যায়। অনেকটা যাত্রার গান ও অভিনয় অংশের মতো হয়ে পড়ে। সেখানেই যাত্রার সঙ্গে পাঁচালীর সাদৃশ্য মেলে।
কারো কারো মতে নাটগীত থেকে যাত্রার উদ্ভব ঘটেছে। মধ্য যুগের বাংলায় যাত্রা বলতে দেবোৎসবই বোঝাত। এই উৎসব উপলক্ষে নৃত্যগীত হত বলে একে ‘নাটগীত’ বলা হত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ওই ধরনের নাটগীত। যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে এই নাটগীত হতো বলে ক্রমে এই নাটগীতকেই যাত্রা বলা হতো।
মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে অভিনয় অর্থে ‘যাত্রা’ শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না। উৎসব অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। চৈতন্যভাগবতেও তার উল্লেখ রয়েছে—‘অঙ্কের বিধানে নৃত’। গীতগোবিন্দে নৃত্যগীত রয়েছে, রাগ-তালের নির্দেশ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা-কৃষ্ণ-বড়াই—তিনটি চরিত্রের কথোপকথনের এবং নৃত্যগীতের মধ্যে বেশ নাটকীয়ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এগুলির মধ্যে প্রাচীন ও মধ্য যুগের নাটগীত বা যাত্রার ধরনটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।
একথা ঠিক, প্রাচীনকাল থেকেই যাত্রার মতো একটি লৌকিক নাটক (Folk Draina) এদেশে প্রচলিত ছিল। মধ্য যুগে তাকেই নাটগীত বলত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও একটি প্রচলিত লোক-নাট্যের ধারাকে সংস্কার করে আদর্শরূপ দেবার চেষ্টা রয়েছে। ভরতের নির্দেশিত নূতন রূপ সমাজের উচ্চতর লোকের মধ্যে গৃহীত ও প্রচলিত হয়। নিম্নস্তরে প্রাচীন লোকনাট্যের ধারাটি প্রবাহিত হতে থাকে। সারা ভারতে এক এক অঞ্চলে এক এক রূপে প্রচলিত হয়। পূর্ব-ভারতে এই ধারা সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করে। তাই ক্রমে জয়দেবের গীতগোবিন্দে কিংবা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পরিচিত হয়েছে।
ধর্মের বিষয়বস্তুই যাত্রার অবলম্বন। তার মধ্যে বিশেষ করে মধ্য যুগে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। কালক্রমে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গলের বিষয়বস্তু নিয়েও রাসযাত্রা, ভাসানযাত্রা তৈরি হতে থাকে।
মধ্য যুগে চৈতন্যদেবের অভিনয়ের খবর পাওয়া যায়। তাতে যাত্রার ধরনটিও লক্ষ করা যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ উপেক্ষা করে চৈতন্য খোলামঞ্চে যাত্রার মতো অভিনয় করতেন। বোঝা যায়, চৈতন্যদেব এই অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর ধর্মভাব প্রচারের জন্য জনসংযোগের সুযোগ নিয়েছিলেন। বৃহত্তর জনগণের কাছে যাওয়ার অভিপ্রায়েই চৈতন্য গৃহবন্দি মঞ্চব্যবস্থাকে সরিয়ে রেখে খোলামঞ্চে অভিনয় করেছিলেন।
চৈতন্যদেবের অভিনয়ের খবর তাঁর জীবনী গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায়। নদীয়ায় তিনি রুক্মিণীহরণ ও ব্রজলীলা অভিনয় করেন। নীলাচলে অভিনয় করেন ব্রজলীলা ও রাবণবধ পালা। এই অভিনয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে বলা যায়—
- খোলা জায়গায়, উন্মুক্ত মঞ্চে অভিনয় হত।
- পালা তৈরি করা থাকতো না, পালার সূত্রটি ঠিক করা থাকতো।
- গান বাঁধা থাকতো।
- উপস্থিত মতো বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কিছু সংলাপ মিলিয়ে পাত্রপাত্রী নৃত্য ও ভাবভঙ্গি সহযোগে অভিনয় করতো।
- সব চরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করতো।
- বৃদ্ধ-বৃদ্ধা চরিত্র হাস্যরস সৃষ্টির জন্য থাকতো।
- সাজসজ্জা করা হতো।
- দোহার থাকতো।
- প্রবেশ-প্রস্থান ছিল।
- সংলাপ ও নৃত্যগীত থাকতো।
- ভক্তিভাবের ধর্মীয়আবেশ পালাটিকে ঘিরে রাখতো।
চৈতন্যদেবের অভিনয়ের প্রভাবে সে যুগে অনেক যাত্রাপালা লিখিত হয়। কবি কর্ণপুর, রায় রামানন্দ, রূপগোস্বামী, দেবীনন্দন সিংহ প্রভৃতির পালাগুলি উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে অনেকগুলি সংস্কৃত নাটক ও পালা বাংলায় অনুবাদ হয়। অভিনীত হয়ে সেগুলি প্রচার লাভও করেছিল। লোচনদাস অনুবাদ করেন রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটকের, যদুনন্দন দাস করেন রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব, পুরুষোত্তম মিশ্রের চৈতন্যচন্দ্রোদয় (কর্ণপুর)। বৈষ্ণবধর্ম ও পদাবলীর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণযাত্রারও প্রসার লাভ ঘটতে থাকে।
মধ্য যুগে পালরাজাদের কাহিনী নিয়েও যাত্রাপালা লেখা হয়। তাছাড়া রাধাকৃষ্ণ পালার প্রাধান্য সত্ত্বেও অন্য ধর্ম ও কাহিনী নিয়েও পালা লেখা হয়। চণ্ডী-মনসা প্রভৃতি শাক্ত কাহিনী, ধর্মমঙ্গল কাহিনী, গোপীচন্দ্র কাহিনী, গোরক্ষনাথ কাহিনী নিয়েও পালা লেখা হয়। তবে অষ্টাদশ শতক অবধি লিখিত কোনো যাত্রাপালার পরিচয় পাওয়া যায়নি।
অষ্টাদশ শতক বাংলার ইতিহাসের পালাবদলের কাল। মোঘল শাসনের অবসান, নবাবী আমলের শুরু। শাসন নেই, নিরাপত্তা নেই, রয়েছে খাদ্যাভাব—সে এক দুঃস্বপ্নের সময়। তার ওপর বর্গীর হাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষ। বিপর্যস্ত জনজীবনের মাঝে এলো ইংরেজ। ১৭৫৭-এর পলাশীর যুদ্ধ। বিজয়ী ইংরেজ শাসনব্যবস্থা শক্ত করলেও, শোষণ ও অত্যাচার হলো আরো নির্মম ও গভীরতর। পলাশীর যুদ্ধের তের বছরের মধ্যে ঘটে গেল মর্মান্তিক ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।
ক্ৰমে গ্রামবাংলাকে বিপর্যস্ত করে নগর কলকাতা গড়ে উঠছে। কলকাতায় ইংরেজের সাহচর্যে প্রচুর মানুষ ধনী হয়ে উঠলো। সামাজিক প্রতিষ্ঠা না হলেও এই ‘হঠাৎ নবাবের দল’ তখন রঙীন জীবনে ভরপুর। শিক্ষা নেই, রুচি নেই, পুরনো সমাজবন্ধন নেই, ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নেই—অথচ অর্থ আছে, আছে জীবন উপভোগের তাড়না। এদের নাগর-পৃষ্ঠপোষকতাতেই গড়ে উঠেছে কবিগান, খেউড় গান, হাফ-আখড়াই গান। সে এক রুচি ও ঐতিহ্যহীনতার স্বৈরাচার চলেছে বাঙালি সংস্কৃতির ওপর। কৃষ্ণযাত্রাও এই প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি—যাত্রাও নিম্নরুচি লাভ করে। অসুস্থ নগরজীবনের মানসিকতায় যাত্রার মধ্যেও কুরুচি এসে গেল। নারদ, ব্যাসদেব চরিত্রকে দিয়ে ভাড়ামো সৃষ্টি, অশ্লীলতার বাড়াবাড়ি, আদিরসের প্রাবল্য—যাত্রাপালাগুলিকে কদর্য করে তুলল। এই সময়েই কৃষ্ণযাত্রার ভক্তিরস তরল উচ্ছ্বাস ও খিস্তি-খেউড়ে ভেসে গেল। এই সময়েই কৃষ্ণযাত্রার নাম হয়ে গেল কালীয়দমন যাত্রা।
উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের যুগ। বিশেষ করে নগরকেন্দ্রিক নবজাগ্রত বাঙালি নতুন যুগের ভাবনায় জীবন গড়তে চলেছে। ভাবজগতের পরিবর্তনের ফলে অষ্টাদশ শতকে যেগুলি সাদরে গৃহীত হয়েছিল, উনিশ শতকের নবজাগ্রত চেতনায় সেগুলিও বাতিল হতে লাগলো। রুচিহীন যাত্রাও এই সময়ে শিক্ষিত জনসমাজে অনাদৃত হয়ে পড়ল। ‘যাত্রা দেখে ফাতরা লোকে’ এইরকম কথা শিক্ষিত বাঙালির দিক থেকেই চালু হয়।
এই নতুন যুগে অনাদৃত যাত্রাকে সংস্কৃত ও পাংক্তেয় করে তোলার চেষ্টা শুরু হল। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকেই সেই প্রয়াস লক্ষ করা গেল। সংস্কারের কাজে এগিয়ে এলেন শিবরাম, শ্রীদামদাস, সুবলদাস অধিকারী এবং পরমানন্দ অধিকারী। শিবরাম যে চেষ্টা শুরু করেছিলেন শ্রীদাম-সুবল ও তাঁর শিষ্য পরমানন্দের মধ্যেই তা প্রবলরূপে দেখা দিল। এরা প্রত্যেকেই কালীয়দমন যাত্রা অভিনয় করতেন। শ্রীদাম-সুবল যাত্রা পালায় অভিনয় ও সঙ্গীতকে উন্নত করলেন। পরমানন্দেরও নিজের দল ছিল। সেখানে অভিনয়েও তিনি কিছু পরিবর্তন করলেন। তার লেখা ‘কালীয়দমন যাত্রা’য় তিনিই প্রথম প্রচলিত যাত্রার মধ্যে বৈচিত্র্যহীন বৈষ্ণবগীতির যে প্রাবল্য ছিল, তার পরিবর্তে নাটিক ক্রিয়া এবং সংলাপ ব্যবহার করেন। যদিও ভক্তিরস, আদিরস ও ভাড়ামো তখনো যাত্রার প্রধান আকর্ষক বস্তু ছিল।
উনিশ শতকের প্রথম দিকে লোচন অধিকারী (তার পালার নাম: অক্রুর সংবাদ, নিমাই সন্ন্যাস), বদন অধিকারী (মান, দান, মাথুর-পালা) গোবিন্দ অধিকারী (কৃষ্ণযাত্রা, কালীয়দমন যাত্রা, কৃষ্ণকালী, মুক্তাবলী) প্রভৃতি পালাকারেরা গতানুগতিক যাত্রার ঢঙ ও রীতি কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের নিদর্শন রেখেছেন। সেইযুগে এরা খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। সমকালীন মধুসূদন কান (মধু-কান)-এর ঢপকীর্তন, অক্রুর সংবাদ, কলঙ্কভঞ্জন প্রভৃতি দর্শক মনোরঞ্জক হয়ে উঠেছিল।
উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কলিরাজার যাত্রা (১৮২১), নলদময়ন্তী (১৮২২), কামরূপযাত্রা, রাজা বিক্রমাদিত্য যাত্রা, নন্দবিদায় যাত্রার অভিনয়ের খবর পাওয়া যায়। কলকাতার ও আশেপাশে ধনী বাঙালির বাড়িতে এইসব যাত্রানুষ্ঠান হত। কামরূপ যাত্রা শ্যামসুন্দর সরকারের বাড়িতে (৯ মার্চ, ১৮২২), রাজা বিক্রমাদিত্য যাত্রা ভূকৈলাসের মুখুজ্জে বাড়িতে (৩১ মে, ১৮২৩), নবিদায় রামাদ মুখোপাধায়ের চেষ্টায় (মার্চ, ১৮৪৯), শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়িতে (১৪ এপ্রিল, ১৮৪৯) অভিনীত হয়েছিল।
বড়লোকের বাড়িতে ছাড়াও এই সময়ে গ্রামাঞ্চলে, শহরের হাটে, বাজারে, মেলায় সাধারণ মানুষের আমোদ-প্রমোদের জন্যও যাত্রানুষ্ঠান হত। তবে সেগুলির ধার ও ভার ধনী বাড়ির অভিনয়ের মতো হত না।
উনিশ শতকের প্রথম ভাগেই ‘নতুন যাত্রা’ নামে একধরনের যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। বিষয়বস্তু ছিল হয় বিদ্যাসুন্দর, নয় নলদময়ন্তী কাহিনী। সেখানে মালিনীর নৃত্যগীত একটি বিশিষ্ট অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়। খেমটা নাচেরও ব্যবহার শুরু হলো। এদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হচ্ছেন গোপাল উড়ে। এর অন্য বিষয়ের যাত্রার মধ্যেও অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এই নৃত্য ও গীত ঢুকে পড়ে। এই সূত্র ধরে ক্রমে নতুন যাত্রায় কালুয়া-ভুলুয়া, মেথর-মেথরানী, ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানি, নাপিত-নাপিতানি প্রভৃতি অশ্লীল নৃত্যগীত প্রবেশ করে আবার যাত্রাকে নিম্নরুচির বাহন করে তোলে। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ও তার শিষ্য রামধন মিস্ত্রী প্রথমে (১৮২২) বিদ্যাসুন্দর পালার এই অবনমন ঘটান। প্যারীমোহন তাঁর যাত্রাপালায় সস্তা জনপ্রিয়তারই পথ ধরেন। গোপাল উড়ে এসবেরই সর্বাঙ্গীণ রূপে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কৃষ্ণযাত্রার ভক্তিবিহ্বলতা দূর হয়ে গিয়ে এখানে নৃত্যে-গীতে, সঙ্-য়ের উপস্থিতিতে, সস্তা সংলাপে যাত্রাপালা নিম্ন ও অসুস্থ রুচির হাত ধরে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল।
গোপাল উড়ের যাত্রাপালা বিদ্যাসুন্দরের এতোই ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল যে, শ্যামবাজারের ধনী নবীন বসুর বাড়িতে নতুন আমদানী থিয়েটারের রীতিতে ‘বিদ্যাসুন্দরের’ অভিনয় হয়েছিল (১৮৩৫)। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নাট্যশালা স্থাপনের চিন্তার মূলে যে গোপাল উড়ের যাত্রা, সেকথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন। খুবই জনপ্রিয় গোপাল উড়ে ও বিদ্যাসুন্দর পালাকে সেযুগে সহজে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। তার শিষ্য কৈলাস বারুই এই ধারা টেনে নিয়ে যান। লোকাধোপা নামে পরিচিত লোকনাথ দাস গোপাল উড়ের পথ অনুসরণ করে লেখেন বিদ্যাসুন্দর, নলদময়ন্তী, শ্রীমরে মশান, কলঙ্কভঞ্জন।
উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত নতুন সম্প্রদায় এই যাত্রার প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছিল। ক্রমে এই সমাজের কাছে যাত্রা অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে। বাঙালি ধনী সম্প্রদায়ের প্রাসাদ-মঞ্চগুলিতে তখন ইংরেজি ধরনের থিয়েটার চালু হয়েছে; মঞ্চ বেঁধে, সেট সেটিংস ব্যবহার করে, দৃশ্যপট সাজিয়ে, উইংস ও যবনিকার অন্তরাল সৃষ্টি করে। আলো, সঙ্গীত এবং অভিনয়ের এই থিয়েটার নতুন সম্প্রদায়ের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠেছে। সেই তুলনায় সমতল ভূমিতে যাত্রার অভিনয় হয় মুক্ত স্থানে, দর্শক ও অভিনেতা একই তলে প্রকাশ্যে সহাবস্থান করে। পয়ারে সংলাপ, তাতে গানের অহেতুক প্রাধান্য, ‘জুড়িগান’ ও ‘বালকদের গান’, বিবেক-রঙ-ঢং-খেমটা নাচ, নিম্নরুচি ও অশ্লীলতার যাত্রাপালা নব্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকদের আনুকূল্য পায়নি। বরং থিয়েটার আদরণীয় হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বক্তব্যে (বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাঘ, ১২৮০ শকাব্দ) এই নব্য ভাবনাটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে—ইহার (থিয়েটারের) প্রাদুর্ভাবে যাত্রা কবি খেউড় প্রভৃতি দূষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে—ইহা কর্তৃক বঙ্গদেশে নীতির উৎসেদ ও নির্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহা আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।’
এই সম্প্রদায়ের হাতেই রয়েছে নব্য সংস্কৃতির বিকাশের চাবিকাঠি-তাদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে নতুন যাত্রা বিকাশের পথ খুঁজে পায়নি। বরং অবহেলায় অনাদরে ম্লানমুখে নব্য সংস্কৃতির চৌহদ্দির বাইরে অবস্থান করছিল।
উনিশ শতকের মধ্যভাগে কৃষ্ণযাত্রাকে নতুন করে গড়ে তােলার উদ্যোগ নিলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী। নবোদ্ভূত সমাজে প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার ধর্মভাবের প্রভাব খুব ছিল না। ফলে কৃষ্ণযাত্রা ক্রমে লুপ্ত হতে থাকে এবং বিদ্যাসুন্দর ও নলদময়ন্তী পালার ব্যভিচার শুরু হয়েছিল। কৃষ্ণকমল প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার আদর্শটি গ্রহণ করে, কৃষ্ণযাত্রার বিষয়বস্তুর একঘেয়েমি কাটিয়ে, চৈতন্যজীবন, রামায়ণ ইত্যাদি থেকে কাহিনী গ্রহণ করলেন। রুচিবিকৃতি দূর করে যাত্রাকে মার্জিত করে নিয়ে নতুন সমাজের কাছে গ্রহণীয় করে তোলার চেষ্টা করলেন। ভাঁড়ামো, অশ্লীলতা, সঙ্-য়ের নাচ ও গানের বিকৃতি থেকে যাত্রাপালাকে মুক্ত করে উনিশ শতকের মধ্যভাগে কৃষ্ণকমল নতুন সংস্কারে হাত দিলেন। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণকমলের কয়েকটি পালা উল্লেখযোগ্য—নিমাই সন্নাস (১৮৩০), স্বপ্নবিলাস, রাই উন্মাদিনী, বিচিত্র বিলাস, ভরতমিলন, সুবল সংবাদ, নন্দবিদায়, গন্ধর্বমিলন।
উনিশ শতকের মধ্যভাগে কৃষ্ণকমল বাংলার পূর্ব অঞ্চলে কৃষ্ণযাত্রাকে ছড়িয়ে দিয়ে জনপ্রিয় করেন। রাঢ় অঞ্চলে এই দায়িত্ব নেন নীলকণ্ঠ মুখখাপাধ্যায়। কিন্তু দুজনের আপ্রাণ চেষ্টাতেও কৃষ্ণযাত্রা সে জনপ্রিয়তা ফিরে পেল না। নতুন যুগের নতুন দাবীর অন্য পথ ধরলো।
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন প্রমোদ-মাধ্যম থিয়েটার বা ‘বিলিতি যাত্রা নতুন সমাজের কাছে বেশি গৃহীত হয়েছে। নতুন নতুন মঞ্চ গড়ে উঠেছে, নাটক লিখিত ও অভিনীত হচ্ছে। বিলিতি যাত্রা বা নতুন থিয়েটার তখন কলকাতার ধনী সম্প্রদায়, শিক্ষিত সমাজ এবং নবোদ্ভূত জনগণের কাছে সবচেয়ে আদৃত প্রমোদ ব্যবস্থা। এই থিয়েটারের প্রভাবেই ‘নতুনযাত্রা’ গীতাভিনয়ে পরিণত হলো।
থিয়েটার জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও সবার পক্ষে এই থিয়েটার দেখার সুযোগ ছিল না। কিংবা সবার পক্ষে এই থিয়েটার অভিনয় করার আর্থিক সঙ্গতি ও সম্বল ছিল না। তাই যাত্রার মধ্যে দিয়েই নাট্যরস পরিবেশনের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হল গীতাভিনয়। কৃষ্ণযাত্রা ও নতুনযাত্রার গীত অংশ সংক্ষিপ্ত করে, নতুন নাটকের অভিনেয় অংশকে প্রাধান্য দেওয়া হল। প্রাচীন ও নতুন উভয় যাত্রার ভিত্তির ওপর ইংরেজি আদর্শে রচিত বাংলার নাটকগুলির প্রত্যক্ষ ফলে সৃষ্টি হল গীতাভিনয়।
কৃষ্ণযাত্রা থেকে গীত, নতুন যাত্রা থেকে নৃত্য, সমসাময়িক নাটকের সংলাপ-প্রাধান্য ও সংঘাত-এর নাট্যধর্ম—এই চার নিয়ে গীতাভিনয় তৈরি হলো। প্রাচীন যাত্রার ভক্তি, নতুন যাত্রার আনন্দ ও ইংরেজি আদর্শে রচিত বাংলা নাটকের কারুণ্য এতে গৃহীত হলো। যাত্রার দেশজ রস সংস্কারের সঙ্গে নতুনকালের রসপিপাসা মিশ্রিত হওয়ার ফলে সাধারণ জনগণ, শিক্ষিত জনগণ, ধনী বাঙালি সকলেই এতে পরিতৃপ্ত হলো। গানের যে ধারা ক্রমে নিম্নরসের আবেশে উপেক্ষিত হচ্ছিল, গীতাভিনয়ের মধ্যে সেই রাগসঙ্গীত আবার প্রাণ ফিরে পেল। বিষয়বস্তুতে কৃষ্ণকথা ছাড়াও পুরাণের বহুবিচিত্র কাহিনী স্থান পেল। কাহিনীর বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতির সঙ্গেই চরিত্র সৃষ্টির দিকেও নজর দেওয়া হলো। ধর্মভাব অনেকাংশে মুক্ত হওয়ার ফলে সর্ব ধর্মের মানুষের কাছেই আদৃত হলো। কৃষ্ণযাত্রার সংক্ষিপ্ত কাহিনীকে পঞ্চাঙ্ক নাটকের অনুকরণে বিস্তৃত করে তোলা হলো। সবমিলিয়ে কৃষ্ণযাত্রাকে অপসারিত করে গীতাভিনয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নিজের জায়গা করে নিল। যাত্রার কুরুচি, থিয়েটারের ব্যয়ভার—দুটো থেকেই গীতাভিনয় জনগণকে মুক্তি দিল। যাত্রায় পাওয়া গেল নানা বিষয়, থিয়েটারি অভিনয়, পারস্পরিক সংলাপ, গানের কথা ও সুরের বৈচিত্র্য, মহার্ঘ সাজসজ্জা, উচ্চাঙ্গের রাগরাগিণী এবং দেবতার সঙ্গে মনুষ্য চরিত্রও।
নাট্যকার মনোমোহন বসু যাত্রাকেও ভালবাসতেন। অথচ যাত্রার অধোগতি মনোব্যথার কারণ হয়েছিল। মনোমোহন আধুনিক থিয়েটার ও দেশীয় রুচির সংমিশ্রণে যাত্রা ও নাটকের মেলবন্ধনে কয়েকটি নাটক লেখেন। রামাভিষেক (১৮৬৮), সতী নাটক (১৮৭৪), হরিশ্চন্দ্র (১৮৭৫), পার্থপরাজয়, যদুবংশ উল্লেখযোগ্য। গানের সংখ্যা কমিয়ে, দীর্ঘ গায়ন বন্ধ করে, গায়ন পদ্ধতির সংস্কার করে, পাত্রপাত্রীর সংলাপ স্বাভাবিক করে তুলে, ভক্তি ও করুণরসের যোগান দিয়ে এবং অশ্লীলতা ও ভাড়ামো থেকে মুক্ত করে লেখা তার নাটকগুলি বৌবাজার বঙ্গনাট্যালয় থিয়েটারের মতো অভিনয় করল। সঙ্গে সঙ্গে বৌবাজারের যাত্রার দলও সেগুলি অভিনয় করল। বোঝা যায়, মনোমোহন দুই রীতিতেই অভিনয়যোগ্য করে নাটকগুলি লিখলেন এবং সঙ্গে পুস্তিকা জুড়ে দিয়ে যে যার পছন্দের বাছাইয়ের হদিশ দিয়ে দিতেন। মনোমোহনের প্রচেষ্টায় নতুন করে যাত্রা লেখা ও অভিনয়ের আয়োজন শুরু হয়ে গেল।
তার আগেই অবশ্য কয়েকজন গীতাভিনয় রচয়িতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (শকুন্তলা, ১৮৬৫), হরিমোহন রায় (রত্নাবলী, ১৮৬৫, শ্রীবৎসচিন্তা, ১৮৬৬, জানকীবিলাপ, ১৮৬৭, মালিনী, ১৮৭৫)। কালিদাস সান্যাল (নলদময়ন্তী)। তিনকড়ি ঘোষাল (সাবিত্রী সত্যবান, ১৮৬৫) মুলে নাট্যকার ছিলেন বলে যাত্রাপালায় নাটকের আদর্শই গ্রহণ করেন। গীতাভিনয় লিখলেও নামে ‘নাটক’ কথাটি ব্যবহার করতেন। যাত্রা ও নাটককে সজ্ঞানে কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা এগুলিতে লক্ষ করা যায়। গীতাভিনয়ের হুজুগে তখন খ্যাতিমান নাট্যকারদের নাটকগুলিকেও গীতাভিনয়ে রূপান্তরিত করে অভিনয় শুরু হয়ে যায়।
মনোমোহনের পরে পরেই এলেন মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, যাত্রা জগতে তিনি মদন মাষ্টার নামেই পরিচিত। চন্দননগরে তাঁর পেশাদারি যাত্রার দল ছিল। যাত্রার প্রয়োগ ও উপস্থাপনায় তিনি সংস্কার করলেন। হুগলী স্কুলের শিক্ষক মদনমোহন আধুনিক শিক্ষার সুযোগে প্রচলিত যাত্রার সংস্কার করেন। নৃত্যগীত, সুর, বাদ্য, সাজসজ্জার সংস্কার করেন। যাত্রার প্রয়োগ প্রাধান্যের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা যায় তাঁর দক্ষযজ্ঞ, হরিশ্চন্দ্র, রামবনবাস, ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র, দুর্গামঙ্গল পালাগুলিকে।
থিয়েটারের পাশে শহর-শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলে গীতাভিনয় যাত্রাও জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। এই কাজে যারা প্রধান দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন মতিলাল রায়, ব্রজমোহন রায়, অহিভূষণ ভট্টাচার্য, ধনকৃষ্ণ সেন, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ মুখখাপাধ্যায় প্রমুখ পালাকার ও পরিচালকবৃন্দ। প্রত্যেকের নিজস্ব যাত্রার দল ছিল, তাই নিয়ে যাত্রাপালা অভিনয় করতেন। গীতাভিনয়গুলি যাত্রার মতোই মঞ্চবিহীন খোলা আসরেই অভিনীত হতো।
উনিশ শতকের শেষার্ধে সবচেয়ে খ্যাতিলাভ করেন মতিলাল রায়। যাত্রাপালা লিখতেন, নিজের দলে অভিনয় করাতেন, নিজে অভিনয় করতেন। ঠিক যে সময়ে বাংলা নাটকের জগতে গিরিশচন্দ্র নাটকগুলি লিখতে শুরু করেছেন—সেই সময়েই মতিলাল তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে যাত্রাপালা অভিনয় করছেন। তাঁর যুগে মতিলাল রায় খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিলেন। মনোমাহন বসুর গীতাভিনয়গুলি নাটকের কাছাকাছি। মতিলাল রায়ের গীতাভিনয়গুলি যাত্রারীতির নিকটবর্তী। মতিলালের পালাকে নাটকের চেয়ে যাত্রারূপেই অভিনয় করা সহজ ও সঙ্গত। মনোমোহনের যেমন গানগুলি বাদ দিয়ে থিয়েটারে অভিনয় সহজ।
প্রথমে নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায় (১৮৮০) খুলে অভিনয় শুরু করেন। পরে নিজের নামে সম্প্রদায় খুলে দীর্ঘদিন অভিনয় করেন। মতিলাল প্রথমে পাঁচালী রচয়িতা ও গায়ক ছিলেন। কথকের বক্তৃতা ও পাঁচালীর পৌরাণিকভাব মিশ্রিত করে লোকশিক্ষা ও ধর্মশাস্ত্রের কথকতার আয়োজন করেন। গানে পল্লীগীতির সুর মিলিয়ে দেন। যাত্রাপালায় থিয়েটারী ঢং এনে, অভিনয়ের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা ও কলাকৌশলের প্রয়োগ করে তিনি দর্শকদের মোহিত করে দেন। তাঁর ৪০টি পালায় রয়েছে প্রায় হাজারের ওপর গান। সেই গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দিত। কয়েকটি পালা—তরণীসেন বধ, রামবনবাস, সীতাহরণ (১৮৭৮), বিজয়চণ্ডী (১৮৮০), দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ (১৮৮১), ভীষ্মের শরশয্যা, কর্ণবধ, ভরত আগমন (১৮৮৮), নিমাই সন্নাস, ব্রজলীলা (১৮৯৪), যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক (১৯০০), রাবণবধ, পাণ্ডবনির্বাসন, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ, গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ প্রভৃতি। ভক্তিভাব, করুণরসের সঙ্গে বীর রৌদ্র ও হাস্যরসের ব্যবহার, শালীনতাবোধ, গানের বৈচিত্র্য তাঁর পালাকে প্রাচীন যাত্রা থেকে উন্নত ও জনপ্রিয় করে তুলেছিল।
হারাধন রায় (নলদময়ন্তী, সুরথ উদ্ধার, মীরা উদ্ধার, কাদম্বরী লক্ষ্মণ বর্জন, রামাবতার), ধনকৃষ্ণসেন (বিধ্বমঙ্গল, উমাতারা, কর্ণবধ, রাবণের মোহমুক্তি), ব্রজমোহন রায় (অভিমন্যবধ, রামাভিযেক, সাবিত্রীসত্যবান, রাবণবধ, কংসবধ), ধর্মদাস রায় (চিন্তার চিন্তামণি লাভ, প্রভাসে নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণ, ভাগীরথী মহিমা), পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য (পারিজাত হরণ, সুবলমিলন, জনা, সতীর পতিভক্তি, মায়াগীত) উনিশ শতকের শেষার্ধের উল্লেখযোগ্য পালাকার।
উনিশ শতকে গীতাভিনয় সমবেত প্রচেষ্টায় জনপ্রিয়তার ঊর্ধ্বে উঠেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে থিয়েটারের প্রতিস্পর্ধী জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল। কিন্তু যাত্রা ক্রমে থিয়েটারের ঢংয়ে বেশি অভিনীত হওয়াতে পালাগুলি নাট্যধর্মী হয়ে উঠলো, অথচ আধুনিক নাটকের শেক্সপীয়রীয় ক্রিয়াবহুলতা, দ্বন্দ্ব গীতাভিনয়ে সম্ভব হয় না। বৈচিত্র্যহীনতার ভারে গীতাভিনয় শ্লথগতি প্রাপ্ত হলো।
এই সময়েই নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও তাঁর অনুগামী নাট্যকারেরা থিয়েটারে পৌরাণিক নাটকের বন্যা বইয়ে দিলেন। দেখাদেখি পৌরাণিক যাত্রা শুরু হল। নতুন যাত্রায় আধ্যাত্মিক ভাব ছিল না। ধর্মবোধ নিরপেক্ষ আনন্দ, মজা ও কৌতুক সৃষ্টি প্রধান লক্ষ্য ছিল। পৌরাণিক যাত্রায় ভক্তি ও বিশ্বাসের ভাব প্রকাশ পেল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত পুরাণাদি অন্য গ্রন্থ থেকে পৌরাণিক যাত্রার বিষয়বস্তু গৃহীত হলো। উনিশ শতকের শেষ ভাগেই হিন্দুধর্মবোধের ফলশ্রুতিতেই ভক্তিভাব পৌরাণিক নাটক ও যাত্রায় প্রচলিত হয়েছিল। থিয়েটারে ভক্তিভাব ও বাঙালির জীবনাদর্শ নগরজীবনে প্রচারিত হয়েছিল। পৌরাণিক যাত্রা নগর ছাড়িয়ে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের কাছে ভক্তিভাব ও জীবনাদর্শের সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্টবাদ, কর্মফল, সংস্কার ও বিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে লাগল। গৈরিশ ছন্দে লেখা যাত্রাগুলি বিয়োগান্তক হতো না নাটকের মতো। বিয়োগান্তক হলে ‘মেল্তা’ জুড়ে দিয়ে মিলনান্তক করা হতো। পৌরাণিক নাটক কমে যাত্রার সঙ্গে ‘মেল্তা’ গ্রহণ করেছিল। দ্বৈতনৃত্যগীত, ভাঁড় চরিত্র সৃষ্টি, আবেগধর্মী সংলাপ নাটকে চালু হয়েছিল। গীত-প্রাধান্যও শুরু হয়েছিল। আবার পৌরাণিক নাটকের ভাব ও ভঙ্গি যাত্রা গ্রহণ করে চলেছিল।
উনিশ শতকের শেষভাগের যাত্রায় আখড়াই বদী নাচ দিয়ে কাহিনী শুরু হতো। অল্পবয়সী ছেলেরা নর্তকী সেজে গান গেয়ে আখড়াই বন্দি নাচতো। বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে দেশি বেহালা, ঢোল, বায়াতবলা, মন্দিরা ব্যবহৃত হতো। দেবদেবী বন্দনার পরে মূল পালা শুরু হত। প্রস্তাবনা জুড়ি গায়কের গান দিয়ে শুরু। জুড়ি গায়ক, স্বতন্ত্র চরিত্র নয়, পাত্র-পাত্রীর মনোভাব সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করতো। পোষাক ছিল—গায়ে সাদা চোগা চাপকান, মাথায় পাগড়ি। দলে চার জন থাকত—চারকোণে। জুড়ির গানকে বলে ‘উক্তগীত’, জুড়ির সাহায্যে থাকত হাফজুড়ি। আর ‘বিবেক’ যখন তখন এসে বিষয়ের ভাব ও চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও অভীপ্সা গানে গানে প্রকাশ করে দিয়ে যেত। যাত্রাদলের অভিনেতা, বাদ্যকর এবং কর্মচারীদের বলত ‘আসামী’। থিয়েটারে ১৮৭৩ থেকেই পাকাপাকিভাবে মেয়েরা অভিনয় শুরু করে, কিন্তু যাত্রায় অভিনেত্রী আসতে আরো অনেক বিলম্ব হয়েছে। উনিশ শতক জুড়ে পুরুষরাই সব চরিত্রে অভিনয় করেছে।
মহিলা পরিচালিত কিছু যাত্রাদলের খবর পাওয়া যায়। রাজা বৈদ্যনাথের কোনো বারবিলাসিনী উনিশ শতকে প্রথম মহিলা যাত্রাদল পরিচালনা করেন। চন্দননগরের বৌমাষ্টারের দল (মদন মাষ্টার মারা গেলে, তার স্ত্রী এই দল পরিচালনা করতেন বলে এইরকম নাম), নবদ্বীপের বৌকুণ্ডুর দল (নীলমণি কুণ্ডুর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী অধিকারী হন) নানা যাত্রাপালা অভিনয় করেছিল।
উনিশ শতকের সত্তর-আশির দশকেই ছিল সখের যাত্রার দল। উমেশ মিত্রের দল, আড়পুলি গলির দল, সিমলার ‘সকের যাত্রা কোম্পানি প্রভৃতি। ক্রমে গড়ে ওঠে পেশাদারি যাত্রার দল। থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে এইসব দল সে যুগে সাফল্য লাভ করেছিল। বেলগাছিয়ার হরিনারায়ণ রায়চৌধুরীর দল, মতিলাল রায়ের দল, ব্রজমোহন রায়ের দল, মদনমাষ্টারের দল, নীলমণি কুণ্ডুর দল সে যুগে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল।
মনে রাখতে হবে ১৮৭২-এর ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’ নামে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল বাগবাজারের এই রকমেরই একটি সখের যাত্রার দল-তারা ধনী বাঙালির জাঁকজমকের প্রাসাদ-মঞ্চ থেকে বাংলা নাটককে মুক্ত করে এনে সর্বসাধারণের উপভোগের থিয়েটার চালু করেছিল।
উনিশ শতকের নানা পরিবর্তনের ধারায় যাত্রা যেরূপে নির্দিষ্ট হয়েছিল, বিশ শতকে সেখানে আবার কিছু সংযোজন ও পরিমার্জন হলো। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও মথুর সাহার চেষ্টায় নৃত্যগীতের প্রাধান্য কিছু কমল, অভিনয়ের গুরুত্ব বেশি করে প্রতিষ্ঠিত হল। ফলে যাত্রা ও থিয়েটার খুব কাছে এসে গেল। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের ‘পদ্মিনী’ পালা থেকেই (প্রকাশকাল ১৩১১ সাল) যাত্রাকে আর গীতাভিনয় রূপে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। হয়ে গেল ‘থিয়েট্রিকাল যাত্রা’। ‘যাত্রা শোনার’ যুগ পালটে হয়ে গেল ‘যাত্রা দেখার’ যুগ। অর্থাৎ সঙ্গীত কমে অভিনয় অংশ বৃদ্ধি পেল। গানে থিয়েটারি সুর ও নাচে থিয়েটারি প্রথা প্রবর্তিত হলো। দলগুলির নামও হয়ে গেল থিয়েট্রিকাল যাত্রা কোম্পানী কিংবা অপেরা কোম্পানী। যাত্রার বিষয়বস্তু পুরাণ থেকে সরতে সরতে ইতিহাসের কাছে এসে গেল। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি পালা লক্ষ করলেই সেটি বোঝা যাবে-নলদময়ন্তী, প্রহ্লাদচরিত, যদুবংশধ্বংস, মহীরাবণ, ভৃগুচরিত্র তার গোড়ার দিকের রচনা। পরে লিখছেন পদ্মিনী, রাণী জয়মতি, চাণক্য, কালাপাহাড়, রণজিতের জীবনযজ্ঞ।
১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধের প্রবল আন্দোলনে স্বদেশ-প্রেমের জোয়ার এসেছিল জনমনে। বাংলা থিয়েটারেও ইতিহাসকে অবলম্বন করে দেশাত্মবোধের নাটক প্রচুর অভিনীত হতে লাগল। যাত্রাতেও ভাব ও বিষয়ের পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। ভক্তি, দৈব ও বিশ্বাসের স্থলে স্বদেশচেতনা, দেশভক্তি এবং দেশমাতৃকার বন্দনা যাত্রাপালায় আচরিত হতে লাগল। সামাজিক জীবনধারা ও মানুষের মুক্তির জয়গানও যাত্রায় গৃহীত হল। যাত্রাপালার কাহিনীতে যুগান্তকারী পরিবর্তন হল। মানুষের আবির্ভাব ঘটলো। যাত্রাপালায় দেবদেবী থেকে ক্রমে মনুষ্য চরিত্রের আবির্ভাবের ক্রমপর্যায়টি এইরকম—দেবদেবী—মহাপুরুষ চরিত্র—ইতিহাসের চরিত্র—সাধারণ মনুষ্য চরিত্র। প্রথমে দেবদেবী, তারপরে মহাপুরুষ চরিত্র, তারপরে ইতিহাসের চরিত্র এবং সবশেষে সাধারণ নরনারী যাত্রাপালায় প্রতিষ্ঠা লাভ করলো।
বঙ্গভঙ্গের যুগে স্বদেশী যাত্রার শ্রেষ্ঠ পালাকার চারণকবি মুকুন্দ দাস। তাঁর নিজের দলের তিনি পালা রচয়িতা, পরিচালক, অভিনেতা এবং গায়ক। তাঁর পালায় তিনি রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের কথা, দেশানুরাগের কথা এবং তার সঙ্গে সমাজসংস্কারের কথাও নিয়ে এলেন। বঙ্গভঙ্গের উন্মাদনার যুগে মুকুন্দদাস বাংলার প্রান্তে প্রান্তে দেশমাতৃকার পরাধীনতার গ্লানি ও স্বদেশভূমির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কথা পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর পালায় কাহিনী ছিল শিথিল কিন্তু হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস ছিল প্রবল। দেশীয় সুরে সহজ সরল ভাষায় তার গান সহজেই আবেদন সৃষ্টি করত, নৃত্যঅংশ ছিল। চরিত্র সৃষ্টির চেয়ে ঘটনা ও বক্তব্য বর্ণনাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। তাই বক্তৃতা অংশ বেড়ে গিয়েছিল। তবে তার স্বদেশী যাত্রার আবির্ভাবে যাত্রাপালা থেকে ভক্তিভাব ক্রমে দূরে সরে গেল।
তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পালা—মাতৃপূজা, পথ, সাথী, সমাজ, পল্লীসেবা, ব্রহ্মচারিণী, কর্মক্ষেত্র, দাদা, জয়পরাজয় প্রভৃতি। তবে বিষয়বস্তু ছিল—হিন্দু মুসলমান ঐক্য, অস্পৃশ্যতা বর্জন, বিদেশী পণ্য বর্জন, স্ত্রী শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, পল্লীসেবা, বাঙালির কর্মক্ষেত্র এবং অবশ্যই দেশমাতৃকা বন্দনা। তাঁর মাতৃপূজা, পথ, সাথী পালা ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। তিনি আড়াই বছর কারারুদ্ধ ছিলেন।
এই সময়ের উন্মাদনায় এবং মুকুন্দদাসের প্রভাবে কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় মাতৃপূজা পালা লিখে কারারুদ্ধ হন। পালাটিও বাজেয়াপ্ত হয়। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের রণজিতের জীবনযজ্ঞ এই সময়কার রচনা। মথুর সাহা (পদ্মিনী, ভরতপুরের দুর্গজয়), ভূষণদাস (মাতৃপূজা)-এর পালাগুলি নিষিদ্ধ হয়। পরে ভোলানাথ রায় (পঞ্চনদ, দাক্ষিণাত্য), পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় (টিপু সুলতান), ব্রজেন্দ্রকুমার দে (বাঙালি), সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (মাটির মা), পূর্ণদাস (শৃঙ্খলমোচন) এই ধরনের পালা রচনা করেছিলেন। তবে এঁদের ক্ষমতা কম থাকায় এবং বঙ্গভঙ্গের উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে যাওয়ায় যাত্রায় এই ধারাও কমে যায়।
মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২১) সময় থেকে সামাজিক সমস্যা এবং সামাজিক নরনারী যাত্রায় ভালোভাবে স্থান পেয়ে যায়। সেইসঙ্গে সমাজের নানা সমস্যা, অস্পৃশ্যতা, অসবর্ণ বিবাহ, জাতপাত, যাত্রায় গৃহীত হলো। তবে সামাজিক যাত্রায় আধুনিক নাটকের মতো ঘাত-প্রতিঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্য নাটিক ক্রিয়া দেখানো সম্ভব ছিল না। তাই জীবনদ্বন্দ্বের গভীরে না গিয়ে সামাজিক যাত্রা সমাজের উপরিতলের ঘনঘটা ও চমক দিয়ে কাহিনী ভরিয়ে দিল, তার সঙ্গে যাত্রায় অতিলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টির দিন চলে গেল। সামাজিক যাত্রার লৌকিক উপাদান, কাহিনী, চরিত্র, সাজপোষাক সব কিছুর মধ্যে দিয়ে ‘illusion’ বা নাট্যমায়া বর্জন করা হলো। তার সঙ্গে ঐতিহ্যমূলক কাহিনী বর্জন করে সমসাময়িক সমাজজীবনের কাহিনী গ্রহণ করে যাত্রাপালায় বিষয়বেচিত্র্য বাড়ানো হয়েছে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে টালমাটাল বাংলায় যুদ্ধ, মহামারী, মন্বন্তর, আগস্ট আন্দোলন, কালোবাজারি, মজুতদারির যুগে বাংলা যাত্রারও অনেক পরিবর্তন সাধিত হলো। গণনাট্য, নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে বাংলা নাটকে নতুন জোয়ার এসে যায়। বিষয়ে, ভাবে, চরিত্রবিন্যাসে ও প্রয়োগকুশলতায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন বাংলা নাটক ও তার অভিনয়ে লক্ষ করা গেল, বাংলা যাত্রাতেও তার প্রভাব পড়ল। বাংলা যাত্রাও নতুনভাবে বেঁচে উঠে আবার প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে চাই। এই সময়কালীন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পালা হলো—ব্রজেন্দ্রকুমার দে’র আকালের দেশ (১৯৪৫), কানাই শীলের দেশের দাবী (১৩৫৬), বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বেইমান (১৩৫৭), জীতেন্দ্রনাথ বসাকের মানুষ (১৩৫৪), সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের রক্তবীজ (১৩৫৮) উল্লেখযোগ্য। নানা বিষয়ের মধ্যে এগুলিতে রয়েছে স্বাধীনতার কথা, দেশপ্রেমের কথা, পঞ্চাশের মহামন্বন্তরের কথা, ধনী-দরিদ্রের শ্রেণীসংগ্রামের কথা (রক্তবীজ), মানুষের নতুন করে বেঁচে ওঠার কথা।
এই সময়কালের সবচেয়ে খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে (১৯০৭-১৯৭৬) তাঁর শিক্ষা রুচি ও শিল্পবোধে যাত্রায় নতুন মাত্রা এনে দিয়েছেন। তাঁর নিজের দল ছিল না, তিনি ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তাঁর পালা যাত্রাদলগুলি নিয়ে অভিনয় করেছে। ত্রিশের দশকের সূচনায় তিনি পেশাদারি যাত্রার জন্য পালা লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম পালা ‘স্বর্ণলঙ্কা’ ১৯২৫ সালে লেখা। তিনি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, সামাজিক, রূপক ও পল্লীগাথা—সব নিয়েই যাত্রাপালা রচনা করেছেন। ইতিহাসের চেয়ে কল্পনাপ্রধান রোমান্স, হিন্দুমুসলমান ঐক্যবোধ, দেশপ্রেম, জাতির কর্মপ্রবণতা, সমাজপতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, রাজশক্তির দম্ভে জাতির দুর্দশা, শাসকের অদূরদর্শিতার পরিণাম, গণজীবনে দুর্দশার সন্ধান প্রভৃতি তাঁর পালার বিষয়বস্তু। তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পালা—স্বর্ণলঙ্কা (১৯২৫), বজ্রনাভ (১৯৩২), স্বামীর ঘর (১৯৪৫), মায়ের ডাক (১৯৪৭), বাঙালি (১৯৪৮), আকালের দেশ (১৯৪৫)—এগুলি দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে অভিনীত হয়েছে। পরে তিনি লেখেন গাঁয়ের মেয়ে (১৯৫১), ধর্মের বলি (১৯৫৬), রাজা দেবিদাস (১৯৫৭), সোনার ভারত (১৯৬১), কবি চন্দ্রাবতি (১৯৬১)। এছাড়া তাঁর সোনাই দীঘি, সম্রাট জাহাঙ্গীর, বিচারক, যাদের দেখেনা কেউ, রক্তের নেশা, দেবতার গ্রাস, লোহার জাল, ধুলার স্বর্ণা, প্লাবন প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয় পালা রয়েছে।
ব্রজেন্দ্রকুমার দে’র জ্ঞান-পাণ্ডিত্য ও শালীনতাবোধ তাঁর পালাগুলিকে গভীর ও বহু বিস্তৃত করেছে। তিনি ভাড়ামো বর্জন করে চরিত্র ও ঘটনা উপযোগী হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। প্রচলিত দীর্ঘ সংলাপ সংক্ষিপ্ত করেছেন। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা তাঁর ছিল না। সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা, সেই সম্প্রদায়ের চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের মুখ দিয়েই বলিয়েছেন। ছদ্মবেশী চরিত্র এনে কাহিনীতে চমক সৃষ্টি করেছেন। প্রচলিত যাত্রায় চরিত্র শুধুমাত্র ঘটনা বহন করতো। তিনি চরিত্র বিশ্লেষণের দিকে জোর দিয়েছেন। কাহিনী গ্রহণ ও বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি রস সৃষ্টিতে নিপুণ ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যাত্রাপালা লিখতে শুরু করে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলায় নিরন্তর যাত্রাপালা লিখে গেছেন। বহু ঘটনার উত্থান-পতনের সাক্ষা ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর যাত্রাতেও বিষয়েব নানা বিস্তার ঘটিয়ে তাঁর পালাকে বহুমুখী করে তুলেছিলেন। অবক্ষয়ী যাত্রাপালাকে নানাভাবে উন্নত করার চেষ্টা করে গেছেন।
বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশক থেকে আধুনিক যাত্রাপালা নতুনভাবে গড়ে উঠেছে। এই সময়ে চলচ্চিত্রের এবং নাটকের অসম্ভব জনপ্রিয়তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যাত্রাদলগুলি নতুনভাবে পুনর্গঠিত হতে শুরু করে। আধুনিক টেকনোলজির সুযোগসুবিধা। নানাভাবে গ্রহণ করে যাত্রা প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে থাকে। একেবারে পেশাদারি প্রথায় পরিচালিত যাত্রা দল তার পুরনো মোহ ঝেড়ে ফেলে নতুনভাবে গড়ে ওঠে। চলচ্চিত্র ও নাটকের খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালক, সুরকার গ্রহণ করে যাত্রার জনপ্রিয়তা ও মান বাড়ানোর চেষ্টা হয়। নাট্যকারদের দিয়ে পালা লেখানো হতে থাকে। নতুন পালাকাররাও আসতে থাকে। খোলামঞ্চে অভিনয় হলেও আলো, সাজসজ্জা, চমক প্রায় থিয়েটারি কৌশলে হতে থাকে। যান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা নেওয়ার ফলে নানাদিকে নতুনত্ব সঞ্চার হয়। পালার বিষয় এখন থেকে পৌরাণিক জগৎ ছেড়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিষয় গ্রহণ করতে থাকে। এদেশ এবং বিদেশের নানা ঘটনা, নানা খ্যাতিমান চরিত্র, নানা সংগ্রাম, নানা উত্থান-পতন যাত্রার বিষয়রূপে গৃহীত হতে থাকে। পুরনো যাত্রার গন্ধ কিংবা রেশ এগুলির মধ্যে নেই বলে অনেকেই ব্যথা পেয়ে থাকেন। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার সব সুযোগ গ্রহণ করে যাত্রা তার অস্বিত্ব বজায় রেখে নিজের পথে চলতে চলতে ক্রমেই চলচ্চিত্র কিংবা থিয়েটারের প্রতিস্পর্ধী মাধ্যম হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আধুনিক যাত্রার বিচারে, তার ভালোমন্দ নির্ণয় করতে গিয়ে আধুনিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট মাথায় রাখতেই হবে। সেকথা ভুলে গেলে ক্রম অগ্রসর শিল্পমাধ্যমের যথার্থ বিচার হবে না।


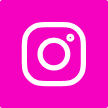


Leave a Reply