রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্টার থিয়েটারের অবদান আলোচনা কর।
স্টার থিয়েটার
৬৮ নং বিডন স্ট্রিট কলকাতা
উদ্বোধন: ২১ জুলাই, ১৮৮৩
স্থায়িত্বকাল: ২১ জুলাই, ১৮৮৩ – ৩১ জুলাই ১৮৮৭
প্রতিষ্ঠাতা: গুর্মুখ রায়
নাটক: দক্ষযজ্ঞ (গিরিশচন্দ্র ঘোষ)
কলকাতার ধনী ব্যবসায়ির পুত্র গুর্মুখ রায়’ বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা। থিয়েটারে প্রমোদের মোহে এবং বিশেষ করে বিনোদিনীর আকর্ষণে গুর্মুখ রায় থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। গিরিশ তখন প্রতাপচাঁদ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে নতুন থিয়েটারের আশায় ঘুরছিলেন। ন্যাশনালের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে ‘ক্যালকাটা স্টার কোম্পানী’ নামে একটি থিয়েটারের দল কোনক্রমে চালাচ্ছিলেন। অমৃতলাল মিত্র, অঘোরনাথ পাঠক, নীলমাধব চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, কাদম্বিনী, ক্ষেত্ৰমণি, বিনোদিনী প্রমুখ গিরিশ-অনুরাগী শিল্পী নিয়ে গিরিশচন্দ্র এই ‘ক্যালকাটা স্টার কোম্পানী’ চালু করেছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটাবের মঞ্চ ভাড়া নিয়ে তিনরাত্রি যথাক্রমে ২৮ ও ৩১ মার্চ এবং ১৭ এপ্রিল, ১৮৮৩, অভিনয়ও করেছিলেন। গুর্মুখ রায় গিরিশের কাছে প্রস্তাব দেন নতুন থিয়েটার ওলার। শর্ত একটাই—অভিনেত্রী বিনোদিনীকে তার রক্ষিতা হতে হবে। গিরিশ প্রমুখের অনুরোধে বিনোদিনী নতুন থিয়েটারের আশায় এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। তাছাড়া কথা ছিল, বিনোদিনীর নাম অনুসারেই এই নতুন নাট্যশালার নাম হবে ‘বি-থিয়েটার’।
বাগবাজারের কীর্তিচন্দ্র মিত্রের ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের খালি জমি ইজারা নিয়ে গুর্মুখ রায়ের অর্থে এবং গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, দাসুচরণ নিয়োগী, অমৃতলাল মিত্র প্রমুখের তত্ত্বাবধানে নতুন ‘ইষ্টক নির্মিত’ পাকা রঙ্গালয় তৈরি হলো। বিনোদিনীর নামে নামকরণ হয়ে, শেষ মুহূর্তে ‘স্টার থিয়েটার’ নামে রেজিষ্ট্রি করা হলো। বিনোদিনী কিন্তু মনপ্রাণ দিয়ে থিয়েটার চেয়েছিলেন এবং সেই থিয়েটার হবে তার নামে—এই রঙীন আশায় তিনি গুর্মুখ রায়ের আশ্রিতা হয়েছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীদের চক্রান্তে তাঁর সব আশা নষ্ট হয়ে গেল। এর নাম যে ‘স্টার’ দেওয়া হবে এমন একটা পরিকল্পনা গিরিশের মধ্যে ছিল এবং তার অস্থায়ী নাট্যদলের নাম তিনি ‘ক্যালকাটা স্টার থিয়েটার’ আগেই রেখেছিলেন। নতুন থিয়েটারের বাসনায় তিনি বিনোদিনীকে ‘টোপ’ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন মাত্র। বিনোদিনীও থিয়েটার ও নিজের নামাঙ্কনের প্রতি স্বভাবতই দুর্বল ছিলেন। তাছাড়া বিনোদিনীর নামে নামকরণ না হওয়ার আরেকটা কারণ হল সামাজিক বাধা। বারাঙ্গনা অভিনেত্রীর নামে একটি পাবলিক থিয়েটারের নামকরণ হবে, তাও তার জীবৎকালেই, এতখানি দুঃসাহস অনেকেরই ছিল না। তার ওপর বিনোদিনীর প্রতি অনেকেরই ঈর্ষা এবং সন্দেহ থাকাও স্বাভাবিক ছিল।
শুরু হল স্টার থিয়েটার। মালিক গুর্মুখ রায় হলেও এই মঞ্চের সর্বেসর্বা হলেন গিরিশ। তিনিই ম্যানেজার, নাট্যকার, পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা। প্রথম চার বছর একচ্ছত্রভাবে গিরিশের সব পৌরাণিক নাটক, পঞ্চরং-গীতিনাট্য এখানে অভিনীত হয়েছে। স্টেজ ম্যানেজার জহরলাল ধর, সঙ্গীত পরিচালক বেণীমাধব অধিকারী, কোষাধ্যক্ষ হরিপ্রসাদ বসু। প্রধান অভিনেতা ছিলেন গিরিশ নিজে, তাছাড়া অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোর পাঠক, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, বিনোদিনী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, গুণবিহারিণী প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রী।
১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই, শনিবার গিরিশের লেখা ‘দক্ষযজ্ঞ’ নাটক নিয়ে স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হও মহাসমারোহে। বিজ্ঞাপন বেরোল—
Grand Opening Night/Star Theatre.
Beadon Street./
Propietor: Baboo Goormuk Roy/Saturday, 21st July./
Baboo G.C. Ghose’s New Drama/Dakshya Yajna./
Everything Grand and wonderful/ G.C. Ghose. Manager.
(The Indian Daily News. 21 July 1883)
অভিনয় করলেন: দক্ষ—গিরিশ, মহাদেব—অমৃতলাল মিত্র, দধীচি—অমৃতলাল বসু, ব্ৰহ্মা—নীলমাধব চক্রবর্তী, বিষ্ণু—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, সতী—বিনোদিনী, তপস্বিনী—ক্ষেত্ৰমণি, প্রসূতি—কাদম্বিনী। দক্ষ, মহাদেব ও সতীর ভূমিকায় অভিনয় অনবদ্য হয়েছিল। বিশেষ করে মহাদেবরূপী অমৃত মিত্র, তাঁর অভিনয়ে সকলকে বিমোহিত করে দিয়েছিলেন। অভিনয়, সঙ্গীত, দৃশ্যসজ্জা, আলোর ব্যবহার, কারসাজি দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। ‘দক্ষযজ্ঞ’ নাটক দিয়ে স্টারের গৌরবময় যাত্রা শুরু হলো।
গুর্মুখ রায় মালিক হিসেবে ছিলেন মোটমাট ছয় মাস। তার থাকাকালীন স্টারে অভিনীত হয়—১৮৮৩: দক্ষযজ্ঞ (২১ জুলাই), ধ্রুবচরিত (১১ আগস্ট), রামের বনবাস (২৯ আগস্ট), সীতার বনবাস (২৬ সেপ্টেম্বর), সীতাহরণ, চক্ষুদান (রামনারায়ণ, ২৭ অক্টোবর), মেঘনাদবধ (২১ নভেম্বর), সধবার একাদশী (দীনবন্ধু, ৫ ডিসেম্বর), রাবণবধ (৮ ডিসেম্বর), নলদময়ন্তী (১৫ ডিসেম্বর), চোরের উপর বাটপাড়ি (অমৃতলাল, ২৬ অক্টোবর)।
এই ছয় মাসে দীনবন্ধু, রামনারায়ণ, অমৃতলালের একটি নাটক, মেঘনাদবধের নাট্যরূপ (গিরিশচন্দ্র) ছাড়া আর সবই গিরিশের লেখা নাটক। এবং গিরিশের সব নাটকই পৌরাণিক নাটক। দক্ষযজ্ঞের পর ধ্রুবচরিত্র ও নলদময়ন্তীও খুব সাফল্য লাভ করেছিল। ধ্রুবচরিত্র নাটকেই গিরিশ প্রথম বিদূষক চরিত্র সৃষ্টি করেন এবং অমৃতলাল বসু সেই চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করে তাকে প্রতিষ্ঠা করেন। ধ্রুব চরিত্রে ভূষণকুমারী গানে ও অভিনয়ে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। নলদময়ন্তী নাটকের অভিনয় উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। অমৃতলাল মিত্র (নল), অমৃতলাল বসু (বিদূষক), বিনোদিনী (দময়ন্তী) প্রমুখের অভিনয়ের প্রশংসা সংবাদপত্রের সমালোচনায় করা হয়েছিল।
১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে গুর্মুখ রায় আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের লোকজনের পীড়নে এবং ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে স্টারের স্বত্ব ছেড়ে দিতে চান। বিনোদিনীর জন্যই এই থিয়েটার, তাই তাকেই এর স্বত্ব, অন্তত অর্ধেক স্বত্ব দিতে চান। কিন্তু গিরিশ প্রমুখের প্রতিবন্ধকতায় বিনোদিনী কোনো স্বত্ব পেলেন না। গুর্মুখ রায় হতাশ হয়ে মাত্র এগারো হাজার টাকায় স্টার থিয়েটারের স্বত্ব বিক্রি করে দিলেন স্টারেরই চার জনকে অমৃতলাল মিত্র, দাসুচরণ নিয়োগী, হরিপ্রসাদ বসু ও অমৃতলাল বসু—১৮৮৪-র জানুয়ারি মাসে। গিরিশ পারিবারিক শর্তের কারণে মালিকানার অংশ নেননি। দক্ষযজ্ঞ ছাড়া স্টারের অন্য কোনো নাটকে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অভিনয়ও করেননি। গুর্মুখ চলে গেলেও বিনোদিনী স্টারে রয়ে গেলেন।
চার জন নতুন মালিকের তত্ত্বাবধানে স্টার আরো চার বছর চলেছিল। গিরিশ রইলেন সর্বেসর্বা হিসেবেই। ম্যানেজার, অভিনয় শিক্ষক, নাট্যকার হিসেবে। এই চার বছরের অভিনয়ের উল্লেখযোগ্য তালিকা—১৮৮৪: পূর্বের নাটকগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয় করা হয়। তাছাড়া অভিমন্যুবধ (১৬ মার্চ), কমলেকামিনী (২৯ মার্চ), বৃষকেতু, হীরার ফুল, (২৬ এপ্রিল) চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্জে (অমৃতলাল, ২৬ এপ্রিল), আদর্শ সতী (অতুল মিত্র, ২১ মে), শ্রীবৎসচিন্তা (৭ জুন), চৈতন্যলীলা (২ আগস্ট), প্রহ্লাদ চরিত্র (২২ নভেম্বর), বিবাহ বিভ্রাট (অমৃতলাল, ২২ নভেম্বর)।
এই বছরেও অমৃতলাল বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র ও দীনবন্ধুর একটি করে নাটক ছাড়া বাকি সব নাটকই গিরিশচন্দ্রের লেখা। এর সবই পৌরাণিক নাটক। এই বছরে নতুন নাটকের মধ্যে গিরিশের ‘চৈতন্যলীলা’র অভিনয় নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। পুরাণের বিষয় নিয়ে এতদিন নাটক লিখে গিরিশ ধর্মীয় কাহিনী বলছিলেন। চৈতন্যলীলায় শ্রীচৈতন্যের জীবন আশ্রয় করে তিনি এই নাটকে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের জয়গান এবং ধর্মীয় ভক্তিবাদের প্রবল স্রোত বইয়ে দিলেন। ধর্ম ও ভক্তির ভাবাবেগে হিন্দুধর্ম ও জাতীয়তাবাদ একাকার হয়ে গেল।
নিমাই-বিনোদিনী এবং নিতাই—বনবিহারিণী, নৃত্যে গীতে ও অভিনয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিলেন। এই নাটকে সুর সৃষ্টি করেন ও নৃত্য শিক্ষা দেন বেণীমাধব অধিকারী। চৈতন্যলীলা দেখতে আসেন পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪। তিনি নাট্যরসের চাইতে ধর্মীয় ভক্তিবাদের উন্মাদনায় আপ্লুত হন এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিশেষ করে চৈতন্যরূপী বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেন। সমাজে নিন্দিত ও শিক্ষিত মহলে অপাঙক্তেয় বাংলা থিয়েটার রামকৃষ্ণের পদার্পণে পবিত্র এবং গৃহীত হতে থাকে।
তাই থেকে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবশ্য স্মরণীয় ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। থিয়েটারের গ্রিনরুমে প্রখ্যাত কোনো নাট্যব্যক্তিত্বের ছবি না থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষিত হতে থাকলো।
এখানে গিরিশের প্রহ্লাদ চরিত্র তেমন জমেনি। তুলনায় প্রায় একই সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারে রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহ্লাদ চরিত্র অনেক বেশি সমাদর পেয়েছিল। স্টারে বরং অমৃতলালের মজার নাটক বিবাহ-বিভ্রাট খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল—১৮৮৫: চৈতন্যলীলা, ২য় ভাগ (১০ জানুয়ারি), দোললীলা (১ মার্চ), মৃণালিনী (১ এপ্রিল), পলাশীর যুদ্ধ (২৬ এপ্রিল), প্রভাস যজ্ঞ (৩০ মে), বুদ্ধদেবচরিত (১৯ সেপ্টেম্বর)।
এই বছরেও গিরিশের লেখাই প্রায় সব নাটক এবং সবগুলি পৌরাণিক। শুধু বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপ, নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যের নাট্যরূপ দুটি ব্যতিক্রম। অবশ্য এই দুটি নাট্যরূপ গিরিশেরই দেওয়া।
চৈতন্যলীলা প্রথম ভাগের অভিনয়ের সার্থকতায় এবং বিক্রির সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তার দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আশানুরূপ হলো না। প্রভাস যজ্ঞ কিছুটা চললেও সবচেয়ে সার্থক হল ‘বুদ্ধদেবচরিত’। স্যার এডুইন আর্নল্ডের কাব্য ‘লাইট অফ এশিয়া’ অবলম্বন করে গিরিশ এই নাটকটি লেখেন। অভিনয় করেছিলেন: সিদ্ধার্থ—অমৃতলাল মিত্র, শুদ্ধোধন—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, বিদূষক-শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুজাতা—প্রমদাসুন্দরী, গোপা—বিনোদিনী।
সৌভাগ্যবশত স্যার আর্নল্ড সে সময়ে কলকাতায় থাকার ফলে নাটকটির অভিনয় দেখেন। তার খুবই ভালো লাগে। তিনি এই অভিনয়ের ও নাটকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সংবাদপত্রে চিঠি লেখেন—
১৮৮৬: বিমঙ্গল ঠাকুর (১২ জুন), বেল্লিকবাজার (২৬ ডিসেম্বর), কমলেকামিনী (২৬ ডিসেম্বর)। এছাড়া আগের নাটকগুলিও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অভিনয় করা হয়েছিল।
এই বছরেও সবই গিরিশের লেখা পৌরাণিক নাটক অভিনীত হয়েছে। তবে সবচেয়ে সফল প্রযোজনা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর। এই নাটকেই গিরিশ প্রথম দেখালেন ইন্দ্রিয়জ প্রেম কীভাবে সাধনার পথে ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমোন্মাদনায় পরিণত হয়। ‘ভক্তমাল’ গ্রন্থ থেকে কাহিনী নিলেও গিরিশ তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, অনুভব এবং রামকৃষ্ণদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে নতুন করে রচনা করলেন। শুধু ভাবময় চরিত্র সৃষ্টিতেও তিনি অসামান্য কৃতিত্ব দেখালেন। এই নাটকের বড়ো সম্পদ এর গানগুলি। যেমন কথা, তেমনি সুর এবং নটনটীদের গায়নভঙ্গি। কাহিনী, ভাব, চরিত্র, সঙ্গীত ও অভিনয়ে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর একটি সফল প্রযোজনা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। অভিনয়ে ছিলেন—অমৃতলাল মিত্র (বিল্বমঙ্গল), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (সাধক), অঘোরনাথ পাঠক (ভিক্ষুক), বিনোদিনী (চিন্তামণি), গঙ্গামণি (পাগলিনী)। পাগলিনী, চিন্তামণি ও বিল্বমঙ্গলের অভিনয় অসামান্য হয়েছিল।
এছাড়াও বেল্লিকবাজারের রঙ্গরস ও ব্যঙ্গ এবং অমৃতলাল বসুর (দোকড়ি সেন) রঙ্গ ও শ্লেষাত্মক অভিনয়ে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। ‘বেল্লিকবাজার’ প্রসঙ্গে আরো একটি উল্লেখযোগ্য খবর হলো এই নাটকেই বিনোদিনীর মঞ্চে শেষ অভিনয়।
১৮৮৭: রূপসনাতন (২১ মে), বুদ্ধদেবচরিত ও বেল্লিকবাজার (৩১ জুলাই)।
এই বছর গিরিশেরই সব নাটক অভিনীত হল। নতুন নাটকের মধ্যে রূপসনাতন খুবই সাফল্যলাভ করেছিল। বিশেষ করে শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের ভাববিহুল অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করেছিল।
১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে শেষ অভিনয়। নাটক বুদ্ধদেবচরিত ও বেল্লিকবাজার। অমৃতলাল বসু অভিনয় শেষে মর্মস্পর্শী ভাষায় দর্শকদের বিদায় সম্ভাষণ জানান।
১৮৮৭ সাল স্টারের পক্ষে ভালো যায়নি। ১৮৮৭-এর ১ জানুয়ারি বিনোদিনী সহকর্মীদের দুর্ব্যবহারে ‘স্টার’ ছেড়ে দিলেন। স্টারে তাঁর শেষ অভিনয় ‘বেল্লিকবাজার-এর রঙ্গিণীর ভূমিকায়। বিনোদিনী ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে শুধু স্টার থিয়েটারই ছাড়লেন না, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ থেকেই চিরতরে বিদায় নিলেন। তারপরেও তিনি দীর্ঘজীবন বেঁচেছিলেন, কিন্তু কখনোই আর পাদপ্রদীপের আলোয় আসেননি।
স্টার তখন এমনিতেই ভালো চলছিল না। অন্যদিকে ধনকুবের মতিলাল শীলের নাতি গোপাল লাল শীল থিয়েটার করার সখে মত্ত হয়ে কৌশল করে স্টার থিয়েটারের জমি কিনে নিলেন। স্টারের স্বত্বাধিকারীদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হলো। তারা বাধ্য এবং নিরুপায় হয়ে ত্রিশ হাজার টাকায় এই থিয়েটার বাড়ি ছেড়ে দেন গোপাল শীলকে।
বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের বাড়িতে গোপাল লাল শীল খুললেন এমারেল্ড থিয়েটার। ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের প্রায় পাঁচ বছরের ইতিহাস শেষ হলো।
রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্টার থিয়েটারের অবদান
বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের কার্যাবলীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক—
- মধ্যবিত্ত যে যুবক সম্প্রদায় একটা জাতীয় আবেগে ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭২) তৈরি করেছিল সেই দলেরই বেশ কিছু ছেলে এই স্টারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই স্টার, আদি ন্যাশনালেরই ধারাবাহী, উত্তরসূরি। প্রধান শিল্পী ও কর্মীরা একই। পার্থক্য মালিকানায়। গোড়ার ন্যাশনাল ছিল শিল্পী ও কর্মীদের, স্টার হল একজন মালিকের। থিয়েটারে অনাগ্রহী একজন নটীলোলুপ মালিকের। স্টারের মধ্যে পূর্বতন ন্যাশনালের উত্তরাধিকার ছিল বলেই বাঙালির অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল।
- স্টারের পূর্বে সব থিয়েটারের নামের মধ্যেই একটা জাতীয়তাবোধের আবেগ ছিল। ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল ওরিয়েন্টাল প্রমুখ। ১৮৭৬-এর অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইনের ফাঁস চেপে বসার ফলে থিয়েটারে নাট্যাভিনয় ও নাটক থেকে জাতীয়তার আবেগ দূরে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারের নামকরণ থেকেও পূর্বের সেই অনুরাগ ফিকে হয়ে গেল। স্টার থেকেই নামকরণ হতে থাকল অন্য রকমস্টার, এমারেল্ড, বীণা, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনূর, অরোরা।
- এই স্টারেই গিরিশ তার নাট্যকার জীবনের সেরা নাটকগুলি রচনা করেছিলেন। চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, বুদ্ধদেব চরিত, রূপসনাতন, প্রহ্লাদচরিত, প্রভাসযুদ্ধ, অভিমন্যবধ, নলদময়ন্তী প্রভৃতি তাঁর সেরা পৌরাণিক নাটকগুলি এই স্টারের জন্যই লিখিত ও অভিনীত হয়। গিরিশ পূর্ণোদ্যমে পৌরাণিক নাটক রচনা শুরু করেছিলেন।
- বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবনের সেরা সময়ও এই স্টারেই। নানা চরিত্রে অসামান্য অভিনয় তাঁকে খ্যাতির উচ্চ শিখরে নিয়ে যায়। গিরিশ ও বিনোদিনীর যুগলবন্দী বাংলা থিয়েটারের এক গৌরববাজ্জ্বল অধ্যায়। আবার এই স্টারেই বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবনের শেষ অধ্যায় রচিত হয়ে যায়। খ্যাতির তুঙ্গে থাকতে থাকতেই তিনি এই স্টারেই জীবনের শেষ অভিনয় করেন।
- এখানেই ‘চৈতন্যলীলা’র অভিনয় দেখতে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসেন। অভিনয় দেখে অভিভূত তিনি ‘সোনার আতা ও শোলার আতা’র বিভেদ ভুলে (তার কাছে আসল নকল এক হয়ে গিয়েছিল।) সকলকে আশীর্বাদ করেন। বিশেষ করে চৈতন্যরূপী বিনোদিনীকে ‘চৈতন্য হোক’ বলে আশীর্বাদ করেন। বিনোদিনীর ঘৃণিত জীবনে এইরকম মহাপুরুষের আশীর্বাদ তাকে মোহাবিষ্ট করে তোলে। আধ্যাত্মিক ভাবোন্মাদনা দেখা দেয়। এই সময়েই তাঁর কন্যা শকুন্তলার মৃত্যু, স্টারের সহযোগীদের বিরূপ ব্যবহার, গিরিশের ছলনা ও চক্রান্ত্রে প্রতি অভিমান এবং নতুন আশ্রিত বাবুর থিয়েটারে অভিনয়ের অনিচ্ছা—বিনোদিনীকে বিপর্যস্ত করে তুলছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তখন থেকেই বিনোদিনী ভক্তির দিকে চলে যেতে থাকেন এবং এক সময়ে অভিনেত্রী জীবন ত্যাগ করে পুরোপুরি আধ্যাত্মিক জীবনচর্চায় নিমগ্ন হন। বাংলা থিয়েটার তার সেরা অভিনেত্রীর অভিনয় প্রতিভা থেকে বঞ্চিত হয়।
- শ্রীরামকৃষ্ণদেব থিয়েটারে আসেন ধমভাবের আকর্ষণে। তাতে বাংলা থিয়েটারের লাভ ও ক্ষতি দুটোই হলো। ক. লাভ এতোদিন যে থিয়েটার ভদ্র ও ঘনীয় মানুষের কাছে আপাঙক্তেয় ছিল, রামকৃষ্ণদেবের পদার্পণে তা ধন্য ও পবিত্র হলো। এরপর থেকে থিয়েটারের প্রতি মানুষের বিমুখ মনোভাব অনেকাংশে দূরীভূত হল। সামাজিকভাবে থিয়েটার যেন পাঙক্তেয় হয়ে উঠলো। খ. ক্ষতি শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণে ও আশীর্বাদে বিনোদিনী শুধু নয়, ধীরে ধীরে গিরিশের জীবনেও পরিবর্তন আসে। তাতে তাদের ব্যক্তিজীবনে যে শান্তিই আসুক না কেন, বাংলা থিয়েটারের ক্ষতি হয়েছে অপূরণীয়। বিনোদিনী অভিনয় ছেড়ে দিলেন, শৈব গিরিশ ‘ভক্ত ভৈরবে’ রূপান্তরিত হলেন। এরপর থেকে গিরিশের নাটকে পৌরাণিক বিষয়ের মধ্যে অহৈতুকি ভক্তিবাদ এবং রামকৃষ্ণপ্রচারিত ভক্তিতত্ত্ব প্রাধান্য পেতে থাকে। এই সময় থেকেই গিরিশের সব নাটকেই, এমন কি সামাজিক, ঐতিহাসিক নাটকেও ভক্তি ধর্মের তারল্য ও রামকৃষ্ণদেবের মতবাদ এবং সেই ধরনের চরিত্র সৃষ্টি হতে থাকে। গিরিশের নাটকের নাট্যগুণ বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- স্টার থিয়েটারে পঁচানব্বই ভাগ নাটকই পৌরাণিক নাটক অভিনীত হয়। পুরাণের বিষয় ও ধর্মীয় ভাব জাতীয় জীবনে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। হিন্দুধর্মভাব ও জাতীয়তাবোধ তখন যেন একাকার। রঙ্গক্ষেত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেল।
- স্টার একজন ব্যবসায়ির মালিকানাধীন হয়ে শুরু হলেও ছয় মাসের মধ্যেই অভিনেতা ও কর্মীদের স্বত্বাধীনে চলে আসে। সেইভাবেই চলে। তবে ১৮৭২-এর ন্যাশনাল থিয়েটার শিল্পী ও কর্মী সবাই মিলে চালাত। স্টারে কিন্তু সবাই নির্দিষ্ট চার জনের মালিকানাতেই চলেছিল।
- অনেক হাত ফেরতা হয়ে স্টারের ৬৮ নং বিডন স্ট্রীটের বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার ওপর দিয়ে চিত্তরঞ্জন এভেন্যু রাস্তা তৈরি হয়েছে।


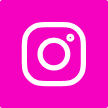


Leave a Reply