ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে কবি রমাকান্ত রথের কৃতিত্ব আলোচনা কর।
রমাকান্ত রথ
স্বাধীনতা-উত্তর ওড়িয়া কাব্যধারার একজন বিশিষ্ট কবি রমাকান্ত রথ। তাঁর জন্ম ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর। তিনি ছিলেন ইংরাজী সাহিত্যের ছাত্র। কটকের রাভেনশ কলেজ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পেশায় ছিলেন আই, এ. এস। অবসরপ্রাপ্তির আগে তিনি ওড়িশা সরকারের চিফ সেক্রটারির পদে কর্মরত ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে থাকলেও তাঁর কাব্যচর্চা অব্যাহত থেকেছে। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি সাহিত্যিকরূপে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে পদ্মভূষণ সম্মানলাভ করেন। সাহিত্য আকাদেমির তিনি সহ–সভাপতি পদও অলংকৃত করেছেন।
তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হ—১. কেতে দিনারে (১৯৬২) ২. অনেকা কোঠারি (১৯৬৭), ৩. সন্দিগ্ধ মৃগয়া (১৯৭১), ৪. সপ্তম ঋতু ( ১৯৭৭), ৫. সচিত্র আন্ধার (১৯৮২), ৬. শ্রী রাধা (১৯৮৪), ৭. শ্ৰী পলাতক ( ১৯৯৭)। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি কাব্যচর্চা শুরু করেন। কাব্যচর্চা বিষয়ে তিনি কবির সচেতন চৈতন্যের বিস্তারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন—‘‘The first and most important requirement is that the author must abandon his ego -sense. It is only then that he can perceive what connects one man to another, the living to the dead…The dreamer to the dream, echos to original sound.’’(Ramakanta Rath) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই রমাকান্ত রথ পাঠক মনে গভীর অভিমুদ্রণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম ‘কেতে দিনারে’ অর্থাৎ বিগত সময়। মূলত রোমান্টিক ভাবনাই ব্যঞ্জিত হয়েছিল এই কাব্যগ্রন্থে। তাঁর কবিতার বাচন ও ছন্দ ওড়িয়া কাব্যধারায় নতুন প্রস্থানের জন্ম দিয়েছিল। তিনি কাব্য বিষয়ে পাশ্চাত্যের এজরা পাউণ্ড প্রমুখের নৈর্বক্তিক জীবনবোধ, ইমেজিসম প্রভৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কাব্যবিষয়ে চৈতন্যবোধ, প্রজ্ঞার বিস্তার,জীবনের ব্যাপ্ত বিস্তার, বাস্তব ও অধিবাস্তব-তত্ত্বে আস্থাবান ছিলেন। তিনি মানুষের জীবনে তার যাপিত সময় এবং সেখানে নিয়তির অমোঘ লীলাকে কাব্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সেই সূত্রে মানুষের জীবনে নৈঃশব্দ, একাকীত্ব তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর কাব্যের কথক দেখা যায় নিজের আত্মচৈতন্যের সঙ্গেই সংযুক্ত থেকেছে বেশি, সমাজসত্তা, সামাজিকতার বোধ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। আত্মনিমগ্নতা থেকেই তাঁর কাব্যে বোধ ও বোধির জন্ম হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘অনেকা কোঠারি’ অর্থাৎ একাধিক ঘর। এই কাব্যগ্রন্থে আঠারোটি কবিতা আছে। এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত তিনটি দীর্ঘ কবিতা—‘বাঘ শিকার’, ‘অনন্ত শয়ান’, ‘দুর্ঘটনায় মৃত্যু’ শীর্ষক কবিতায় কবির অধিবাস্তব চেতনার প্রকাশ দেখা যায়, যেখানে পাঠক কবিসত্তার রুদ্ধস্বরের ক্ষীণাভাস লাভ করেন—‘‘hear the voice of the mendicant, which sometimes chokes and is not easily heard’’। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘সন্দিগ্ধ মৃগয়া’তে কবিচিত্তে দোলাচলতার প্রকাশ ঘটেছে। ‘সপ্তম ঋতু’ কাব্যগ্রন্থে কবির প্রতীক নির্মাণ এর প্রবণতা লক্ষিত হয়েছে। ‘সচিত্র আন্ধার’ বা ‘চিত্রময় অন্ধকার’ কাব্যগ্রন্থে কবির অধিবিদ্যামূলক চেতনার প্রাবল্য লক্ষিত হয়েছে। এই চেতনাই পরিণতি পেয়েছে তাঁর ‘শ্রীরাধা’ কাব্যগ্রন্থে। এই কাব্যগ্রন্থের উপজীব্য মৃত্যু-অতিক্রমী প্রেম। রাধার রূপকে যে ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে। এটিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। ‘শ্রীরাধা’ কাব্যের একটি অংশের অনুবাদ এইরকম—
Come, Take half
of the remainder of my life,
but fill every moment
of the mine
with your infatuation
was the bargain unfair?
Then leave me with a single moment
And take away the rest of my life,
But like the sky, fill the whole space
Above the moment. (Sriradha: part 19)
কবির রাধা এখানে বিরহখিন্না নন, ভাবসম্মিলনের অনন্ত প্রাপ্তিতে বিশ্বাসী। মৃত্যুকে সে অতিক্রম করেছে এই ভালোবাসার অনুভূতির তীব্রতায়—
My lifetime,
Unconcerned with its nearing death,
Would everyday renew its pilgrimage
To the early years of your youth,
You would exist as a mass of blue
Carved by my command. (ঐ)
Sriradha: আটান্ন সংখ্যক কবিতাতেও কবি রাধার প্রতীকে অনন্তের সঙ্গে আমাদের অস্তিত্বকে সমন্বিত করছেন এই বলে—
You have, my dearest, always suffered
All my inadequacies with a smile.
I know I am not destined to bring you back once you’ve left
All I can do hereafter, till the last day of my life,
Is to collect the fragments of what you are
And try to piece them together.
অনন্তের রূপ ও রূপকল্পের সন্ধানে আর নির্মাণেই কবি খণ্ড সত্তার সার্থকতা অনুভব করেছেন। কবিকৃত অপর একটি কবিতাংশের অনুবাদ এইরকম—
I offer this water to you,
My father, grandfather and great grandfather,
And to you, soldiers and generals
Who fought for us and who fought against us?
And who were killed by the war.
I stand here, on this battle field,
And give this water and this rice to you
You must be hungry and thirsty.
(A request to the dead)
এই কবিতায় কবি জীবনের মৌল সম্বল অন্ন আর জলকেই উজাড় করে দিতে চান বৃহতের উদ্দেশে। ‘Line Addressed to her Non- Resident presence’ কবিতায় কবি, তাঁর অনাম্নী প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে তাঁর অস্তিত্বের নিভৃত্যপনকে বর্ণনা করেছেন। কবির কল্পনায় ব্যক্তি, বৃহত্তর সমাজ, তার সামষ্টিক অস্তিত্ব, মহাজগত সব কিছুই মিলে মিশে আছে—
The steamer arrives every morning
To say good morning to women
Who hold entire rivers in their eyes?
The earth and the outer space are one.
The eyes of eyes and the ears of ears
Walk about in shaded coconut groves,
And gods and goddess stand at your doorsteps
Yearning for morsels of benediction
Flowing from your meditation on yourself.
কবি অনুভব করেন, এই পরিপার্শ্ব থেকে মহাজগত যেন বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছে সেই অনাম্নীর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই—
After your leave, what remains?
Bare rocks, the moonlight’s darkness
Erasing all future,
Several blood-stained tears, dead soldiers
Guarding unused gunpowder on the sea -bed,
And the desolate road I must walk on
Till the last day of my life.
রমাকান্ত রথের কাব্য-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য
কবি রমাকান্ত রথের কাব্যপাঠে যে কাব্যবৈশিষ্ট্যগুলি দৃষ্ট হয়, সেগুলি এইরূপ—
- দৃশ্যমান জগত ও মহাজগত, ব্যক্তি সত্তা ও অনন্তের উপলব্ধির যৌগপত্যে কবির কাব্যভুবন নির্মিত হয়েছে।
- পুরাণের আকল্পও কবি–ভাবনাকে বৃহতের সমীপবর্তী করেছে।
- কবির প্রকৃতিচেতনা তাঁর মহাজাগতিক বোধের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত হয়ে গেছে।
ওড়িয়া সাহিত্যধারায় কবি রমাকান্ত রথ এক নবীন কাব্যবোধ ও কাব্যভাষার জন্ম দিয়েছেন। ওড়িয়া সাহিত্যে তাঁর অবদান স্বীকৃত হয়েছে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিটিতে—‘‘the poems of Ratha arrest the common reader’s attention by a keenness of observation and by an intellectual quality that is not usual with the common run of this class of writers. Clarity of vision and a genuine coordinating spirit, present in each of his pieces, set them apart from the others, they prove also that form by itself has little to do with genuine poetic creation.’’ (Mayadhar Mansinha/A History of Oriya Literature)।


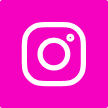


Leave a Reply