বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির প্রাক্কথা সম্পর্কে আলোচনা কর।
বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রাক্কথা
চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সূচনা চর্যাপদ থেকেই। কিন্তু ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকে। সেকারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় বাঙালির সেই প্রাচীনতম ঐতিহ্যের পরিচয় নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে যেভাবে সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহটঠের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে ঠিক তেমনি বাংলাদেশ আর্যভাষা প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে সংস্কৃত এবং প্রাকৃত, অপভ্রংশ যা কিছু রচিত হয়েছে তার আলোচনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মুখ্য অঙ্গ না হলেও উপক্রমণিকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বের ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—১. সংস্কৃত সাহিত্য ২. প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্য ৩. অবহটঠ সাহিত্য।
সংস্কৃত সাহিত্য
ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় প্রত্নলিপিতে ও ভূমিদানপত্রে। বাংলাদেশের প্রাচীনতম লিপি পাওয়া গেছে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে। প্রত্নলিপিবিদদের মতে লিপিটি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর অর্থাৎ অশোকের সমসাময়িক। মহাস্থানগড়ের লিপিটি ছোট এবং খণ্ডিত। এরপর যে লিপিটা পাওয়া গেছে সেটি প্রায় সাতশো বছর পরের সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক। এটির ভাষা সংস্কৃত। বাঁকুড়া জেলার অনতিদূরে শুশুনিয়া পাহাড়ের বিধ্বস্ত গুহার গায়ে বিষ্ণুর চক্রের নীচে ও পাশে এই লিপির কয়েকটি ছত্র উৎকীর্ণ আছে। এই দুটি লিপি ছাড়াও গুপ্ত রাজাদের আমলে প্রায় আট দশ খানা ভূমিদান পত্র বা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছিল।
খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর আগে বাংলাদেশের সাহিত্যগুণসম্পন্ন গদ্য পদ্য লেখা নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে সপ্তম শতাব্দীর আগেই বাঙালির সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য রচনার পরিচয় খুব দুর্লভ নয়। এইসময় যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল—পালকাপ্য রচিত ‘হস্ত্যায়ুর্বেদ’। ‘চান্দ্রব্যাকরণে’র প্রণেতা চন্দ্রগ্রহণ ওই যুগে আবিভুত হয়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তিনি ‘লোকানন্দ’ নামক নাটক এবং ‘শিষ্যলেখ’ নামক ধর্মকাব্য রচনাও করেছিলেন বলেও জানা যায়। এইসময় বাংলাদেশের বেশকিছু ন্যায়শাস্ত্রবিষয়ক টীকা এবং ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। যেমন—শ্রীধর ভট্টের ‘ন্যায়কন্দলি’, ভবদেব ভট্টের ‘ব্যবহারতিলক’, ‘প্রায়শ্চিত্ত ব্যাকরণ’, জীমূতবাহনের ‘দায়ভাগ’, ‘ব্যবহারমাতৃকা’, হলায়ুধের ‘ব্রাহ্মণসর্বস্ব’।
সেকালের বাঙালি কবিরা বড় বড় কাব্য অপেক্ষা ছোট ছোট কবিতা রচনায় বেশি তৎপর ছিলেন এবং এইসব শ্লোকে বাঙালির লিরিকধর্মিতা নতুন রূপ লাভ করেছিল। এইসময় বাংলাদেশে সংস্কৃত কবিতা রচনা ও রসচর্চার বিস্তার ছিল বিচিত্র। বিদ্যাধর সংকলিত ‘সুভাষিত রত্নকোষ’ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বস্তুত তুর্কি আক্রমণ-পূর্ব বাংলাদেশের কবিতাকৃতির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন ধরা আছে এই ‘সুভাষিত রত্নকোষ’ এবং ‘সদুক্তিকর্ণামৃত’ নামক সংকলন গ্রন্থে। এই দুটি সংকলনগ্রন্থের সংকলন কাল দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগ অর্থাৎ বঙ্গে তখনও পাল রাজাদের রাজত্ব চলছে। বিদ্যাধর সংকলিত ‘সুভাষিত রত্নকোষ’ সংস্কৃত ভাষায় প্রথম সংকলিত কোষকাব্য। এর আগে এইভাবে শ্লোক সংগ্রহের উদ্যোগ দেখা যায়নি। এতে প্রায় দেড়শ জন কবির ১৭৩৮টি শ্লোক গৃহীত হয়েছে। রচয়িতারা অনেকেই বাঙালি কবি ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনায় বাঙালি কবিরা যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তারই ঐতিহাসিক দলিল এই সংকলনগ্রন্থ। সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় তাঁর ‘সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালির দান’ গ্রন্থে জানিয়েছেন ‘সুভাষিত রত্নকোষ’-এর অংশবিশেষ ‘কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়’ নামক সংকলনগ্রন্থ। এই সংকলনের সম্পাদক এফ. ডব্লিউ টমাস সমগ্র পুথিটিকে ‘কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়’ নামে অভিহিত করেছেন। এই গ্রন্থের রচয়িতা কে তা জানা যায়নি তবে বৌদ্ধ ছিলেন তার প্রমাণ হল এই গ্রন্থের প্রথম দুটি ব্রজ্যায় বৌদ্ধ কবিতাগুলি সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থটিতে মোট ৫২৫টি কবিতা আছে। কবিরা কেউই একাদশ শতাব্দীর পরবর্তী নয়। তাই খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের মধ্যে গ্রন্থখানি সংকলিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। গ্রন্থের শ্লোকগুলি গীতিকবিতাধর্মী এবং বিভিন্ন ব্রজ্যায় বিভক্ত।
বাংলাদেশের সংকলিত আরেকটি জনপ্রিয় সংকলনগ্রন্থ হল ‘সদুক্তিকর্ণামৃত’ এই সংকলনগ্রন্থের সংকলক হলেন রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি বটু দাসের সুযোগ্য পুত্র মহামাণ্ডলিক শ্রীধর দাস। এই গ্রন্থে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের বাঙালির জীবন ও সমকালীন সমাজের যে প্রতিফলন প্রতিফলিত হয়েছে। এতে মোট পাঁচটি প্রবাহ এবং একটি প্রবাহে কয়েকটি বীচি, প্রত্যেক বীচিতে পাঁচটি করে কবিতা সংকলিত হয়েছে। এখানে ৪৮৫ জন কবির ২৩৭০টি কবিতা সংকলিত হয়েছেন। ‘সদুক্তিকর্ণামৃত’-এর মত সংকলন গ্রন্থের গুরুত্ব যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। এই সংকলনগ্রন্থ থেকে সমকালীন বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম দর্শন এবং বাংলার বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লেও পরোক্ষভাবে বৈষ্ণব পদাবলীতে এবং মঙ্গলকাব্যের দৈনন্দিন জীবনবিষয়ক কবিতাগুলিতে এর প্রতিফলন পড়েছে। বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে বিভিন্ন ধরনের শ্লোক রচনার মধ্যে দিয়ে বাঙালির লিরিক মননের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছিল তার প্রমাণ এই সংকলন। গ্রন্থটি বাঙালি কবিদের রচিত এবং বাঙালির দ্বারা সংকলিত প্রথম সংকলনগ্রন্থ।
বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না তার কারণ সেনযুগে যখন নতুন করে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চা আরম্ভ হয়, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অন্ধকার যুগ তখন শুরু হয়েছে। সুতরাং এইসব অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষায় বিশুদ্ধ সাহিত্য রচনার অবকাশ ঘটেনি। এ সময় যে-সমস্ত নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি ছিল— বিশাখদত্তের ‘মুদ্রারাক্ষস’ নারায়ণ ভট্টের ‘বেণীসংহার’ মুরারির ‘অনর্ঘরাঘব’, ক্ষেমীশ্বরের ‘চণ্ডকৌশিক’। কিন্তু নাটকগুলিতে এমন কোনো উল্লেখ নেই যার দ্বারা নাট্যকারদের জাত-কুল নির্ণয় করতে পারা যায়। কাব্যের ক্ষেত্রেও শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত, নীতিবর্মার কীচকবধ, প্রভৃতি বাঙালি কবিদের রচনা মনে করা হলেও সেই দাবির পিছনে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। এইসময় ‘রামচরিত’ নামক এই গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। যার রচয়িতা অভিনন্দ। রামপালের মহামন্ত্রী প্রজাপতি নন্দীর পুত্র, যিনি নিজেকে ‘কলিকা-বাল্মীকি’ বলে পরিচয় দিতেন, তেই সন্ধ্যাকর নন্দীও একটি ‘রামচরিত’ কাব্য রচনা করেছিলনে। কাব্যটিতে রামায়ণের কাহিনির পাশাপাশি রামপাল, দ্বিতীয় গোপাল এবং মদনপালের রাজত্বের ইতিহাস বর্ণিত আছে।
লক্ষণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্ন
উমাপতি ধর
সংস্কৃত কবি, লক্ষণসেনের অন্যতম মন্ত্রী। সুবর্ণগ্রামে (বর্তমান সোনারগাঁও) তাঁর জন্ম। উমাপতি লক্ষ্মণসেনের (আ. ১১৭৮-১২০৬) রাজসভার পঞ্চরত্নের অন্যতম ছিলেন। অপর চারজন ছিলেন জয়দেব, গোবর্ধন, শরণ ও ধোয়ী। জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দম্ কাব্যে উমাপতির বাগ্-বিন্যাসের প্রশংসা করেছেন। উমাপতি লক্ষ্মণসেনের পিতামহ বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালেখ রচনা করেন। এটি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত গৌড়ীয় রীতির স্বীকৃত নমুনা। তিনি লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনও রচনা করেন বলে ধারণা করা হয়। উমাপতিধরের আর কোনো মুখ্য রচনা পাওয়া যায়নি। শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত, জলহনের সূক্তিমুক্তাবলী এবং রূপগোস্বামীর পদ্যাবলী ও শার্ঙ্গধরপদ্ধতি কোষকাব্যে উমাপতির বেশ কিছু শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। বৈষ্ণবতোষিণী গ্রন্থেও তাঁর অনেক শ্লোক পাওয়া যায়। তাঁর কোনো কোনো শ্লোকে লক্ষ্মণসেনের বিজয়কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে আরও দুজন উমাপতির নাম জানা যায়। তাঁদের একজন শ্রীকৃষ্ণের জীবন অবলম্বনে কৃষ্ণচরিত ও চন্দ্রচূড়চরিত কাব্য প্রণয়ন করেন। অপরজনের গ্রন্থের নাম পারিজাতহরণ। গ্রিয়ার্সনের মতে, এ উমাপতি ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো এক সময় বর্তমান ছিলেন। আবার কেউ কেউ এ তিনজনকে একই ব্যক্তি বলে মনে করেন।
শরণ
তিনি ছিলেন সংস্কৃত কবি। তিনি গৌড়রাজ লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কথিত পঞ্চরত্নের অন্যতম ছিলেন। তাঁর সহকর্মী ছিলেন জয়দেব। জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দম্ কাব্যে শরণ সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি দুরূহ কাব্য রচনায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। শরণের মুখ্য কোনা রচনার সন্ধান পাওয়া যায়নি; তবে শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃতে শরণ, শরণদেব, শরণদত্ত ও চিরন্তন শরণের নামে বহু শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। রূপ গোস্বামীর পদাবলীতেও শরণের রচনার উদ্ধৃতি আছে। দুর্ঘটবৃত্তি নামক একখানা গ্রন্থের প্রণেতা হিসেবেও শরণদেবের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত এঁরা সকলে একই ব্যক্তি ছিলেন।
ধোয়ী
ধোয়ী একজন সংস্কৃত কবি ও লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্নের অন্যতম। ধোয়ী নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে বিভিন্ন জন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং তন্তুবায় সম্প্রদায়ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এ যাবৎ তাঁর একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেটি হলো ‘পবনদূত’। কাব্যটি বাঙালি কবিদের রচিত সংস্কৃত দূতকাব্যসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। মন্দাক্রান্তা ছন্দে ১০৪টি শ্লোকে রচিত এ কাব্যের শেষভাগের একটি শ্লোকে (১০১) গৌড়েন্দ্র লক্ষ্মণসেনকে কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কাব্যটিতে লক্ষ্মণসেন এবং গৌড়সহ ভারতের অন্যান্য কতিপয় স্থান ও নদনদীর বর্ণনা আছে। লক্ষ্মণসেন দিগ্বিজয় উপলক্ষে দক্ষিণদেশে গেলে কুবলয়বতী নাম্নী এক গন্ধর্বকন্যা তাঁর প্রেমাসক্ত হয় এবং সে পবন অর্থাৎ বায়ুকে দূত করে তাঁর নিকট প্রেরণ করে। এটাই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু। কাব্যটিতে গৌড়দেশের রাজধানীর চমৎকার বর্ণনা আছে। সে বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তখন বাংলায় সুপারি গাছের প্রাচুর্য ছিল (শ্লোক ৩৮)। আরও জানা যায় যে, দিগ্বিজয়কালে লক্ষ্মণসেন দক্ষিণদেশীয় রাজাদের পরাজিত করেন এবং তাঁর সময়ে বিজয়পুর ছিল গৌড়ের রাজধানী। এছাড়া তৎকালীন ভারতের দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের কিছু ভৌগোলিক তথ্যও এ কাব্য থেকে পাওয়া যায়। পবনের গতিপথের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি পান্ড্যদেশ, উরগপুর, সেতুবন্ধ, কাঞ্চীপুর, চোল, কেরল, অন্ধ্র, কলিঙ্গ, সুহ্ম প্রভৃতি স্থান; তাম্রপর্ণী, সুবলা, কাবেরী, গোদাবরী, রেবা, নর্মদা, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদী এবং ভিল ও শবরজাতির নাম উল্লেখ করেছেন। কাব্যটি রচনায় কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের প্রভাব আছে, তবে মেঘদূতের মতো এতে পর্ববিভাগ নেই। এর ভাষা প্রাঞ্জল ও সরস। ধোয়ীর কবিপ্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ জয়দেব তাঁকে ‘কবিক্ষ্মাপতি’ (কবিদের রাজা) এবং ‘শ্রুতিধর’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে দূতকাব্য রচনার দৃষ্টান্ত বিরল। এ হিসেবে পবনদূত সংস্কৃত দূতকাব্যের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। পবনদূত ব্যতীত সদুক্তিকর্ণামৃত, সুভাষিতমুক্তাবলী, শার্ঙ্গধরপদ্ধতি প্রভৃতি কোষকাব্যে ধোয়ী রচিত অনেক প্রকীর্ণ কবিতা পাওয়া যায়।
গোবর্ধন আচার্য
লক্ষণসেনের রাজসভার একজন সংস্কৃত কবি। তাঁর পিতা নীলাম্বরও ছিলেন একজন সংস্কৃত পন্ডিত এবং তিনি ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। কবি জয়দেব ও গোবর্ধন ছিলেন সমসাময়িক এবং লক্ষ্মণসেনের সভাকবি। গোবর্ধন স্বয়ং কাব্যমধ্যে বলেছেন, জনৈক সেনকুলতিলক রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর গ্রন্থ রচিত; এ সেনকুলতিলকই লক্ষ্মণসেন। গোবর্ধনের বিখ্যাত গ্রন্থের নাম আর্যাশপ্তশতী। হালের গাথাশপ্তশতী অনুসরণে এটি রচিত। আর্যাছন্দে রচিত এ গ্রন্থের নামকরণ অনুযায়ী এতে সাতশ শ্লোক থাকার কথা, কিন্তু বাস্তবে আছে ৭৬৪টি। শ্লোকগুলি শৃঙ্গাররসপ্রধান, পরস্পর নিরপেক্ষ এবং বর্ণানুক্রমে রচিত। কাব্যটি বিভিন্ন বিভাগ বা ব্রজ্যায় বিভক্ত। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষের খন্ড খন্ড চিত্র নিয়ে শ্লোকগুলি রচিত।
গোবর্ধনের রচনায় অলঙ্কারশাস্ত্রে নিষ্ঠা ও পরিহাসরসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এতে তৎকালীন গৌড়বঙ্গের রাজকীয় ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির কামকলাবিলাস ও ভুজঙ্গবৃত্তি প্রকটরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এতে একদিকে যেমন মানুষের অনাবিল দাম্পত্য প্রেম ও তরুণ প্রেমের উচ্ছ্বাস বর্ণিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আবার যৌনজীবনের নানা দিক যেমন, বিধিবহির্ভূত নাগরপ্রেম, যথেচ্ছ যৌনাচার ইত্যাদি চিত্রিত হয়েছে। দারিদ্রের কারণে মানুষের সামাজিক অধঃপতন, আবার তার মধ্যেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথার্থ ভালবাসার চিত্রও এ কাব্যে পাওয়া যায়। পাঠকসমাজে কাব্যটি খুবই জনপ্রিয় ছিল, যে কারণে একটি কাব্য রচনা করেই গোবর্ধন বিখ্যাত হয়েছিলেন। হিন্দি কবি বিহারীলালের প্রসিদ্ধ কাবগ্রন্থ সৎসঈ গোবর্ধনের আর্যাশপ্তশতী অনুসরণে রচিত। কবি জয়দেবও গোবর্ধনের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। পরবর্তীকালের সূক্তিমুক্তাবলী, শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, পদ্যাবলী প্রভৃতি কোষকাব্যে গোবর্ধনের বিভিন্ন শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে।
মহাকবি জয়দেব
জয়দেব দ্বাদশ শতকের কবি। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার অজয় নদের তীরবর্তী কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি গ্রামে তাঁর জন্ম। কেউ কেউ তাঁকে মিথিলা বা উড়িষ্যার অধিবাসী বলেও মনে করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ভোজদেব, মাতা বামাদেবী এবং স্ত্রী পদ্মাবতী। জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্নের অন্যতম; কারও কারও মতে তিনি কিছুকাল উৎকলরাজেরও সভাপন্ডিত ছিলেন। জয়দেবের বিখ্যাত রচনা ‘গীতগোবিন্দম্’। এটি একটি সংস্কৃত গীতিকাব্য। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এর মুখ্য বিষয়। ২৮৬টি শ্লোক এবং ২৪টি গীতের সমন্বয়ে ১২ সর্গে এটি রচিত। বর্ণিত বিষয়ের তত্ত্বনির্দেশক বারোটি ভিন্ন ভিন্ন নামে সর্গগুলির নামকরণ করা হয়েছে, যথা: সামোদ-দামোদর, অক্লেশ-কেশব, মুগ্ধ-মধুসূদন, স্নিগ্ধ-মধুসূদন, সাকাঙ্ক্ষ-পুন্ডরীকাক্ষ, ধৃষ্ট-বৈকুণ্ঠ, নাগর-নারায়ণ, বিলক্ষ-লক্ষ্মীপতি, মুগ্ধ-মুকুন্দ, মুগ্ধ-মাধব, সানন্দ-গোবিন্দ এবং সুপ্রীত-পীতাম্বর। কাব্যের নায়ক-নায়িকা রাধা-কৃষ্ণ হলেও তাঁদের প্রতীকে জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্ক এবং নর-নারীর চিরন্তন প্রেমই এর মূল বক্তব্য। রাগমূলক গীতসমূহ এ কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। পরবর্তীকালের বাংলা পদাবলি সাহিত্যে এর গভীর প্রভাব পড়েছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও সাহিত্য-রসিকদের নিকট গীতগোবিন্দম্ এক সময় পরম শ্রদ্ধার বিষয় ছিল। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে এটি এখনও নিত্য পঠিত হয়। ভারত ও ভারতের বাইরেও গ্রন্থটি বেশ জনপ্রিয় এবং ইংরেজিসহ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। গীতগোবিন্দম্-এর ওপর প্রায় অর্ধশত টীকাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। গীতগোবিন্দম্-এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এতে চরণশেষে অন্তমিল অনুসৃত হয়েছে, যা সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রায়শই দুর্লভ। এর ভাষা সহজ-সরল এবং প্রায় বাংলার কাছাকাছি। সংস্কৃত ও বাংলার যুগসন্ধিক্ষণে রচিত বলে গ্রন্থটির ভাষা এরূপ সহজ ও বাংলার অনুগামী হয়েছে। শ্রীধরদাসের কোষকাব্য সদুক্তিকর্ণামৃতে (১২০৬) গীতগোবিন্দম্-এর ৫টি শ্লোক ব্যতীত জয়দেবের নামাঙ্কিত আরও ২৬টি শ্লোক পাওয়া যায়। শিখদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেবে (ষোল’শ শতক) জয়দেবের দুটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। নাভাজি দাসের ভক্তমাল, হলায়ুধ মিশ্রের সেকশুভোদয়া প্রভৃতি গ্রন্থে এবং প্রচলিত জনশ্রুতিতে জয়দেব ও পদ্মাবতী সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। বৈষ্ণব সহজিয়াগণ জয়দেবকে আদিগুরু এবং নবরসিকের অন্যতম বলে মর্যাদা দিয়ে থাকেন। বীরভূমের কেন্দুবিল্বতে প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তিতে জয়দেব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, যা ‘জয়দেব মেলা’ নামে পরিচিত। এ মেলায় এখন বাউলদের সমাবেশ এবং বাউল আখড়াসমূহ বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে।
প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্য
প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। পালি, বৌদ্ধ-সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত, কাব্যের প্রাকৃত, অর্ধমাগধী—সবই প্রাকৃত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃত মধ্যভারতীয় আর্যভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বৈদিক বা সংস্কৃত থেকে এর উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। সংস্কৃত ভাষার যে রূপটি ছিল সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা, তা এক সময় শিথিল ও সরল হয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ ধারণ করে। কালক্রমে এগুলিকেই বলা হয় প্রাকৃত ভাষা। প্রাকৃত ভাষার নামকরণ প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন যে, এর প্রকৃতি বা মূল হচ্ছে ‘সংস্কৃত’, তাই প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত বলে এর নাম হয়েছে প্রাকৃত। আবার কেউ কেউ বলেন, ‘প্রকৃতি’ অর্থ সাধারণ জনগণ এবং তাদের ব্যবহূত ভাষাই প্রাকৃত ভাষা, অর্থাৎ প্রাকৃত জনের ভাষা প্রাকৃত ভাষা। তাই সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় নীচ শ্রেণীর অশিক্ষিত পাত্র-পাত্রীর ভাষা প্রাকৃত। তবে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার শুধু এদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এ ভাষায় অনেক মূল্যবান গ্রন্থও রচিত হয়েছে, যথা: গুণাঢ্যের বড্ডকহা বা বৃহৎকথা (আনু. ১ম শতক), হালের গাহাসত্তসঈ বা গাথাসপ্তশতী (আনু. ২য়-৩য় শতক), বাক্পতিরাজের গউডবহো বা গৌড়বধ (৮ম শতক) প্রভৃতি। হয়তো বিদ্বানদের ভাষা সংস্কৃত ছিল বলে সাহিত্যে এ ভাষাই প্রাধান্য পায়, আর প্রাকৃত হয়ে যায় কেবল সাধারণ লোকের ভাষা। প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি ও স্থিতিকাল মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৫ম/৬ষ্ঠ থেকে খ্রিস্টীয় ১০ম/১১শ শতক পর্যন্ত ধরা হয়। প্রাকৃত ভাষা প্রধানত পাঁচ প্রকার মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী ও পৈশাচী। গুরুত্ব বিচারে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতই শ্রেষ্ঠ। এর আদি নাম ছিল ‘দাক্ষিণাত্যা’, কিন্তু মহারাষ্ট্র অঞ্চলের ভাষা বলে স্থান-নামের প্রভাবে এর নতুন নাম হয় ‘মহারাষ্ট্রী’। হালের গাহাসত্তসঈ, বাক্পতিরাজের গউডবহো, সংস্কৃত নাট্যে নীচ শ্রেণীর পাত্র-পাত্রীর সংলাপ ও সঙ্গীতে এ ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের প্রধান কয়েকটি লক্ষণ হলো: ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ, সংস্কৃত স-স্থানে হ ইত্যাদি। মহারাষ্ট্রীর পরে শৌরসেনীর অবস্থান। এটি মথুরা অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। মথুরার রাজা শূরসেনের নামানুসারে এর নাম হয় ‘শৌরসেনী’। এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লক্ষণ হলো: সংস্কৃত ত-স্থানে দ, থ ও হ-স্থানে ধ ইত্যাদি। সংস্কৃত নাটকে সাধারণ নারী ও অশিক্ষিত পুরুষ এ ভাষায় কথা বলত। মাগধী প্রাকৃত ছিল পূর্বভারতীয় মগধের ভাষা, তাই এর নাম হয়েছে ‘মাগধী’। সংস্কৃত নাট্যে নীচ শ্রেণীর পাত্র-পাত্রীর সংলাপে এ ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। অশ্বঘোষের নাটক, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম্ প্রভৃতি গ্রন্থে এ ভাষার প্রাচীনতম রূপটি দেখা যায়। এ ভাষার বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ হলো: কেবল শ-র ব্যবহার, র-স্থানে ল, জ-স্থানে য, ত-স্থানে দ/ড, ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ ইত্যাদি। এই মাগধী প্রাকৃত থেকেই বাংলাসহ পূর্বভারতীয় আধুনিক ভাষাসমূহের উৎপত্তি হয়েছে। অর্ধমাগধীর ব্যবহার জৈনদের মধ্যে বেশি প্রচলিত ছিল। জৈনশাস্ত্রসমূহ এ ভাষায়ই রচিত। তাই একে জৈনপ্রাকৃতও বলা হয়। অশ্বঘোষ ও ভাসের নাটক ছাড়া আর কোথাও এর ব্যবহার নেই। অর্ধমাগধী প্রাকৃতের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: পদান্ত অ-স্থানে এ/ও, কেবল স-এর ব্যবহার, ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ ইত্যাদি। পৈশাচী প্রাকৃত পিশাচদের ভাষা এরূপ একটি মতবাদ প্রচলিত আছে। এর মূল কেন্দ্র ছিল ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। গুণাঢ্যের বৃহৎকথা এ ভাষায় রচিত। পৈশাচী প্রাকৃতের প্রধান কয়েকটি লক্ষণ হলো: ণ-স্থানে ন, গ-স্থানে ক, ঘ-স্থানে খ, জ-স্থানে চ ইত্যাদি। এ ছাড়া প্রাকৃতের আরও কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো পদান্তে ম-স্থলে ং, যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের আদিতে ছাড়া অন্যত্র যুগ্মধ্বনিতে পরিণত হওয়া, শব্দরূপ ও ধাতুরূপে দ্বিবচন বিলুপ্ত হওয়া ইত্যাদি। প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিবর্তনে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায় আদি বা মৌখিক প্রাকৃত, সাহিত্যিক প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ-অবহট্ঠ। প্রথম স্তরের স্থিতিকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৫ম/৬ষ্ঠ থেকে খ্রিস্টীয় ১ম শতক। এ সময় প্রাকৃতের শুধু মৌখিক ব্যবহার ছিল, সাহিত্যে এর কোন ব্যবহার ছিল না। বিভিন্ন শিলালেখ, তাম্রলিপি এবং অশোকের অনুশাসনেও এ ভাষা ব্যবহূত হতো। দ্বিতীয় স্তরের স্থিতিকাল খ্রিস্টীয় ১ম থেকে ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত। এ সময় বিভিন্ন প্রাকৃতে মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং সংস্কৃত নাটকে নীচ পাত্র-পাত্রীর সংলাপেও এ ভাষা ব্যবহূত হয়েছে। তৃতীয় স্তরের স্থিতিকাল ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম/১১শ শতক পর্যন্ত। পরে বিভিন্ন আধুনিক ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য সেসব আধুনিক ভাষার পাশাপাশি ১৮শ শতক পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে এ ভাষার ব্যবহার হয়েছে। প্রাকৃতে যথার্থ সাহিত্যচর্চার নিদর্শন পাওয়া যায় দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ সাহিত্যিক প্রাকৃতে। এ সময় জৈন ধর্মমূলক এবং ধর্মনিরপেক্ষ এ দুধারায় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। জৈনদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ আগমশাস্ত্র বা সিদ্ধান্ত (আয়রঙ্গসুত্ত, সূয়কড়ঙ্গসুত্ত ইত্যাদি) খ্রিস্টীয় ৫ম শতকের মধ্যে রচিত। এতে জৈনাচার্য মহাবীরের বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া আগমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ নিজ্জুত্তি, চুণ্ণী, পউমচরিঅম্ (জৈন রামায়ণ), হরিবংশপুরাণ (জৈন মহাভারত) এবং জৈন আচার্য ও তীর্থঙ্করদের জীবনী অবলম্বনে বিভিন্ন চরিতকাব্যও রচিত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ প্রাকৃত সাহিত্য ছিল গণজীবনের একেবারে কাছাকাছি। এতে সামাজিক উপাদান ছিল সবচেয়ে বেশি। এ সাহিত্যকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়: সংস্কৃত নাটকে সংলাপ ও গীতিকবিতা, মহাকাব্য, নীতিকাব্য, ঐতিহাসিক কাব্য ও কথানক কাব্য। প্রাকৃত ভাষার প্রথম সাহিত্যিক প্রয়োগ দেখা যায় সংস্কৃত নাটকে। নাট্যকাররা নীচ শ্রেণির পাত্র-পাত্রীর মুখে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা দিয়েছেন। এভাবে চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের ফলে নাট্যকাহিনীর বাস্তবতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভাস-কালিদাসসহ বিভিন্ন বাঙালি রচিত সংস্কৃত নাটকেও এ রীতি অনুসৃত হয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রম্, কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়ম্, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম্ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রেমবিষয়ক অনেক গীতিকবিতা প্রাকৃতে রচিত হয়েছে। এছাড়া স্বতন্ত্রভাবেও অনেক গীতিকবিতা রচিত হয়েছে, যা পরে গাহাসত্তসঈ, বজ্জালবগ্গ (আনু. ১১শ শতক) ইত্যাদি কোষগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। প্রাকৃত গাথাকাব্যের মতো অপভ্রংশেও এক শ্রেণির কাব্য রচিত হয়েছে, যা দোহা বা দোহাকোষ নামে পরিচিত। এর কবিতাগুলিতে অন্ত্যানুপ্রাস অর্থাৎ চরণান্ত মিল দেখা যায়। পরবর্তীকালে বাংলাসহ অন্যান্য আধুনিক সাহিত্যে অন্তমিলের এই রীতি অনুসৃত হয়েছে। দোহাকোষগুলিতে ধর্মসাধনার সহজ উপদেশ মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এই দোহাকোষগুলি বাংলা ভাষার উৎপত্তিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। প্রাকৃত মহাকাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবর সেনের রাবণবহো বা রাবণবধ (৫ম/৬ষ্ঠ শতক), বাক্পতিরাজের গউড়বহো বা গৌড়বধ (৮ম শতক), পুষ্পদন্তের (১০ম শতক) জসহরচরিউ বা যশোধরচরিত ও নায়কুমারচরিউ বা নাগকুমারচরিত, গুণচন্দ্র গণীর মহাবীরচরিয় বা মহাবীরচরিত (১১শ শতক), কোঊহলের লীলাবঈকহা বা লীলাবতীকথা, হেমচন্দ্রের (১০৮৮-১১৭২) কুমারপালচরিয় বা কুমারপালচরিত প্রভৃতি। প্রথমটিতে রামায়ণের রাবণবধ এবং দ্বিতীয়টিতে গৌড়রাজের নিধন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থটিতে যথাক্রমে রাজা যশোধর এবং জৈনাচার্য নাগকুমারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জৈনগুরু মহাবীরের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে মহাবীরচরিয় এবং সিংহল রাজকন্যা লীলাবতীর প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে লীলাবঈকহা। কুমারপালচরিয়ের কাহিনী অন্হিলবাদের রাজা কুমারপালের জীবনী। নীতিকাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য জিনদত্ত সূরির চ্চচরী, উপদেশরসায়নরাস ও কালস্বরূপকুলকম্। এগুলিতে গুরু জিনবল্লভ সূরির বন্দনা এবং নানাবিষয়ক উপদেশমালা লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রাকৃত ঐতিহাসিক কাব্য হিসেবে উপর্যুক্ত গৌড়বহো, লীলাবঈকহা এবং কুমারপালচরিয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখ করা যায়। এগুলিতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আছে। এছাড়া জিনপ্রভ সূরির তীর্থকল্প গ্রন্থটির নামও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এতে এমন অনেক রাজা ও তীর্থের নাম আছে যা ইতিহাস রচনায় সহায়ক হতে পারে। প্রাকৃত কথানক কাব্য হচ্ছে আগমগ্রন্থের ভাষ্যান্তর্গত বিভিন্ন উপকথা। এ বিষয়ে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ভবদেব সূরির কালকাচার্য কথানক। এটি গদ্যে-পদ্যে রচিত। এতে ধর্মব্যাখ্যার পাশাপাশি প্রচুর সাহিত্যরসের উপাদান আছে। এছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থ হলো শ্রীচন্দ্রের কথাকোষ (১২শ শতক), সোমচন্দ্রের কথামহাবোধি (১৫শ শতক), গুণাঢ্যের বড্ডকহা প্রভৃতি। বড্ডকহা শুধু প্রাকৃতেই নয়, সংস্কৃত গল্পসাহিত্যেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই পরবর্তীকালে এটি অবলম্বনে সংস্কৃতে রচিত হয়েছে সোমদেবের কথাসরিৎসাগর, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী এবং বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথা। প্রাকৃত ভাষায় অনেক গদ্যপ্রধান রচনাও রয়েছে। সেসবের মধ্যে আছে কাহিনীমূলক সাহিত্য, নাটক, ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দ, জ্যোতিষ ও দর্শন। কৃষ্ণকথা অবলম্বনে সঙ্ঘদাস ও ধর্মসেন গণী রচিত বসুদেবহিন্ডী এবং হরিভদ্র সূরির সমরাইচ্চকহা (সমরাদিত্যকথা) উল্লেখযোগ্য কাহিনীকাব্য। প্রাকৃত সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাট্যশাখা ততটা বিকশিত হয়নি। এক্ষেত্রে রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী (১০ম শতক), নয়চন্দ্রের রম্ভামঞ্জরী (১৫শ শতক), রুদ্রদাসের চন্দ্রলেখা (১৭শ শতক), বিশ্বেশ্বরের শৃঙ্গারমঞ্জরী (১৮শ শতক) উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃত ব্যাকরণের ইতিহাস খুবই প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। ব্যাকরণ রচয়িতা হিসেবে শাকল্য, কোহল, বামনাচার্য, সমন্তভদ্র প্রমুখের নাম জানা গেলেও তাঁদের গ্রন্থ পাওয়া যায় না। এঁদের পরে বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশ, হেমচন্দ্রের শব্দানুশাসন, ত্রিবিক্রমের প্রাকৃত ব্যাকরণ, মার্কন্ডেয়র প্রাকৃতসর্বস্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হেমচন্দ্র প্রাকৃত ব্যাকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। প্রাকৃতে অভিধানও খুব একটা রচিত হয়নি। ধনপালের পাইয়লচ্ছী-নামমালা (১০ম শতক) এবং হেমচন্দ্রের দেশি-নামমালা (১২শ শতক) গ্রন্থদুটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়টিতে অজ্ঞাতমূল দেশি ও আঞ্চলিক শব্দসমূহ সংকলিত হয়েছে। প্রাকৃত ছন্দ নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে। ছন্দোবৈচিত্র্য প্রাকৃত কাব্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃতে অনেক ছন্দোগ্রন্থ রচিত হয়েছে, তবে পিঙ্গলের প্রাকৃতপৈঙ্গল এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এতে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ উভয় ছন্দ সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা ছন্দের উৎপত্তি ও বিকাশে প্রাকৃত ছন্দের প্রভাব সংস্কৃত ছন্দের চেয়েও বেশি। প্রাকৃতে যেসব দর্শনগ্রন্থ রচিত হয়েছে তার অধিকাংশই জৈনদর্শনবিষয়ক। খ্রিস্টীয় ১ম-২য় শতকের তিনটি বিখ্যাত দর্শনগ্রন্থ হলো প্রবচনসার, নিয়মসার এবং পঞ্চাস্তিকায়সার। বিখ্যাত জৈন দার্শনিক সিদ্ধান্ত চক্রবর্তী নেমিচন্দ্র দ্রব্যসংগ্রহ ইত্যাদি পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে আরও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। জ্যোতিষ বিষয়ে প্রাকৃতে বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তার মধ্যে দিগম্বর জৈনাচার্য দুর্গাদেবের রিষ্ট সমুচ্চয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি অর্ঘকান্ড ও মন্ত্রমহোদধি নামে আরও দুটি জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করেন। প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষায় রচিত যেসব গ্রন্থের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো তাতে তৎকালীন সমাজের অনেক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সে যুগের সাধারণ মানুষের জীবন-যাপন, তৎকালীন ভারতের জ্ঞান ও শিল্পসাধনা, দ্যূতক্রীড়া, ব্যভিচার, পানদোষ, চৌর্যবৃত্তি, প্রকৃতির বর্ণনা ইত্যাদি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।
অবহটঠ সাহিত্য
নবম শতাব্দীর থেকে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত পশ্চিমে গুজরাট থেকে পূর্বে বাংলা অব্দি সমগ্র আর্যাবর্তে অপভ্রংশের অর্বাচীন রূপ অবহটঠ বা ‘অপভ্রষ্ট’ প্রচলিত ছিল লোকসাহিত্যের ভাষারূপে। বাংলা দশম শতাব্দী থেকে ধীরে ধীরে প্রাদেশিক রূপ লাভ করলেও সামনে কোন আদর্শ না থাকায় তা সাহিত্যে তেমনভাবে গৃহীত হয়নি। তবুও কথ্যভাষায় পদ ও বাক্রীতি সমসাময়িক অবহটঠ রচনার মধ্যে প্রায়ই আত্মপ্রকাশ করেছে। বুদ্ধের জীবনী কাব্য ‘ললিতবিস্তর’-এ অবহটঠের কিছু নিদর্শন লক্ষ করা যায়। অষ্টম শতাব্দীর আগে থেকেই অপভ্রংশ ও অবহটঠ উত্তরভারতে সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী সাধুভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ভাষায় জৈনদের লেখা অনেক বই পাওয়া গিয়েছে। বৌদ্ধ সহজপন্থীদের এবং শৈব নাথপন্থীদের অপভ্রংশ ছড়া, পদ সবই ধর্মবিষয়ক। এর বাইরে অবহটঠ কবিতা পাওয়া যায় কোন কোন গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে, একটি শিলালেখে ও একটি সংকলনগ্রন্থে। যে শিলালিপিতে অবহটঠ রচনা পাওয়া গেছে সেটি মালব থেকে পাওয়া। শিলালিপিটি বোম্বাই প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়াম-এ রক্ষিত আছে। শিলালিপির রচনাকাল দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শব্দ। নীতিবাক্য, বহুদর্শীর উপদেশ, আবহাওয়া ও কৃষি সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ে ছড়া অবহটঠেও প্রচলিত ছিল। এগুলি বরাবর চলে এসেছে কালোচিত ভাষা পরিবর্তন নিয়ে। বাংলায় এমন ছড়া ডাকের বচন নাম পেয়েছে। ধর্মদাসের ‘বিদগ্ধমুখমণ্ডন’ সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বে উল্লিখিত আছে। সুতরাং বইটির রচনাকাল দ্বাদশ শতাব্দীর পরে নয়। এখানে এমন কয়েকটি প্রহেলিকা বা সমস্যা-শ্লোক আছে যাতে প্রশ্ন-উত্তর অথবা শুধু উত্তর অবহটঠে দেওয়া। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে সংকলিত প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রাকৃত পৈঙ্গল গ্রন্থের নাম অনেকগুলি কবিতা ও গান পাওয়া গিয়েছে যেগুলি অপভ্রংশ-অবহটঠে ছন্দোনিবন্ধ গ্রন্থ হল ‘প্রাকৃতপৈঙ্গল’। তবে অবহটঠে লেখা হলেও এতে বাংলা, মৈথিলী প্রভৃতি আধুনিক ভাতরীয় ভাষার ছাপ রয়েছে।


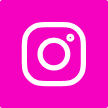







Leave a Reply