বাংলা নাটকের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অবদান আলোচনা কর।
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩) একাধারে কবি, নাট্যকার, সংগীত রচয়িতা, সুরকার, গায়ক এবং একজন স্বদেশপ্রেমিক। নাট্যকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি মূলত নাট্যসাহিত্যে আধুনিক নাটকের বৈশিষ্ট্য রূপায়ণে। রচনার আঙ্গিক, ভাষা ও ভাবের দিক থেকে তিনি বাংলা নাটকের মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন দিকের আগমন ঘটালেন। নাট্যসাহিত্যে তাঁর অবদান মূলত ঐতিহাসিক নাট্যকাররূপে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য আঙ্গিককে নাট্যসাহিত্যে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান যথেষ্ট। তাছাড়া উনিশ শতকের বাংলাদেশে নবচেতনার বিকাশে তাঁর নাটকগুলির ভূমিকা ছিল অসামান্য।
দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনাকে চার শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন— (১) ঐতিহাসিক নাটক:- ‘তারাবাঈ’ (১৯০৩), ‘প্রতাপসিংহ’ (১৯০৫), ‘দুর্গাদাস’ (১৯০৬), ‘নূরজাহান’ (১৯০৮), ‘মেবার পতন’ (১৯০৮), ‘সোরাব রুস্তম’ (১৯০৮), ‘সাজাহান’ (১৯০৯), ‘চন্দ্রগুপ্ত’ (১৯১১), ‘সিংহল বিজয়’ (১৯১৫)। (২) সামাজিক নাটক:- ‘পরপারে’ (১৯১২), ‘বঙ্গনারী’ (১৯১৫)। (৩) পৌরাণিক নাটক:- ‘পাষাণী’ (১৯০০), ‘সীতা’ (১৯০৮), ‘ভীষ্ম’ (১৯১৪)। (৪) প্রহসন:- ‘একঘরে’ (১৮৮৯), ‘কল্কি অবতার’ (১৮৯৫), ‘বিরহ’ (১৮৯৭), ‘ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার’ (১৯০০), ‘প্রায়শ্চিত্ত’ (১৯০২), ‘পুনর্জন্ম’ (১৯১১), ‘আনন্দ বিদায়’ (১৯১২)।
ঐতিহাসিক নাটক
জাতীয় উন্মাদনা ঐতিহাসিক নাটকের সাধারণ লক্ষণ ও মৌল প্রেরণা হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের মৌলিকতার প্রমাণ রয়েছে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকে জাতীয় ভাবধারার প্রতিফলন ঘটেছে নাট্যকারের ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার প্রতিচ্ছবিতে। নাট্যকার দীর্ঘকাল প্রবাস জীবন-যাপনের ফলে পাশ্চাত্য জীবনধারার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ইহজগতের প্রতি উন্মুখতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, যা তাঁর মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছিল। সুতরাং এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার পরিচয় নেওয়া আবশ্যক। ব্যক্তিগত জীবনে বিলাত থেকে প্রত্যাগত হয়ে হিন্দু সমাজে একঘরে হয়েছিলেন বলে তিনি ধর্ম সম্বন্ধে সংস্কার ও অহেতুক ভক্তিভাব বর্জন করে মানবিকতানির্ভর যুক্তিবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন।
‘তারাবাঈ’ (১৯০৩) দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম ইতিহাসাশিত নাটক। নাটকের মূল বৃত্তান্তও রাজস্থান থেকে গৃহীত। এই নাটকটির রচনা বঙ্গভঙ্গের আগে হলেও এর মধ্যে স্বদেশপ্রেমের অভাব নেই। হিন্দু মেলার পর থেকেই দেশের লোকের মনে অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত করবার প্রয়াস নাট্যকারদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। তবে বঙ্গভঙ্গের সমসময়ে ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ আরও সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অতীত ইতিহাসের মোহময় পরিবেশের প্রতি তাঁর চিত্তের যে একটি স্বাভাবিক উন্মুখতা ছিল, মুখ্যত সেই প্রেরণাতেই নাটকটি পরিকল্পিত। এজন্য নাটকটিতে সমসাময়িক চিন্তাধারায় অতীত ইতিহাসের ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যানের পরিবর্তে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহারই নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল। বীর চরিত্রের অন্বেষণ করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে রাজপুতবীর চরিত্র পৃথ্বীরাজ নাট্যকারকে আকৃষ্ট করেছে। এছাড়া নাটকের নাম ভূমিকায় বীরাঙ্গনা চরিত্রকেও ঠিক এই কারণে এনেছেন। শুধু তাই নয়, জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি যে নারী মুক্তির আন্দোলন | সেই সময় চলছিল সে দিকের প্রতি দৃষ্টি রেখে নাট্যকার তারাবাঈ চরিত্রকে অঙ্কন করেছেন। তাই তারাবাঈ দ্বিজেন্দ্রলালের স্ত্রী-স্বাধীনতার আকাঙক্ষায় রূপলব্ধ।
দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভাকে স্বদেশী আন্দোলন কতখানি প্রভাবিত করেছিল তার প্রথম সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ‘প্রতাপসিংহ’ (১৯০৫) নাটকে। নাট্যকার প্রতাপসিংহকে ‘জাতীয় বীর’ রূপে গ্রহণ করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় নাট্যকার বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের শৌর্য, বীর্য, দেশপ্রেম ও অতুলনীয় আত্মত্যাগের মহিমময় চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রতাপের সংগ্রামশীলতা ও দুঃখ বরণের কাহিনি সে যুগের রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু চরিত্রটির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বকে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। নাটকটিতে সমসাময়িক স্বদেশবোধের প্রকাশ নানাভাবে ঘটেছে। চারণকবি পৃথ্বীরাজের পত্নী যোশীর চরিত্রও ঐ ভাবের বাহক। পৃথ্বীরাজও মোগল বন্দনা ছেড়ে অবশেষে জাতীয় প্রেরণার সঙ্গীত রচনা করেছেন। সমসাময়িক স্বদেশী আন্দোলনের দিনে দ্বিজেন্দ্রলাল জাতীয় যে দুর্বলতাগুলির কথা উল্লেখ করেছিলেন নাটকটিতে যেন তারই অবিকল প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।
টডের রাজস্থান কাহিনি অবলম্বনে দ্বিজেন্দ্রলালের পরের নাটক ‘দুর্গাদাস’ (১৯০৬)। নাট্যকার স্বদেশ ও স্বজাতিবোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় বীর রূপে দুর্গাদাসকে নাট্যকার রূপ দিয়েছেন। কিন্তু চরিত্রটির মধ্যে আদর্শের আতিশয্য বড্ড বেশি। বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় স্বদেশপ্রেমের সহনীয়তাকে, বীরত্বের রূপকে অতিমাত্রায় দেখাবার পক্ষপাতী ছিলেন নাট্যকার–যা তখনকার নেতাদের মধ্যে অভাব ছিল। সেজন্য হয়ত চরিত্রটির মধ্যে উচ্ছ্বসিত স্বদেশপ্রেম ও অপূর্ব বীরত্ব কীর্তির উপস্থাপনা করেছেন। রাণা প্রতাপের স্বদেশপ্রীতির মধ্যে একটি মর্ত্য পরিচয় ছিল—দুর্গাদাস চরিত্রে তার অভাব। সেজন্য চরিত্রটিকে রক্তমাংসের মানুষ বলে বোধ হয় না। আসলে দ্বিজেন্দ্রলাল আসল স্বদেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাতে চেয়েছিলেন চরিত্রটির মধ্যে।
‘দুর্গাদাস’-এর পরবর্তী নাটক ‘নূরজাহান’ (১৯০৮) নাট্যকারের স্বতন্ত্র রচনা ও সার্থক সৃষ্টি। এই নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার নায়িকা চরিত্রকে দোষে-গুণে ভরা চরিত্ররূপে ও বাহিরের দ্বন্দ্ব অপেক্ষা অন্তরের দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যার জন্য ব্যক্তিচরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবসমীক্ষার সমন্বয়ে নূরজাহানকে ট্রাজিক চরিত্ররূপে উপস্থাপন করতে পেরেছেন।
নূরজাহানের অন্তর্জীবন, তার গভীরতর সত্তার আত্মক্ষয়ী সংগ্রাম-ই দ্বিজেন্দ্রলালের অবলম্বন। নাট্যকার তৎকালীন যুগজীবনের পটভূমিকায় দুই বিপরীত চিত্তবৃত্তির দ্বন্দ্ব দেখাতে চেয়েছেন। একজন ঘরোয়া তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ নারীর কল্যাণীর রূপ—তার মানবিক সত্তা। অন্যজন দয়ামায়াহীন ক্ষমতাগৃধ্নু মানুষের পৈশাচিক সত্তা। এই দুই বিপরীত চিত্তবৃত্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে কীভাবে নূরজাহান চরিত্রের দানবীয় সত্তার কাছে মানবীয় সত্তার পরাজয় ঘটল এবং কীভাবে সেটি ধীর অথচ অনিবার্য ধ্বংসের দিকে আকর্ষণ করল, এইটিই চরিত্রটির মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। এখানেও নাট্যকার মনুষ্যত্ববোধের কথাই বলেছেন।
রাজস্থানের ইতিবৃত্ত নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল যে নাটক রচনা শুরু করেছিলেন, ‘মেবার পতন’ (১৯০৮) সেই ধারায় শেষ নাটক। নাটকটিতে জাতীয় ভাবধারার প্রতিফলন থাকলেও জাতীয় প্রেমেই সমাপ্ত নয়, তা বিশ্বপ্রেমে পরিব্যাপ্ত। উগ্র স্বদেশবোধ থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের পরিবর্তমান মানসের এটি একটি স্পষ্ট স্বাক্ষর।
‘সাজাহান’ (১৯০৯) দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। সাজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্ব নূরজাহানের পরিপূরক। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মাধ্যমে নাট্যকার এই নাটকটিকে সার্থক ট্রাজেডি রূপে চিত্রিত করেছেন। এই সময় নাট্যকারের স্বাদেশিকতাবোধ কমে এসেছিল। তবুও মহামায়া চরিত্রের মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটেছে। নাট্যকার উগ্র জাতীয়তাবোধের যে পরিপন্থী ছিলেন তার প্রমাণ আমরা পূর্ববর্তী নাটকগুলিতে পেয়েছি। সেদিক থেকে সরে এসে দ্বিজেন্দ্রলাল মানুষের ক্ষমা, ধৈর্য, প্রেম, প্রীতি ও মানবিকতার উদ্বোধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সাজাহানের বাৎসল্য স্নেহ তাই সম্রাটত্বের কাছে পরাজয় বরণ করেনি। তাই দেখি, ঔরঙ্গজেব সব কিছু পেয়েও মনুষ্যত্বকে হারিয়েছিল বলে সে জয়ী হয়নি, নিজেকে শেষ পর্যন্ত অপরাধী মনে করে পিতার পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করেছে। সম্রাট সত্তা ও পিতৃ সত্তার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ট্রাজেডির নায়ক সাজাহান অপরাধী পুত্রকে ক্ষমা করে তার বাৎসল্যস্নেহের পরিণামী রূপটিকে স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করেছেন।
পরপর পাঁচটি রাজপুত মোগল ইতিহাস নিয়ে নাটক রচনার পর দ্বিজেন্দ্রলাল দৃষ্টি ফেরান হিন্দুযুগের প্রতি। এর ফলস্বরূপ তিনি লেখেন ‘চন্দ্রগুপ্ত’ ও ‘সিংহল বিজয়’। পুরাণ ও গ্রীক ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটক রচনা করেছেন। ‘চন্দ্রগুপ্ত’ তার বৈমাত্রেয় ভাই নন্দকে সিংহাসনচ্যুত করে চাণক্যের সাহায্যে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটান। এই কাহিনি অবলম্বনে দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রীক ইতিহাস থেকে সেলুকাস অ্যান্টিগোনাস ও হেলেনের বৃত্তান্ত জুড়ে দিয়ে তিনি চন্দ্রগুপ্ত নাটক রচনা করেন। নাটকে চাণক্য চরিত্রের বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি তার ব্যর্থ জীবনের যন্ত্রণাও স্থান এই নাটকের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ যুগলক্ষণ। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিকতার পরিচয় এই নাটকে পরিস্ফুট হয়েছে। সেই সঙ্গে এই নাটকে ঘটনাবিন্যাসের উৎকর্ষও পূর্বাপেক্ষা বেশি।
‘সিংহল বিজয়’ দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর প্রকাশিত। এই নাটকের কাহিনি পুরোপুরি ঐতিহাসিক নয়। বিজয়সিংহের সিংহল বিজয় কাহিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে এই নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। এই নাটকেও নাট্যকারের দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। নাটক হিসেবে ‘সিংহল বিজয়’ তত উল্লেখযোগ্য নয়।
পৌরাণিক নাটক
পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ জনপ্রিয়তার যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরাণকে নাট্যরূপ দিয়েছেন। যুক্তিবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশচন্দ্রের প্রবর্তিত ভক্তিভাব ও আধ্যাত্মিকতাকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ বুদ্ধিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে সংশয়াতুর করে তুলেছিল। তাই পৌরাণিক নাটক রচনায় তাঁর বস্তুবাদী ও যুক্তিনিষ্ঠ মন অলৌকিক ও দৈব বিশ্বাসকে মেনে নিতে পারেনি। তিনি পুরাণকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন বাস্তবরসে সমৃদ্ধ করে, মানবীয়ভাবে।
দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম পৌরাণিক নাটক ‘পাষাণী’ (১৯০০)। এই নাটকের প্রকাশ সমালোচক মহলে প্রবল বাদানুবাদ সৃষ্টি করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের রামায়ণ কাহিনির স্বীকরণ করেছেন এই নাটকে। নাট্যকার রামায়ণের অহল্যার অভিশাপ বৃত্তান্ত ও পাষাণরূপিণী হওয়ার ঘটনা গ্রহণ করেননি। তিনি পুরাণ কাহিনির অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত অংশকে বাদ দিয়েছেন। কৈলাস পর্বতের নির্জন শিখরে ইন্দ্র ও অহল্যার সুখ সম্ভোগকে, ইন্দ্রের আসক্তিতে ভাটা পড়া, অহল্যাকে পরিত্যাগকালে অহল্যার ইন্দ্রকে ছুরিকাঘাত, আহত ইন্দ্রকে গৌতম ও চিরঞ্জাবের শুশ্রুষা, পতিআশ্রমে মনোবিকারগ্রস্ত অহল্যার প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি কাহিনি রামায়ণ অনুমোদিত নয়। অহল্যার গৌতমের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও গৌতমের ক্ষমা—‘রামায়ণ’ কাহিনি বহির্ভূত।
‘পাষাণী’ নাটকে যুক্তিবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন পুরাণের আধুনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন ‘সীতা’ (১৯০৮) নাটকেও পৌরাণিক কাহিনির ‘নবভাষ্য’ দান করেছেন। তিনি এই নাটকে রামায়ণের ‘উত্তরকাণ্ড’ ও ভবভূতির ‘উত্তররামচরিতে’র কাহিনি অবলম্বন করলেও মূল কাহিনিকে গ্রহণ-বর্জন করেছেন। নিজস্ব যুক্তিবাদী মন ও সমাজ দৃষ্টির নিরিখে রাম চরিত্র অঙ্কনেও চিরাচরিত আদর্শ পরিত্যাগ করে ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন বাসনাকে স্থান দিতে চেয়েছেন। বাল্মীকি রামায়ণে সীতার নির্বাসন-এর ব্যাপারটি নাট্যকার সমর্থন করতে পারেননি। এইজন্য তিনি সীতার বনবাস আখ্যানটিতে ভবভূতিকেই অনুসরণ করেছেন। এর ফলে নাট্যকার রামচন্দ্র চরিত্রটিকে বনবাসের দায় থেকে অনেকখানি মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন।
প্রহসন
দ্বিদ্বেন্দ্রলাল তাঁর প্রহসনগুলিতে সমকালীন সমাজের নানা দোষ-ত্রুটিকে ব্যঙ্গের কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন। মানসিকতায় তিনি ছিলেন সংস্কারপন্থী। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত দ্বিজেন্দ্রলাল সব সময়ে ছিলেন উদার মতাদর্শে বিশ্বাসী। তাই কোনো সংকীর্ণতা, ভাড়ামি, সমাজের কলুষতাকে তিনি পছন্দ করতেন না। তাই তাঁর প্রহসনে তিনি কুসংস্কারকে যেমন ব্যঙ্গ করেছেন তেমনই ব্যঙ্গ করেছেন উগ্র সংস্কারপন্থীদের ও সংস্কারের নামে ভণ্ডামিকে। নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, গোঁড়া পণ্ডিত, বিলাতফের্তা, সুদখোর কৃপণ, ডাকাত, উকিলের ভণ্ডামি প্রভৃতি তৎকালীন সামাজিক চিত্রকে প্রহসনে তুলে ধরেছেন।
‘ত্র্যহস্পর্শ’ বা ‘সুখী পরিবার’ (১৯০০):-প্রহসনটির কেন্দ্রীয় ঘটনা হল বিবাহ বিভ্রাট। প্রহসনটি শিল্পসৃষ্টির দিক থেকে সার্থক না হলেও সমাজের বিভিন্ন স্বরূপের পরিচযায়ক। বহুবিবাহ বহুদিন থেকেই সমাজে চলে আসছে। উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষার পর জনসমাজ এই প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। এই প্রহসনে বৃদ্ধ বয়সে বিজয়গোপালের বিবাহলিন্সাকে কেন্দ্র করে ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়েছে।
‘প্রায়শ্চিত্ত’ (১৯০২):-এই সমাজ বিদ্রুপাত্মক প্রহসনের উৎসর্গক্ষেত্রে বাল্যবন্ধু ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে নাট্যকার লিখেছেন—“বিলাতফের্তা সমাজে যে অর্থলোলুপতা, কৃত্রিমতা ও বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে—তাহা তোমাকে স্পর্শ করে নাই।” বিলাত ফেরত সমাজের কৃত্রিমতা ও আচার-আচরণের আতিশয্য, নব্যহিন্দুদের স্ত্রীশিক্ষা দেওয়ার উকট প্রচেষ্টা ও শিক্ষিতা মহিলাদের শিক্ষার নামে কু-শিক্ষাকে এখানে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। প্রহসনটির ভাব ও বিষয়ের উপর অমৃতলালের প্রভাব বিদ্যমান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদের চিত্রকে দ্বিজেন্দ্রলাল তুলে ধরেছেন।
সামাজিক নাটক
জীবনের শেষপ্রান্তে এসে দ্বিজেন্দ্রলাল দুটি সামাজিক নাটক রচনা করেন। ‘পরপারে’ নাটকে বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের মূঢ়তা ও ভণ্ডামির চিত্র চিত্রিত হয়েছে। মহিম মাতৃভক্ত হয়েও স্ত্রীর প্ররোচনায় মাকে পরিত্যাগ করে। এরপর সে বারাঙ্গনা ও মদে আসক্ত হয়। ঘটনাচক্রে বারবণিতা শান্তাকে গুলিবিদ্ধ করে স্ত্রী সরযুর সহযোগিতায় মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে অবশেষে মহিম শান্তার কাছে পরপার সম্পর্কিত দীক্ষা গ্রহণ করে। এই কাহিনি নির্মাণে কোন সংগতি চোখে পড়ে না। একজন খেয়ালী জমিদারের দানশীলতা এবং পতিতার চরিত্র মাহাত্ম প্রাধান্য লাভ করেছে।
‘বঙ্গনারী’ নাটকে পণপ্রথা ও বাল্যবিবাহের কুফল বর্ণিত হয়েছে। এই নাটকে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব যথেষ্ট। সদানন্দ নাট্যকারের উদ্দেশ্যের বাহন। কেদার পাগলাটে প্রকৃতির হলেও কৌতুকস্নিগ্ধ চরিত্র। নাটকের সুশীলা চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। সে ইংরেজিশিক্ষিত যুক্তিবাদী, বিদ্রোহিনী নারী। এ নাটকটিও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে না।
দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য
- দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের জনপ্রিয়তার মূল উৎস তার অপরূপ ভাষা। তার এ ধরনের শক্তিশালী, কবিত্বপূর্ণ এবং নাটকীয় ভাষা আর কেউ ব্যবহার করতে পারেননি।
- সংলাপ রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের মৌলিকতা প্রশংসনীয়। তিনি তাঁর নাটকে গদ্য ও পদ্য উভয় শ্রেণির সংলাপ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সংলাপের ভাষা উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে ভরা। যার ফলে নাটকে এক রোমান্টিক আবেদন সৃষ্টি হয়েছে। তবে গদ্য সংলাপে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব সর্বাধিক।
- দ্বিজেন্দ্রলাল গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন শেকসপিয়র, বার্ণার্ড শ, গলসওয়ার্দি প্রভৃতি ইওরোপীয় নাট্যকারদের নাটক। তাই তিনি তাঁর নাটককে আধুনিক নাট্যরীতির প্রকাশের উপযুক্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন। যেমন—
- (ক) মঞ্চসজ্জা, অভিনয় ও রূপসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্য নাট্যরীতিকে অনুসরণ করেছেন।
- (খ) স্বগতোক্তির ব্যবহার কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বলে তা বর্জন করেছেন।
- (গ) পাত্র-পাত্রীদের আচরণ ও অভিব্যক্তি সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন।
- (ঘ) বিদূষক জাতীয় কোন চরিত্র তিনি অঙ্কন করেননি।
- (ঙ) সংলাপে নাট্যশ্লেষ ও রূপকধর্মিতার ব্যবহার।
- (চ) নাটকীয় একোক্তিগুলি (dramatic monologue) পাশ্চাত্য নাট্যানুসারী।
- (ছ) নাটকীয় সংগীত পরিবেশনের নৈপুণ্যও প্রশংসনীয়।
- (জ) তিনি নাটকের ত্রি-ঐক্য বিধি মেনে চলেছেন। স্থান, কাল সম্বন্ধে প্রতিটি অংকের প্রতিটি দশ্যে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই চলেছেন।
- (ঝ) দৃশ্যের পরিবেশ রচনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব যথেষ্ট। শেকসপিয়রের প্রভাব এক্ষেত্রে নাট্যকারের উপর বেশি।
- নাটকে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপায়ণে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব সমধিক। অন্তর্দ্বন্দ্বময় চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—চাণক্য, নূরজাহান, ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি। এমনকি তাঁর অঙ্কিত নারীচরিত্রগুলিও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। যেমন, নূরজাহান, জাহানারা, হেলেন, মহামায়া প্রভৃতি চরিত্র নিঃসন্দেহে তেজস্বিনী ও স্বাতন্ত্র্যময়ী।
- গিরিশচন্দ্রের নাটকে যে ধর্মভাব ও আধ্যাত্মিকতা ছিল তা থেকে বাংলা নাটককে মুক্তিদান করলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগে যে ভক্তি ও ধর্মবিশ্বাস মানুষের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল তা থেকে সরে এসে আধুনিক জীবনের সমস্যাকেই নাটকে যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে তুলে ধরলেন দ্বিজেন্দ্রলাল।
- ঐতিহাসিক নাটকের অনুকূল পরিবেশ রচনায়, জাতীয়তাবোধের বিকাশে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি (মেবার পতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, নূরজাহান) বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক রূপে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।


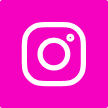




Leave a Reply