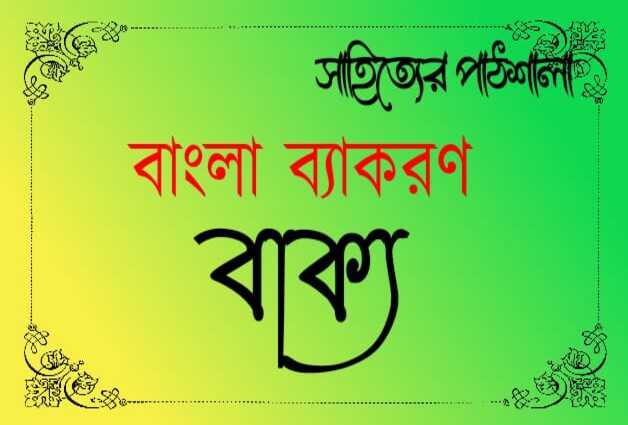
বাক্যের সংজ্ঞা দাও। বাক্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর।
বাক্য প্রকরণ ও বাক্যের বৈশিষ্ট্য
বাক্য সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হল বাক্য প্রকরণ। বাক্যের গঠন, বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য, প্রকারভেদ, বাক্যে পদের ক্রম ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় এখানে আলোচিত হয়।
বাক্যের বৈশিষ্ট্য
সাধারণ কতকগুলো পদ মিলে মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করলে বাক্য তৈরি হয়। তবে, বাক্যে পদ ব্যবহৃত হওয়ারও নিয়ম-শৃঙ্খলা রয়েছে। এলোমেলো পদ বাক্য গঠন করতে পারে না। সঠিক ও পরিপূর্ণ বাক্যের তিনটি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ বা গুণাবলি থাকে। বাক্যের বৈশিষ্ট্য হল ৩টি। যেমন- (ক) আকাঙ্ক্ষা (খ) আসত্তি বা নৈকট্য ও (গ) যোগ্যতা। নিচে বাক্যের ৩টি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল:
ক. আকাঙ্ক্ষা (Expectancy)
বাক্যে বা উক্তিতে বক্তা বা শ্রোতার আরো বলা বা শোনার ইচ্ছেকেই আকাঙ্ক্ষা বলে। অর্থাৎ বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বক্তার আরো কিছু বলার থাকে, শ্রোতারও আরো শুনতে ইচ্ছে হয়। অন্যথায় বাক্যটি অসম্পূর্ণ থাকে। যেমন- লোকটি ব্যাগ নিয়ে, এখানে বাক্যটি শেষ করার জন্য বক্তার আকাঙ্ক্ষা আছে। ওপরের বাক্যটির আকাঙ্ক্ষিত অংশ হল ‘বাজারে গেল’।
খ. আসত্তি বা ক্রম বা নৈকট্য (Proximity)
যেসব পদ মিলে বাক্য গঠিত হয় বাক্যে সেসব পদের একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। অর্থাৎ কোন পদের পর কোন পদ বসবে তা নির্দিষ্ট আছে। পদগুলোর ক্রমিক অবস্থানের পরিবর্তন হলে বাক্যের অর্থ পরিবর্তন হয়, কখনো বাক্যই গঠিত হতে পারে না। বাক্যের এই লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যকে আসত্তি বা নৈকট্য বা ক্রম বলে। যেমন- সে বাড়ি কাল যাবে। এই বাক্যটিতে আসত্তির অভাব আছে। বাক্যটি শুদ্ধ নয়। আবার, গিয়ে চিঠি তুমি দিও বাড়ি আমাকে। এখানে বাক্যের কি বক্তব্য বোঝা যায় না। আসলে এটা কোন বাক্যই নয়। পদগুলো আসত্তি বা ক্রম অনুসারে বসেনি। শুদ্ধ বাক্যটি হবে তুমি বাড়ি গিয়ে আমাকে চিঠি দিও।
গ. যোগ্যতা (Compatibility)
বাক্যে পদগুলো নিয়ম অনুসারে সাজালেই বাক্য হবে না। বাক্যের অর্থ মানব অভিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বাক্যের অর্থ প্রচলিত জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। না হলে তাকে পাগলের প্রলাপ ভাবা হবে। বাক্য গঠিত হবে তবে তা অর্থহীন-যুক্তিহীন প্রলাপ হবে। যেমন- লোকটি জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বাক্যটি ব্যাকরণগত দিক দিয়ে সঠিক। তবে অর্থানুসারে এটি বাক্য নয়। কাজেই, বাক্য লেখার সময় বা কথা বলার সময় বাক্যের অর্থের যৌক্তিক থাকতে হবে।
বাক্যের অংশ ও গঠন
বাক্যের অংশ দুটি- ক) উদ্দেশ্য, খ) বিধেয়। বাক্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় অর্থাৎ বাক্যের কর্তাকেই উদ্দেশ্য বলা হয়। উদ্দেশ্য কখনো ঊহ্য থাকতে পারে। আবার উদ্দেশ্য অনেক পদ দ্বারা সম্পর্কিত হতে পারে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য একটি পদেই সীমাবদ্ধ থাকবে এমন কোন কথা নেই। যেমন— লোকটি বই পড়ছে। আমার ভাই সোফায় বসে বই পড়ছে। এখানে ‘লোকটি’ ও ‘আমার ভাই সোফায় বসে’ উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তাই বিধেয়। অর্থাৎ বাক্যে কর্তা সম্পর্কে যা বলা হয়ে থাকে তাকে বিধেয় বলা হয়। ওপরের দুটি উদাহরণের ‘বই পড়ছে’ বিধেয়।
বাক্যের গঠনগত প্রকারভেদ
গঠন অনুসারে বাক্যকে চার ভাগে ভাগ করা হয়— (ক) সরল বাক্য (খ) জটিল বাক্য (গ) যৌগিক বাক্য (ঘ) মিশ্রবাক্য।
সরল বাক্য
বাক্যের একটি মাত্র উদ্দেশ্য এবং অন্য কোন বাক্যের সঙ্গে যে বাক্যের সম্পর্ক থাকে না, তাকে সরল বাক্য বলে। এক্ষেত্রে সাধারণত একটি ক্রিয়াপদ থাকে।
উদাহরণ:
ক. আমার বাড়ি আসাম।
খ. আমার ছোট ভাই কমল প্রতিদিন কলেজে যায়।
গ. আমার ছোট ভাই কমল প্রতিদিন বাইকে করে ৫ মাইল দূরে কলেজে যায়।
লক্ষণীয় যে, বাক্য বড় হলেও সরল বাক্য হতে পারে। কর্তার উদ্দেশ্য ও প্রধান ক্রিয়া একাধিক না হলে, শর্তযুক্ত বাক্য না হলে, খণ্ড বাক্য ও উপবাক্য না থাকলে বাক্য সরল হবে। সরল বাক্যের কর্তা সম্পর্কে তথ্য যোগ হতে পারে, স্থান কাল পাত্র সম্পর্কে তথ্য যোগ হতে পারে, তবে বাক্যের মূল উদ্দেশ্য ঠিক থাকবে। ওপরের ২নং ও ৩নং উদাহরণ লক্ষ করলে বোঝা যাবে কিভাবে সরল বাক্য বড় হতে পারে। বাক্যটির মূল অংশ কমল কলেজে যায়। পরবর্তীতে কমলকে সম্পর্কিত করা হয়েছে, তার কলেজে যাওয়া সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়াহয়েছে। তবু, ‘কমল কলেজে যায়’ বাক্যের মৌলিক গঠনের কোনো পরিবর্তন হয়নি।
জটিল বাক্য (Complex)
একটি প্রধান বাক্যের সাথে অন্য একটি অপ্রধান বা খণ্ডবাক্য মিলে জটিল বাক্য তৈরি হয়। জটিল বাক্য সাধারণত শর্তসাপেক্ষে তৈরি হয় অর্থাৎ একটি অংশের সাথে অন্য অংশটি শর্তসাপেক্ষে তৈরি হয়। ইংরেজিতে যেমন বলা হয়, প্রধান Clause এর সাথে Subordinate Clause মিলে জটিল বাক্য তৈরি হয়। এখানে শর্ত বা সম্পর্ক তৈরি করতে সাপেক্ষ সর্বনাম পদ থাকে।
উদাহরণ:
ক. সে এলেই তবে আমি যাবো (শর্তসাপেক্ষ পদ সে, তবে)।
খ. যদি লেখাপড়া কর তাহলে পরীক্ষায় পাস করবে (শর্তসাপেক্ষ পদ যদি, তাহলে)।
গ. যখন ঘণ্টা পড়বে তখন, স্কুলে ছুটি হবে (শর্তসাপেক্ষ পদ যখন, তখন)।
উল্লেখ্য যে, শর্তসাপেক্ষ সর্বনাম পদ ঊহ্য থাকতে পারে, কর্তাও ঊহ্য থাকতে পারে।
১নং উদাহরণে, আমি যাব— প্রধান বাক্য।
সে এলেই-অপ্রধান খণ্ড বাক্য।
২নং উদাহরণে, (তুমি) পরীক্ষায় পাস করবে— প্রধান বাক্য।
যদি লেখাপড়া কর—অপ্রধান খণ্ডবাক্য।
৩নং উদাহরণে, স্কুল ছুটি হবে— প্রধান বাক্য।
যখন ঘণ্টা পড়বে—অপ্রধান খণ্ড বাক্য।
আরো উদাহরণ:
ক) আপনি যদি চান তাহলে আমি রাতে আসতে পারি।
খ) যত বেশি বই বিক্রি হবে বইয়ের দাম তত কমবে।
গ) যে লোকটি কাল এসেছিল সে আমার ছোট ভাই।
ঘ) যদি কাল হরতাল হয় তাহলে বাস চলবে না।
লক্ষণীয়: জটিল বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়াতে রূপান্তরিত করলে জটিল বাক্যটি সরল বাক্যে পরিণত হয়। ওপরের উদাহরণগুলো পরিবর্তন করা হল:
ক) আপনি চাইলে আমি রাতে আসতে পারি। সরল বাক্য
খ) বেশি বিক্রি হলেই বইয়ের দাম কমবে। সরল বাক্য
গ) গতকাল আসা লোকটি আমার ছোট ভাই। সরল বাক্য
ঘ) হরতাল হলে বাস চলবে না। সরল বাক্য
যৌগিক বাক্য
এক বা একাধিক সরল বাক্য, জটিল বাক্য মিলে যৌগিক বাক্য তৈরি হয়। এক্ষেত্রে বাক্যগুলো সংযোজক অব্যয়দ্বারা যুক্ত হয়ে যৌগিক বাক্য গঠিত হয়। যৌগিক বাক্য বেশ দীর্ঘ হয়। ও, এবং, তবু, কিন্তু, তাহলে, তবে, তবু, নইলে, আর ইত্যাদি অব্যয় পদ বাক্যকে যোগ করতে সাহায্য করে। জটিল বাক্যের মতো এখানে শর্তযুক্ত বাক্য গঠিত হয় না। বাক্যের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র বাক্যগুলো স্বাধীন বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাদের মূল বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও তারা বাক্য হিসেবে মূল্য পায়। জটিল বাক্যের ক্ষেত্রে তা হয় না। যৌগিক বাক্য গঠনের উপাদান হল— সরল বাক্য, জটিল বাক্য ও সংযোজক অব্যয়। অবশ্য বাক্যে এদের স্থান আগে পরে হতে পারে এবং সরল বাক্য ও জটিল বাক্যের সংখ্যা বাড়তে পারে।
উদাহরণ:
ক) তাকে বলা হয়েছিল তবে সে আসেনি।
খ) আমার তার কথা মনে নেই কিন্তু তার ঠিকই মনে আছে।
গ) রাতে মেঘ ডাকছিল এবং প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হল সকাল থেকে।
ঘ) আকাশে অজস্র তারার মেলা, মৃদু বাতাস আর নীরবতা মিলে তৈরি হয়েছে হিরন্ময় এক পরিবেশ।
ঙ) তাকে দেখে মনে হল কোন গাঁয়ের এক গোবেচারা, কথাবার্তা চাল-চলনে কোন আধুনিকতার ছোঁয়া নেই, অথচ সে এম.এ. পাস করেছে কৃতিত্বের সঙ্গে।
চ) সে এল, দেখল, এবং জয় করল।
লক্ষণীয় যে, জটিল বাক্যে সংযোজক অব্যয় অনেক সময় ঊহ্য থাকে। সে স্থানে কমা (,) ব্যবহার করে সংযোজক অব্যয়ের কাজ চালানো হয়।
বাক্যের অর্থগত প্রকারভেদ
অর্থানুসারে বাক্যকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়— (ক) বিবৃতিমূলক (খ) প্রশ্নবাচক (গ) অনুজ্ঞাবাচক (ঘ) ইচ্ছাবাচক (ঙ) বিস্ময়সূচক (চ) প্রার্থনাবাচক।
বিবৃতিমূলক বাক্য
যে বাক্যে সাধারণতভাবে কোন কিছু বর্ণনা করা হয়, তাকে বিবৃতিমূলক বাক্য বলে। যেমন- পৃথিবী সূর্যের অন্যতম গ্রহ। লেখাপড়া না করলে বিদ্যার্জন সম্ভব নয়। বিবৃতিমূলক বাক্যকে দু’ভাগে বিভক্ত করা হয়— ক) অস্তিবাচক বাক্য, খ) নেতিবাচক বাক্য।
ক. অস্তিবাচক বাক্য
বিবৃতিমূলক বাক্যের অর্থ যদি হ্যা-বোধক হয় তবে সেই বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্য বলে। অর্থাৎ নঞর্থক না হলেই বাক্যটি অস্তিবাচক।
উদাহরণ:
ক. প্রসেনজিৎ বাড়িতে আছে।
খ. সমুদ্রের ওপর সেতু ছিল।
গ. সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।
ঘ. তাকে খুব নির্দয় মনে হয়।
খ. নেতিবাচক বাক্য
বিবৃতিমূলক বাক্যের অর্থ না-বাচক হলে সেই বাক্যকে নেতিবাচক বাক্য বলে।
উদাহরণ:
ক. প্রসেনজিৎ বাড়িতে অনুপস্থিত নেই।
খ. সমুদ্রের ওপর সেতু ছিল না এমন নয়।
গ. সূর্য অন্যদিকে নয় পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।
ঘ. তাকে দয়ালু বলে মনে হয় না।
প্রশ্নবাচক বাক্য
যে বাক্যে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়, তাকে প্রশ্নবাচক বাক্য বলে।
উদাহরণ:
ক.আপনি কি বাড়ি যাবেন?
খ. আপনার বাড়ি কোথায়?
গ. তিনি কি কাল আসবেন?
অনুজ্ঞাবাচক বাক্য
যে বাক্যে আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, নিষেধ, প্রার্থনার বোধ প্রকাশ পায় তাকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলে।
উদাহরণ:
ক.বাড়ি যাও।
খ. নিয়মিত কলেজে যাবে।
গ. আমার জন্য একটা বই এনে দিও।
ইচ্ছাবাচক বাক্য
যে বাক্যে কর্তার ইচ্ছে ব্যক্ত হয়, তাকে ইচ্ছাবাচক বাক্য বলে।
উদাহরণ:
ক. আমার যদি এক কোটি টাকা থাকত।
খ. আমার ইচ্ছে তিনি দীর্ঘজীবী হোন।
গ. ভারত বিশ্বকাপে জয়ী হবে।
বিস্ময়সূচক বাক্য
যে বাক্যে আবেগ, আনন্দ, উচ্ছ্বাস, উল্লাস, বিরক্তি, ভয়, ক্ষোভ ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে।
উদাহরণ:
ক. আহ: কি সুন্দর দৃশ্য!
খ. অ্যাঁ: কি কাণ্ডটাই না করলে!
গ. সাব্বাস! আমরা বিজয়ী হয়েছি।
প্রার্থনাবাচক বাক্য
যে বাক্যে প্রার্থনা, নিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাকে প্রার্থনাবাচক বাক্য বলে।
উদাহরণ:
ক. সে সফল হোক।
খ. এদেশের বুকে সফলতা নেমে আসুক।
গ. বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।
বাক্য পরিবর্তন
যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্য
বাক্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, বাক্যের (১) অর্থ পরিবর্তন করা যাবে না। (২) যৌগিক বাক্যের যে কোন একটি স্বাধীন খন্ডবাক্যকে (অর্থের গুরুত্ব বিবেচনা করে) অপরিবর্তনীয় রেখে সরল বাক্যের কাঠামোতে আনতে হবে। অর্থাৎ কর্তা + বিধেয় (সমাপিকা ক্রিয়া)। (৩) অবশিষ্ট স্বাধীন খন্ডবাক্যগুলোকে অসমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে সরল বাক্যে পরিবর্তন করা হয়। তবে, এর ব্যতিক্রম থাকে। (৪) সংযোজক অব্যয় বাদ দেয়া হয়।
যৌগিক: সে আমাকে ডেকেছিল কিন্তু আমি যাইনি।
সরল: সে আমাকে ডাকলেও আমি যাইনি।
যৌগিক: লোকটি দরিদ্র এবং সৎ।
সরল: লোকটি দরিদ্র হলেও সৎ।
যৌগিক: বাতাসে অমরতার গন্ধ, তবু তার সেদিকে খেয়াল নেই।
সরল: বাতাসে অমরতার গন্ধ থাকলেও তার সেদিকে খেয়াল নেই।
যৌগিক: কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।
সরল: কন্যার বাপ সবুর করিলেও বরের বাপ চাহিলেন না।
(দু’বার ক্রিয়া ব্যবহার না করাই বিধেয়)
জটিল বাক্য থেকে সরল বাক্য
নিয়ম : (১) অর্থ পরিবর্তন করা যাবে না। (২) শুধুমাত্র অপ্রধান খন্ডবাক্যের অসমাপিকা ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করতে হবে। (৩) সমাসবদ্ধ করে বা প্রত্যয় যোগ করে সরল বাক্যের কাঠামো তৈরি করতে হবে। (৪) জটিল বাক্যের শর্তযুক্ত পদ বা সাপেক্ষ সর্বনাম ও অন্যান্য অব্যয় পদ দিতে হবে।
জটিল: যখন স্কুল ছুটি হয়, তখন বালকেরা মাঠে খেলা শুরু করে।
সরল: স্কুল ছুটি হলে বালকেরা মাঠে খেলা শুরু করে। (হলে অসমাপিকা ক্রিয়া)
জটিল: সে যে কথা বলে তা ঠিক নয়।
সরল: তার কথা ঠিক নয।
জটিল: ফের যদি আসি তবে সিঁধকাঠি সঙ্গে করিয়াই আসিব।
সরল: ফের আসিলে সিঁধকাঠি সঙ্গে করিয়াই আসিব।
জটিল: যে পন্ডিত সে মূর্খ।
সরল: পন্ডিতই মূর্খ
জটিল: যদি সে রাতে আসে তাহলে কাল সকালে আমি যাব।
সরল: যে রাতে এলে আমি সকালে যাব।
সরল বাক্য থেকে জটিল বাক্য
লক্ষণীয়, (১) সরল থেকে জটিল ও যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করার সময় অর্থের আমূল পরিবর্তন করা যাবে না। (২) জটিল ও যৌগিক বাক্যের কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাক্য তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ জটিল বাক্য থেকে শর্তযুক্ত সাপেক্ষ সর্বনাম ও যৌগিকের ক্ষেত্রে সংযোজক অব্যয় যোগ করতে হবে।
সরল: সকালে সূর্য ওঠে।
জটিল: যখন সকাল হয় তখন সূর্য ওঠে।
যৌগিক: সকাল হয় এবং সূর্য ওঠে।
সরল: রকিব খুব বুদ্ধিমান ছেলে।
জটিল: যার নাম রকিব সে খুব বুদ্ধিমান।
যৌগিক: তার নাম রকিব এবং সে খুব বুদ্ধিমান।
সরল: প্রকৃতির রূপ এসে পৌঁছে মনের গহীনে।
জটিল: যা প্রকৃতির রূপ তা এসে পৌঁছে মনের গহীনে।
যৌগিক: এই প্রকৃতির রূপ এবং তা এসে পৌঁছে মনের গহীনে।
সরল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য
সরল: তিনি আর বেঁচে নেই।
যৌগিক: তিনি আগে ছিলেন, এখন নেই্ (এখানে কমা (’) যৌগিক অব্যয়ের কাজ করে)
সরল: শিক্ষক এলেও ক্লাস হয়নি।
যৌগিক: শিক্ষক এসেছেন, কিন্তু ক্লাস হয়নি। (জটিল বাক্যের মতো মনে হলেও এখানে শর্তযুক্ত বাক্য গঠিত হয়নি, সেজন্য বাক্যটি যৌগিক)
সরল: অনুগ্রহ করে সব খুলে বলুন।
যৌগিক: অনুগ্রহ করুন এবং সব খুলে বলুন।
সরল: গ্রামের ওপারে তুরাগ নদী।
যৌগিক: এখানে গ্রামের শেষ এবং তারপরে তুরাগ নদী।


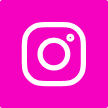


Leave a Reply