রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে মিনার্ভা থিয়েটারের অবদান আলোচনা কর।
মিনার্ভা থিয়েটার
৬ নং বিডন স্ট্রিট, কলকাতা
প্রতিষ্ঠাতা: নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়
প্রতিষ্ঠা: ২৮ জানুয়ারি, ১৮৯৩
স্থায়িত্বকাল: ২৮ জানুয়ারি, ১৮৯৩ – বর্তমান সময় পর্যন্ত
নাটক: ম্যাকবেথ (শেক্সপীয়ার, অনুবাদ: গিরিশচন্দ্র)
স্টার থিয়েটারের মতোই মিনার্ভা থিয়েটার ঐতিহ্যসমৃদ্ধ। এই থিয়েটার নিজস্ব নামে বর্তমান পর্যন্ত চলছে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পেছনে গিরিশচন্দ্রের উদ্যোগ ও নেতৃত্ব কাজ করেছিল। অর্থব্যয় করলেন নাগেন্দ্রভূষণ আর থিয়েটারের দল তৈরি ও নাট্যাভিনয়ের যাবতীয় দায়িত্ব নিলেন গিরিশচন্দ্র। অভিনয়-শিক্ষক বা মাস্টার রূপে যোগ দিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। বাংলা থিয়েটারের দুই স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব অনেকদিন বাদে এক থিয়েটারে মিলিত হলেন, বিডন স্ট্রিটের যে জমিতে আগে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানেই নির্মিত হলো নতুন থিয়েটার বাড়ি। নতুন দলে অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবে রইলেন গিরিশ, অর্ধেন্দু ছাড়া, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), চুনীলাল দেব, নিখিল দেব, নীলমণি ঘোষ, কুমুদনাথ সরকার, অনুকুল বটব্যাল, অঘোরনাথ পাঠক, তিনকড়ি, প্রমদাসুন্দরী, পরমাসুন্দরী প্রভৃতি। সঙ্গীত শিক্ষক রইলেন দেবকণ্ঠ বাগচী। স্টেজ ম্যানেজার ধর্মদাস সুর।
মহাসমারোহে শেক্সপীয়রের বিখ্যাত ট্রাজেডি ‘ম্যাকবেথ’ নাটক দিয়ে মিনার্ভাব উদ্বোধন হল, ২৮ জানুয়ারি, ১৮৯৩। অনুবাদ করলেন গিরিশচন্দ্র। বহু পরিশ্রমে অনুবাদ করে এবং দীর্ঘদিন অনুশীলন করিয়ে নাটকটি অভিনয় করা হলো। ড্রপসিন আঁকেন ইংরেজ চিত্রকর মিঃ উইলিয়ার্ড এবং রূপসজ্জা ও দৃশ্যসজ্জা করেন পিমসাহেব। অভিনয়ে ছিলেন: ম্যাকবেথ—গিরিশ, লেডি ম্যাকবেথ—তিনকড়ি, ম্যালকম—দানীবাবু, ব্যাঙ্কো—কুমুদ সরকার, ম্যাকডাফ—অঘোরনাথ পাঠক, লেডি ম্যাকডাফ—প্রমদাসুন্দরী; অর্ধেন্দুশেখর—ডাকিনী, ডাক্তার, দ্বারপাল, হত্যাকারী প্রভৃতি নানা চরিত্রে অভিনয় করেন।
শেক্সপীয়রের নাটকের এতো সুন্দর অনুবাদ এবং সেই অনুবাদ নাটকের এতো মর্যাদাপূর্ণ ও সাফল্যজনক অভিনয় বাংলা মঞ্চে খুব কমই হয়েছে। শিক্ষিত ও রুচিশীল দর্শকের কাছে এই অভিনয় খুবই প্রশংসা লাভ করলো। পত্র-পত্রিকাও অকুণ্ঠচিত্তে সাধুবাদ জানালো, তিনকড়িকে লেডি ম্যাকবেথের চরিত্রে গিরিশ নিজে হাতে অমানুষিক অধ্যবসায়ে তৈরি করেছিলেন। গিরিশ নিজেও ম্যাকবেথের চরিত্রে অনন্যসাধারণ অভিনয় করলেন। পণ্ডিত ও বিদগ্ধ মহলে ম্যাকবেথ প্রযোজনা এবং অভিনয়ের খ্যাতি প্রতিষ্ঠা পেল। কিন্তু তখনকার মঞ্চের সাধারণ দর্শক এই নাটককে গ্রহণ করতে পারলো না। তাদের মানসিক সাজুয্য না পেয়ে তিন-চার রাত অভিনয়ের পর থেকেই রঙ্গালয়ে দর্শক কমে যেতে লাগল। অর্থাগম কমে গেল। প্রচুর অর্থব্যয়ে নির্মিত ম্যাকবেথ প্রযোজনা দশ রাত অভিনয়ের পরই বন্ধ করে দিতে হলো। ভালো ও উন্নতমানের নাট্যাভিনয়ের যে প্রচেষ্টায় গিরিশচন্দ্র নেমেছিলেন, ‘ম্যাকবেথ’-এর অভিজ্ঞতা তাকে অন্য শিক্ষা দিল। ক্ষুব্ধ গিরিশ এবার নামালেন হাল্কা নাচ গানের নাটক ‘মুকুলমুঞ্জরা’ এবং ‘আবুহোসেন’। ‘ম্যাকবেথ’-এর অর্থক্ষতি সুদে-আসলে পুষিয়ে দিল এই নাটক দুটি। পেশাদার ব্যবসায়িক থিয়েটারের সীমাবদ্ধতা সেদিন গিরিশের মতো অনেককেই আতঙ্কিত করে তুলেছিল।
এই দুটি নৃত্যগীতের নাটকে নৃত্য ও সঙ্গীত শিক্ষা দিলেন শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু) ও দেবকণ্ঠ বাগচী। ‘আবু হোসেন’-এর অভিনয়ে (২৫ মার্চ, ১৮৯৩, প্রথম অভিনয়) দ্বৈত নৃত্যগীতে মাতিয়ে দিলেন তিনকড়ি (দাই) এবং রাণুবাবু (মশুর)। আর আবু হোসেনের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর কৌতুক অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চ প্রাণোচ্ছলতায় ভরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সহযোগিতা করলেন আবুর মা’র চরিত্রে গুলফন হরি। মুকুলমুঞ্জরা’র বরুণচাঁদের চরিত্রাভিনয়েও অর্ধেন্দুশেখর রসের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। এই ধরনের অভিনয়ে তখন অর্ধেন্দুর জুড়ি ছিল না।
সাফল্যের তুঙ্গে উঠে মিনার্ভা এবারে পর পর অভিনয় করে গেল কয়েকটি নাটক। সপ্তমীতে বিসর্জন (১১-১০-৯৩), নল-দময়ন্তী (২৪-১২-৯৩), জনা (২৩-১২-৯৩), বড়দিনের বখশিস (২৫-১২-৯৩), কমলেকামিনী (২৭-১২-৯৩), বেজায় আওয়াজ (দেবেন্দ্রনাথ বসু, ২৭-১-৯৪), করমেতিবাঈ (১৪-৭-৯৪), প্রফুল্ল (১৩-৭-৯৫) প্রভৃতি গিরিশের নাটকগুলি অভিনয় হল। ‘প্রফুল্ল’ এর আগে স্টারে অভিনীত হয়েছিল। সেখানে যোগেশ চরিত্রে অভিনয় করেন অমৃতলাল মিত্র। মিনার্ভাতেই প্রথম গিরিশচন্দ্র যোগেশ চরিত্রে অভিনয় করলেন। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখছেন—“গিরিশের যোগেশের পার্শ্বে অমৃতলালের যোগেশ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। মনে হইল একজন যথার্থ যোগেশ, আর একজন যোগেশ সাজিয়াছেন।’’ (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর)। মাঝে কয়েকটি পুরনো নাটক সধবার একাদশী (দীনবন্ধু), পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (গিরিশ), দক্ষযজ্ঞ (গিরিশ), পলাশীর যুদ্ধ (নাট্যরূপ: গিরিশ), মেঘনাদবধ (নাট্যরূপ: গিরিশ) অভিনয় করা হয়েছিল। এরই ফাঁকে হাল্কা নৃত্যগীতের নাটক স্বপ্নের ফুল, ফণির মণি, এবং হাল্কা ব্যঙ্গ প্রহসন সভ্যতার পাণ্ডা, পাঁচকনে প্রভৃতি লিখে গিরিশ এখানে অভিনয় করিয়েছেন।
এইগুলির মধ্যে ‘জনা’ এবং ‘পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস’ খুবই মঞ্চসফল হয়েছিল। দর্শকেরও আনুকূল্য লাভ করেছিল। জনার ভূমিকায় তিনকড়ি, বিদূষক চরিত্রে অর্ধেন্দুশেখর (তিনি মিনার্ভা ছেড়ে দিলে এই চরিত্রে গিরিশ অভিনয় করতেন), প্রবীরদানীবাবু, মদনমঞ্জরী-কুসুমকুমারী। গিরিশের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে ‘জনা’ শ্রেষ্ঠ। জনার চরিত্রে অভিনয় তিনকড়ির জীবনেও শ্রেষ্ঠ অভিনয়। অর্ধেন্দুশেখর বিদূষকের অভিনয়ে মজা নিয়ে আসতেন, সঙ্গে ভক্তির মিশেল দিয়ে তাকে খুবই আদৃত করে তুলতেন। গিরিশ বিদূষক চরিত্রকে হাল্কা থেকে সিরিয়াস করে তুলতেন। একই চরিত্রে দুই প্রতিভার ভিন্ন রূপদান সে যুগের দর্শকেরা খুবই উপভোগ করেছিলেন।
‘পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস’ নাটকটিও খুব জমেছিল। দ্রৌপদী—তিনকড়ি। ভীম—হরিভূষণ ভট্টাচার্য। বৃহন্নলা—দানীবাবু। কীচক—অঘোরনাথ পাঠক। উত্তর—গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদের সকলের সম্মিলিত উচ্চ অভিনয়ে নাটকটি জনসমাদৃত হলো। পুরনো নাটককে নতুন ছাঁচে ও ছাঁদে অভিনয় করিয়ে গিরিশ আবার কৃতিত্ব দেখালেন। প্রফুল্ল’ নাটকের অভিনয়েও নতুন প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হলো। তাঁর নিজ হাতে গড়া প্রফুল্ল নাটকের অভিনয় স্টারে প্রথম হওয়ার সময়ে তিনি যোগেশের চরিত্রে অমৃতলাল মিত্রকে একভাবে গড়ে তুলেছিলেন। সে অভিনয়ে অমৃত মিত্র খ্যাতি লাভ করেন। মিনার্ভায় গিরিশ নিজে ‘যোগেশ’ সাজলেন (রমেশ-সুরেশ—চুনীলাল ও দানীবাবু) এবং গৃহকর্তা সম্মানিত যোগেশের সব হারানোর রিক্ততা ও শারীরিক অবসন্নতার যে রূপ অভিনয়ে ফুটিয়ে তুললেন তা বাংলা মঞ্চে তুলনারহিত হয়ে রইলো।
এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। ‘বড়দিনের বখশিস’ এবং ‘পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস’ অভিনয়ের সময়ে ব্রিটিশের পুলিশ বাধা দেয়। বড়দিনের মজা নিয়ে লেখা ‘বেকুবের একজাই’ নামটি পাল্টে এবং কিছু পরিবর্তন করে ‘বড়দিনের বখশিস’ নামে সেটিকে সেখানে অভিনয় করা হয়। আর পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে কীচক-দ্রৌপদীর অত্যাচারের দৃশ্যে অশ্লীলতা রয়েছে এমন অভিযোগ পুলিশ তোলে। গিরিশ কিছু অংশ পাল্টে নিজে এরপর থেকে কীচকের ভূমিকায় অভিনয় করতে থাকেন।
১৮৯৬-তে গিরিশ মিনার্ভা ছেড়ে দেন। মালিক নাগেন্দ্রভূষণের সঙ্গে আর্থিক ব্যাপারে তাঁর বনিবনা হয়নি। নাগেন্দ্রভূষণের অমিতব্যয়িতা এবং কাপ্তেনী মনোভাবের জন্য প্রচুর আয় সত্ত্বেও মিনার্ভার আর্থিক সঙ্গতি গড়ে ওঠেনি। বরং ঋণভার বেড়েই চলেছিল। দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য বেড়ে গেল। গিরিশ মিনার্ভা ছেড়ে আবার স্টারে যোগ দিলেন। গিরিশ-শূন্য মিনার্ভার দুর্দশা শুরু হলো। ১৮৯৬-এর সেই দুর্গতির দিনে মিনার্ভা থিয়েটারে সিটি থিয়েটার সম্প্রদায় কয়েক মাস (এপ্রিল-জুন) অভিনয় চালিয়ে যায়।
তারপরে ভাঙা মিনার্ভার পরিচালনার দায়িত্ব নেন চুনীলাল দেব। তিনি এবং দুর্গাদাস দে মিলে এখানে জুবিলি যজ্ঞ, আকবর, লক্ষ্মণ বর্জন, ফটিকচাদ, আলিবাবা, পলাশীর যুদ্ধ, লবাবু প্রভৃতি নাটক প্রহসনের অভিনয় করান। ১৮৯৭-এর পুরো বছরটাই এইভাবে কেটে যায়। কিন্তু মিনার্ভা থিয়েটারের দুর্দশা কাটে না বরং অবনতি হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মালিক নাগেন্দ্রভূষণ বাধ্য হয়ে ১৮৯৮-এর ৩১ মার্চ মিনার্ভা থিয়েটারকে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করে দেন। যারা কেনে তাদের কাছ থেকে ১৮৯৯-তে শ্রীপুরের জমিদার নরেন্দ্রনাথ সরকার মিনার্ভা কিনে নেন এবং মালিক ও পরিচালক হয়ে নব উদ্যমে থিয়েটার চালাতে থাকেন। অর্ধেন্দুশেখর এই সময়েই এখানে যোগ দেন।
২৯ মে, ১৮৯৯, দুর্গাদাস দে’র লেখা ‘শ্রী’ নাটক দিয়ে নতুনভাবে মিনার্ভায় অভিনয় শুরু হল। তারপরে মালিক নরেন্দ্রনাথের নিজের লেখা নাটক ‘মদালসা’ এখানে অভিনীত হল। পর পর এখানে অভিনয় হলো কিশোরসাধন, জুলিয়া, পলাশীর যুদ্ধ, জেনানা যুদ্ধ, বসন্তবিহার, মাধবীকঙ্কন, বসন্ত রায় প্রভৃতি নাটক, নাট্যরূপ এবং গীতিনাট্যের। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত চললো। কিন্তু কোনো অভিনয় সেভাবে সার্থক হলো না বা অর্থাগম ঘটলো না।
১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল থেকে ২২ জুন পর্যন্ত মিনার্ভায় অভিনয় বন্ধ থাকে। কারণ, থিয়েটার গৃহ এবং মঞ্চকে বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সাজানো হয়। গ্যাসের আলোর বদলে পুরোপুরি বৈদ্যুতিক আলো স্থায়ীভাবে ব্যবহার শুরু হয় ১৯০৩-এর ৭ নভেম্বর থেকে। নাটক রঘুবীর। ম্যানেজার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত দিয়ে তার শুরু। নরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে এবার মিনার্ভায় নিয়ে এলেন। সঙ্গে এলেন আবার অর্ধেন্দুশেখর। এদের দুজনের সাহায্যে কিছুদিন মিনার্ভা চললো। গিরিশ বঙ্কিমের ‘সীতারাম’ উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করলেন (২৩ জুন, ১৯০০)। অভিনয় করলেন: সীতারাম—গিরিশ, গঙ্গারাম—দানীবাবু, চন্দ্রচূড়—অঘোর পাঠক, গঙ্গাধর—ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়, স্ত্রী—তিনকড়ি, জয়ন্তী—সুশীলবালা, নন্দা—সরোজিনী, রমা—পুঁটিরাণী।
এদের অভিনয়ে, গিরিশের নাট্যরূপের গুণে এবং স্বয়ং বঙ্কিম-উপন্যাসের ঘটনার আকর্ষণে ‘সীতারাম’ জনপ্রিয় হলো। এর আগে ক্লাসিক থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মিনার্ভা হেরে যাচ্ছিল, সীতারাম সে দুর্দশা কাটিয়ে দিল। সীতারামের পর ‘মণিহরণ’ গীতিনাট্য গিরিশ লিখে অভিনয় করলেন। তারপরে নন্দদুলাল গীতিনাট্যও অভিনীত হল। নৃত্য-গীত ও ভক্তিরসের এইসব গীতিনাট্য দর্শকের ভালো লেগেছিল। কিন্তু নাট্যরস হিসেবে এগুলি অকিঞ্চিত্বর।
পাশাপাশি অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারের তখন রমরমা। তা সত্ত্বেও গিরিশের পরিচালনায় মিনার্ভা বেশ দাঁড়িয়ে গেল। আর্থিক লাভও হতে লাগল। কিন্তু এই সময়েই গিরিশের সঙ্গে মালিক নরেন্দ্রনাথের মননামালিন্য শুরু হয়। নরেন্দ্রনাথ গিরিশের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে দিলেন। ক্লাসিক থিয়েটার গিরিশকে সসম্মানে তাদের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে নিল। গিরিশ-বিহীন মিনার্ভা যখন কিছুতেই ভালোভাবে চলছে না, তখন নরেন্দ্রনাথ নিজেও থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। মালিক হলেন জমিদার প্রিয়নাথ দাস। সহযোগী বেণীভূষণ রায়।
১৯০৩-এর ১০ মে ক্লাসিকের অমরেন্দ্রনাথ প্রিয়নাথের কাছ থেকে মাসিক পাঁচশশা টাকা ভাড়ায় তিন বছরের জন্য মিনার্ভা লীজ নিয়ে একসঙ্গে দুটো থিয়েটার মিনার্ভা ও ক্লাসিক চালাতে লাগলেন।
অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার বাড়ির সংস্কার করলেন। গ্যাসের পরিবর্তে স্থায়িভাবে আলোর ব্যবস্থা করলেন। ১৯০৩-এর ৭ নভেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ‘রঘুবীর’ নাটক দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভার উদ্বোধন করলেন। তিনি স্বয়ং অভিনয় করলেন নাম-ভূমিকায়। কিন্তু নাটকটি দর্শকপ্রিয় হলো না। নামালেন বঙ্কিমের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের নাট্যরূপ, ১৫ নভেম্বর, ১৯০৩। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘হিতে বিপরীত’ অভিনয়ের পর তারা ঢাকায় যান (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৪) অভিনয় করতে। লর্ড কার্জনের ঢাকা আগমন উপলক্ষে মিনার্ভা সেখানে আমন্ত্রিত হয়। এইভাবে কিছুদিন আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও মিনার্ভা চালিয়ে অমরেন্দ্রনাথ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মালিকানা নিয়ে মামলা হয়। অমরেন্দ্রনাথ শেষে আদালতের রায়ে আবার মালিক হয়ে (২৪ ডিসেম্বর, ১৯০৩) অভিনয় শুরু করেন। কিন্তু আবার ব্যর্থ হয়ে এবারে মিনার্ভা লীজ দিলেন ধনী ব্যবসায়ী মনোমোহন পাঁড়েকে। মনোমোহন এবার থিয়েটারটি সাবলীজ দিলেন চুনীলাল দেবকে; মাসিক সাতশো পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায়।
চুনীলাল মিনার্ভার দায়িত্ব নিয়ে নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহ করে থিয়েটার চালাবার ব্যবস্থা করলেন। তাদের সঙ্গে ‘শেয়ার’-এর ব্যবস্থা করলেন। মোটামুটি ভাঙা মিনার্ভা গুছিয়ে নিয়ে চুনীলাল মনোমোহন গোস্বামীর ‘সংসার’ দিয়ে শুরু করলেন। কিন্তু ক্লাসিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তিনিও হেরে যেতে লাগলেন। এই সময়েই তিনি রঙ্গালয়ে উপহার-প্রথা চালু করলেন। চুনীলাল ‘বসুমতী’র মালিক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে এই কাজে হাত দিলেন। উপেন্দ্রনাথ এই রঙ্গালয়ের ‘উপহার’ গ্রন্থাবলীর প্রকাশক ছিলেন। বসুমতী গ্রন্থাবলী’র পরবর্তী সূচনা এখান থেকেই। টিকিটের দাম অনুযায়ী উপহারের গ্রন্থসংখ্যা ঠিক হতো। ‘ফাউ’ হিসেবে গ্রন্থ পাওয়ার লোভে মিনার্ভায় দর্শকের ভিড় বেড়ে গেল। চুনীলাল মিনার্ভায় অতুল গ্রন্থাবলী উপহার দেন। সেদিন ২৩ আগস্ট, ১৯০৪ এবং অভিনীত হয়েছিল তিনটি অতি অকিঞ্চিৎকর নাটক ‘নন্দ বিদায়’, ‘লক্ষ্মণ বর্জন’, কুব্জা ও দর্জী। এতো ভিড় যে, পরের দিনই আবার এই তিন বাজে নাটকের অভিনয় করতে হল এবং ‘হাউসফুল’। এবারে ক্লাসিকও গ্ৰন্থ উপহার শুরু করলো। একই সঙ্গে মিনার্ভা ও ক্লাসিক গ্রন্থ উপহারের হিড়িক ফেলে, লোভ দেখিয়ে খদ্দের টানতে লাগলো। উভয় থিয়েটারের তরফ থেকে দর্শকেরা সে সময়ে উপহার পেয়েছিল অতুলকৃষ্ণ মিত্রের গ্রন্থাবলী, মাইকেল গ্রন্থাবলী, কালীপ্রসন্নের মহাভারত, রন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ, শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি। এছাড়া বৃষ্টির দিনে থিয়েটার ফেরৎ দর্শক উপহারের ছাতা মাথায় দিয়ে, বই বগলে নিয়ে দলে দলে চলেছে—এমন বর্ণনা দেখা যায়। এই প্রতিযোগিতায় ক্লাসিক আর্থিক দুর্দশায় পড়লো, চুনীলাল সাফল্য পেলেন। যারা দর্শক আকর্ষণের জন্য এইসব কাণ্ড করতে পারেন, তারা নাট্যাভিনয়ের উন্নতির চেষ্টা করবেন তা ভাবাই যায় না।
এবারে গিরিশ, অর্ধেন্দুশেখর, অপরেশের সম্মিলনে মিনার্ভার হৃতগৌরব ফিরে এলো। ‘হরগৌরী’ অভিনয়ের পর ‘বলিদান’ নামানো হলো (৮ এপ্রিল, ১৯০৫)। গিরিশের নতুন নাটকের অভিনয়ে করুণাময় করলেন গিরিশ এবং রূপচাঁদ অর্ধেন্দুশেখর। গিরিশ এই সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অর্ধেন্দুশেখর করুণাময় করেন। আবার একই চরিত্রে দুই প্রতিভাবান অভিনেতার বিভিন্ন রূপদান দর্শকদের মোহাবিষ্ট করে রাখল।
এরপরই নামাননা হলো দ্বিজেন্দ্রলালের ‘রাণাপ্রতাপ’, ২৯ জুলাই ১৯০৫। লর্ড কার্জনের ‘বঙ্গভঙ্গ’ প্রস্তাব নিয়ে ১৯০৩ থেকেই সারা বঙ্গদেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। অর্ধেন্দু মঞ্চে জাতীয়তাবোধের ভাবনার উদ্বোধনের চেষ্টা তখন থেকেই করতে থাকেন। রঘুবীর, প্রতাপাদিত্য, রাণাপ্রতাপ (১৯.০৭-১৯০৫) প্রভৃতির অভিনয়ে মিনার্ভা থিয়েটার স্বদেশপ্রেম প্রবাহিত করতে চাইলো।
১৯০৫-এর ৬ সেপ্টেম্বর ‘বঙ্গভঙ্গ’ ঘোষণা করেন লর্ড কার্জন। এবারে জাতীয়তাবোধের আন্দোলন তুমুল আকার ধারণ করে। স্টারে রাণাপ্রতাপ সাড়া ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে স্টার কর্তৃপক্ষের মতান্তর হয়, নাট্যকার তাঁর নাটক তুলে এনে মিনার্ভাতে দেন। মিনার্ভা রাণাপ্রতাপ অভিনয় করল, জমলো না। তখন গিরিশ রচনা করলেন ‘সিরাজদৌল্লা’, মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত হলো ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫: সিরাজ—দানীবাবু, মীরজাফর—নীলমাধব চক্রবর্তী, করিমচাচা—গিরিশ, দানশা ফকির ও ড্রেক—অর্ধেন্দুশেখর, লুৎফা—সুশীলাবালা, ঘেসেটি বেগম—সুধীরাবালা, ক্লাইভ—ক্ষেত্রমোহন, জহরা—তারাসুন্দরী।
সিরাজদৌল্লার অভিনয়ে বাংলা মঞ্চে নতুন প্রাণের সাড়া দেখা দিল। ১৮৭৬-এর অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে ব্রিটিশ-বিরোধী কিংবা দেশপ্রেমমূলক নাটক বাংলা মঞ্চে কেউ অভিনয়ের সাহস দেখায়নি। মঞ্চ থেকেই জাতীয়তাবোধ, স্বাধীনতার মন্ত্রোচ্চারণ হারিয়ে গিয়েছিল। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের আন্দোলন নিয়ে বঙ্গভঙ্গ মেতে ওঠায় বাংলা রঙ্গমঞ্চও অনেকদিন বাদে স্বদেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ, স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রভৃতি প্রসঙ্গ নিয়ে নাটক অভিনয়ে উদ্বেল হয়ে পড়ে। গিরিশ এই সময়ে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচনা করতে থাকেন। যে ঐতিহাসিক নাটক গিরিশ বলতে গেলে লেখেনইনি, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উন্মাদনার যুগে গিরিশ তাই রচনা করলেন। এবং ইতিহাসের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে দেশের জাতীয়তাবোধ, স্বাধীনতা স্পৃহা ও পরাধীনতার বেদনা ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন। ইতিহাসের চরিত্রগুলি নিয়ে তাদের ‘ন্যাশনাল হিরো’ বা জাতীয় বীর নায়কের মর্যাদায় দর্শকমনে প্রতিষ্ঠিত করলেন।
‘সিরাজদৌল্লা’ প্রচণ্ড জনপ্রিয় হলো। জাতীয় আন্দোলনের দিনে বাংলা মঞ্চ সেদিন তার দায়িত্ব যথারীতি পালন করতে পেরেছিল।
গিরিশের ‘মীরকাশিম’ একই ভাবনায় লেখা। অভিনীত হলো ১৬ জুন, ১৯০৬। মীরজাফর চরিত্রে গিরিশ এবং মীরকাশিম চরিত্রে দানীবাবুর অভিনয়ে সেদিন বাংলার ইতিহাস মূর্ত হয়ে উঠেছিল। হলওয়েল, হে এবং মেজর এডামস এই তিনটি চরিত্রে অর্ধেন্দু অবিস্মরণীয় অভিনয় করেন। মিনার্ভায় ‘মাস্টার’ অর্ধেন্দুশেখরের উদ্যমে এবং ম্যানেজার গিরিশের প্রচেষ্টা মিলেমিশে থিয়েটারে ন্যাশনালিটির উদ্বোধন ঘটিয়েছিল। ডাঃ হরনাথের লেখা জাগরণ (১৭ ডিসেম্বর, ১৯০৫), বাসর (২৬ ডিসেম্বর), সংসার ও নসীব (৩ জানুয়ারি, ১৯০৬), দুর্গেশনন্দিনী (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬) অভিনীত হয়েছিল। বাসর গিরিশের লেখা এবং দুর্গেশনন্দিনী তারই নাট্যরূপ। সংসার মনোমোহন গোস্বামীর এবং নসীব চুনীলাল দেবের অপেরা। সিরাজদৌল্লা একটানা পঞ্চাশ রাত্রি অভিনীত হয়ে সাড়া ফেলেছিল। মীরকাশিমও ভালো চলেছিল। আর সাফল্য পেয়েছিল দুর্গেশনন্দিনী। অভিনয় করেছিলেন—গিরিশচন্দ্র (বীরেন্দ্র সিংহ), অর্ধেন্দুশেখর (বিদ্যাদিগগজ), দানীবাবু (ওসমান), তারক পালিত (জগৎ সিংহ), নীলমাধব চক্রবর্তী (অভিরাম স্বামী), সুশীলাবালা (তিলোত্তমা), তিনকড়ি (বিমলা)।
প্রত্যেকেরই অভিনয় নাটকটিকে খুবই আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। বিদ্যাদিগগজের ভূমিকায় অর্ধেন্দুর অভিনয় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ১৯০৬-এর আর উল্লেখযোগ্য অভিনয় হলো রাণাপ্রতাপ, প্রতাপাদিত্য, জনা, আলীবাবা, পাণ্ডবগৌরব, প্রফুল্ল, চৈতন্যলীলা, বিবাহবিভ্রাট, অভিমন্যু বধ, শিরী-ফরহাদ (অতুল মিত্র), কপালকুণ্ডলা। বড়দিনের বড় আসরে (২৩-৩০ ডিসেম্বর) পরপর আটদিন দশটি নাটকের অভিনয় করা হয়েছিল—সংসার, সিরাজদৌল্লা, দুর্গেশনন্দিনী, আলিবাবা, বেল্লিকবাজার, মীরকাশিম, শিরী-ফরহাদ, দুর্গাদাস, বলিদান, আলিবাবা।
বঙ্গভঙ্গের উন্মাদনা যততা কমে যেতে থাকে রঙ্গালয় থেকে দেশপ্রেমের নাটকও বিদায় নিতে থাকে। তবুও এই সময়ে গিরিশের মতোই ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচনা করেন। ঐতিহাসিক নাট্যকার রূপে পূর্ণ খ্যাতিতে এই সময়েই দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব ঘটে। তার প্রতাপসিংহ, তারাবাই, দুর্গাদাস এই উন্মাদনাকালে রচিত। কিছু পরে লেখা মেবারপতন, সাজাহান, নূরজাহান এবং চন্দ্রগুপ্ত। অনেকগুলিই মিনার্তায় অভিনীত হয়। মিনার্ভা থিয়েটার থেকেই ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং গিরিশের ঐতিহাসিক নাটকের পূর্ণ যাত্রা শুরু হয়। প্রথম দুজনের খ্যাতি বিস্তার লাভ করে এই থিয়েটার থেকেই।
১৯০৬-এ (২৮ এপ্রিল) মিনার্ভায় সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে বৈদ্যুতিক পাখার বন্দোবস্ত করা হয়, তখন সিরাজদৌল্লার অভিনয়ে ভিড় বেড়েই চলেছিল। আর, এখানেই বহু প্রশংসিত ও পূর্ব অভিনীত ‘চৈতন্যলীলা’ নাটকের নতুন করে অভিনয়ে গিরিশ ও অর্ধেন্দুশেখর দুটি ছোট্ট ও বিশিষ্ট ভূমিকায় (মাধাই ও জগাই) অভিনয় করেন। স্টারে চৈতন্যলীলার স্বর্ণযুগে এরা অভিনয় করেননি। কিন্তু ঐ দুটো ছোট্ট ভূমিকায় তাঁরা অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কীভাবে মাতাল বর্বর শাক্ত পাষণ্ড মাধাই ও জগাই চৈতন্যের স্পর্শে ক্রমে ভক্তে রূপান্তরিত হচ্ছে তারা তা শারীরিক ও বাচিক অভিনয়ে মঞ্চে মূর্ত করে তুলেছিলেন। ছোট্ট ভূমিকার অভিনয়েও যে চিরস্মরণীয় অভিনয় করা যায়, অর্ধেন্দু তা আগেই দেখিয়েছেন। এখানে গিরিশও তার দোসর হলেন। দু’জনের অভিনয়ে মদে মাতাল ও ধর্মে মাতাল দুই ভাবাবেগের বিভিন্ন রূপ মূর্ত হয়ে উঠে একাকার হয়ে গিয়েছিল।
১৯০৭ শুরু হলো গিরিশের ‘য্যায়সা ক্যা ত্যায়সা’ দিয়ে, ১ জানুয়ারি অভিনয়ে সুশীলাবালা (গরব) ও পরবর্তী অভিনয়ে দানীবাবু (হারাধন) মলিয়েরের নাটকটিকে জমিয়ে দিয়েছিলেন। এই বছরেই মিনার্ভা ও স্টার দুই থিয়েটারই এক সঙ্গে ‘প্রফুল্ল’ নামায়। স্টারে (১ জুন) এবং মিনার্ভায় (২ জুন) তখন বেশ প্রতিযোগিতা জমে ওঠে। স্টারে ম্যানেজার অমৃতলাল বসু এবং ডিরেক্টার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। মিনার্ভায় মালিক মনোমোহন পাঁড়ে, ম্যানেজার গিরিশ এবং মাষ্টার অর্ধেন্দুশেখর। স্টারে যোগেশ—অমৃতলাল মিত্র, মিনার্ভায় অর্ধেন্দুশেখর। গিরিশের হাতে গড়া অমৃত মিত্র যোগেশের অভিনয়ে গুরু গিরিশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলেন—তোমার অধীত বিদ্যা দেখাব তোমায়’—এমন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলো। দর্শক দুটো থিয়েটারেই প্রফুল্ল দেখলেন। সে এক উন্মাদনা ও তর্কাতর্কির পর্ব চললো থিয়েটারে।
১৯০৭-এর জুলাই থেকে মিনার্ভা দুরবস্থায় পড়ে। দানীবাবু, তিনকড়ি, কিরণবালা এবং গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা ছেড়ে কোহিনূরে চলে গেলেন। মিনার্ভা বিপদে পড়ে এবারে স্টার থেকে অমরেন্দ্রনাথ দত্তকে পাঁচশো টাকা মাইনে ও বাড়তি বোনাস দিয়ে নিয়ে এলেন, সঙ্গে কুসুমকুমারী। ৩১ জুলাই থেকে অমরেন্দ্রনাথের নাম ম্যানেজার হিসেবে বিজ্ঞাপিত হতে থাকে। অর্ধেন্দুশেখর ‘মাস্টার’ হিসেবে থেকে গেলেন। অক্টোবর থেকে তিনিও কাজে নেমে পড়লেন। অভিনীত হলো—প্রফুল্ল (২৭ অক্টোবর), দুর্গাদাস (৩ নভেম্বর; (অর্ধেন্দুরাজসিংহ, অমর দত্ত-দুর্গাদাস), সিরাজদৌল্লা (১৭ নভেম্বর), ছত্রপতি শিবাজী (প্রথম অভিনয় ২ নভেম্বর, শিবাজী-অমর দত্ত), দলিতা ফণিনী (অমর দত্ত, ৩০ নভেম্বর)।
১৯০৮-এ অভিনীত হলো—বলিদান, নূরজাহান (১৪ মার্চ), প্রায়শ্চিত্ত (দ্বিজেন্দ্রলাল), মেবার পতন (২৬/১২), শাস্তি কি শান্তি (গিরিশ ৭/১১), আর সব পুরনো নাটক। ২৫ এপ্রিল অমর দত্ত মিনার্ভা ছেড়ে দিলেন। তখনো অভিনীত হয়ে চললো নুরজাহান, নবীন তপস্বিনী, য্যায়সা ক্যা ত্যায়সা, তুফানী। ‘তুফানী’ থেকেই মিনার্ভার ভাগ্য আবার ফিরে এলো। উঠে দাঁড়াল মিনার্ভা। ‘জাফর’ করলেন অর্ধেন্দু। সে এক মনোমুগ্ধকর অভিনয়। তারপরে রাণাপ্রতাপ, সিরাজদৌল্লা—পুরনো গৌরবের যুগ ফিরে এলো।
ফিরে এলেন গিরিশ মিনার্ভায়, ১৯ জুলাই থেকে সিরাজদৌল্লা দিয়ে শুরু করলেন তাঁর কাজ। কিন্তু তার আগেই অর্ধেন্দু মনোমালিন্যের কারণে মিনার্ভা ছেড়ে চলে গেলেন (৬ জুলাই)। স্বাস্থ্যও তখন তাঁর একেবারে ভেঙে পড়েছিল। তখনো অভিনীত হল সোরাবরুস্তম (দ্বিজেন্দ্রলাল, ১৯ সেপ্টেম্বর), শাস্তি কি শান্তি (গিরিশ, ৭ নভেম্বর), মেবারপতন (দ্বিজেন্দ্র, ২৬ ডিসেম্বর)।
১৯০৯-এ উল্লেখযোগ্য অভিনয় হল দ্বিজেন্দ্রলালের ‘সাজাহান’ (২১ আগস্ট), ‘দুর্গাদাস’ (৮ ডিসেম্বর) এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গকৌতুক ‘নূতন অবতার’ অবলম্বনে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যরূপ দেওয়া ‘ভগীরথ’ (প্রথম অভিনয়: ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৯)। ‘সাজাহান’ নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন: প্রিয়নাথ ঘোষ—সাজাহান, দানীবাবু—ঔরঙ্গজেব, হরিভূষণ ভট্টাচার্য—দিলদার, সুধীরাবালা—জাহানারা, সুশীলাবালা—পিয়ারা, তারক পালিত—দারা। পরে তারাসুন্দরী (জাহানারা) এবং অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (দিলদার) অভিনয়ে অংশ নেন। নাচে গানে সুশীলাবালা পিয়ারা চরিত্রে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেন। জাহানারা রূপী তারাসুন্দরীও আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন।
১৯১০-এ বঙ্কিমের ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসের নাট্যরূপ, গিরিশের অশোক (৩ ডিসেম্বর) এবং শঙ্করাচার্য (১৫.১.১০) এখানে প্রথম অভিনীত হয়। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের ‘ঠিকে ভুল’ (মলিয়ের অবলম্বনে) অভিনীত হয় ১ অক্টোবর। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের ‘হিরন্ময়ী’ (২৪ জুলাই), ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘বাঙ্গলার মসনদ’ (২ জুলাই)।
১৯১১-তে মনোমোহন তাঁর ‘মিনার্ভা’র এক-তৃতীয়াংশ বেচে দিলেন মহেন্দ্রনাথ মিত্রকে বাইশ হাজার টাকায়। ১৭ জুন মহেন্দ্রনাথ নতুন করে ‘মিনার্ভা’ চালু করেন, অতুলকৃষ্ণের ‘রকমফের’ নাটক দিয়ে।..রকমফের’ নাটকটি শেরিডানের বিখ্যাত School for scandal’ অবলম্বনে লেখা। মনোমোহনের আমলে অভিনীত হয় ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘পলিন’ (৪.২.১১), ‘ঝকমারি’ (গিরিশ, ৮ এপ্রিল)। গিরিশ তখন মিনার্ভায় আছেন।
গ্রেট ন্যাশনালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ‘বলিদান’ (গিরিশ) নামানো হলো। করুণাময় চরিত্রে অভিনয় করলেন স্বয়ং গিরিশ (১৫.৭.১৯১১)। মঞ্চে গিরিশের এই শেষ অভিনয়, এরপরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। গিরিশের মৃত্যু হয় ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯১২।
দ্বিজেন্দ্রলালের ‘চন্দ্রগুপ্ত’ এখানেই প্রথম অভিনীত হলে, ২২ জুলাই, ১৯১১। দানীবাবু চাণক্য চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেন। নরীসুন্দরী করেন ছায়া চরিত্রটি।
গিরিশচন্দ্রের ‘তপোবল’ (১৮ নভেম্বর, ১৯১১) এবং ‘গৃহলক্ষ্মী’ (২১ সেপ্টেম্বর, ১৯১১) এখানেই প্রথম অভিনীত হয় এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। উল্লেখ্য, গৃহলক্ষ্মী নাটকটি গিরিশচন্দ্র শেষ করে যেতে পারেননি। মোটে চারটি অঙ্ক লিখতে পেরেছিলেন। অভিনয়ের অগিদে পঞ্চম অঙ্কটি লিখে নাটকটি শেষ করেন দেবেন্দ্রনাথ বসু। অবশ্য নাট্যকার হিসেবে গিরিশের নামই বিজ্ঞাপিত হয়েছিল।
১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর ‘বঙ্গভঙ্গ’ আইন রদ হয়। ১৯১২-এর ১ এপ্রিল থেকে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হয় দিল্লীতে। কলকাতার অর্থনীতি এবং জীবনযাপন পদ্ধতির ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। যদিও তখনকার নাটক ও নাট্যাভিনয় দেখে পরিস্থিতির এই বদলের কোনো হদিশ পাওয়া যায় না।
১৯১২-এর ১২ মে মালিক মহেন্দ্রনাথ মিত্রের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীদের আপত্তি সত্ত্বেও মনোমোহন মিনার্ভা থিয়েটারের দখল নেন এবং নিজেকে মালিক বলে ঘোষণা করেন। দুপক্ষে মামলা শুরু হয়। এই সময়ে অমৃতলাল বসু স্টার ছেড়ে মিনার্ভায় নাট্যাচার্যরূপে যোগ দেন। তাঁর নাটক ‘খাসদখল’ এখানে অভিনয় করেন। আবার ‘রঙ্গিলা’ (অপরেশচন্দ্র), রুমেলা (সৌরীন্দ্রমোহন), রূপের ডালি (ক্ষীরোদপ্রসাদ) প্রভৃতি নাটক এখানে অভিনীত হলো। তাছাড়া অতুলকৃষ্ণ মিত্রের ‘আসল-নকল’, ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘সোফিয়া’ অভিনীত হয়। ‘আসল-নকল’, ‘সেরিডান’-এর নাটক অবলম্বনে লেখা। রবীন্দ্রনাথের ‘বিদায়-অভিশাপ’ এখানে প্রথম অভিনয় হয় ১৯১৩-এর ২ আগস্ট। ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম ১০ মে, ১৯১৩।
১৯১৪-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা বেজে উঠেছে। এখানে যদিও এই মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কোনো ফল দেখা দেয়নি, কিন্তু ইতিহাসের এই ঘনঘটার কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলা নাটক বা নাট্যশালাতেও পড়েনি। সে তার গতানুগতিক পথেই এগিয়ে চলেছিল। এই সময়ের প্রাক্কালে অভিনীত হয়েছিল প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর ‘ভাগ্যচক্র’ (১৫.১১.১৩), অমৃতলাল বসুর ‘নবযৌবন’ (২০.১২.১৩); দেবকণ্ঠ বাগচীর ‘হেস্তনেস্ত’ (২১.৩.১৪); ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘নিয়তি’ (২১.৩.১৪) ; রাজকৃষ্ণ রায়ের ‘মনোচোরা’ (২০.৬.১৪) [এই নাটকের সবটাই গানে গানে রচিত ইন্ডিয়ান অপেরা]; প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের ‘ক্লিওপেট্রা’ (৫.৯.১৪); ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘আহেরিয়া’ (২৬.১২.১৪) ; অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘আহুতি’ (৬.৩.১৫) [Wilson Buret-এর ‘The sign of the Cross’ অবলম্বনে লেখা] অভিনীত হয়। ওই সময়ে (২৭.২.১৫) স্টারে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ওই একই বিদেশী নাটকের নাট্যরূপ অভিনীত হয়েছিল। এছাড়া, অপরেশচন্দ্রের শুভদৃষ্টি [Lytton রচিত ‘lady of lions’ অবলম্বনে রচিত)। অভিনীত হয়েছিল ৩ ডিসেম্বর, ১৯১৫।
মহেন্দ্রনাথের ভাই উপেন্দ্রনাথের কাছে মামলায় হেরে যাবেন বুঝতে পেরে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট থেকে মনোমোহন পাড়ে ৬ নং বিডন স্ট্রিট থেকে মিনার্ভা থিয়েটারকে স্থানান্তরিত করেন ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে, যেখানে তখন চলছিল কোহিনুর থিয়েটার, তার মালিক ছিলেন মনোমোহন, ম্যানেজার দানীবাবু। গিরিশের ‘কালাপাহাড়’ নাটক দিয়ে কোহিনূর মঞ্চে মিনার্ভার অভিনয় শুরু হয়। মিনার্ভার শিল্পী ও কলাকুশলীরাও দুভাগে ভাগ হয়ে দুই মিনার্ভায় কাজ ও অভিনয় করতে থাকেন। আবার মামলা হয়। মামলায় এবার জিতে মহেন্দ্র মিত্রের ভাই উপেন্দ্রকুমার পুরনো মিনার্ভা মঞ্চে (৬ নং বিডন স্ট্রিট) মিনার্ভাকে ফিরিয়ে আনেন, ম্যানেজার হলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মিনার্ভায় মনোমোহনের যুগ শেষ হলো বলা যায়। ১৯১৫ এর ১ সেপ্টেম্বর থেকে কোহিনূর মঞ্চে তিনি নিজের নামেই মনোমোহন থিয়েটার খোলেন।
উপেন্দ্রনাথ মিত্রের কর্তৃত্বে মিনার্ভায় নতুন করে অভিনয় শুরু হলো; ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর দ্বিজেন্দ্রলালের ‘সিংহল বিজয়’ নাটকের প্রথম অভিনয় দিয়ে। ম্যানেজার তখন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সিংহবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করলেন তিনি।
এই সময় মিনার্ভার দল কলকাতার বাইরে গিয়ে আমন্ত্রিত অভিনয় করছিল মাঝে। তার ফলে কলকাতার মিনার্ভার অভিনয় প্রায়ই বন্ধ থাকতো। তার মধ্যেও অভিনীত হয় ‘বঙ্গনারী’ (দ্বিজেন্দ্রলাল), ‘মোতির মালা’ (বরদাপ্রসন্ন), বঙ্গের রাঠোর (ক্ষীরোদপ্রসাদ), রামানুজ (অপরেশচন্দ্র) প্রভৃতি।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) পরবর্তীকালে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের কথা বলা যায়। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের ‘মিশরকুমারী’ নাটক এখানে অভিনীত হয়, ৫ জুলাই, ১৯১৯। শিল্পীরা ছিলেন কুঞ্জলাল চক্রবর্তী (আবন), হাঁদুবাবু (রামেসিস), সুশীলাসুন্দরী (নেনাহেরিন), প্রিয়নাথ ঘোষ (সামন্দেশ)। এই অভিনয় খুবই সাফল্যলাভ করেছিল। ‘মিশরকুমারী’র অভিনয় দেখে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর আনন্দের কথা কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন (২১ জুলাই, ১৯১৯)—‘দেশকাল পাত্র বিশেষে যথোপযোগী দৃশ্যপট ও সাজগোছ এবং সরঞ্জাম যথাসম্ভব ঠিক রেখে দর্শকের চোখে নিপুণভাবে ধরা বাংলা থিয়েটার মিনার্ভাতেই প্রথম দেখেছি। অভিনয়কালে পাত্র-পাত্রীগণের চারিদিকটা ফাকি এবং ফাক না রেখে যথোপযোগী আসবাবপত্র শোভাসৌন্দর্যে মনোরম করে তোলা ‘মিশরকুমারী’তেই প্রথম দেখলাম। এজন্য আপনাদের রঙ্গপীঠের অধ্যক্ষ ও শিল্পীগণকে প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম।’
১৯২২-এর ১১ ফেব্রুয়ারি অভিনীত হলো দ্বিজেন্দ্রলালের ‘চন্দ্রগুপ্ত’, তারপরে ‘সাজাহান’, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘প্যালারামের স্বাদেশিকতা’। এই নাটকে ব্রিটিশবিরোধী ভাবনা থাকাতে সরকার নাটকটি বাজেয়াপ্ত করে (২৯.৭.১৯২২)। সাহেব চরিত্রে নরেশ মিত্র অসামান্য কুশলতা দেখান।
এই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং বিষাদান্তক সংবাদ হলো, মিনার্ভা থিয়েটার আগুন লেগে পুড়ে যায়। ১৮ অক্টোবর ১৯২২ (১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক)। প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত মালিক উপেন্দ্রনাথ তাঁর দলবল নিয়ে তখন কলকাতার বাইরে আবার অভিনয় করা শুরু করেন। এবং নব-উদ্যমে পুড়ে যাওয়া রঙ্গালয়টি পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারে উঠে পড়ে লাগলেন। আর সময় পেলে কলকাতার আলফ্রেড থিয়েটার ভাড়া নিয়ে অভিনয়ও চালিয়ে যান। এই সময়েই চিত্তরঞ্জন দাশের কাহিনী ‘ডালিম’ অবলম্বনে নাট্যরূপ দেন বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এবং আলফ্রেড থিয়েটারে মিনার্ভা অভিনয় করে।
উপেন্দ্রনাথ মিত্র নতুন করে নবউদ্যমে মিনার্ভা গড়ে তুলে আবার অভিনয় শুরু করেন। মিনার্ভার সাজসজ্জা ও মঞ্চ এবং আঙ্গিক প্রয়োগের নানা অভিনব বৈচিত্র্য আনা হলো। এই সময় থেকেই মিনার্ভায় নাটক অভিনয়ের সময় সংক্ষিপ্ত করা হয় এবং টিকিটের দামও কমানো হয়।
১৯২৫-এর ৮ আগস্ট শুরু হলো নবনির্মিত মিনার্ভায় নতুন করে নাট্যাভিনয়। নাটক ‘আত্মদর্শন’। এই সময় থেকে মিনার্ভায় দর্শকদের নানা সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে মহিলা দর্শকদের জন্য। তাদের জন্য আলাদা বিশ্রামগৃহ এবং ‘যাহাতে শিশুদের নিরাপদে গদিমোড়া খাটে শোয়াইয়া নিশ্চিন্তমনে মহিলারা অভিনয় দেখিতে পারেন’—তারও ব্যবস্থা হয়েছিল। ১৯৩৮ পর্যন্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক ছিলেন। তাঁর সময়েই খ্যাতনামা অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী কিছুকাল এখানে যুক্ত থেকে অভিনয় করেন (১৯৩০ থেকে)। সে সময়কার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাট্যাভিনয় হলো মিশরকুমারী (এপ্রিল, ১৯৩০), বেহুলা (৩০ আগস্ট, ১৯৩০), চন্দ্রনাথ (৯ অক্টোবর, ১৯৩১), প্রতাপাদিত্য (২ আগস্ট, ১৯৩২), দেবযানী (১০ ডিসেম্বর, ১৯৩২)। এসব নাটকে নানা চরিত্রে অসামান্য অভিনয়ের স্বাক্ষর রাখেন অহীন্দ্র চৌধুরী। যেমন আবন (মিশরকুমারী), চন্দ্রধর (বেহুলা), শুক্রাচার্য (দেবযানী) ইত্যাদি।
১৯৩২-এ নতুন আমদানী সবাক চলচ্চিত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে মিনার্ভায় টিকিটের দাম আবার কমানো হয়।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে (১৯৩৯-৪৫) মিনার্ভা নতুন পরিচালক বোর্ডের অধীনে আসে। ১৯৪২ থেকে কাজ শুরু করে। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, নীরদাসুন্দরী প্রভৃতি খ্যাতিমান শিল্পী মিনার্ভায় যোগ দেয়। এখানে অভিনয় কালেই (‘কাটাকমল’ নাটকে) দুর্গাদাস অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান। তখন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য যোগ দেন। পরে সরযূবালা, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র প্রমুখ অভিনেতা অভিনেত্রীরা আসেন। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য অভিনয়গুলি হলো—দেবদাস, দুইপুরুষ (তারাশঙ্কর), ধাত্রীপান্না, সীতারাম, কাশীনাথ, রাষ্ট্রবিপ্লব (শচীন সেনগুপ্ত) প্রভৃতি। এখানে প্রখ্যাত নট ছবি বিশ্বাস, নুটু বিহারী (দুইপুরুষ) এবং রনবীর (ধাত্রীপান্না) চরিত্রে অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। দেবদাস নাটকেই ছবি বিশ্বাসের অভিনয় জীবনের শুরু (১১ মার্চ, ১৯৪৪)।
স্বাধীনতার পরে কয়েক বছর নানা কারণে মিনার্ভা বন্ধ থাকে।
১৯৪৯ থেকে আবার নিয়মিত অভিনয় শুরু হয়। অহীন্দ্র চৌধুরী এই সময়ে মিনার্ভায় ফিরে আসেন (১৯৫০)। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁসীর রাণী (২১ জুলাই, ৪৯), সুধীন্দ্রনাথ রাহার বিক্রমাদিত্য (২২ ডিসেম্বর, ৪৯), অভিনয় হওয়ার পর ১৬ জুন, ১৯৫০-এ অভিনীত হলো ‘দেবদাস’ শুরশ্চন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ। রাজকৃষ্ণ রায়ের নরমেধযজ্ঞ (২২ নভেম্বর, ৫০), মন্মথ রায়ের ‘চাঁদ সদাগর’ (১৯৫০)। তারপরে ১৯৫১-এর ২৩ মার্চ শুরু হয় শরৎন্দ্রের ‘চন্দ্রনাথ’ (নাট্যরূপ: বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র)। অভিনয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী (কৈলাস খুড়ো), ছবি বিশ্বাস (চন্দ্রনাথ), সরযু (সরযূ দেবী) খুব ভালো অভিনয় করেন। মিনার্ভা আবার আর্থিক সাফল্যের মুখ দেখে। মিনার্ভার একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনারূপে সে যুগে ‘চন্দ্রনাথ’ নাট্যাভিনয়কে মনে রাখতে হবে।
শচীন সেনগুপ্তের ‘তুষারকণা অভিনীত হলো ৭ অক্টোবর ১৯৫১। ইন্দু ভট্টাচার্যের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঐ বছরেরই ২১ ডিসেম্বর অভিনয় হলো।
তারপরে বঙ্কিমচন্দ্রের সুবর্ণগোলক (নাট্যরূপ: বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র) অভিনীত হলো ১৩ মার্চ, ১৯৫২। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক ‘কেরানীর জীবন’ (২৫ অক্টোবর, ১৯৫২) বিষয় ভাবনায়, বাস্তব জীবন রূপায়ণে এবং উচ্চমানের অভিনয়ে দর্শকচিত্ত জয় করেছিল। মন্মথ রায়ের ‘জীবনটাই নাটক’ (২৯ জানুযয়রি, ৫৩), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘ঝিন্দের বন্দী’র নাট্যরূপ অভিনীত হলো। ‘ঝিন্দের বন্দী’তে অভিনয় করেছিলেন—ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, সরযূ দেবী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। কাহিনীর রস এবং এঁদের অভিনয়ের উচ্চমানের গুণে নাটকটি দর্শক সাফল্য লাভ করে। এর পরে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জাহাঙ্গীর’ অভিনীত হয় (১৫ অক্টোবর, ৫৩), বিধায়ক ভট্টাচার্যের ‘পিতাপুত্র’ (১৫ জানুয়ারি ৫৫) মহেন্দ্র গুপ্তের ‘সারথী শ্রীকৃষ্ণ’ (১৯৫৫), নিরুপমা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে ‘দেবত্র’ (৫৫), ঠাকুর রামকৃষ্ণ (৫৫) ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের মহানায়ক শশাঙ্ক (৮ অক্টোবর, ৫৫) ধারাবাহিক অভিনয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।
১৯৫৫-এর ২২ ডিসেম্বর সন্তোষ সেনগুপ্ত রচিত ‘এরাও মানুষ’ নাটকটি অভিনীত হয়ে সাড়া ফেলে দেয়। অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেন। বিকলাঙ্গ ভিখিরিদের জীবনযন্ত্রণা, তাদের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনার উচ্চকিত সেন্টিমেন্ট দর্শক আনুকূল্যে সার্থকতা পেয়েছিল। দুশো রাত্রির ওপর এই নাটকটি সে সময়ে অভিনীত হয়েছিল। সন্তোষ সেনগুপ্তের ‘মধ্যবিত্ত’ (৪ অক্টোবর, ৫৬) প্রশান্ত চৌধুরীর ‘প্রত্যাবর্তন’ (৮ ডিসেম্বর, ৫৬) কেদারলাল রায়ের ‘কুন্তী কর্ণ কৃষ্ণ’ (৫ জুলাই, ৫৭), জলধর চট্টোপাধ্যায়ের ‘ড. শুভঙ্কর’ (ডিসেম্বর ’৫৮) এই সময়কালের উল্লেখযোগ্য অভিনয়। এই সময়ে কিছুদিন এখানে শিশিরকুমার ভাদুড়ি তাঁর জীবনরঙ্গ নাটকটি অভিনয় করেন এবং নিজেও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন।
পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে প্রথমে ‘বহুরূপী’ নাট্যগোষ্ঠী শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় এখানে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করে। সপ্তাহের তিনদিন, বৃহস্পতি, শনি ও রবিবারে ‘ছেঁড়া তার’ ও ‘রক্তকরবী’র নিয়মিত অভিনয় শুরু করে। মাত্র দুমাস এখানে অভিনয়ের পর দর্শক আনুকূল্যে ব্যর্থ হয়ে অভিনয় বন্ধ করে দেয়। যে শিক্ষিত, বিদগ্ধ ও রুচিশীল সীমিত রসিক দর্শকের জন্য তারা তাদের দলের হয়ে মাঝে মাঝে অভিনয় করতো, সাধারণ রঙ্গালয়ে পেশাদারি ভাবে নিয়মিত অভিনয় করতে গিয়ে সাধারণ দর্শকের আনুকুল্য থেকে তারা বঞ্চিত হলেন।
মিনার্ভার তখন এমনিতেই দুরবস্থা। প্রায়ই অভিনয় বন্ধ থাকে। অভিনয় হলেও সেগুলি কোনোদিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য নয়। এই দশ বৎসরের সঙ্কটকালে বহুরূপী এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।
তারপরে উৎপল দত্তের পরিচালনায় তাঁর ‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ’ (এল, টি, জি) মিনার্ভা থিয়েটার ‘লীজ’ নিয়ে ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত একাদিক্রমে বহু নাটকের সাফল্যজনক অভিনয় করে। ২৭ জুন ১৯৫৯ থেকে তারা এখানে অভিনয় শুরু করে। ওথেলো, ছায়ানট, নীচের মহল, অঙ্গার, ফেরারী ফৌজ, তিতাস একটি নদীর নাম, কল্লোল, প্রফেসর মামলক, তীর, মানুষের অধিকারে, লেনিনের ডাক প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ে পেশাদারি থিয়েটারের জগতে নতুন ভাবোন্মাদনা ও উদ্দীপনার জোয়ার নিয়ে আসেন। রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তার প্রসারে ও প্রগতিশীল চেতনার বিকাশে লিটল থিয়েটার গ্রুপ-এর প্রযোজনাগুলি বাংলা ব্যবসায়িক থিয়েটারের জগতে নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। অভিনয়ে পরিচালনায়, দৃশ্যসজ্জায়, সেট নির্মাণে, আলোক সম্পাতে, সুর ও সঙ্গীত ব্যবহারে এবং নাট্যবিষয়ের গুরুত্বে, সম্মিলিত অভিনয়ে সেদিন মিনার্ভা জনকল্লোলমুখী হয়ে উঠেছিল। ১৯০৫-এর পর আবার মিনার্ভা তার থিয়েটারকর্মে মানুষের প্রতি তার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে পেরেছিল।
‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ তাদের অভিনয়ের জন্য মিনার্ভার নাম পরিবর্তন করে ‘শিশির নাট্য মন্দির’ রাখার পরিকল্পনা করেছিল। যদিও আইনঘটিত এবং অন্যান্য কারণে শেষ পর্যন্ত মিনার্ভা নামটিই ব্যবহার করা হয়েছিল।
আরেকটি কথা, ‘মিনার্ভা’-তে নিয়মিত অভিনয় করতে এসেই অভিনেতা ও পরিচালক উৎপল দত্ত থিয়েটারের দাবিতে ক্রমান্বয়ে নাট্যকার হয়ে পড়লেন। মিনার্ভায় শুধু উচ্চমানের নাট্যাভিনয় নয়, নাট্যকার উৎপল দত্তকেও সম্ভব করে তুললো।
‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ’ মিনার্ভা ছেড়ে চলে গেলে (২৮ জুলাই, ১৯৭১) মিনার্ভার অভিনয় প্রায় বন্ধ হতে বসে। ‘নাট্যকর্মী পরিষদ’ নামে মিনার্ভার কর্মীসংস্থা এখানে ‘প্রবাহ’ নাটক কিছুদিন অভিনয় করে। ১৯৭২-এ অভিনয় করে ‘১৭৯৯’ নামে নাটক। নাট্যকার ও পরিচালক অসিত বসু। এদের কোনো প্রায়াসই সেভাবে সার্থক হয়নি।
১৯৭০-এর দশকে কলকাতার বেশ কিছু পেশাদার থিয়েটার ব্যবসা চালাবার ঝোকে তাদের থিয়েটারে ‘এ’-মার্কা ‘ব্রো হট’ নাটক অভিনয় করতে থাকে। নাট্যাভিনয় নিম্নমান ও রুচির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। মিনার্ভা তার এই দুর্দিনে (তখন মালিক কস্তুরচাদ জৈন) ওইভাবে থিয়েটারকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল। সেরকম কয়েকটি নাটক হলো—সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে সমর মুখার্জীর নাট্যরূপে এবং তারই পরিচালনায় প্রজাপতি (২৫ এপ্রিল, ১৯৭৪), ব্যভিচার (৩০ মে, ১৯৭৬) ইত্যাদি। এই ধারা বেয়েই নব্বইতেও মিনার্ভা অস্তিত্বহীনতার মাঝে অভিনয় করেছিল ‘এক্সজোন’, সুহাস’ ‘শুধু তোমাকে চাই’ নামীয় রুচিহীন বিকৃত সব নাটক। কিছু কিছু দল মিনার্ভা ভাড়া নিয়ে এইসব নাটকাভিনয়ের আয়োজন করেছিল। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে ‘স্বর্ণবলয়’ (১৫ অক্টোবর, ১৯৭৭), সুনীতকুমার দাসের রচনা ও পরিচালনায় বান্ধবী (১৯৭৮), সুবোধ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে বাসুদেব ঘোষের নাট্যরূপ ও পরিচালনায় জয়া (১৪ আগস্ট, ১৯৭৯), সমর মুখার্জীর রচনা ও পরিচালনায় প্রিয়ার খোঁজে (২ নভেম্বর, ১৯৮০) প্রভৃতি এইসব অকিঞ্চিৎকর নাট্যপ্রযোজনার তালিকায় পড়ে।
১৯৭০-এর দশকের পর থেকে মিনার্ভা প্রায় জীর্ণ ও ব্যবহারহীন হয়ে পড়ে। কখনো কোনো নাট্যদল উদ্যোগী হয়ে মিনার্ভা ভাড়া নিয়ে কিছু নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। কিন্তু কোনটিই ভালভাবে বা বেশি দিন চলেনি। এই ভাবে বিডন স্ট্রিটে মিনার্ভা থিয়েটার তার প্রাচীন ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার অন্তে অস্তিত্বের নিরালম্ব ও জনশূন্যতা হাহাকার নিয়ে পড়ে আছে।
রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে মিনার্ভা থিয়েটারের অবদান
- মিনার্ভা প্রতিষ্ঠার পর থেকে শতবর্ষ অতিক্রম করে গেল। শতবর্ষব্যাপী একটি থিয়েটারের অস্তিত্বই তার ঐতিহ্য ও সাফল্যের প্রমাণ দেয়। যদিও স্টার থিয়েটারের তুলনায় তার গৌরব অনেক কম। বহু মালিকানা বদল সত্ত্বেও মিনার্ভা তার অভিনয় চালিয়ে গেছে। গিরিশ, অর্ধেন্দুশেখর, অমরেন্দ্রনাথ, অপরেশচন্দ্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস, নির্মলেন্দু, ছবি বিশ্বাস—থিয়েটার জগতের খ্যাতিমান পুরুষেরা এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মিনার্ভার মাহাত্ম্য বাড়িয়ে দিয়েছেন।
- গিরিশ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত সব নাটকের অভিনয় এখানেই হয়েছে।
- নানা বিচিত্রমুখী নাটকের প্রযোজনায় মিনার্ভা খ্যাতিলাভ করেছিল। ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক গীতিনাট্য অপেরা, পঞ্চরং, প্রহসন-নক্সা—সব জাতীয় নাটকের অভিনয়েই মিনার্ভা সাফল্য লাভ করে।
- গিরিশের জীবনের শেষ দশ বারো বছর তিনি প্রায় মিনার্ভাতেই কাটিয়েছেন। পরিণত বয়সের নাট্যরচনাগুলি সব মিনার্ভার জন্যই। তাঁর পরিণত অভিনয় শিক্ষাদান এই মিনার্ভার শিল্পীদের জন্য।
- অর্ধেন্দুর স্বাজাত্যবোধ ও দেশানুরাগ এই মিনার্ভার মধ্য দিয়েই আবার প্রকাশ লাভ করেছিল। ব্রিটিশের শাসনের চোখ রাঙানি অস্বীকার করে মিনার্ভা দেশপ্রেমের নাটক অভিনয় করে গেছে। থিয়েটারকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শরিক করে তুলতে পেরেছিল।
- এল. টি. জি. এই মিনার্ভাকেই নতুন যুগের থিয়েটারের ‘প্রাণস্থল’ করে দিয়ে গেছে।
- বাঙালির জাতীয়জীবনের উত্থান-পতনের শরিক হওয়ার চেষ্টা মিনার্ভা সবসময়েই করে গেছে। নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে মিনার্ভার শতবর্ষব্যাপী বিচিত্রমুখী নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত করে রেখেছে।


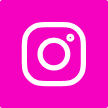


Leave a Reply