রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য সম্পর্কে আলোচনা কর।
অন্নদামঙ্গল কাব্য
অন্নদামঙ্গল রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচনা। কাব্যটি দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক কাব্য। ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র রায় এই কাব্য রচনা করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাংলায় প্রতিমায় দেবী অন্নপূর্ণার পূজা প্রচলন করেন। তিনিই ভারতচন্দ্রকে রায়গুণাকর উপাধি প্রদান করেন এবং দেবীর মাহাত্ম্যব্যঞ্জক একটি কাব্য রচনার অনুরোধ করেন। সমগ্র কাব্যটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত— (ক) অন্নদামঙ্গল বা অন্নদামাহাত্ম্য, (খ) বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল ও (গ) মানসিংহ বা অন্নপূর্ণামঙ্গল। মঙ্গলকাব্য ধারায় অন্নদামঙ্গল কাব্যকে একটি পৃথক শাখা রূপে গণ্য করা হয় না; কারণ ভারতচন্দ্র ভিন্ন অপর কোনো কবি এই বিষয়বস্তু অবলম্বন করে কাব্যরচনা করেননি।
দেবী অন্নদার উৎপত্তি
চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী এবং অন্নপূর্ণা বা অন্নদা এদের উদ্ভবের পেছনে যে বৈদিক ঋষি কল্পনায় উদ্ভাসিত পৃথিবীমাতার অন্নদা রূপের মিশ্রণ রয়েছে, তা মূলত একইরূপ। মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী নিজেকে শাকম্ভরী রূপে অভিহিত করেছেন এবং এই রূপেই তিনি পৃথিবীকে শস্য শ্যামল করে রাখেন। মঙ্গলচণ্ডীদেবী একাধারে শান্ত ও উগ্র। তিনি কল্যাণময়ী, তাই তিনি অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পশুকুলকে আশ্রয় দেন। অন্যদিকে অন্নদা বা অন্নপূর্ণা প্রকৃতই কল্যাণময়ী মাতৃমূর্তি। তিনি সন্তানকে যেচে বর দেন। তাঁর কৃপায় ভক্তের সন্তান ‘দুধে-ভাতে’ থাকে। সুতরাং কালকেতু যে দেবীর কৃপালাভ করেছিলেন, তাঁর ছদ্মবেশ অপসারণ করলে দেখা যাবে তিনি আসলে পশুমাতা বনদেবী, বৈদিক বহু অন্নদাত্রী মৃগমাতা অরণ্যানী।
চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী ও অন্নদা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শক্তিদেবতার বিভিন্ন নাম দেখতে পাওয়া যায়। যেমন— দুর্গা, নারায়ণী, সতী, ভগবতী, গৌরী, পার্বতী, সনাতনী, সর্বাণী, সর্বমঙ্গলা, অম্বিকা, চণ্ডী ইত্যাদি। অবশ্য এই বিভিন্ন শক্তিদেবতা পরিণামে শিবের একমাত্র পত্নীরূপে অর্থাৎ শক্তিরূপে পরিণতি লাভ করেছেন। একমাত্র শক্তির বিভিন্ন নাম হলেও এবং পরিণামে একই শক্তিতে পরিণতি লাভ করলেও এদের উদ্ভবের ইতিহাস পরস্পর স্বতন্ত্রই ছিল।
দেবী অন্নদা বা অন্নপূর্ণার উদ্ভবের উৎস সন্ধান করতে গেলে, চণ্ডীদেবীকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তার ধারাটি অনুধাবন করতে হবে। এই সাহিত্যের তিনটি ধারা লক্ষ করা যায়—(১) মহিষমর্দিনী চণ্ডীর ধারা—অসুরদের সম্রাট মহিষাসুর একবার দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। সেই যুদ্ধে দেবরাজ পরাভূত হলেন এবং মহিষাসুর ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। তখন দেরাজের দুর্গতির সীমা রইল না। সমস্ত দেবতা গিয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। মহিষাসুরের অত্যাচারের বিবরণ শুনে বিষ্ণু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন আর অন্যান্য দেবতারা তো ক্রোধান্বিত ছিলেনই। ক্রুদ্ধ দেবকুলের মুখ হতে তেজ নির্গত হতে লাগল। সেই অশেষ তেজঃপুঞ্জ হতে ত্রিভুবন উজ্জ্বলকারিণী এক দেবী সমুদ্ভূতা হলেন। সমস্ত দেবতা বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে এই দেবীকে রণসাজে সজ্জিত করে দিলেন। ইনিই মহিষাসুরমর্দিনী। ‘চণ্ডিকাবিজয়’, ‘দুর্গামঙ্গল’ কাব্যে এই দেবী বন্দিতা হয়েছেন। (২) মঙ্গলচণ্ডীর ধারা কালকেতু ও ধনপতি উপাখ্যানে অর্থাৎ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যসমূহে বন্দিতা দেবী। (৩) অন্নদা বা অন্নপূর্ণার ধারা—অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে এই দেবীর বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতচন্দ্রই এই কাব্যধারার প্রবর্তক। তাই তিনি তাঁর কাব্যের প্রারম্ভে লিখেছেন—
ভারত ও পদ-আশে নূতন মঙ্গল ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।।
এই অন্নদাই আবার দেবী কালিকা। অন্নদামঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে কালিকা দেবীরই মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী হতে অন্নদা বা কালিকার রূপান্তর পর্যন্ত ধারাটিকে আমরা এভাবে বিবৃত করতে পারি— (১) চণ্ডীদেবী, ইনি উগ্রা প্রকৃতির দেবতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রথম আবির্ভাব দেখতে পাওয়া যায়। ইনিই পরবর্তী যুগে দেবী দুর্গারূপে প্রতিভাত হয়েছেন। (২) চণ্ডীদেবীর সঙ্গে নানা পৌরাণিক ও লৌকিক ল দেবীর মিশ্রণজাত মঙ্গলচণ্ডী দেবী—ইনি শান্তোগ্র দেবতা। (৩) ইনিই পরিণামে ‘সন্তানকে দুধে ভাতে’ রাখবার দেবতা বা অন্নদা বা অন্নপূর্ণা হয়ে একেবারে পরিপূর্ণ মাতৃমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন।
দেবী অন্নদার সঙ্গে আবার বৈদিক অরণ্যানী দেবতার বেশ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বেদে অদিতি, পৃথ্বী, সীতা, অরণ্যানী প্রভৃতি ভূমি ও শস্যদেবতাদের কথা পাওয়া যায়। এই সকল দেবতার মধ্যে দেবী মাতা অদিতিই প্রধান। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (মহিষমর্দিনী চণ্ডীর উদ্ভব এই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে) দেবী বলেছেন যে, তিনিই পৃথিবীকে ফলে, শস্যে পূর্ণ করে তোলেন এই জন্যই তিনি শাকম্ভরী। শারদীয়া দুর্গাপূজার একটি প্রধান অঙ্গ নবপত্রিকা পূজা। কলা, হলুদ, কচু, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধান। প্রভৃতি দ্বারা এই পূজা হয়ে থাকে। এই পূজা ভূমিমাতার পূজা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই যে অন্নদা বা অন্নপূর্ণা যাবতীয় জীবের অন্নের সংস্থান করে থাকেন, তাঁকে ভূমি বা শস্য দেবতারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।
চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, দুর্গা বা অন্নদা বা অন্নপূর্ণা—এরা একই শক্তির বিভিন্ন রূপ। তবে এঁদের বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হবার বিভিন্ন কারণ দেখতে পাওয়া যায়। মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডীর উল্লেখ বা নিদর্শন কাব্যে বা প্রস্তরশিল্পে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে দেখা যায়। খ্রিস্টীয় একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে লক্ষ্মী-সরস্বতী কার্তিক-গণেশ সমন্বিত মহিষমর্দিনী দুর্গা প্রতিমার আবির্ভাব দেখতে পাওয়া যায়। অতঃপর চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাংলার কাব্যে মঙ্গলচণ্ডীর কাহিনির সঙ্গে উমামহেশের কাহিনি যুক্ত হতে দেখি। ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের মধ্যে এই দেবীকেই কালিকা দেবীরূপে বন্দিত হতে দেখতে পাই। তারপর অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রে এসে অন্নদামূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। তান্ত্রিক বা বৌদ্ধতান্ত্রিক, পৌরাণিক, লৌকিক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রভাবে এই দেবী এক এক সময় এক এক মূর্তি ধারণ করেছেন। অবশ্য তার সঙ্গে সাময়িক কারণ তো ছিলই।
কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র
মধ্য যুগের শেষ পর্বের কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবন বড়ই বিচিত্র। তার সাহিত্যও চিত্তাকর্ষী। কবি ঈশ্বর গুপ্ত দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে ভারতচন্দ্রের জীবনের নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সেই তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, ধনী ভূস্বামী বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম। ১৭০৫-১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে হাওড়া ও হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরসুট পরগণার অধীনে পেঁড়ো গ্রামে কবির জন্ম। তাঁর পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় একজন সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ছিলেন। কোন কারণে বর্ধমানরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে নরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্য ভুরসুট আক্রমণ করে গ্রাস করেন। বর্ধমানের মহারাজের সঙ্গে বিবাদের ফলে নরেন্দ্রনারায়ণ সর্বস্বান্ত হন।
ফলে ধনীর দুলাল ভারতচন্দ্রকে ছেলেবেলা থেকেই নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়। ভূস্বামী পিতা নিঃস্ব হলে কবিকে বাল্যকাল থেকেই মণ্ডলঘাট পরগণার অধীনে নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে থাকতে হয়। সেখানে মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সেই তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ অধিগত করেন এবং এই বয়সেই গুরুজনের সম্মতির অপেক্ষা রেখেই মাতুলালয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রামে বিয়ে করে বসেন। তখন অর্থকরী ফরাসী শিক্ষা লাভই জীবিকার প্রধান অবলম্বন হওয়ায় বাঁশবেড়িয়ার বিখ্যাত রামচন্দ্র মুন্সীর কাছে ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিশোর কবিকে যে এই বিদ্যাভ্যাসের সময় কিরূপ কৃচ্ছসাধন করতে হয়েছিল তার বিবরণ দিয়েছেন ঈশ্বর গুপ্ত—“দিবসে একবার মাত্র রন্ধন করিয়া সেই অন্ন দুইবেলা আহার করেন, প্রায় কোন দিবস ব্যঞ্জন পাক করেন নাই। একটি বেগুনপোড়ার অধভাগ এবেলা এবং অধভাগ ওবেলা আহার করিয়া তাহাতেই তৃপ্ত হইয়াছেন।” (ঈশ্বর গুপ্ত কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত)।
ফারসী ভাষা শিক্ষালাভ করে বাড়িতে ফিরে ভাইদের পরামর্শে পিতৃসম্পত্তি উদ্ধারের আশায় বর্ধমানে গিয়ে উপস্থিত হলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি রাজকর্মচারীদের চক্রান্তে কারাগারে প্রেরিত হলেন। ভারতচন্দ্র ছিলেন অতিশয় বাকপটু। তাই কারাগারে থাকাকালীন তিনি কারাধ্যক্ষকে বিনয়ন বচনে বশীভূত করে কারাগার থেকে মুক্ত হন। সেখান থেকে তিনি মারাঠা অধিকৃত কটকে গিয়ে ঐ অঞ্চলের মারাঠা সুবাদার শিবভট্টের সাহায্যে এক ভৃত্য সহ কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে পুরীধামের শঙ্করাচার্য মঠে অবস্থান করেন। পরে কবি একদল বৈষ্ণবের সঙ্গে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। কিন্তু মাঝপথে আত্মীয়দের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি আবার সংসারে ফিরে আসেন। জীবিকার সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি চন্দননগরের ফরাসি গভর্ণমেন্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং চৌধুরী মহাশয় কবির বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আশ্রয় দিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কবির গ্রাসাচ্ছাদনের নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা করবার জন্য নবদ্বীপের অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে অনুরোধ করেন। ভারতচন্দ্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সভায় স্থান দিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে কবি মুকুন্দের আদর্শে চণ্ডীমঙ্গলের ধারা অনুসরণ করে ‘অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার জন্য অনুরোধ করেন। এই কাব্যের জন্য তিনি কবিকে ‘রায়গুণাকর’ উপাধি দিয়েছিলেন। গুপ্তকবি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—“ভারত বলিলেন, মহারাজ, কিরূপ রচনা করিতে অনুমতি করেন।” রাজা কহিলেন, “মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (যিনি কবিকঙ্কণ নামে বিখ্যাত ছিলেন), তিনি যে প্রণালীক্রমে কবিতায় চণ্ডী রচিয়াছিলেন, তুমি সেই পদ্ধতিক্রমে অন্নদামঙ্গল পুস্তক প্রস্তুত কর।”
সম্ভবত রাজার নির্দেশেই ‘অন্নদামঙ্গলের’ সঙ্গে ‘বিদ্যাসুন্দর’ ও ভবানন্দ মজুমদারের প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর কৃষ্ণচন্দ্ৰ কবিকে মূলাজোড় গ্রাম ছয়শত টাকা রাজস্বের বিনিময়ে ইজারা দেন এবং বাড়ি তৈরি করার জন্য কবিকে একশত টাকা দান করেন। সেখানে বাড়ি তৈরি করে মূলাজোড়েই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং মাঝে মাঝে কৃষ্ণনগর ও ফরাসডাঙ্গায় যাতায়াত করতে থাকেন। কিন্তু পত্তনিদারের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে ভারতচন্দ্র রাজার কাছে বাস পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেন, রাজাও তার অনুরোধে সাড়া দিয়ে পার্শ্ববর্তী ‘গুস্তে’ গ্রামে কবির বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। কবি ওখানে বসবাসের জন্য প্রবৃত্ত হলে গ্রামবাসীদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত কবি মূলাজোড়েই থেকে যান। এই গ্রামে এখনও ভারতচন্দ্রের বংশধররা বর্তমান। ঈশ্বর গুপ্তের মতে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে কবি ভারতচন্দ্র মৃত্যুবরণ করেন।
কবির এই জীবন পরিচয় থেকে বোঝা যায়, ভারতচন্দ্রকে বাল্য বয়স থেকেই ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্যে কাটাতে হয়। কিন্তু তিনি এইসব বিপর্যয়কে জয় করেছেন প্রখর বুদ্ধির দ্বারা। যে আত্মসম্মান ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁর ছিল, তার দ্বারা তিনি প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বলেছেন—“অষ্টাদশ শতাব্দীর দরবারী আদর্শে তিনি বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐশ্বর্য পান নাই, জমিদার পুত্র হইয়াও জমিদারের উমেদারী এবং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দাসত্ব করিয়াছেন; সরস্বতীর বরপুত্র হইয়াও তাহাকে লক্ষ্মীমন্তদের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। কিন্তু এই দুর্বিপাকের মধ্যে পড়িয়াও তাঁহার মুখের হাসি ও চোখের কটাক্ষ নিভিয়া যায় নাই, রঙ্গের উতরোল উল্লাস ও ব্যঙ্গের তির্যকতা তাঁহার সদা-প্রসন্ন মনটিকেই উদ্ঘাটিত করিয়াছে রচনার মধ্যে দিয়া তাহার কৌতুকপ্রবণ চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে—এমনকি কণ্ঠস্বরের ওঠানামা পর্যন্ত যেন কর্ণগোচর হইতেছে।”
প্রমথ চৌধুরীও ভারতচন্দ্র’ প্রবন্ধে (প্রবন্ধ সংগ্রহ) ভারতচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে বলেছেন—“রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হয়েও তার দারিদ্র ঘোচেনি, এবং দারিদ্র্য তাঁকে নিরানন্দ করিতে পারেনি, করেছিল শুধু ‘প্রমোদের প্রভু’। এ প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব। যথার্থ আর্টিস্টের মন সকল দেশেই সংসার নির্লিপ্ত, কস্মিনকালে বিষয় বাসনায় আবদ্ধ নয়।”
ভারতচন্দ্রের কাব্য পরিচয়
ভারতচন্দ্রের প্রথম রচনা সত্যপীরের পাঁচালী’ (১৭৩৮)। এই পাঁচালী বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। ঈশ্বর গুপ্ত মনে করেন, রামচন্দ্র মুন্সীর নির্দেশে চৌপদী ছন্দে সত্যপীরের পাঁচালী রচিত হয়।
ভারতচন্দ্রের পরবর্তী রচনা ‘রসমঞ্জরী’ (১৭৪৯)। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে এবং কামসূত্রে নায়ক-নায়িকাদের যেসব লক্ষণাদির বর্ণনা আছে ভারতচন্দ্র তাই অনুসরণ করে এই প্রকীর্ণ কবিতাগুলি রচনা করেন। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ মৈথিলি কবি ভানুদত্ত কামশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্র মিলিয়ে ‘রসমঞ্জরী’ শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীর আদর্শ ভানুদত্তের এই গ্রন্থ। কাব্যারম্ভে ভারতচন্দ্র বলেছেন—
রসমঞ্জরীর রস ভাষায় করিতে বশ।
আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া।
বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্যের সার্থক দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে প্রথমেই ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীর নাম করেছেন। কারণ রসমঞ্জরীর কোথাও কোথাও গীতিকবিতার স্পর্শ আছে।
ভারতচন্দ্রের পরবর্তী রচনা ‘নাগাষ্টক’ (১৭৫০)। কবি যখন মূলাজোড় গ্রামে বাস করতেন, তখন স্থানীয় জমিদার রামচন্দ্র নাগের অত্যাচারের প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করে কবি সংস্কৃতে এই কাব্যটি রচনা করেন।
১৭৫২-৫৩-র মধ্যে ভারতচন্দ্র তিন খণ্ডে অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় খণ্ডে ভারতচন্দ্র কাব্যরচনার সন উল্লেখ করেছেন—
বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্ৰহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।।
অর্থাৎ বেদ-৪, ঋষি-৭, রস-৬, ব্ৰহ্ম-১। অঙ্কস্য বামা গতি। তাই ১৬৭৪ শকে (১৬৭৪ শক + ৭৮ বছর) অর্থাৎ ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে কবি এই অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।
অন্নদামঙ্গল তিন খণ্ডে বিভক্ত— ক) অন্নদামঙ্গল, (খ) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর, (গ) অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ। এই কাব্যরচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—দেবী অন্নদা কীভাবে ভবানন্দ মজুমদারকে কৃপা করলেন এবং ভবানন্দ কীভাবে জাহাঙ্গীরের দ্বারা অন্নপূর্ণা পূজা করিয়ে রাজত্ব ও রাজা খেতাব লাভ করলেন—সেই বর্ণনা দেওয়া।
বাংলা যখন আলীবর্দীর শাসনে, যখন বর্গীর আক্রমণে বাংলা পর্যন্ত সেই সময়ের বর্ণনা দিয়ে অন্নদামঙ্গলের শুরু। নবাব কর্তৃক কৃষ্ণচন্দ্রের কয়েদ হওয়া। বিপন্ন রাজার অন্নদা বন্দনা সভাসদ কবি ভারতচন্দ্রকে দেবী মাহাত্ম বিষয়ক গান লিখতে আদেশ প্রভৃতি হল গ্রন্থেৎপত্তির কারণ। এরপর পৌরাণিক আখ্যান অনুসরণে এবং কাশীখণ্ড অবলম্বনে সতীপ্রসঙ্গ, হর-পার্বতীর বিবাহ, তাদের গার্হস্থ্য জীবন বর্ণিত। শিব অন্নপূর্ণার কাছে মনের সুখে ভোজন করে কাশীতে অন্নদার মন্দির নির্মাণ করে মাহাত্ম্য প্রচারের কথা বলেন।
এই কাহিনির সঙ্গে আরও দুটি কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। একটিতে ব্যাসদেবের ব্যাসকাশী নির্মাণে ব্যর্থতা ও অশেষ দুর্গতি বর্ণিত হয়েছে। এই পৌরাণিক কাহিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাশীখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় কাহিনি হরিহোড়ের বৃত্তান্ত এবং ভবানন্দ মজুমদারের প্রতি দেবীর কৃপা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং প্রথম খণ্ডের কাহিনির মধ্যে তিনটি উপকাহিনি— (ক) হর-পার্বতী ও ব্যাসদেব, (খ) হরিহোড়, (গ) ভবানন্দ।
অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড ‘বিদ্যাসুন্দর’। তবে এই খণ্ড প্রকৃতপক্ষে ‘কালিকামঙ্গল’ নামে খ্যাত। কারণ ভারতচন্দ্র প্রচলিত কালিকামঙ্গলের উপর ভিত্তি করে এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ছাপাখানার কল্যাণে বহু বিদ্যাসুন্দর তৎকালীন জনমানসে ছাপা হয়ে প্রচারিত হয়। ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের কবিরূপে খ্যাতি লাভ করেছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি শুরু হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকায়।
অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডের শেষে ভারতচন্দ্র লিখেছিলেন—
ইতঃ পর কহে শুন রায় গুণাকর।
প্রতাপাদিত্য মানসিংহের সমর।।
সুতরাং ভবানন্দ মজুমদারের বাড়িতে দেবী অচলা হলে মজুমদার কীভাবে প্রাধান্য লাভ কলেন তা বর্ণনা করার জন্য তিনি প্রথম খণ্ডের পরেই প্রতাপ-মানসিংহের যুদ্ধ, প্রতাপের পরাভব ও ভবানন্দের প্রাধান্য লাভের পরিকল্পনা করেছিলেন। বাংলা জয়ের জন্য প্রেরিত মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের ভূমিকা বিদ্যাসুন্দরের প্রারম্ভে বর্ণিত হয়েছে। ভবানীর বরপুত্র প্রতাপাদিত্য প্রবল প্রতাপান্বিত হলে বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাকে দমন করার জন্য মানসিংহকে বাংলায় পাঠিয়ে দেন। মানসিংহ বর্ধমানে উপনীত হলেন। সেই সময় দেবী অন্নদার কৃপায় ভবানন্দও বর্ধমানে গিয়ে মানসিংহের কানুনগো হলেন। সেখানে একদিন মানসিংহ একটি সুড়ঙ্গ দেখে নিতান্তই কৌতূহলবশত ভবানন্দকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে কানুনগো তার বৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করলেন—
বিবরিয়া মজুন্দার বিশেষ কহেন তার
যেইরূপে সুড়ঙ্গ হইল।।
সুতরাং কাহিনির এই প্রেক্ষাপট রচনা করে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি রচনা করেছেন। বর্ধমানরাজ বীরসিংহের পরমা সুন্দরী ও বিদূষী কন্যা বিদ্যা ও কাঞ্চীরাজ গুণসিন্ধুর পুত্র সুন্দরের গোপন মিলনই এর প্রধান আখ্যান। সুন্দর দেশী কালিকার কৃপায় সুড়ঙ্গ খনন করে সুগোপনে অনুঢ়া রাজকন্যা বিদ্যার শয়নগৃহে উপস্থিত হয়। উভয়ের সেই গোপন মিলন সংক্রান্ত কাহিনিটি ভবানন্দ মানসিংহকে সবিস্তারে নানা ছন্দে শুনিয়েছেন।
ঈশ্বর গুপ্তের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ড শুনে কবিকে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করত প্রথম খণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কবিও রাজার ইচ্ছানুসারে অতি কৌশলে ‘বিদ্যাসুন্দর’ রচনা করে রাজাকে শুনিয়েছিলেন।
আসলে অন্নদামঙ্গল ও অন্নপূর্ণামঙ্গল (প্রথম খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ড) পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ কাহিনি। মধ্যভাগের কাহিনি অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি কবি পৃষ্ঠপোষকের অনুরোধে সুকৌশলে মূল কাহিনির সঙ্গে এই রোমান্টিক গল্পকে সংযোজিত করেছেন।
ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর-এর সুর মূলত গীতি-প্রধান। কথিত আছে, বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করে ভারতচন্দ্র তা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে উপস্থিত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র তখন কাজে ব্যস্ত থাকায় বইটি পাশে রেখে দেন। তাই ভারতচন্দ্র কিছুক্ষণ পর মহারাজকে বললেন— “মহারাজ, পুথিখানি এইভাবে রাখিবেন না, ইহার রস গড়াইয়া পড়িবে।” তা শুনে কৃষ্ণচন্দ্র পুথিটি খুলে দু’একটি পাতা পড়লেন ও পড়ে বললেন— “বাস্তবিকই যে রস তুমি সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা গড়াইয়া পড়িবারই মত।”
কাব্যে ভাষার কারুকার্য যথেষ্ট। ছন্দেও তিনি গতানুগতিক রীতি বর্জন করে ভাবের অনুকুল ছন্দ সৃষ্টি করেছেন। পদের মিলের দিক দিয়েও ভারতচন্দ্র প্রথম উপান্ত স্বর থেকে মিলের নিয়ম প্রবর্তিত করলেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য বিদ্যাসুন্দর কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন— “ভাবের গভীরতার জন্য নহে, রসের উচ্ছলতার জন্য ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। কাব্যখানি মঙ্গলকাব্যের আকারে লিখিত হইলেও কালীর মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া তাহাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। একটি মানবিক প্রণয় কাহিনীকেই আধ্যাত্মিক গৌরব দিবার জন্য কালিকার নাম ইহাতে আনিয়া যুক্ত করা হইয়াছে।”
তৃতীয় খণ্ড ‘মানসিংহ’ বা ‘অন্নপূর্ণামঙ্গল’। দেবী অন্নপূর্ণার কৃপাবশত জমিদারী লাভ করে ভবানন্দের রাজ-উপাধির দ্বারা সমাজে প্রাধান্য বিস্তার, ভবানন্দের অন্নপূর্ণা—কৃপালাভ এবং জাহাঙ্গীরকে দেবীভক্ত করবার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই খণ্ডের কাহিনি বাংলায় মুঘল অভিযানের পটভূমিকায় স্থাপিত। মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে এসে দুর্যোগে বিপন্ন হয়েছিলেন, তখন ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের কানুনগো হয়ে দেবী অন্নপূর্ণার কৃপায় মুঘল ও রাজপুত বাহিনীকে অন্নদান করে রক্ষা করেছিলেন। তবে এই ঘটনা ইতিহাস স্বীকৃত নয়। এই খণ্ডের প্রতাপাদিত্যের কাহিনির ভিত্তি কিছু জনশ্রুতি, কিছু ইতিহাস আর কিছু কল্পনা।
তৃতীয় খণ্ডের কাহিনি হল—প্রতাপাদিত্য দমনে মানসিংহ বাংলায় এলে ভয় তার কানুনগাে নিযুক্ত হলেন এবং ঝড়বৃষ্টিতে অতিব্যাকুল মুঘল রাজপুত বাহিনা দেবী অন্নপূর্ণার কৃপায় অন্নদান করে তাদের প্রাণরক্ষা করলেন। দিল্লি যাওয়ার সময় মানসিংহ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি ভবানন্দকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন এবং যাতে মজুমদারের ঐহিক সুবিধা হয়, সে ব্যবস্থা করবেন। মানসিংহ ভবানন্দের উপদেশে অন্নপূর্ণা পূজা করে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন। প্রতাপাদিত্যকেও তিনি পরাভূত ও বন্দি করে দিল্লি যাত্রা করলেন ভবানন্দকে নিয়ে। এদিকে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়। প্রতাপাদিত্যের শবদেহ নিয়ে মানসিংহ চললেন বাদশাহকে ভেট দিতে। বাদশাহ তুষ্ট হয়ে বাংলা জয়ের ব্যাপারে জানতে চাইলে। মানসিংহ ভবানন্দকে দেখিয়ে বললেন যে, অন্নপূর্ণার মহাভক্ত ভবানন্দ দেবীর কৃপায় তাদেরকে দারুণ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং তাকে রাজা উপাধি ও জমিদারী দান করা উচিত। ইসলাম ধর্মাবলম্বী জাহাঙ্গীর হিন্দুর দেবীর এই অলৌকিক ক্ষমতা অস্বীকার করে, ভবানন্দের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ভূতুড়ে কাণ্ড বলে মনে করে ভবানন্দকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করলেন। কারাবাসের সময় ভবানন্দ অন্নপূর্ণার স্তব করলে দেবী আকাশবাণীতে মজুমদারকে সান্ত্বনা দিলেন। এরপর ঘটনাচক্রে জাহাঙ্গীর হিন্দুধর্মের প্রতি বিরূপতা ত্যাগ করে, অন্নপূর্ণা ভক্ত হলেন এবং ভবানন্দের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হয়ে দিল্লিতে অন্নপূর্ণার পূজার নির্দেশ দিলেন। ভবানন্দও অন্নপূর্ণা পূজার পর বাড়িতে ফিরে এলেন। বাড়ি ফিরেও ভবানন্দ অন্নপূর্ণা পূজা করলেন, তখন স্বয়ং দেবী আবির্ভূত হয়ে ভবানন্দের সঙ্গে আলাপ করলেন। দেবীর নির্দেশে ভবানন্দের পুত্র গোপাল রাজপদ পাবে স্থির হল। এবার এল শাপ অবসানের পালা। কুবের পুত্র নলকুবের ভবানন্দের মর্ত্যকায়া ত্যাগ করে স্বর্গে ফিরে যান।
অন্নদামঙ্গল কি নূতনমঙ্গল?
মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ধারা মঙ্গলকাব্য। এই মঙ্গলকাব্যের ধারায় অন্নদামঙ্গলের স্থান স্বতন্ত্র। কারণ মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত রূপাঙ্গিক ও ভাবধারা অন্নদামঙ্গলে অনুপস্থিত। এমনকি স্বয়ং কবিও তাঁর কাব্যকে একাধিকবার ‘নূতন মঙ্গল’ নামে অভিহিত করেছেন। যেমন, অন্নপূর্ণা বন্দনার শেষে কবি ভণিতায় লিখেছেন—
নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে।
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।
কিম্বা, দেবী সরস্বতীকে বন্দনা জানিয়ে কবি তার কবিকর্মের সাফল্য কামনা করে দেবীর কৃপা প্রার্থনা করে বলেছেন—
দয়া কর মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া
পূর্ণ কর নূতন মঙ্গল।
কবি ভারতচন্দ্র তাঁর নিজের কাব্যকে ‘নূতন মঙ্গল’ নামে অভিহিত করার কারণ শুধু অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্রের পূর্বে কোন কবি রচনা করেননি—এই দিক থেকে নয়। বরং এই কাব্যের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর মধ্যে যে অভিনবত্বের দিকগুলিকে কবি প্রকাশ করেছেন, সেদিক থেকে মধ্য যুগ এক অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে এবং এখানেই অন্নদামঙ্গলকে ‘নূতন মঙ্গল’রূপে অভিহিত করার সার্থকতা।
তুর্কি আক্রমণের ভয়ে ভীত বাঙালির কাছে মঙ্গলকাব্যের গান ছিল তাদের কাছে আদরের সামগ্রী। তাই নির্দিষ্ট কাঠামোয় পূজা প্রচারের মানসে দেব-দেবীর মাহাত্মকীর্তনে মঙ্গলকাব্যের কবিরা তাদের লেখনী ধারণ করেছিলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের ধারায় সেই পুচ্ছগ্রাহিতার অভিমুখী হলেন না, বরং এই ধারায় নতুন, কাহিনি বিন্যাস করে, যুগের রুচি ও চাহিদাকে মর্যাদা দিয়ে নিজ প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে রচনা করলেন মঙ্গলকাব্যের ধারায় এক স্বতন্ত্র মঙ্গলকাব্য—যার নাম ‘অন্নদামঙ্গল’। মঙ্গলকাব্যের আধারে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল তাই অধরা। অন্নদামঙ্গল মঙ্গলকাব্য ঠিকই কিন্তু তা অভিনব মঙ্গলকাব্য। এই অভিনবত্বের কারণগুলি অনুসন্ধান করা যেতে পারে—
(এক) বহিরাক্রমণের কারণে, আর্য-অনার্য বর্গসংযোগের প্রয়োজনে মধ্য যুগে যে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ভারতচন্দ্রের সময় সেই প্রয়োজন প্রায় অপসৃত হওয়ায় পৌরাণিক লৌকিক দেবদেবীর প্রতি মানুষের আস্থা, বিশ্বাস কমতে থাকল। মঙ্গলকাব্যের দেবতারা যেহেতু ফলপ্রদ দেবতা, তাই সেখানে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক অনেক বেশি। ভক্ত যেমন নিত্য প্রয়োজনে তাদেরকে কাজে লাগায় তাঁরাও তেমনি ভক্তের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেন। যেমন, কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যে দেখিয়েছেন, দেবী চণ্ডী যেমন কালকেতুর বাড়িতে নিজে কাঁখে করে ধনঘড়া বয়ে দিয়ে এসেছেন, তেমনি দেবীও কালকেতুকে দিয়ে বন কাটিয়ে গুজরাট নগরে প্রজাপত্তন করে তাদেরকে দিয়ে পূজা করিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের এই নির্দিষ্ট ছক বেশিরভাগ কবিই মেনে নিয়েছেন। এই ধারায় ব্যতিক্রম শুধু ভারতচন্দ্র। কেননা অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেখানে বিলাসব্যসন, ব্যভিচার ও কৃত্রিমতা সমাজের সর্বত্র প্রসারিত সেখানে ভক্তির কাব্য হিসেবে মঙ্গলকাব্যের আবেদন জনমানসে হারাল। তাই ভারতচন্দ্র সেই যুগের সংবেদনকে উপলব্ধি করে মঙ্গলকাব্যের ধারায় অভিনবত্ব আনবার জন্য এই মৃতপ্রায় ধারায় সঞ্জীবনী সম্পর্কে শেষবারের মতো সজীব করে তুলেছিলেন।
(দুই) শিল্পীর প্রতিভা-ই পারে সামান্যের উপর অসামান্যের আলো ফেলতে করতে পেরেছিলেন ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন শাখার কাব্যগুলির পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, সমস্ত কাব্যের গঠনভঙ্গি এবং বিষয়বস্তুর অবতারণার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নাই। যেমন, বন্দনা অংশ, আত্মপরিচয় বা গ্রন্থেৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। শাপভ্রষ্ট দেবশিশু স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আগমন করে দেবদেবীর মহিমা প্রচারান্তে আবার স্বর্গে প্রত্যাবর্তন—এই হল মঙ্গলকাব্যের মূল বিষয়বস্তু। এই বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের গতানুগতিকতায় বিচিত্র রসাবেদনের অভাবে মঙ্গলকাব্যের আবেদন মানুষের কাছে ক্রমশ কমে আসছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্র অতি সাধারণ বস্তুকে অসাধারণের মহিমায়। ভূষিত করলেন, বর্ণহীন একঘেয়েমির মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকের স্ফুরণ ঘটালেন।
(তিন) মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিকতার ভিড়ে ভারতচন্দ্র হারিয়ে গেলেন না। সেজন্য একদিকে যেমন মঙ্গলকাব্যের ধারানুযায়ী দেবদেবীর বন্দনা, স্বপ্নাদেশ, সৃষ্টিতত্ত্ব হরগৌরীর সংসার চিত্র, দেবীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে, অপরদিকে তেমন নগরজীবনের সার্থক চিত্রলিপি, মানবিকতাবাদ প্রভৃতি তাঁর কাব্যকে পরবর্তী যুগে ভাবধারায় সমৃদ্ধ করে তুলেছে।
(চার) অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবিরা যেখানে দেবীর নির্দেশে কাব্য রচনার সূত্রপ, বলে গ্রন্থেৎপত্তির কারণ অংশে জানিয়েছেন, সেখানে ভারতচন্দ্র তাঁর পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশে কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। যেমন কবিকঙ্কণের কাব্যে—
দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণ ছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখা যায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় কাব্য রচনার সূত্রপাত একথা জানিয়ে দেবী যাতে কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল করেন সেই কামনা করেছেন—
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের আপদ হর।
গায়কের কণ্ঠে কর বাস।
এই দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে মঙ্গলকাব্যের ধারায় স্বতন্ত্র। কারণ, দেবতার মহিমা অপেক্ষা অন্নদাতা পৃষ্ঠপোষকের মহিমাকে বড় করে দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, রাজার মঙ্গল, রাজ্যের মঙ্গলও তিনি চেয়েছেন অন্নপূর্ণার কাছে—‘অন্নপূর্ণা বন্দনা’ অংশে।
(পাঁচ) ভারতচন্দ্রের দেবী অন্নদা মঙ্গলকাব্যের রমনা ও প্রতিহিংসাপরায়ণা দেবী নন, ইনি শান্ত-শ্ৰী সমন্বিত স্নেহময়ী মাতৃমূর্তির প্রতীক। যদিও দেবীর এই রূপ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরুত্থান ও বৈষ্ণব প্রভাবের কারণে, তবুও এই দেবী নিখিল জনের অন্নদাত্রী রূপে আবির্ভূত, ঈশ্বরী পাটনীর মুখ দিয়ে সন্তান দুধে ভাতে থাকার বর চেয়ে নিয়েছেন অন্নদার কাছে। এমনকি স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে দেবী বলেছেন—
আরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী।
তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী।।
কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে।
মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোষহ আমারে।।
(ছয়) কাব্যের ভণিতা প্রয়োগেও নতুনত্ব লক্ষ করা যায়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে যেখানে দেবদেবীর প্রসাদে ভণিতা ব্যবহার করা হত, ভারতচন্দ্র সেখানে শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন পৃষ্ঠপোষক অন্নদাতা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি। তাই ভণিতায় কৃষ্ণচন্দ্রের নাম ও গুণাগুণের ব্যবহার দেখা যায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে। যেমন, বর্গীর উৎপাতে বাংলা বিপর্যস্ত; কৃষ্ণচন্দ্র ধার্মিক রাজা। তবুও—
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্মিক লোক ঠেকে গেল দায়।।
নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শান্তমতি।।
এ ধরনের কৃষ্ণচন্দ্রও অদৃষ্টের দোষে মুর্শিদাবাদের নবাবের কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। ধার্মিক কৃষ্ণচন্দ্রের এই বিপদে দেবী অন্নপূর্ণা বা অন্নদার টনক নড়ল—
অন্নপূর্ণা ভগবতী মূরতি ধরিয়া।
স্বপনে কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া।।
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়।।
আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ।
কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস।।
স্বপ্নে দেবী আরও বললেন—
সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়।।
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও।।
তখন, সেই আজ্ঞা মত কবি রায় গুণাকর।
অন্নদামঙ্গল কহে নবরসতর।।
মঙ্গলকাব্যের স্বপ্নাদেশের ঘটনা অন্নদামঙ্গল কাব্যে থাকলেও অন্নদামঙ্গলে সেই আজ্ঞা দেবীর নয়, তা কৃষ্ণচন্দ্রের।
(সাত) কাব্যের অন্তর্নিহিত দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, কাহিনির কাঠামোর মধ্যে অভিনবত্ব। যেমন, দেবখণ্ড অংশে মূল কাঠামো বজায় রেখে ভারতচন্দ্র পৌরাণিক ও লৌকিক শিবকাহিনির বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু এই বর্ণনায় সাধারণ লক্ষণকে অতিক্রম করে তিনি শিব ও অন্নপূর্ণার মানবিক রূপ চিত্রিত করেছেন। তাই দেখি অন্নপূর্ণার রূপ বর্ণনা ও বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যার রূপবর্ণনায় পার্থক্য খুব কম। তাঁর কাব্যের সর্বত্র নাগরিক জীবনের প্রভাব পড়েছে। প্রাক-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তিনিই প্রথম এবং একমাত্র কবি, যাঁর কাব্যে নগর জীবনের চিত্র স্থানলাভ করেছে। হরগৌরীর সংসারের দুঃখময় চিত্র, বৃদ্ধ মহাদেবের সঙ্গে কুমারী গৌরীর পরিণয়, হরিহহাড়ের পত্নীদের মধ্যে সতীনসুলভ বিবাদ প্রভৃতি চিত্রকে ঐ যুগের সমাজচিত্রের প্রতিফলন হিসাবে অঙ্কিত করে তিনি নূতনত্বের সৃষ্টি করেছেন।
(আট) হাস্যরস সৃষ্টিতে এবং রঙ্গব্যঙ্গের প্রয়োগেও কবি ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে এনেছেন নতুনত্ব। তাঁর কাব্যে রঙ্গ আছে ঠিকই কিন্তু তার চেয়ে বেশি আছে ব্যঙ্গ। এই ব্যঙ্গ প্রচলিত সমাজ ধর্মের প্রতি। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—“হাসি জিনিষটাই অশিষ্ট, তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত। সাহিত্যের হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি। প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রোক্তি। ….ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের। প্রধান রস কিন্তু আদি রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়—মস্তিষ্ক, জীবন নয়—মন।”
ভারতচন্দ্র প্রচলিত সমাজবিধিকে ব্যঙ্গ করেছেন বিদ্যাসুন্দরের কাব্যে। ধর্মবিষয়ে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস ভারতচন্দ্রকে ব্যঙ্গ করতে প্রেরণা জুগিয়েছে। সামাজিক জীবনের বৈপরীত্যকেও রূপ দিয়েছেন ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে। তাই একদিকে রয়েছে গঙ্গা ও ব্যাসের কোন্দল, ব্যাসের মনোবিকার, শিবের ভাড়ামি, কামাচারের প্রতি কালিকার সস্নেহ প্রশ্রয় অন্যদিকে অন্নদার কৃপাময়ী মূর্তি, তীর্থ মঙ্গলকথন, কবির গঙ্গাভক্তি ও গানগুলির বিগলিত ভক্তিরস। যেমন, বিদ্যার গর্ভ সংবাদে রাজার কাছে ক্রুদ্ধ রানির ব্যঙ্গ—
যৌবনে কামের জ্বালা কত বা বহিবে বালা।
কথায় রাখিব কত ঠেলে।
কিম্বা, নারীগণের পতিনিন্দা অংশে ব্যঙ্গ—
আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে।।
(নয়) কাব্যের রূপচর্চার মধ্যেও রয়েছে নতুনত্ব। তাই কাব্যের মধ্যে নিয়ে এসেছেন মণ্ডনকলার চাতুর্য ও ‘যাবনীমিশাল’ ভাষা। ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগেও ভারতচন্দ্রের বৈদগ্ধ্য মঙ্গলকাব্যের ধারায় নিয়ে এসেছে নতুনত্ব।
সুতরাং মধ্য যুগের মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক ধারায় ভারতচন্দ্র পুচ্ছগ্রাহিতার দোষে দুষ্ট নয়; বরং তার কাব্য বিষয়বস্তু, রূপকর্ম ও মণ্ডনকলার দিক থেকে হয়ে উঠেছে এক যথার্থ নূতন মঙ্গল।
যুগসন্ধির কবির বৈশিষ্ট্য
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব এক যুগসন্ধির লগ্নে। মোগল সাম্রাজ্য সূর্য অস্তায়মান, বিদেশি বণিকদের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমবিস্তারী। বর্গীর হাঙ্গামায় মানুষের জীবন তখন দুর্বিষহ। অত্যাচার, উৎপীড়ন, আশ্রয়হীনতা, নিরাপত্তার অভাব তখন মানুষের নিত্যসঙ্গী। তার উপর অন্ন সমস্যায় মানুষ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। অপরদিকে এই সময় এক নব্য অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে। এদের আচার ব্যবহারে প্রকট হয়ে উঠেছে মোঘল দরবারের অনুকরণে বিলাস ব্যভিচার, ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের উন্মাদনা। প্রেমের সূক্ষ্মতা এদের কাছে স্থূল ইন্দ্রিয়বিলাস মাত্র। প্রথা ও সংস্কার পালনের ক্ষেত্রে শিথিলতা, ধর্মবিশ্বাসে সংশয় ও জিজ্ঞাসার সূত্রপাত, জীবনের ফাঁক ও ফাঁকি, রিক্ততা ও হতাশাকে ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের চাকচিক্যে গোপন করবার প্রয়াস তখন শুরু হয়েছে। ঠিক এই পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব এবং তার অন্নদামঙ্গল তাই যুগসন্ধির কাব্য।
অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন—“ভারতচন্দ্র সম্পর্কে এই ‘সন্ধিযুগের কবি’ আখ্যাটি সবদিক হইতেই অতি সুপ্ৰযুক্ত বলিয়া মনে হয়। মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের মাঝখানে আবির্ভাব হইয়াছিল ভারতচন্দ্রের। তাঁহার কাব্য সৃষ্টিতে পরস্পর জড়িত হইয়া রহিয়াছে অস্তগামী এবং উদযওন্মুখ এই দুই যুগেরই প্রধান লক্ষণগুলি।”
দ্বিতীয়ত, চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রেও যুগস্বভাবকে ভারতচন্দ্র অতিক্রম করতে পারেননি। ভারতচন্দ্রের মহাদেব চরিত্রটি সমকালীন সাধারণ জনসমাজের যথার্থ প্রতিনিধি। দেবাদিদেব মহাদেবের মহিমা ভারতচন্দ্রের হাতে ধূলিধূসরিত হয়েছে। দেবাদিদেবের তপস্বী মূর্তিটিকে তিনি কামোন্মত্ত বৃদ্ধে রূপান্তরিত করেছেন। ভিখারী শিবকে নিয়েও তিনি অশোভন কৌতুকে মেতে উঠেছেন। গ্রাম্য বালকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের দলপতি হিসেবে স্বয়ং কবিও যেন দেবাদিদেবের চরিত্রে সংশয়, সন্দেহ ও উপহাসের ধূলি নিক্ষেপ করেছেন। ঈশ্বরী পাটনী নিজের সন্তানকে বিড়ম্বিত, অসহায়, অরক্ষিত জীবন থেকে মুক্তির জন্য, দেবীর কাছে কামনা করেছেন, আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে। আসলে এই কামনা সমকালীন জীবনের অসহায়তা থেকে জাত।
তৃতীয়ত, শুধুমাত্র কাহিনি বা চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রেই নয়, সমকালের বিভিন্ন প্রবণতাকে কবি ভারতচন্দ্র তার কাব্যে প্রকাশ করেছেন। মধ্যযুগীয় দৈবনির্ভরতা ও দৈববিশ্বাস তাঁর কাব্যে মুখ্য হয়ে ওঠেনি, যুগসন্ধির সংশয় সন্দেহই বরং প্রধান হয়ে উঠেছে।
চতুর্থত, মধ্যযুগের কবি হয়েও আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা এবং মানবকেন্দ্রিকতা ভারতচন্দ্রের কাব্যে বর্তমান। তাই দেবতার নির্দেশে তিনি কাব্য রচনা করেননি, তা করেছেন আশ্রয়দাতার নির্দেশে। ভারতচন্দ্রের দেবদেবীর চরিত্রও মানবসংস্করণ মাত্র। যেমন, বিষ্ণুর প্রতি ব্যাসদেবের উক্তি—
বিষ্ণুর দেখেছি গুণ নন্দী করেছিল খুন।
কিঞ্চিৎ যোগ্যতা তার নাই।।
পঞ্চমত, প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতচন্দ্রের যে কটাক্ষ, তা তাকে আধুনিক মনোভাবাপন্ন কবিরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ‘বসুন্ধরের মর্ত্যলোকে জন্ম’ অংশে ভারতচন্দ্র দেখিয়েছেন, যে সমাজে একজন নারীর লজ্জা রক্ষার জন্য পদ্মপত্রের প্রয়োজন হয়, সেই সমাজেই একদল ‘গেঁয়ো লোক’ ব্যঙ্গ করে নাম দেয় পদ্মিনী—
তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উঠে গায়।।
লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন।।
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থিচর্ম সার।
গেয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার।।
ষষ্ঠত, ভারতচন্দ্রের আঙ্গিক সচেতনতার মধ্যে রয়েছে আধুনিকতার লক্ষণ। শব্দচয়ন, যাবনীমিশাল ভাষার প্রয়োগ, সংস্কৃত ছন্দের সুচারু প্রয়োগ, অলংকারের আভিজাত্য প্রভৃতিতে তৎকালীন যুগরুচির পরিচয়কে যেমন ভারতচন্দ্র তুলে ধরেছেন, তেমনি আধুনিক সাহিত্যের মণ্ডনকলাকেও স্থান দিয়েছেন। কাহিনি পরিবেশনে, চরিত্র চিত্রণে, ভাষা প্রয়োগে, ছন্দনৈপুণ্যে, অলংকার সন্নিবেশে সর্বত্রই ভারতচন্দ্র গোষ্ঠীগত গতানুগতিকতা লঙ্ঘনের প্রয়াসী।
সপ্তমত, ভারতচন্দ্রের অন্নদা প্রতিহিংসাপরায়ণ চণ্ডিকা মূর্তি নয়, দেবী আবির্ভূত হয়েছেন অন্নদাত্রী রূপে। নিরন্নের বাড়িতে অন্ন তুলে দিতেই তো দেবীর আবির্ভাব হয়। এই যে আধুনিক মনন এটা ভারতচন্দ্রের নিজস্ব।
ভারতচন্দ্রের কবিত্ব
বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের শুরু ছাপাখানার প্রচলনে, গদ্যের ব্যবহারে এবং বলাবাহুল্য তা ইংরেজের সংস্পর্শজনিত যুক্তিবাদ, মানবিকতাবোধ ও অতীতের পুনর্মূল্যায়নজনিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কবি মুকুন্দের কাব্য যেহেতু মধ্য যুগের এবং তখনো বাংলা সাহিত্যে তথা সমাজজীবনে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেনি, তাই তাঁর কাব্যে আধুনিকতার সূত্র অনুসন্ধান করতে গেলে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। কেননা আধুনিক মন নিয়ে মধ্য যুগের কাব্যের আধুনিকতার অনুসন্ধান করলে সবসময় তা সফল নাও হতে পারে। তবে কবি মুকুন্দের কাব্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে আধুনিকতার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে তা অনেক সমালোচকই অকপটে স্বীকার করেন—
(এক) ভারতচন্দ্র দেবদেবীর প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাদেরকে হাস্যকর ভঁড়ে পরিণত করেছেন। তার দেবী বিশ্বাস শিথিল হয়ে গিয়েছিল এবং এই রন্ধ্রপথ দিয়ে তিনি আধুনিক কাব্যের সূচনা করে গেছেন—এরূপ কথা অনেকেই বলেছেন। তবে এটা আশা করি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, মধ্যযুগীয় সাহিত্যের নরলীলার প্রথম সচেতন কবি তিনি। অন্নদামঙ্গলে দেবদেবীর চরিত্র একেবারে মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই এর কাব্যে দেবদেবীর মহিমা অপেক্ষা মানববাচিত ত্রুটি-বিচ্যুতি অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।
(দুই) ভারতচন্দ্র ছন্দের নানামুখিন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন কায়দা কসরতের সাহায্যে। তিনি একঘেয়েমিপুৰ্ণ পুরাতন ছদকে বাদ দিয়ে ভাব প্রকাশের উপযোগী ছন্দ ও ভাষা ব্যবহার করেছেন। নানামুখী সংস্কৃত ছন্দের (তূনক, ভূজঙ্গ প্রয়াত) সাহায্যে তিনি তীক্ষ কণ্ঠস্বরকে প্রকাশ করেছেন। যেমন, শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দে ভারতচন্দ্র লিখেছেন—
ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজে নাগারা।
বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোতারা।।
ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো ভাষা আছে ঠিকই কিন্তু প্রবাদের এত নিপুণ প্রয়োগ ও তীক্ষ্ণাগ্ৰ বচনের ব্যবহার আধুনিক মননের উপওগী। এটা এসেছে বুদ্ধির ধার বা ঔজ্জ্বল্যের জন্য। লোকপ্রজ্ঞা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক এই প্রবাদগুলি হল—‘হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়’, ‘মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন’, যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে’, ‘সে কহে বিস্তার মিছা যে কহে বিস্তর’। ভাষা প্রয়োগে ভারতচন্দ্র পুরাতন রীতি গ্রহণ করলেও তার মধ্যে তিনি কাঁপন ধরিয়েছেন। ফরাসী মিশ্র ভাষার বহুল প্রয়োগ তিনি করেছেন—কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে। গতানুগতিকতার ক্লান্তিকর একঘেয়েমিতে মানুষ যখন তিক্ত বিরক্ত ভারতচন্দ্র তখন অন্নদামঙ্গলে অনুকরণের পথ ছেড়ে মন দিলেন সরস ভাষার দিকে।
(তিন) অন্নদামঙ্গল মঙ্গলকাব্য হলেও কাব্যের গুরুত্বের আপেক্ষিকতার ক্ষেত্রে ভেদ রয়েছে। বিদ্যাসুন্দরে দেবীকে বিপদে রক্ষা করতে বলা হয়েছে। গুরুত্বের দিক হতে মানসিংহও কম নয়। কারণ এটি প্রথম অর্ধ-ঐতিহাসিক কাব্য। পুরাতন মঙ্গলকাব্যের আদল থাকলেও আপেক্ষিকতার তারতম্যে ভেদ এসে গেছে। যখন মঙ্গলকাব্যকে অনড় অচল বলে মনে হচ্ছিল তখন তাকে ভারতচন্দ্র সচল ও গতিময় করলেন। অন্নদামঙ্গলে দেবী অন্নদা অন্নদাত্রী। তিনি তাঁর ভক্ত সন্তানকে দুধে-ভাতে থাকার বর দেন।
(চার) মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তুকে চারটি বিভাগে ভাগ করা যায়—বন্দনা অংশ, গ্রন্থেৎপত্তির কারণ বা আত্মপরিচয় অংশ, দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। বন্দনা অংশে বিভিন্ন দেবতার বন্দনা, দ্বিতীয় বিভাগে স্বপ্নে দৈবাদেশের কথা। অবশ্য কবি ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কাব্য রচনা করেছেন—দেবখণ্ড পৌরাণিক ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত, নরখণ্ডে দেবশাপগ্রস্ত স্বর্গবাসী দম্পতির মর্ত্যলোকে আগমন ঘটে ও নানা প্রকার দুঃখ দুর্দশার মধ্যে জীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র গ্রন্থেৎপত্তির কারণ অংশে দেবতার নির্দেশে নয়, অন্নদাতার নির্দেশে কাব্য রচনা করেছেন বলে জানিয়েছেন। ভণিতা প্রয়োগেও নতুনত্ব আছে।
(পাঁচ) ভারতচন্দ্র জীবনবাদী। এই অর্থে তিনি আদর্শবাদীও। কারণ পরিপূর্ণ জীবনকে তিনি পেতে চান; যে জীবনের মধ্যে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সবই আছে। কাম অর্থাৎ ভোগ প্রসঙ্গ। ভারতচন্দ্র আদি রসের কবি নন, সুস্থ জীবনের পক্ষে তা প্রয়োজনীয় খাদ্য। নারী সংসারের বন্ধনসূত্র, আনন্দের উৎস ভাণ্ডারের ঐশ্বর্যরত্ন। এ যুগের ‘যাব না বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী’, আদর্শের দিক হতে ভারতচন্দ্রের থেকে বহুদূরে অবস্থিত হলেও আমাদের কবি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সামনে নারীমহিমায় সীমাবদ্ধ হলেও একটা বরণীয় আদর্শ স্থাপন করতে পেরেছিলেন। যেমন—
পুরুষেরা দেখে যদি নারী মরে যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়।।
নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও যুক্তিবাদের পরিচয় পাই বসুন্ধর-পত্নীর স্বাভাবিক ভোগ জীবনের পক্ষে অখণ্ডনীয় দাবিতে। ক্রন্দনরতা এই নারী যখন অন্নদার কাছে অভিযোগ করতে শুরু করল তখন কিন্তু কাঁদুনির লেশমাত্র ছিল না—অথচ তখন তার বিরহিনীর জীবন। প্রশ্ন করলেন শিব যদি কুচনীর বাড়ি যান তবে তাতে অন্নদার মনের অবস্থা কেমন হবে। এমনকি, মূলে টান দিয়ে বলেছে—
ঠাকুরানী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি।
তবে কেন স্ত্রী-পুরুষে কৈলা রতি সৃষ্টি।।
এই নারী স্বাতন্ত্র্যময়ী উক্তি মঙ্গলকাব্যের অন্য কোথাও পাই না, গোটা বিদ্যাসুন্দর কাব্য ভোগজীবনের উজ্জ্বল রসকাব্য। বিদ্যার গর্ভসংবাদ শ্রবণে বিচলিত ক্রুদ্ধ রানি অন্য গঞ্জনার মধ্যে এ কথাটিও না বলে পারেনি স্বামীকে—‘যৌবনে কামের জ্বালা কত বা বহিবে বালা/কথায় রাখিব কত ঠেলে’। পুরুষ-জাতির পক্ষে মারাত্মক অধ্যায় ‘নারীগণের পতিনিন্দা’—অশ্লীলতার জন্য মারাত্মক নয়, মারাত্মক সত্য ভাষণের জন্য। কবিপত্নীর উক্তি—
শাঁখা সোনা রাঙ্গা শাড়ী না পরিনু কভু।
কেবল বাক্যের গুণে বিহারের প্রভু।।
(ছয়) ধর্মবিষয়ক ধারণায় ভারতচন্দ্রের স্বাতন্ত্র ছিল কিনা—এই ব্যাপারে তার নামে অভিযোগ ওঠে যে তিনি মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কামকাব্য বিদ্যাসুন্দরকে অতিস্ফীত করে প্রবেশ করিয়েছেন। ফলে এতে ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। এর উপর কবি গঙ্গা ও ব্যাস প্রসঙ্গে শোভন আচরণ করেননি। আবার ভক্তিগত ভাবে নিজে বৈষ্ণব হয়েও বৈষ্ণব ভণ্ডামিকে নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু দেবতাকে নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ করেননি। সাম্প্রদায়িকতা মানুষের বুদ্ধিকে কী পরিমাণে মলিন করে দেয় তা দেখানোর জন্য ব্যাসদেবকে গ্রহণ করেছেন। শিবের চরিত্র প্রসঙ্গে বলা যায় শিব চরিত্রকে নিয়ে মঙ্গলকাব্যেও কম ব্যঙ্গ করা হয়নি। তাই ধর্মের ব্যাপারেও তার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। বুদ্ধির মানুষ ও কাব্যিক অনুভূতির মানুষ ভারতচন্দ্র তাই ছিলেন ধর্মসমন্বয়পন্থী।
(সাত) ভারতচন্দ্রের মানবজীবন সম্বন্ধীয় অর্থনৈতিক চিন্তা—এটা কেবল দারিদ্র্য চিন্তা নয়, সমাজজীবনে কতখানি ক্ষতি করেছে তারই চিত্র। দ্বারীর উক্তিতে পরনির্ভরময় যন্ত্রণার ও লাঞ্ছনার মধ্যে বেঁচে থাকার পরিচয় পাই—
ঠকভরা দরবার ছলে লয়ে ঘরদ্বার
ক্ষুরধার ছুঁতে কাটে মাছি।
চাকুরীর মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি ভাই
বিষকৃমি সম হয়ে আছি।।
বিষের মধ্যে যেমন কৃমি বেঁচে থাকে তেমনি অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে দ্বারা বেঁচে আছে। সমাজের অর্থনৈতিক দিক থেকে নির্মম সত্য উচ্চারিত হয়েছে—‘বন্ধু নাই কড়ি বই’ উক্তিতে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে চণ্ডীদাসে, মুকুন্দরামে, রামপ্রসাদে সরল দুঃখকে পাই। ভারতচন্দ্র দুঃখের ছবি যখন আঁকছেন তখন তার উপর গোপন বেদনা ও দুঃখের প্রলেপ আরোপ করেছেন। পদ্মিনীর মারফতে কবি সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছেন। এই অংশে হৃদয়হীন গ্রাম্যলোকের রসিকতার প্রসঙ্গ কাহিনিতে অভিনব। যেমন—
লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন।।
অন্ন বিনা কলেবর অস্থিচর্মসার।।
গেঁয়ো লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার।।
(আট) কাব্যের মধ্যে Contradiction আধুনিকতার পরিচায়ক। হরগৌরীর বাদ-প্রতিবাদে—
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাধ করে একদিন পেট ভরে খাই।।
এ যেমন সমাজের একদিকের ছবি, তেমনি আবার উল্টো দিকের পরিচয় পাই—‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে’ ঈশ্বরী পাটনীর উক্তিতে। শিবের জীবনে ট্রাজেডি হচ্ছে তিনি লক্ষ্মীর কাছেও এক মুষ্টি অন্নভিক্ষা পেলেন না—‘হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়’। এর বৈপরীত্য দেখানো হয়েছে— “লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া’। এইখানেই কবির আধুনিকতা। ক্ষুন্নিবৃত্তি মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন—যার উপর মানব জীবন নির্ভর করছে, কিন্তু আজকের ক্ষুধা তাকে বঞ্চিত করেছে। বুদ্ধদেবের বোধিসত্ব লাভ হয়েছিল সুজাতার দেওয়া পায়েসে। ক্ষুন্নিবৃত্তি দূর করার পর ভিক্ষাপ্রার্থী শিবের চিত্র— “চেতরে চেতরে চেত ডাকে চিদানন্দ/চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ।।/যে জন চেতনামুখী সেই সদাসুখী।/যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুঃখী।” যিনি স্বয়ং সম্বিত চিদানন্দ স্বরূপ, শিবোহম্—আজকের তিনি নিজের হৃদয়ের চৈতন্যকে জাগাতে বলেছেন। এখানেই কবি ভারতচন্দ্রের আধুনিকতা।
(নয়) “সুন্দরের স্বদেশে গমন প্রার্থনা গরীয়সী”। স্বদেশে প্রেমের আবাস রয়েছে—এটাও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্জাত। কবির রহস্য চেতনাকে সঙ্গীতগুলি পরিস্ফুট করেছে। গ্রামীণ জীবনের প্রাণস্পন্দন—“আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো/বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈলা দিগম্বর লো। ….ভারত কহে পাগল নহে, ঐ ভুবনেশ্বর লো।” ক্ষোভকে কৌতুকে সঞ্চারিত করেছেন এই ছড়া জাতীয় ছন্দে। এতে বর্ণনার দুঃখ আছে, সুরে আছে দুঃখ জয় করার আনন্দ। বিদ্যাসুন্দরের শেষে রহস্যময় প্রেমের ছবি পাই (প্রাণ কেমন করে না দেখে তাহারে …’ ইত্যাদি অংশটি), অসাধারণ আধুনিক কবিতা এটি। বাসনার্ত প্রাণের উষ্ণনিঃশ্বাসের স্পর্শ এতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যের ‘চুপে চুপে এসো যেও” …ইত্যাদি অংশের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। ভারাতুর অহঙ্কারও ধ্বনিত হয়েছে উপরের অংশে—সুন্দরকে তার ভাল লেগেছে, তাই সকল নারীরও ভাল লাগবে।
সুতরাং ভারতচন্দ্র প্রাচীন ঐতিহ্যকে নূতন যুগচিন্তার সঙ্গে গ্রথিত করে বাংলা। সাহিত্যে নূর গতিপথের দিশা দেখিয়েছেন। তিনি নুন যুগের যথার্থ বাণীবহ না হতে পারেন কিন্তু যুগসন্ধির কবিরূপে প্রাচীন ও আধুনিক রীতির সমীকরণে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃত্রিম মণ্ডনকলায় ও গীতিসুরের প্রবহমানতায় এর দক্ষতার পরিচয়ও পাওয়া যায়।
ভবানন্দের দুজন অনুচর দাসুবাসুর চরিত্রও বেশ উজ্জ্বল। দাসু-বাসুর চরিত্র দুটি কৌতুকরস সৃষ্টির কারণে উপস্থাপিত হয়েছে। এ ধরনের চরিত্রের পরিচয় পাই কবিকঙ্কণের ধনপতি সদাগরের কাহিনিতে বাঙ্গাল মাঝিদের মধ্যে। সেখানেও শ্ৰীমন্তের নৌকা আটকে গেলে ঘরে ফিরতে পারবে না ভেবে দুঃখ প্রকাশ করেছে। ভারতচন্দ্রও দাসু-বাসুর মধ্যে সেই বিষয়টিকে চিত্রিত করেছেন নিপুণভাবে। ভবানন্দ বন্দী হলে এই দুই অনুচরের জবানিতে চরিত্র দুটি বেশ স্পষ্ট রেখায় চিত্রিত হয়েছে। যেমন—
যুবতী রমণী আছে না রয়ে তাহার কাছে
কেন আনু বামনের সাথে।
কিম্বা,
কুড়ি টাকা পণ দিয়া নতুন করিনু বিয়া
একদিননা ঘর না করিনু।
শুধু কি তাই, ভবানন্দের দিল্লি আসা যে উচিত হয়নি, সে বিষয়েও মন্তব্য করতে ভোলেনি দাসু-বাসু—
হেদে বামনের ছেলে আগু পাছু নাহি চলে
দিল্লী আইল রাজাই করিতে।
দুধে ভাতে ভাল ছিল হেন বুদ্ধি কেটা দিল।
পাতশার দেয়ানে আসিতে।।
দাসুবাসু নিজের প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে গিয়েছিল, তবে ভবানন্দের মুক্তির সংবাদ পেয়ে তারা ফিরে এল—
দাসু বাসু আদি যত পলাইয়াছিল।
সংবাদ পাইয়া সবে আসিয়া মিলিল।।
সুতরাং ভারতচন্দ্র তিনটি খণ্ডে টাইপ চরিত্র অঙ্কন করেননি, চরিত্রগুলি প্রায় সকলেই রক্তমাংসের সজীব চরিত্র। মঙ্গলকাব্যের ধারায় চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে। কবিকঙ্কণের পরই রায়গুণাকরের স্থান—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।


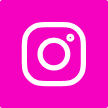










Leave a Reply