রূপক-সাংকেতিক নাটকের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ আলোচনা কর।
রূপক ও সাংকেতিক নাটক
রূপক ও সাংকেতিক নাটককে এক সঙ্গে আলোচনা করার কোনো যৌক্তিকতা নেই, তাদের একই বিভাগে স্থান দেওয়া আরো অর্থহীন। অথচ সাধারণভাবে যে আমরা দুটি শ্রেণীকে একই ধরনের দুটি বিভাগ বলে মনে করি তাই শুধু নয়, সাহিত্য-প্রকরণের কোনো কোনো গ্রন্থে তাদের পৃথক পর্যন্ত না করে আলোচনায় বার বার ‘রূপক-সাংকেতিক’ নাটক হিসাবে উল্লেখ দেখি। এই বিপর্যয় সাহিত্যালোচনাতেও সংক্রামিত হয়েছে, সেইটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের নাটক আলোচনাতেও একই নাটককে কেউ বলেছেন রূপক, কেউ সাংকেতিক, কেউ তত্ত্ব নাটক। নাটকে তত্ত্ব থাকতেই পারে এবং যখন সেই উদ্দেশ্যমূলক নাট্যরসের মতোই প্রধান হয়ে ওঠে তখন তাকে তত্ত্বনাটক বলা যায় না, এমন নয়। কিন্তু একই নাটককে রূপক ও সাঙ্কেতিক, অথবা রূপক-সাঙ্কেতিক বলা কিছুতেই সমীচীন হতে পারে না, অন্তত বললে তা রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক সম্বন্ধে আমাদের ধারণার অস্পষ্টতাকে প্রমাণ করে।
সাংকেতিক নাটক আসলে একটি আধুনিক নাট্যপ্রকরণ। আগেও হয়তো এর বীজ ছিল, কিন্তু সাঙ্কেতিক বা প্রতীকী আন্দোলনের পূর্বে এ জাতীয় নাট্যরচনা সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে রূপকের ব্যবহার দীর্ঘকালের বিভিন্ন উদ্দেশ্যেই অবশ্য, এবং নাটকে তা ব্যবহারের জন্য আধুনিকমনস্কতার কোনো প্রয়োজন নাও থাকতে পারে। আমাদের পঞ্চতন্ত্রের গল্প থেকে শুরু করে আধুনিককালে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘লোকরহস্যের’ আখ্যানগুলি, এমনকি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ‘তোতাকাহিনী’ও রূপকধর্মী। ইংরেজি সাহিত্যে বুনিয়নের ‘পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস’, স্পেনসারের ‘ফেয়ারি কুইন’, জোনাথন সুইফটের ‘গালিভার্স ট্রাভেলস্’ ইত্যাদির সমস্ত রচনাকেই রূপকধর্মী বলা চলতে পারে। রূপকধর্মী রচনা যে কতো প্রাচীন তা বোঝাবার জন্য সমালোচক আব্রাম ঈশপের গল্প এবং চসারের দু-একটি রচনার নামও করেছেন। সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে রূপক ও সাঙ্কেতিক রচনার প্রভেদটি ভালো করে জেনে রাখা দরকার, তাহলে কোনও নাটকের সঠিক শ্রেণি নির্ণয়ে আমাদের অসুবিধা হবে না।
রূপক ও সাংকেতিক নাটকের পার্থক্য
প্রথমত, রূপকের কাজ বক্তব্য বিষয়কে গোপন করে তার একটা প্রতিরূপ খাড়া করা। অর্থাৎ রূপক কাহিনীতে দুটি কাহিনী চলে সমান্তরালভাবে—একটি আপাতকাহিনী, যার অন্তরালে আত্মগোপন করে লেখক দ্বিতীয় কাহিনীটির ওপর বেশি জোর দিতে চান এবং সেটিকে পরিস্ফুট করার জন্যই প্রথম কাহিনীটির পরিকল্পনা করেন। আসলে প্রচ্ছন্ন কাহিনীটিই মূল কাহিনী যেটি বিভিন্ন কারণে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশ করার অসুবিধা তার থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল’ কাহিনীটির উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে প্রাথমিক ভাবে আমরা পেয়েছি একটি লোভী বাঘের গল্প যে তার নিষ্ঠুর হত্যালীলার স্বপক্ষে বেশ কিছু কথা বলে যায়। আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি এর সমান্তর ভাবে লেখক বলতে চান ইংরেজের আগ্রাসী মনোভাব, উদ্যত লোভ এবং পরিকল্পিত শাষণকার্যের কথা। সে কথা বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারেন। এই কারণেই অ্যাব্রামস রূপক বা Allegory-র সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—‘‘An allegory is a narrative in which the agents and action, and sometimes the setting as well, are contrived not only to make sense in themselves, but also to signify a second, correlated order of persons, things concepts, or events.’’
সংকেত বা প্রতীক বলতে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রার সৃষ্টি বুঝি। এই ধরনের সৃষ্টি সময় আর্থার সিমন্সের অভিমত— “It is an attempt to spiritualise literature, to evad the old bondage of exteriority … in this endeavour to disengage the ultimate essence, the soul of whatever exists can be realised by the consciouness.”
এখানেও অবশ্য আপাতকাহিনীটির অন্তরালে অন্য কোনো কথা থাকে, কিন্তু কোনো সমান্তরাল কাহিনী থাকে না—থাকে একটা অনুভূতি বা অব্যক্ত সংবেদন, যাকে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব বলেই প্রতীকধর্মী একটি কাহিনী লেখককে বেছে নিতে হয়। সাংকেতিক নাটকের কাহিনি স্বাভাবিক কারণেই রূপকের মতো নিটোল হয় না এবং প্রকৃত কাহিনী গোপন রাখার দায়ও তার থাকে না—রহস্যময় ভাবে, ইঙ্গিতে ও প্রতীকের সাহায্যে তা অব্যক্ত সেই অনুভূতির প্রতি আকর্ষণ করে যে অনির্বচনীয়কে বচনীয় করবার অসম্ভব প্রয়াস থাকে সাঙ্কেতিক কাহিনীর।
দ্বিতীয়ত, রূপক কাহিনী স্পষ্ট বোঝা যায়—যেমন বোঝা যায় তার আপাতকাহিনী তেমনি তার নেপথ্য কাহিনী। কিন্তু সাঙ্কেতিক নাটকে বা অন্যান্য আখ্যানধর্মী সাহিত্যে এই স্পষ্টতা মোটেই থাকে না। তার নেপথ্যে যে অনুভূতি লেখক সঞ্চারিত করতে চান তা বোঝা পাঠকের পক্ষে আরো শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে অবশ্য নাট্যকারের কিছু করবার থাকে না, কারণ যে অনুভূতি অত্যন্ত গভীর ও প্রায় অনির্বচনীয়, তাই তিনি প্রকাশ করতে চান। এই অনুভূতি প্রকাশের জন্য তিনি যেমন প্রতীকধর্মী কাহিনী নির্বাচন করেন, তেমনি নীলকণ্ঠ পাখির পালক, লোহার জাল, রক্তকরবী ফুল প্রভৃতি কিছু প্রতীক গ্রহণ করে থাকেন। এই সব প্রতীক এবং ব্যঞ্জনাময় ভাষার সাহায্যে বক্তব্য পরিবেষণের চেষ্টা করা ছাড়া তার কোনো উপায় থাকে না।
তৃতীয়ত, রূপকের আবেদন সম্পূর্ণত বুদ্ধির কাছে, সংকেতের আবেদন বোধের কাছে। এই কারণেই বুদ্ধিমান পাঠক রূপকের দ্বিতীয় কাহিনীর অর্থ খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারেন, কিন্তু যথার্থ অনুভূতিশীল মানুষ ছাড়া সংকেতের রহস্য উদ্ধার করা অথবা লেখকের ব্যঞ্জনার কাছাকাছি পৌঁছোন পাঠকের পক্ষে সম্ভব হয় না।
চতুর্থত, সমালোচকের পক্ষে রূপক নাটকের অর্থ বিশ্লেষণ করা বা তার ব্যাখ্যা করা মোটামুটি ভাবে সহজ, কারণ বুদ্ধিপ্রধান নাটকের অর্থ মননশীল সমালোচকের পক্ষে বিশ্লেষণ করতে না পারার কোনও কারণ নেই। সাংকেতিক নাটক অনুভূতিগ্রাহ্য হওয়ার জন্য একদিকে যেমন সমালোচক নিজেই তার রহস্যে বিভ্রান্ত হয়ে যান, অন্যদিকে আর একটা সমস্যাও আছে—একটি গভীর অনুভূতির বিষয়কে যতোটা ভালোভাবে বলা সম্ভব, ঠিক সেইভাবেই উপস্থাপিত করা হয় একটি নাটকে। তাকে এর চেয়ে ভালোভাবে বোঝানো আর সম্ভব নয় অন্য যে-কোনও ভাবে বোঝাতে গেলে সেই সুন্দর সৃষ্টির তুলনায় তা অসুন্দর হতে থাকে। সেই কারণে রূপকের ব্যাখ্যা আমাদের তৃপ্ত করে, সাংকেতিক নাটকের ব্যাখ্যা আমাদের সেভাবে সন্তোষ দান করতে পারে না। .
পঞ্চমত, রূপক নাটক উদ্দেশ্যমূলক এবং সেই কারণেই রূপকাৰ্থ স্পষ্ট হয়ে গেলেই, অর্থাৎ নাটকটি অর্থবোধকভাবে শেষ হলেই, দর্শক তৃপ্তি লাভ করেন। তিনি নাট্যকার যা বলতে চান তার অর্থ বুঝতে পারেন এবং তার অন্তরে আর কোনো প্রশ্ন বা অস্বস্তি থাকে না। কিন্তু সংকেতের ক্ষেত্রে তা হয় না। যে দর্শক গভীর অনুভূতির সাহায্যে নাটকের মূল ব্যঞ্জনার কাছাকাছি উপনীত হতে পারেন তিনি নাট্যকারের গভীর অনুভবের সিংহদ্বারে পৌঁছে যান। এবার নাটকটি সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের অনুভূতি অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং যে গভীর অনুভূতির সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছেন তার তীব্রতা তাকে অভিভূত ও এক আনন্দিত অতৃপ্তি দান করে। রূপক ও সংকেতের পার্থক্য বিষয়ে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, এখানে সাংকেতিক কাব্য-আন্দোলনের প্রধান পুরুষ ইয়েটসের একটি বক্তব্য উদ্ধার করছি—“A symbol is indeed the possible expression of some invisible essence, a transparent lamp about a spiritual flame while allegory is one of the many possible representation of an embodied thing.’’
একটি সার্থক বাংলা রূপক নাটক
রবীন্দ্রনাথের নাটকে সঙ্কেত এবং সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনা কখনোই একেবারে অনুপস্থিত থাকে না, কিন্তু নাটকের শ্রেণী বিচার করার সময় মূল প্রবণতা এবং সঠিক প্রকৃতিই লক্ষ করা উচিত। সেদিক থেকে বিচার করলে, রথ, পথ, রশি প্রভৃতি অনেক সঙ্কেতের ব্যবহার থাকলেও মূলত রবীন্দ্রনাথের ‘কালের যাত্রা’ নাটককে রূপক নাটকের শ্রেণীতেই ফেলা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি, অন্তত রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকের যে পার্থক্যগুলি আমরা চিহ্নিত করেছি সেই সূত্রে বিচার করলে।
এমনিতেই ‘কালের যাত্রা’-র যা আয়তন তাকে নাটিকা বলাই ভালো। মোট তিনটি অংশে বিচ্ছিন্ন এই নাটকের মূল অংশ প্রথমে সন্নিবিষ্ট ‘রথের রশি’, দ্বিতীয় অংশ কবির দীক্ষা একটি দীর্ঘ কবিতামাত্র এবং ‘রথযাত্রা’ ‘রথের রশি’-র পুনরাবৃত্তি। ‘রথের রশি’ অংশের প্রথমেই দেখি রথযাত্রার মেলায় সম্মিলিত মেয়েদের দুশ্চিন্তা, কারণ রথের নেই দেখা। চাকার নেই শব্দ। তাদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেবার জন্য সন্ন্যাসী এসে বলেন—
সর্বনাশ এল।
বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী,
ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।
মেয়েরা আতঙ্কিত হয়, ব্যাপারটা বোঝে না, মনে করে তারা মেলা দেখতে এসেছে—অথচ পূজো আনেনি, তাই এই অঘটন। তারা ছোটে পূজো আনতে। এরপর নাগরিকরা আসে সেখানে, ঘটনাকে তারা অন্যভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করে, কিন্তু সন্ন্যাসী এসে তাদেরও ভয় দেখান। মেয়েরা এরপর ফিরে এসে তাদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্মাদি শুরু করে দেয়। ‘দড়িনারায়ণ’-কে প্রসন্ন করবার জন্য তাতে ঘি, দুধ, পঞ্চগব্য, গঙ্গাজল ঢালা শুরু হয়। নানা নারী নানা মানতও করে ফেলে। এতেও যখন রথের চাকা নড়ে না, সন্ন্যাসী এসে বলে যান—
কালের পথ হয়েছে দুর্গম।
কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত।
করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।
এই শুনে ‘রাস্তা-ঠাকুর’কে পূজো দিতেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে মেয়েরা।
এরপর আছে সৈনিকরা, তাদের কথায় জানা যায় ব্রাহ্মণের মন্ত্রে রথের চাকা ঘোরেনি। তারপর স্বয়ং রাজাও হাত লাগিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। নাগরিকদের আলোচনায় শোনা যায়, শূদ্রদের বাড় বেড়েছে বলেই এই অঘটন। এক নাগরিকের কাছে জানা যায় এ যুগে চলে কে স্বর্ণচক্র। তাই রাজা ডাক দিয়েছেন শেঠজিকে। সৈনিকরা বিশ্বাস করে না, তাদের হাতে যে রথ চলে না তা চলবে ধনপতির হাতে। ধনপতি আসার আগে আরো একটা খবর পাওয়া যায় ‘নর্মদা-তীরের বাবাজিকে আনা হয়েছিল/দড়িতে হাত লাগাবার জন্য।’ তার হাত লাগামাত্র রথের চাকা বসে যেতে লাগল মাটির নিচে। কিন্তু ধনপতিও এসে যখন ব্যর্থ হলেন মন্ত্রী তখন মেয়েদেরই ডাকলেন আবার, যদি তাদের ভক্তির জোরে রথ চলে। সে চেষ্টাও চলে, কিন্তু কোনও কাজ হয় না। তখন চরের মুখে শোনা যায় শূদ্রেরা দলে দলে ছুটে আসছে, রথ নাকি তারাই চালাবে। তারা এসে পড়ে, দলপতির সঙ্গে তর্ক বাধে পুরোহিতের, সৈনিকের, মন্ত্রীর। কেউ তাদের বাধা দিতে পারেন না যখন, তখন সবাই দ্বিধায় জর্জরিত—ওদের আটকানো হবে, না ওদের কাজে সাহায্য করা হবে। এই দ্বিধার মাঝখানেই ওরা হাত দেয় দড়িতে, এবং রথ চলে। কবি আসেন এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে, বললেন অন্যান্য শ্রেণীর মাথা অত্যন্ত উঁচু ছিল বলেই ঠাকুর এবার নিচুর দিকে ফিরেছেন। তবে এই নিচু শ্রেণী যদি কোনোদিন গর্বে অন্ধ হয়ে মনে করে তারাই চালাচ্ছে রথ, তবে আসবে আবার উল্টোরথের পালা।
এই রথযাত্রার মেলা এবং রথ না চলা উপলক্ষে রাজা, মন্ত্রী, ধনপতি ইত্যাদি নিয়ে প্রায় রূপকথার মতো যে আখ্যান নির্মাণ করা হয়েছে, স্পষ্ট বোঝা যায়, তার আড়ালে একটি সমান্তর কাহিনী চলেছে। এই নেপথ্য কাহিনীর মূল সূত্র পাওয়া যাবে কবির ৩১ ভাদ্র, ১৩৩৯ তারিখে লেখা শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠিতে। সেখানে তিনি লিখেছেন—“মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, … তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসত্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।’’
বেশ বোঝা যায়, সমাজ-প্রগতির মার্কসীয় দৃষ্টির কথাই এখানে দ্বিতীয় সমান্তরাল কাহিনী হিসাবে অগ্রসর হয়েছে। এই তত্ত্বদর্শনের মূল কথা হল, যে-কোনও সমাজ সভ্যতার প্রথম অবস্থায় নেতৃত্ব দেন ব্রাহ্মণ্যসমাজ। তাদের মন্ত্রতন্ত্র এবং বিধিনিষেধ স্বয়ং নৃপতিও মানতে বাধ্য হতেন। অবশ্য এরপর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রে এক ধরনের সামঞ্জস্য দেখা যায়, বা বলা যায় কোথাও কোথাও সামান্য বিরোধ সত্তেও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র রাজতন্ত্রের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু রাজশক্তির সামর্থ্য নির্ভর করে ধনিকশ্রেণীর ধনসঞ্চয়ের ওপর, এ বিষয়ে যখন ধনিকশ্রেণী সচেতন হয় তখন ফিউডাল আধিপত্য ঘুচে সমাজের প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়ায় বুর্জোয়া শ্রেণী বা ধনিক শ্ৰেণী। কালের রথ দাঁড়িয়ে থাকে না, সে যতোই অগ্রসর হয় ততোই শূদ্রসমাজ বা শ্ৰমিকসমাজ সংগঠিত হয়, তারা বুঝতে শেখে বুর্জোয়া শ্রেণীর মুনাফার মৌলিক উপাদান তাদের শ্রম। এই বোধে উদ্দীপ্ত হলে শ্রমজীবী শ্রেণীর জাগরণ ঘটে এবং সমাজের নেতৃত্ব যায় তাদের হাতে। সমাজ-বিবর্তনের এই সত্য আমাদের সমাজ বলে নয়, পৃথিবীর অনেক সমাজ সম্বন্ধেই সত্য এবং আমাদের সমাজও যে ঠিক এই পথেই বিবর্তিত হয়ে এসেছে, নাটকে বিভিন্ন শ্রেণীর সংলাপ স্মরণ করলেই তা বোঝা যাবে।
এবার রূপক-সাঙ্কেতিকের লক্ষণ মিলিয়ে বিচার করলেই আমরা দেখতে পাবো—
প্রথমত একটা মোটামুটি স্পষ্ট প্রতিরূপ এই আখ্যানের আছে, মানে এই রূপকথাসুলভ আপাতকাহিনীর।
দ্বিতীয়ত, আমাদের এই কাহিনী এবং নেপথ্যকাহিনীর ব্যাপারটা বুঝে নিতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না, যদিও দড়ি, রাস্তা, পথ, গর্ত প্রভৃতিকে প্রায় সঙ্কেতের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে, এই বায়বীয় নাটকে নারী চরিত্রগুলিই জীবন্ত এবং বাস্তব। তারা যে আচার-অনুষ্ঠানকেই ভক্তি বলে মনে করে, সংস্কারকেই দেবতাজ্ঞানে পুজো করে, এই ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ওই বস্তুগুলির ব্যবহার, প্রতীক হিসাবে ততোটা নয়।
তৃতীয়ত, এই নাটকের আবেদন যতোটা না হৃদয়ের কাছে, ততোটা বুদ্ধির কাছে, এ কথা রবীন্দ্রনাথের অতিবড়ো ভক্ত-সমালোচকও অস্বীকার করতে পারবেন না।।
চতুর্থত, রূপক নাটক বলেই ‘কালের যাত্রা’ অথবা আরো সঠিক অর্থে ‘রথের রশি’ নাটকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার পর দর্শক বা পাঠকের কাছে সরলতর ও সহজগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। সাঙ্কেতিক নাটকের ব্যাখ্যা নাটককে এতো প্রাঞ্জল করতে পারে না।
পঞ্চমত, নাটক সমাপ্ত করে যে তৃপ্তি আমরা পাই, তাও প্রমাণ করে এই নাটকের শ্রেণিরূপই, সাঙ্কেতিক নয়।
একটি সার্থক বাংলা সাংকেতিক নাটক
রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’কে আমরা বিশ্লেষণের জন্য গ্রহণ করতে পারি। রূপক, সাংকেতিক অথবা তত্ত্বনাটক—নাটকের কোন শ্রেণীতে এর স্থান হতে পারে, এ বিষয়ে সুধী পণ্ডিতদের মধ্যেই মতভেদ আছে। আমরা এই নাটককে সাংকেতিক নাটক হিসাবেই চিহ্নিত করতে চাই এবং কেন তা চাই তার কারণগুলি অবশ্যই উল্লেখ করবো কিন্তু তার আগে পুনর্বার স্মরণ করা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের নাটকে রূপক ও তত্ত্ব অনেক সময়ই এমন ভাবে জড়িয়ে থাকতে পারে যে তার সাংকেতিক নাটককেও আমরা পুরোপুরি রূপকবর্জিত বা তত্ত্বনিরপেক্ষ হয়তো বলতে পারি না। আসলে নাটকে কোন ব্যাপারটা প্রাধান্য পেয়েছে এবং রসপরিণতিতে তা ঠিক কী ধরনের আবেদন সৃষ্টি করেছে সেটাই প্রধান কথা।
‘রক্তকরবী’ নাটকের দৃশ্যপট একটিই—মাটির তলায় শ্রমিকরা সোনা খননের কাজে যেখানে নিযুক্ত আছে, সেই যক্ষপুরী। এর কালসীমা সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও নেই এবং সেই কারণেই এ নাটকে কালের মাত্রা যে এক অভিনব ব্যাপ্তি লাভ করেছে এ বিষয়ে কবিসমালোচক শ্রী শঙ্খ ঘোষের মনোজ্ঞ আলোচনা আমাদের অনেকেরই পড়া আছে। নাটকের কাহিনি বলতে সঠিক ভাবে কিছু নেই, অন্তত প্রথাগত ভাবে যাকে আমরা নাট্যকাহিনী বলে থাকি। যে কাহিনীটুকু আছে তাতেও রহস্যময়তা প্রচুর। যক্ষপুরীতে যারা কাজ করেছে তারা। যে এককালে মাটির ওপরে ফসল ফলাতো, অর্থাৎ তারা কৃষক, এ কথা বোঝা যায়। অবশ্য এখন নামটান হলে তারা অনেকেই পরিণত হয়েছে সংখ্যায়। সোনার মাদকতায় ভুলিয়ে, ধর্মের নেশা ধরিয়ে তাদের যন্ত্রের মতো কাজ করানো হয়; কিন্তু সামান্য কেউ কেউ এর মধ্যে ব্যতিক্রম—যেমন ৬৯ঙ সংখ্যাধারী বিশু পাগল। সে তার দুঃখসাধনার কথা ভুলতে পারে না। যক্ষপুরীতে ঢুকেছে প্রাণময়ী এক নারী, নন্দিনী। যক্ষপুরীর রাজা, যিনি জালের আড়ালে থেকে নিষ্প্রাণ দৃঢ়তায় যক্ষপুরীর সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনা করেন, তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করাই ঈশানী পাড়ার নন্দিনীর ব্রত। সে জানে এ কাজে সে সহায়তা পাবে রঞ্জনের, সে যে যক্ষপুরীতে ঢুকে পড়েছে—এই খবর তার জানা আছে। নাটকের একেবারে শেষে রাজা নিজেই জালের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে দেখা যায় জালের মধ্যে মৃত রঞ্জন পড়ে আছে। রাজা বুঝতে পারেন নিজের ভুল, বলেন—“আমি যৌবনকে মেরেছি—এতদিন ধরে আমি সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি।” তারপর আমরা দেখি নিজের বিরুদ্ধে নিজেই লড়াই করবার জন্য ধ্বজা ভেঙে ফেলে রাজা পথে বেরিয়ে পড়েছেন।
কাহিনীর এই সংক্ষিপ্ত আভাস থেকেই বুঝতে পারা যাবে, এখানে সমান্তরাল কাহিনীর প্রশ্ন দূরে থাক, ঠিকমতো বলতে গেলে আপাতগ্রাহ্য কোনও বাইরের কাহিনীই গড়ে ওঠেনি। নন্দিনী কেন যক্ষপুরীতে আসে, রঞ্জন তার সঠিকভাবে কে হয়, রাজার এই জাল ছিন্ন করা এবং তা থেকে তাকে উদ্ধার করার দায়িত্ব সে কেন নেয়, যক্ষপুরীর প্রায় প্রত্যেকটি শ্রমিককেই সে কেন চেনে, যক্ষপুরীর ভেতরে বসে সে বার বার ফসলকাটার গান কেন গায়, এ সব কিছুই আমাদের কাছে রহস্য হয়েই থাকে। এর কাহিনী আমাদের অনেক কিছুর দিকে ইঙ্গিতে ডাক দিয়ে যায় বটে, কিন্তু স্পষ্ট করে যেন কিছুই বলে না। এই সুস্পষ্ট আপাতকাহিনীর অভাব ও সমান্তর দ্বিতীয় কাহিনীর অভাব একদিকে যেমন রূপক নাটক হিসাবে একে অভিহিত করবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়, অন্যদিকে সাঙ্কেতিক নাটক হিসাবে এর দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করে—কারণ এমন এক রহস্যময়তা এই কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে যাতে লেখকের অনির্বচনীয় এক অনুভব এর মধ্য থেকে আভাসিত হয় অথচ সঠিকভাবে ধরা দেয় না। একেই যে সংকেতের প্রাণ বলা যায়, সিমেন্সের পূর্বোল্লিখিত মন্তব্য স্মরণ করলেই তা বোঝা যাবে।
দ্বিতীয়ত, রক্তকরবীর ব্যাখ্যা সঠিকভাবে করা যায় না, বেশি ব্যাখ্যা করতে গেলে এর সৌন্দর্যহানি ঘটবে মনে করেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গেলে অনর্থ ঘটবে। তিনি শুধু মনে রাখতে বলেছেন, এটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি। গল্পাংশ এখানে নিটোল হয়নি তা নিটোল করা সম্ভব নয় বলেই। কিন্তু রক্তকরবীর মঞ্জরী, জালের আবরণ, ধ্বজাপুজার ধ্বজা ইত্যাদি প্রতীক এখানে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যে যায় না, এই সত্যই ইঙ্গিত করে এটি সাঙ্কেতিক নাটক হতে পারে।
তৃতীয়ত, এ কথা মেনে উপায় নেই যে, ‘রক্তকরবী’ নাটকের যদি কোনও আবেদন থাকে তবে তা হৃদয়ের কাছে, বুদ্ধির কাছে নয়। বার বার পাঠ করলে বা একটি অত্যন্ত মনোযোগী পাঠে আমরা এর ব্যঞ্জনা বা গভীর অর্থের কিছুটা হয়তো অনুভব করতে পারি কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে এর কাছে পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব বলেই আমাদের মনে হয়।
চতুর্থত, ‘রক্তকরবী’ নাটক ব্যাখ্যা করার অনেক চেষ্টা সমালোচকগণ করেছেন। কেউ বলেছেন আমেরিকার ধনতন্ত্রের স্বরূপ দেখে ব্যথিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে যক্ষপুরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, কেউ বলেছেন এই নাটকে আমরা ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের এক কল্পিত চেহারা দেখতে পাই–এ ব্যাপারে আতঙ্কিত হয়েই কবি এ নাটক লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ভাবে এই নাটক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন—কখনো বলেছেন এটি কর্ষণজীবী সভ্যতার সঙ্গে আকর্যণজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্ব, কখনো বলেছেন এটি আসলে রামায়ণেরই আধুনিক রূপ, এই নাটকের রাজা এক দেহে রাম ও রাবণ। এই নাটককে মানবিক সংকট এবং মানবিক ভাবনার নাটক হিসাবেও কেউ কেউ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এই নাটকের পক্ষে একটি মানবিক ব্যাখ্যাই সংগত। কিন্তু বিভিন্ন সমালোচক যে বিভিন্ন ভাবে এর ব্যাখ্যা করেন, কেউ সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হন না এবং আমরা কোনো ব্যাখ্যাতেই যেন নাটকের নিহিতার্থ সম্পূর্ণ করে পাই না, রবীন্দ্রনাথ যে বারবার এই নাটকের ব্যাখ্যা করতে নিষেধ করেন, আমরা যত ব্যাখ্যা করি ততোই নাটকের প্রকাশিত রূপের চেয়ে তা অসুন্দর হয়ে পড়ে—এই যাবতীয় ঘটনাই প্রমাণ করে এই নাটকের প্রকৃতি সাংকেতিক, রূপক নয়।
পঞ্চমত, এই নাটক সমাপ্ত করার পর পরম তৃপ্তিতে আমরা সমাচ্ছন্ন হতে পারি না। রাজা কেমনভাবে নিজের বিরুদ্ধে লড়াই-এ যোগ দিতে চলে যান, সবাই শেষ পর্যন্ত নন্দিনীর জয়ধ্বনি দেয় কেন, নন্দিনীর কাজ সমাপ্ত করবার জন্য বিশু পাগল তার রক্তকরবীর কঙ্কন কেন হাতে তুলে নেয়—তার গভীর ব্যঞ্জনা আমাদের মনের মধ্যে গিয়ে বাজতে থাকে, কিন্তু রূপকের মতো স্বচ্ছ ব্যাখ্যায় তা আমাদের বুদ্ধিতে ধরা দেয় না। তাই আমরা বুঝতে পারি এ নাটক আরো বহুদিন আমাদের মনোরম অতৃপ্তিতে ভরিয়ে রাখবে বিশু পাগলকে তার দুখজাগানিয়া যেমন জাগিয়ে রেখেছিল, এ নাটক আমাদের জাগিয়ে রাখে। সুতরাং সমস্ত দিক বিবেচনা করে একে সাংকেতিক নাটক বলা ছাড়া কোনও উপায় নেই বলেই আমাদের মনে হয়।
তথ্যসূত্র:
| কাব্যজিজ্ঞাসা – অতুলচন্দ্র গুপ্ত | Download |
| কাব্যতত্ত্ব: আরিস্টটল – শিশিরকুমার দাস | Download |
| কাব্যমীমাংসা – প্রবাসজীবন চৌধুরী | Download |
| ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব – নরেন বিশ্বাস | Download |
| ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব – অবন্তীকুমার সান্যাল | Download |
| কাব্যজিজ্ঞাসার রূপরেখা – করুণাসিন্ধু দাস | Download |
| কাব্য-শ্রী – সুধীরকুমার দাশগুপ্ত | Download |
| সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য – কুন্তল চট্টোপাধ্যায় | Download |
| সাহিত্য ও সমালোচনার রূপরীতি – উজ্জ্বলকুমার মজুমদার | Download |
| কাব্যালোক – সুধীরকুমার দাশগুপ্ত | Download |
| কাব্যপ্রকাশ – সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত | Download |
| নন্দনতত্ত্ব – সুধীর কুমার নন্দী | Download |
| প্রাচীন নাট্যপ্রসঙ্গ – অবন্তীকুমা সান্যাল | Download |
| পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা – নবেন্দু সেন | Download |
| সাহিত্য প্রকরণ – হীরেণ চট্টোপাধ্যায় | Download |
| সাহিত্য জিজ্ঞাসা: বস্তুবাদী বিচার – অজয়কুমার ঘোষ | Download |


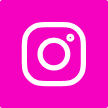


Leave a Reply